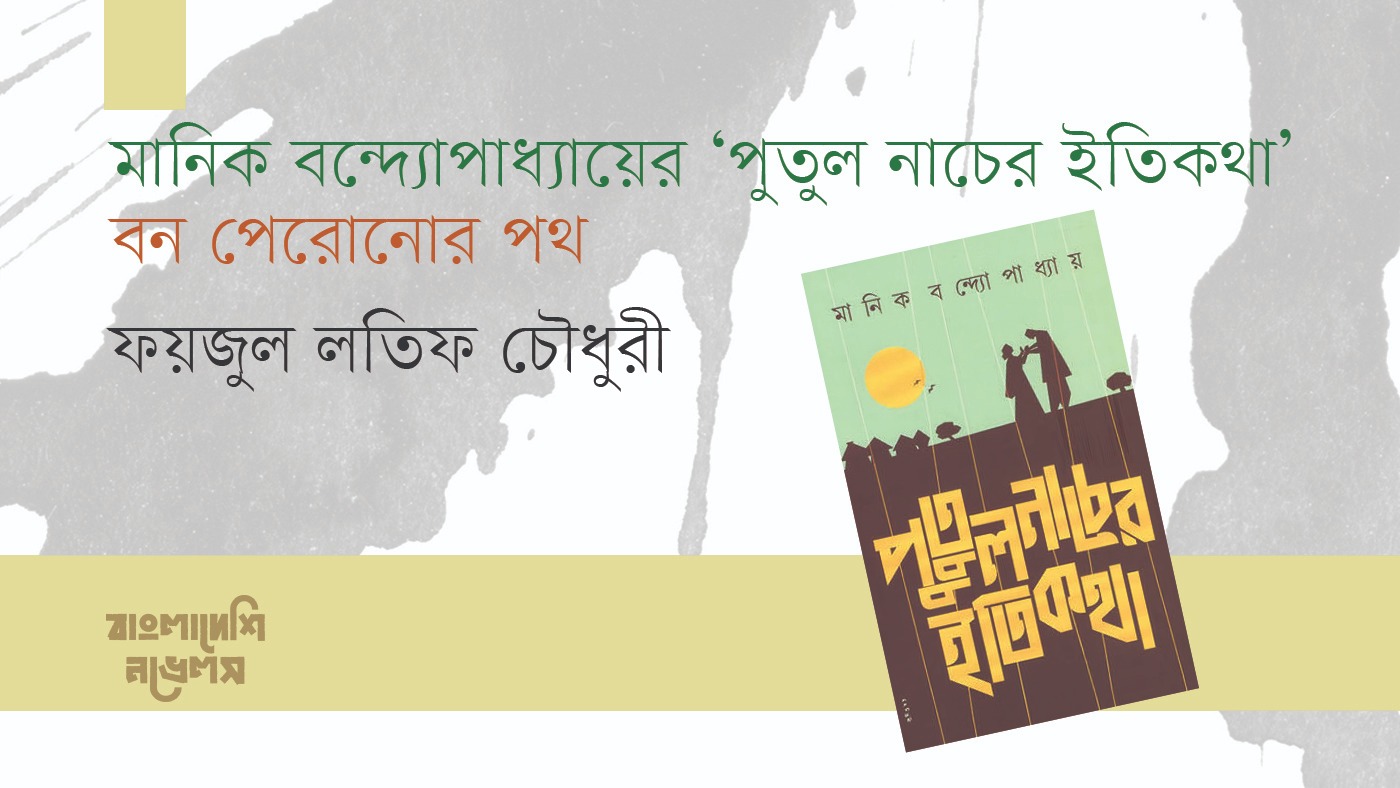‘কান্নাপর্ব’ উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে এর তৃতীয় পৃষ্ঠায় (পৃ ৯) আমি প্রথম থমকে যাই ‘মন্ত্রীসভায় রাজাকারদের কেন বসানো হলো…’ পড়ে। বুঝতে পারি লেখক তেমন একটি সময়ে তাঁর উপন্যাসের ঘটনাকে স্থাপন করতে চাইছেন যেটা বিএনপি-জামাত জোট সরকারের কাল। রাজনীতির এই প্রত্যক্ষতায় উৎসাহিত হয়ে এগুতেই বুঝতে পারি লেখক সাহসী এবং শক্তিমান এবং সে দুটো গুণ তাঁকে এমন একটি কাঠামোতে আটকে রাখছে যেখানে যাত্রাদলের মেয়ে মালতি ওরফে সুজাতা বন্দি সরকারদলীয় এমপি’র পুত্রের প্রমোদখানায়। বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় সে-সংবাদ প্রকাশিত হতেই সরকার প্রধানের উদ্যোগ-তৎপরতা চোখে পরে, যেটি আসলে রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। রাজনীতির কোপানলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতার সে-চিত্র পাঠ করতে করতেই মালতির যাত্রাকর্মীদের মন্তব্য আসে। অন্যান্য প্রিন্সেসদের মন্তব্যগুলো এক ধরনের বিবমিষা জাগাতে থাকে। ভাগ্য ভালো সেটি বেশি দূর এগোয় না। তার আগে আমরা পাই মালতির সাথে এমপি পুত্রের কথোপকথনের কিছু আভাষ। ‘মাইরা গাঙ্গে ভাসায় দিমু’ হুমকি দিতে দিতে যে বলছে ‘তুমি যাত্রাদলে নাচো ক্যান, এইগুলা মহাপাপ। তুমি আর এইসব কইরো না। আমার কাছে থাকো, আমি তোমারে রানির হালে রাহুম’ পাঠককে নাড়াতে থাকে। অসভ্য সমাজের শক্তিধর মানুষদের কর্মকাণ্ডের এই উপস্থাপন এমন এক প্রত্যাশা জাগায় যে আহমাদ মোস্তফা কামাল তাঁর শক্তিমান কলমে এই বইয়ে তা চিত্রণ করবেন। সেটি ভাবতে ভাবতে ১৩ আর ১৪তম পৃষ্ঠা জুড়ে তালিকা সদৃশ বস্তুর ঠাসাঠাসি। এমনভাবেই নবম পৃষ্ঠা পাঠের পর (পৃ ১৫) পেয়ে যাই যেন শক্তির ইঙ্গিত:
… আফটার অল, গল্পটা শুরু করেছি আমি, শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়টাও আমার, মাঝপথে গল্পকে তো আর হারিয়ে যেতে দেয়া যায় না! এই শর্তে যারা গল্পটা শুনতে রাজি আছেন তারা থাকুন, অন্যরা এখানেই থামুন প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ।
না; উপন্যাসে কথকের এমন আচরণ বাংলা সাহিত্যে অভিনব নয়। কিন্তু তবুও বর্তমান আলোচকের ভালো লাগে এ কারণে যে, কথক নিয়ে ঔপন্যাসিকের খেলাটা তার বেশ প্রিয়। প্রিয়তার তীব্রতা এত বেশি যে ২০০০ সালে লিখে ফেলেছিলাম দীর্ঘ ১৮/২০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ ‘উপন্যাসের কথক: প্রসঙ্গ কাঁদো নদী কাঁদো এবং বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ’ [বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ ১ সংখ্যা]। কাহিনির ভেতর দিয়ে একটি প্রতিপাদ্যকে পাঠকের নিকট উপহার দিতে যে ডালিটি দরকার তারও সজ্জা যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটি সকলেরই জানা। আর সে কারণেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম থেকেই বহুরূপী কথকের আবির্ভাব ঘটেছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে কথকও নতুনরূপের আশ্রয় নিয়েছেন। আর কথক নিয়ে এই খেলাটা আমার এতো প্রিয় যে
কোন উপন্যাসেই সাধারণ কথন-ভঙ্গীর ব্যত্যয় দেখলেই আমি শিকারী কুকুরের মতো কর্ণ-জাগা হয়ে উঠি, যেমনটি কান্নাপর্ব-র এই পর্যায়ে এসে আমি হতে থাকি।
আর এর পরপরই লেখক পাঠককে নিয়ে যেতে থাকেন মানিকগঞ্জের সেই এক গ্রামে- মানিকগঞ্জ বাসস্টান্ড নেমে, রিকশায় বউথা ঘাট হয়ে, খেয়ায় কালীগঙ্গা পার করে, সামনের গ্রাম আন্ধারমানিক … এভাবে যেতে যেতে মানিকনগর গ্রামের ঋষিপাড়ায়। সেখানে অকালবৃদ্ধ হরিচরণ, অর্থাৎ মালতির বাবাকে আমরা পাই যিনি কাঁদছেন। আর এমন সময়েই ঔপন্যাসিক জানিয়ে দেন ‘এই গল্প এখন থেকে আপনি তাদের কাছেই শুনবেন…’। এই ‘তারা’ হলো মানিকগঞ্জ শহরের কিছু শিক্ষিত বেকার যুবক যারা শিল্পসাহিত্য চর্চা করে, কিন্তু তেমন কিছু করে উঠতে পারছে না বলে ব্যর্থতার যন্ত্রণায় ভোগে। একক কথক থেকে যৌথ কথকের এই পালাবদল রোমাঞ্চকর।
তেমন মুহূর্তেই যুবকেরা জানায় যে তারা কান্নার উৎস সন্ধান করতে করতে ঐ গ্রামে এসেছে। তারা আবার বলে যে কালীগঙ্গা কাঁদে। তাঁরা সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর লেখা ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসের কথাও বলে। পাঠক টের পান, অনেক কসরত চলছে কথক নিয়ে। একটার ভেতর ঢুকে পড়ছে আরেকটা। এসে পরে ‘আমরা জানতে পারি…’ (পৃ ১৭), রোম দাড়িয়ে যায় আমার। বুঝতে পারি শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) এসে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’ (১৯৯৫) পড়তে গিয়ে আমার এমন শিহরণ হয়েছিল মনে পড়ে। লেখকীয় বর্ণনাশৈলীর অভিনবত্বে শহীদুল জহির দুর্দান্ত পারঙ্গমতা দেখিয়েছিলেন। কামালেও তা দেখি আমরা।
১৬তম পৃষ্ঠায় হরিচরণ দাসের যে কান্না দিয়ে আমার গল্পের কাঠামোকে ছুঁতে চাই, সেখানে ক্রমে এসে দাঁড়াতে থাকে সংখ্যালঘু হরিচরণের অসহায়ত্ব। ঋষিপাড়ার দারিদ্র্যের ভেতর সুন্দরী কন্যা মালতিকে রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা হরিচরণকে দুমড়াতে থাকে। ‘একে তো সুন্দরী, তারপর আবার গরীব, তার ওপর আবার হিন্দু…’ এই বিবিধ যন্ত্রণার ভেতরে মালতির আর্তনাদ ‘দাদারা আপনারা আমারে বাঁচান, নাইলে আমি গলায় ফাঁস দিয়া মরুম’ (পৃ ২০)। এমন পরিস্থিতিতে ঐ যুবকেরা মালতিকে নিয়ে সোনালী যাত্রাদলের মালিক মধুবাবুকে ধরে এবং সেখানে তার আশ্রয় হয় এবং মালতি যাত্রাদলের একছত্র সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠে।
এসব আসলে অনেক আগের কথা। এমপি পুত্র মালতিকে জোর করে আটকে রাখার অনেক আগে। ঘটনা বিন্যাসে এই বৈচিত্র্য কথকবৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে চলে এক অভিনবত্ব। ২৪তম পৃষ্ঠায় এসে সেখানে সংযুক্তি ঘটে ইতিহাসের। কথক যুবকেরা সে-ইতিহাসের পাতা ছুঁতে ছুঁতে পৌঁছতে চায় নতুন এক সত্যে যে সত্য থেকেও অদৃশ্য। ঐ যুবকেরাই উদ্ভাসন ঘটায় এমন বোধের যে নদী-সিকস্তি এ অঞ্চলের পূর্বপুরুষদের গ্রামগুলোর নাম হরিণা, উদাসপুর, আন্ধারমানিক হওয়ার পেছনে তাদের কবিত্ব নিশ্চয়ই কাজ করেছিল। তাদের বোধ থেকে উৎসারিত হয় সেই সত্য যা আমরা সাধারণত স্বীকার করি না। ইছামতির পাড়ে দুই হিন্দুপাড়ার মাঝখানে এক মুসলমানপাড়া। মানুষগুলো মিলেমিশেই থাকলেও
ঠিক সামাজিক সম্পর্ক সেখানে নেই। বিভিন্নতা হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক নয় শুধু, বিভিন্নতা হিন্দুতে-হিন্দুতে, মুসলমানে-মুসলমানেও। এবং এমনভাবেই নির্মিতি পেতে থাকে মানিকনগর বা উদাসপুর গ্রামের কথা, সেসব গ্রামের ঋষিদের কথা।
চতুর্থ অধ্যায়ে এসে উদাসপুরের স্বচ্ছল ব্যবসায়ী বরুণ কুণ্ডুর সঙ্গে পরিচিত করানো হয় পাঠককে। সে সঙ্গে যুক্ত হয় এলাকার মুসলমান ছেলে মঈনুদ্দিনের আত্মহত্যার কথা। সে আত্মহত্যার সাথে কারণ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন জনের মতগুলোও উপস্থাপিত হতে থাকে, যেমনটি আমরা ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’-তে পেয়েছি।
… কেউ বলে অভাবের তাড়নায় ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে… কেউ বলে – ছেলেটা লেখাপড়া শিখেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনলো’ (পৃ ৩১)।
আর এসবের পর আমরা শুনতে পাই বরুণ বাবুর মেয়ে পুতুলের সাথে মঈনুদ্দিনের প্রেম ছিল। এবং লেখক অবিশ্বাস্য দক্ষতায় পাঠককে বারবার চমকাতে থাকেন এ পর্বে। অবাক বিস্ময়ে কাহিনির অভিনবত্ব বিকশিত হতে থাকে। রাতের বেলায় আসার জন্য পুতুলই আসলে মঈনুদ্দিনকে বলেছিল বরুণের প্ররোচণায়। প্রথমে মনে হয় ধর্ম বিষয়টির কারণেই বরুণ কুণ্ডুর আপত্তি ছিল। একটু পরেই বোঝা যায় বরুণ কুণ্ডু সেদিকটার কথা ভেবেই দেখে নাই। পরে জানা যায়, বিষয়টিতে রয়েছে একটি ভিন্ন মাত্রা – পুতুল হিজড়া। একটি পিতৃহৃদয়ের সকল আবেগ দিয়ে মথিত করা এ অংশটি। আর এ অংশটি যখন শেষ হয় (পৃ ৩৮) যুবকেরা বলে ‘দরজা খুলে উঠোনে নেমে দেখি, চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চরাচর …, আমাদের ঘোর লাগে’। স্মরণ করা যেতে পারে যে, চাঁদের আলোয় অনুরূপ ঘোর লাগার বিষয় সে রাতে পূর্ণিমা ছিলতেও পাঠক পড়েছেন। চন্দ্রালোকিত রাতে এমন ঘোর লাগার কথা নাসরীন জাহানের (জন্ম ১৯৬৫) ‘চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার’ (১৯৯৫) বা তার তিন দশক পূর্বে রচিত ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪)-তেও প্রকটভাবে উপস্থিত।
বরুণ কুণ্ডুর এই উপকাহিনি ছাড়াও গ্রন্থে আরও অনেকগুলো উপপ্রসঙ্গ বর্তমান। পাল পাড়ার জয়দেব পালের কথা তেমনই একটি। এমপি পুত্রের হারেমখানা থেকে বেড়িয়ে আসার এ পর্যায়ে হাসিব ঐ এলাকায় আসেন। উদ্দেশ্য যাত্রাদলের মানুষদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখবেন, আর সে কারণেই কিছুদিন থাকবেন সোনালী অপেরার সাথে। ভেতরের উদ্দেশ্য হয়তো একই – শিল্পের উৎসকে খোঁজা। তেমন শিল্পই তো প্রতিমা শিল্প, যার দক্ষ কারিগর জয়দেব পাল। আরো আসে, পরাণ মণ্ডলের কথা যিনি কর্নেট শিল্পী, আসে হরিচরণ অর্থাৎ মালতির বাবার কথা, যাঁর মৃদঙ্গ কথা কয়। সে সবের সঙ্গে এসে যুক্ত হয় বাধইমুড়ি দরবার শরীফের আসাদ ভাই। আসাদ ভাইয়ের সঙ্গে জামিল ভাইয়ের আলাপের ভেতর দিয়ে মূর্ত হয় সে অঞ্চলের বাউলের শতশত বর্ষ পূর্বের লোক-ঐতিহ্যের কথা। সে-ঐতিহ্যের মানুষরাই তো ধর্মের একটি লৌকিক ব্যাখ্যা দান করেছিল, আর সে-কারণেই অঞ্চলের মানুষ সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান না হয়ে বরং মানুষ হওয়ার পথে সামিল হয়েছিল।
বাংলার লোক-ঐতিহ্যের বিপুল যে সম্ভার, সে-সম্ভারের অবহেলিত এক অধ্যায়ে পালদের অবস্থিতি। অথচ পালদের প্রতিনিধি হিসেবে জয়দেব পালের উচ্চারণ যে কোন বোদ্ধা মানুষকে স্তম্ভিত করতে যথেষ্ট। বিস্ময়কর সে-সকল উচ্চারণের অন্তরালের শক্তি কিন্তু লোকশিল্পের মজ্জার ভেতর। শিল্পের জন্যে শিল্পীর ভালোবাসা থাকবে, কিন্তু লোভ থাকবে না – এই যুগান্তকারী বোধ ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল বলেই হয়তো সহস্র সহস্র বছর ধরে এ অঞ্চলে প্রতিমা শিল্পের এমন অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। সে-বোধের ইতিহাসকে উপন্যাসের আত্মস্থ করে লেখক অচিন্তিতপূর্ব এক সৌম্যের পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। হাসিব জামালের মুখ নিসৃত ‘শিল্পীর জন্য ওরকম ঘোরলাগা এক অলৌকিক অপেক্ষা দরকার’ (পৃ ১১৭) এমন কথা সর্বকালের, সর্বদেশের জন্য আবশ্যিক এক বোধ।
আবার ধরা যাক, ঋষিপাড়ার পরাণ দাদুর কথা। কর্নেট বাজান তিনি। বাজনাটি এত হৃদয়স্পর্শী যে সেটি থামলে হাসিব জামালের মত শহুরে সংস্কৃতিবান সাহিত্যিকের মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মুচি পেশার সে মানুষটার পা ছুঁতে। দুই পৃষ্ঠা জুড়ে মালতির বাবা হরিচরণের মৃদঙ্গ বাজনা যেন পাঠককে মোহমুগ্ধ করে রাখে। ‘কথা ক মৃদঙ্গ’ বলে তো তিনি ক্রমে ক্রমে মৃদঙ্গতেই লীন হয়ে গেলেন আর তার মৃদঙ্গ কথা বলতে শুরু করলো। এ যেন গ্রাম্য এক বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গ্রামের এক শিল্পীর জাদু সৃষ্টি। মৃদঙ্গের এমন পারঙ্গমতা হরিচরণের দীর্ঘ ঐতিহ্য, অন্তর্গত সম্পদ। সে-দক্ষতা এত নিখুঁত যে মৃদঙ্গ জামিল ভাইয়ের সামনে গিয়ে ‘হাসিব জামিল’ বোল হয়ে বাজাতে থাকে। আর এক পর্যায়ে ‘মালতি মালতি মালতি’ বলে মৃদঙ্গ করতে থাকে মালতি-বন্দনা, বরুণ কুণ্ডুর কাছে গিয়ে বরুণ-বন্দনা, পুতুল-বন্দনা – যেন মানুষগুলোতে ঘোরগ্রস্থ করে তোলে।
এই যে এতসব অনুযজ্ঞ – এগুলো আসলে মূল যে-প্রতিপাদ্য ঘিরে তা হলো বাংলা অঞ্চলের দীর্ঘলালিত সাংস্কৃতিক চর্চার উৎস সন্ধান এবং উৎসারণ বন্ধের কারণে সৃষ্ট আর্তনাদ। সে আর্তনাদ অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতিকে কাঁদিয়ে চলেছে নিরন্তর। সে আর্তনাদের ব্যাখ্যা আছে হাসিব জামিলের কাছে যে ব্যাখ্যা তিনি উৎসাহী যুবকদের দেন। পাঠকের কাছেও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয়ভাবে মৌলবাদ পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় তারা আক্রমণ করছে জনগণের লোক-ঐতিহ্যকে, যে ঐতিহ্যে ভাঙন না ধরলে মৌলবাদ বাংলার মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না কখনোই।
এই সব অনুযঙ্গের চেয়ে বড় হয়ে বোধ করি দেখা যায় মধুবাবু, অর্থাৎ সোনালী অপেরার অধিকারিকের কথাÑ যার যাত্রাদলে মালতি শিল্পী। দলের মালিকের যাত্রাদলের আসার নিশ্চয়ই একটা ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস আছে চার-পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে (পৃ ৮৮-৯২)। বোঝা যায় শিল্পের প্রতি তার অনুরাগের গভীরতা যার কারণে তিনি হাসিমুখে বাড়ি ত্যাগ করে, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে শিল্পচর্চা তথা যাত্রাশিল্পচর্চায় নেমে পড়েছিলেন। যুবকদের সাথে মধুবাবুর দীর্ঘ আলাপের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে সে-ইতিহাসের কথা। তবে সে-আলাপে প্রেক্ষাপট যখন রচিত হয় তখনই কিন্তু প্রকাশ পেয়েছিল মধুবাবুর দার্শনিক প্রজ্ঞা এবং শিল্পজ্ঞানের গভীরতা, যাত্রাপালার উদ্ভব বিষয়ে তাঁর সুদৃঢ় উচ্চারণ:
… যাত্রাপালাতো আসলে ভদ্দরলোকগো কথা ভাইবা লেখা অয় না। এইটা গরীব মানুষের থিয়েটার। দর্শকরা মঞ্চে আইসা নাটক দেখবো এইরম না ভাইবা মঞ্চরেই দর্শকগো কাছে নিয়ে যাইতে অইবো – এই ভাবনাই কাজ করছে মনে হয়’ (পৃ ৮৪)।
তেমন একজন মধুবাবু এবং যাত্রাদলের প্রেক্ষাপটেই স্থাপিত মালতি-কাহিনি যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে হাসিব জামাল। শহুরে এই কবি-সাহিত্যিক ধরনের মানুষটি কিন্তু উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ অবধি উপস্থিত – কিন্তু তিনি প্রধান কোনো ভূমিকা পালন করছেন বলে আপাতভাবে মনেই হয় না। গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয় যে এই হাসিব জামাল মানুষটি জড়িয়ে আছেন ‘কান্নাপর্ব’-র প্রতিটি পর্যায়ে – তাকে বাদ দিয়ে সে-উপন্যাসের কাহিনির অগ্রসরণই তো অসম্ভব। হাসিব জামালই তো এই উপন্যাসের মূল বোধ অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতির বিলুপ্তির বেদনার খননকারী, ব্যাখ্যাদানকারী, রক্ষা প্রচেষ্টাকারী! অথচ হাসিব জামালের সে সব কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে যে মানুষটি সে হলো মালতি – যাত্রাদলের যে শিল্পী, প্রয়োজনে নাচিয়ে, যার বাবা মৃদঙ্গ শিল্পী হরিচরণ। শিল্পী এবং তার শিল্প – দুটি বিষয়েরই এক সংকট কালকে চিহ্নিত করতে আহমাদ মোস্তফা কামালের এ উপন্যাস রচনা।
এই যে কেন্দ্রিয় চরিত্র মালতি, সে কিন্তু সাধারণ মেয়ে, কিন্তু তার কষ্টতা অসাধারণ, আর তার কষ্টের চিত্রণটিও অসাধারণ। আর সে-কারণেই মালতিকে এমপি-পুত্র আটকে রেখে ভোগ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের প্লট ছড়াতে থাকে বৃত্তাকারে। যেমন সেটি অতীতে যায়। একই সাথে প্রসারিত হয় ভবিষ্যতে। যেমনভাবে সে রাজনীতি-সমাজনীতিকে স্পর্শ করে, তেমনি স্পর্শ করে মননের বহুবিধ স্তর। সে-মননে সঙ্গী যেমন নাগরিক সংস্কৃত জন, তেমনি গ্রামজ প্রান্তজনও বটে।
‘কান্নাপর্ব’ পড়ার কালে আমার বারবার বাংলাভাষায় লেখা জাদুবাস্তবতা ধারার উপন্যাসগুলোর কথা মনে পড়েছে। পড়েছে এ কারণে যে জাদুবাস্তব উপন্যাসেও লেখক যে বর্ণনাকৌশল ব্যবহার করেন তেমন কিছু কৌশলের ব্যবহার এ উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এমনটি নয় যে, ‘কান্নাপর্ব’ একটি জাদুবাস্তব উপন্যাস, নয় এ কারণে যে বাস্তবকে প্রকাশের প্রত্যক্ষ রীতির পথে যে রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এক সময় ল্যাটিন আমেরিকান উপন্যাসে জাদুবাস্তব ধারা তৈরি করেছিল তেমন প্রতিবন্ধকতা আহম্মদ মোস্তফা কামালের উপন্যাস রচনায় ঘটেনি। বাস্তবকে প্রত্যক্ষভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমি নাসরীন জাহানের ‘চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার’ উপন্যাসের কথা স্মরণ করতে চাই। বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশে অসম্ভব জেনেই নাসরীন সে-উপন্যাসে একটি প্রতীকী এবং রূপকথার কাহিনি ফেঁদেছেন। সফল সে উপন্যাসটিতে যদিও কথনশিল্পের চাতুর্য তেমনটি পাওয়া যায় না, যেমনটি শহীদুল জহিরের ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’তে পাওয়া সম্ভব। এবং ‘কান্নাপর্ব’ও কথনশিল্পের ঐ চাতুর্যকে মাধুর্যপূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছে।
বিশেষ করে লেখকের বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে ঋষিপাড়ার সেই মানুষদের কথা, যে সম্প্রদায়ের মানুষ দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিলেন। তাদেরই কেউ কেউ মিলে একটা বাজনা দল
গড়তেন। যে দল দূরদূরান্তে গিয়ে বিয়ে-অন্নপ্রাশনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাদ্য বাজাতেন। তেমন প্রতিটি দলেই তো একজন করে পরাণদাদুও ছিলেন। যেমন প্রতিটি অঞ্চলেই ছিল পাল পাড়া, যাদের মধ্যে একটি-দুটি পরিবার জয়দেব পালের মত প্রতিমার শিল্পী। কী মমতায়, কী যতেœ সে-শিল্পীদের কাজ চলতো সারা দেশ জুড়ে। হরিচরণের মত মৃদঙ্গ শিল্পীও বাংলার আনাচে কানাচে লালিত হয়েছেন কতো কাল ধরে। অথচ মাঝখানের চার দশক পেরুতেই বাঙালির সে-সকল ঐতিহ্যের বিলুপ্তি ঘটেছে দেশের অধিকাংশ অঞ্চল থেকেই। আর সে-বিলুপ্তিই কারণেই তো নদীর কান্না! নদী যে অঞ্চলের, সে-অঞ্চলের লোকবিশ্বাসী মানুষ নদীর সে-কান্না শুনতে পান। কিন্তু ‘কাঁদো নদী কাঁদো’-র পাঠকমাত্রই কান্নাপর্ব পড়ার কালে ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসে বর্ণিত কান্নার কথাকেই স্মরণ করবেন। গভীর অনুসন্ধানী পাঠক হয়তো এই দুটি উপন্যাসের বিবৃত কান্নার মধ্যে সাজুয্য খুঁজতেও চাইবেন। আর তখনই ঔপন্যাসিক হিসেবে কামালের কৃতি সামান্য হলে বিবর্ণ হতে বাধ্য।
২০০২ সালের আগন্তুক থেকে ‘অন্ধ জাদুকর’ (২০০৯) হয়ে এ বছরের ‘কান্নাপর্ব’ পর্যন্ত আহমাদ মোস্তফা কামালের ঔপন্যাসিক যাত্রা। ২০১২ সালেই রয়েছে তাঁর আরেক উপন্যাস ‘পরম্পরা’। ‘আগন্তুক’-এই তাঁর ভাষা সুখদায়ী, বর্ণনা প্রীতিকর। দীর্ঘ একটি প্রেক্ষাপটকে আয়ত্বে আনার চর্চা শুরুর কাল তাঁর। সে চর্চা চার বছরের প্রচেষ্টায় (অন্ধ জাদুকর-এর শেষে উল্লেখ আছে যে সেপ্টেম্বর ২০০৪ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ এ উপন্যাসের রচনাকাল) সংহত রূপ পেয়ে গেছে দ্বিতীয় উপন্যাসেই। ‘অন্ধ জাদুকর’-এই তিনি কথক নিয়ে খেলা শুরু করেন। আগন্তুক থেকেই তাঁর উপন্যাস বড় বেশি ব্যক্তিক অনুভূতিকে আঁকড়ে ধরে রচিত। এক ধরনের আত্মজৈবনিক ‘আগন্তুক’-এর মতো না হলেও ‘অন্ধ জাদুকর’ এবং ‘কান্নাপর্ব’ আত্মজৈবনিক উপাদানে ঠাঁসা। তবে ‘কান্নাপর্ব’-তে এসে সেখানে সামগ্রিক সমাজ এবং সমাজ-নিষ্ঠ দায়বোধকে দায়িত্বে নিয়েছেন কামাল। আর তাই বাঙালির সহস্র বছরের লালিত লোকজ শিল্পের এক ধরনের অনুসন্ধানে নিয়োগ করেছেন নিজেকে, ব্যথিত চিত্ত তাঁর খুঁজে ফেরে বাঙালির ঐতিহ্য, ঐতিহ্যিক সম্পদ যা ঐতিহাসিক কাল ধরে বাঙালির মননকে ঋদ্ধ করেছে। আর এভাবেই কান্নাপর্ব হয়ে উঠেছে মূল্যবান এক পাঠ – বিষয় প্রশ্নে, শৈলী প্রশ্নেও।
তেমনই একটি পরিস্থিতিতে সম্প্রতি আমার ‘বাংলাদেশের কয়েকজন ঔপন্যাসিক’ শিরোনামের ২০০৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির পরিমার্জনার প্রশ্ন আসে। সাত বছর আগের সে-গ্রন্থে অনেক শক্তিমান ঔপন্যাসিককে আমি অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি শুধুমাত্র তাদের সকল অথবা প্রধান উপন্যাস আমাদের পড়া না থাকায় বা দীর্ঘকাল আগে পাঠ থাকলেও সাম্প্রতিক পাঠ না থাকায়। সে-গ্রন্থের ঔপন্যাসিক-তালিকায় শেষ লেখকটি ছিলেন নাসরীন জাহান। এরপর আর কাকে কাকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের রচনা আবশ্যিক, এমন ভাবনা যখন ক্রিয়াশীল তখন যে কয়টি নাম বিবেচনা করতে শুরু করি, তাদের একজন হলেন আহমাদ মোস্তফা কামাল। ‘কান্নাপর্ব’ পাঠকালেই আমি অনুধাবন করতে থাকি একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের উপন্যাসে যে গুটি কয়েক শক্তিমান উপন্যাস রচিত হয়েছে তার অন্যতম একটির লেখকের অন্য উপন্যাসগুলো না পড়া থাকা এতদিন আমার কত বড় সীমাবদ্ধতা ছিল!
আহমাদ মাযহার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক ‘বইয়ের জগৎ’-এর নবম সংকলন (মে ২০১২)-এ প্রকাশিত।