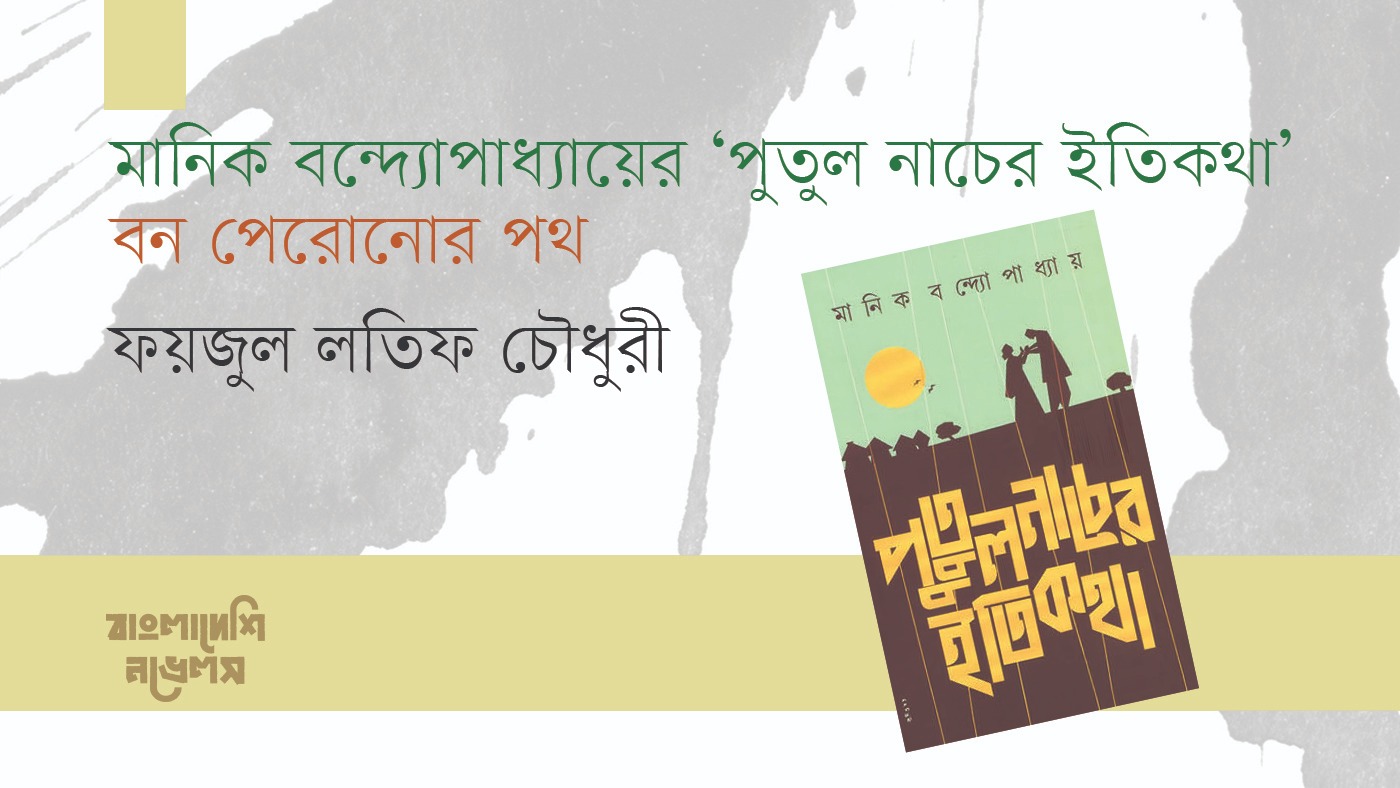বহু রকমের কার্যকারণ সম্মত বা অসম্মত সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে সৈয়দ ওয়ালীউলাহর (১৯২২-৭১) ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮) বাংলা ভাষায় রচিত সুসংহত উপন্যাসগুলির অন্যতম। বিষয় ও শৈলী উভয়গতভাবেই সুলিখিত ও সুগ্রথিত এ উপন্যাসের প্রতিটি বাক্য এমনকি শব্দও এত বেশি অর্থবহ যে আর কোন বাংলা উপন্যাসে তেমনটি হয়েছে বলে মনে হয় না। জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) থেকে অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) হয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-৯৭) পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের মহীরুহদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রেখেই বলতে চাই দার্ঢ্য ভাষায় নির্মিত সুদৃঢ় কাঠামোর দীর্ঘ উপন্যাস বাংলা ভাষায় খুব বেশি লিখিত হয় নি। নবাগত তরুণ ঔপন্যাসিক শেখ আলমামুনের একমাত্র উপন্যাস ‘নুহূলের মনচিত্র’ অনেক বিচারেই হ্রস্ব সে তালিকায় স্থান দিতে বহু পাঠকের আশঙ্কা থাকলেও বর্তমান আলোচক শঙ্কাহীন।
‘নুহূলের মনচিত্র’ শুরু হয়েছে ঘোর লাগা এক বাস্তবতায়, যে ঘোর উপন্যাসের শেষাবধি বর্তমান। শুরুর ঘোর অন্তত ত্রিশ পৃষ্ঠা চলতে থাকার পর টের পাওয়া যায় গল্পের সুতোর অস্তিত্ব – যে অস্তিত্বের কথক আসলে নুহূল নিজেই। স্পষ্ট হয় কংসের পাড়ে অনাবিষ্কৃত এক জাতিসত্তার অস্তিত্ব যা নলুয়া সম্প্রদায় বলে পরিচিত। সে সম্প্রদায়ের পাঁচ বছরের শিশু নুহূলকে আবৃত করে তার যে পরিবার সেটি ক্রমশ প্রকাশমান। সাঁইত্রিশ বছরের তারাব অর্থাৎ নুহূলের বাবার কৈশোরও প্রতিতুলভাবে উপস্থাপিত।
ঠিক যখন মনে হচ্ছিল নুহূলের শৈশব এবং কৈশোর উপস্থাপিত হওয়ার উপক্রম তখনই তারাবের শৈশবকাল সামগ্রিক চিত্রণে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটায়। বাঙাল-নলুয়া দ্বন্দ্বের সামান্য ইঙ্গিত ভাসমান হতেই সেখানে ডেভিস মরিসের উপস্থিতি নতুন দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেয়; যেমনভাবে গারো কিশোরীর সাথে তারাবের প্রেমেও রয়েছে ভিন্নতর দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা। সতেরো-আঠারো বছরের তারাবের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নিজেকে জানার, নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের জানার কৌতুহল। তারাবের ভেতর একজন দার্শনিক মানুষ, অনুসন্ধিৎসু মানুষকে উপস্থাপনের ফলে একটি কার্য-কারণ খুব প্রকট হয়, তা হলো নুহূল যখন ঈশ্বর-পৃথিবী-মানুষ-প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির ভেতর প্রবেশ করতে থাকে এবং সে সকল বিষয়ে তাঁর একান্ত ভাবনাগুলোর প্রকাশ ঘটায় তখন তাকে ‘অস্বাভাবিক’ বা ‘অবাস্তব’ আখ্যায় দূরে ঠেলার কোন উপায় থাকে না। “…তার নিঃশ্বাসের বেগ, শারীরিক অস্থিরতা তারাবকে সচকিত করে। নূহূল জাগ্রত। এবং বুঝতে পারে কী কৌতুহলী উদ্দীপনা তার ছেলেকে জাগ্রত রেখেছে। ছোট্ট ধমনিতে এক অভিন্ন স্রোতের প্রবাহ উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না তারাবের” (পৃ. ৬১)।
ছয় বছর তারাব মরিসের সাহচর্যে দেখতে পায় আদিবাসীদের দলে দলে খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া। তারাবের প্রশ্ন ‘মানুষ কি মানুষকে প্রভাবিত করে শুধু একে অন্যের দীনতা-দুর্বলতার সুযোগেই?’ “দুনিয়ার সবখানে, সবকিছুতে কি শুধু একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা, পরাস্ত করারই প্রচেষ্টা?’ তারাবের মনে পড়ে বাঙালদের সাথে নলুয়াদের সব দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের কারণ ঐ একই – একে অন্যের উপর প্রভাব খাটানোর লড়াই” (পৃ. ৬০)।
নলিবাঁশ সংগ্রহ এবং তা দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী বোনার ব্যবসা যে সম্প্রদায়ের মানুষদের – তাদের পূর্বপুরুষের অনুসন্ধানে তারাব ব্যাকুল বোধ করে। ভারতের উড়িষ্যা নামক রাজ্যে সে পূর্বপুরুষ থাকার একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত মরিস তারাবকে জানাতেই, পরদিন মিশনারি থেকে পালিয়ে, সোমেশ্বরী নদী আর গারোপাহাড় টপকিয়ে সীমানার ওপারে তারাব। সাত বছরের অনিশ্চিত জীবন কাটিয়ে উনত্রিশ বছর বয়সে ফিরে আসে সে। ততদিনে নলুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ পেশা থেকে বিচ্যুত হওয়া শুরু করলেও যেটি ততদিনেও বদলায় না তা হলো বাঙাল-নলুয়া বিদ্বেষ। তারাবের মনে হয় সে বিদ্বেষ “বরং আগের চেয়ে প্রখর ও কৌশলপূর্ণ হয়েছে। বাঙালরা এখনো তাদেরকে নলুয়াই মনে করে। বাঙাল ও নলুয়া এখনো একত্রে বাঙালি হয়ে উঠতে পারে নি” (পৃ. ৬৩)। পেশা বদলে ঝিনুকের খোলস ভেঙে মুক্তা আহরণের কাজ বেছে নেয় তারাব। বিয়ে করে। স্বপ্ন দেখে “বন্য জীবনের গন্ধ থেকে ছেলেকে দূরে রাখতে হবে। তাকে সাহেবি কায়দায় মানুষ করতে হবে। শিক্ষায়, জ্ঞানে, চলনে-বলনে তার ছেলে হবে সবার থেকে আলাদা, সবার উপরে” (পৃ. ৬৫)।
উপন্যাসের শুরুতে কথক দায়িত্বে নুহূল। ঘোরাক্রান্ত নুহূলের সে কথনে সংমিশ্রণ সংলাপের।
“‘আমি! কে!’
‘কে তুমি!’”
নুহূলের এবং অন্য একটি কণ্ঠের এই ক্ষুদ্র সংলাপ, প্রকৃতপক্ষে, মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন তোলে যার উত্তর প্রায় সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসে সন্ধান চলেছে। বোঝা যায় সংলাপে অংশগ্রহণকারী দ্বিতীয় মানুষটি নুহূলের করোটিতে আশ্রিত এক নারী। অথবা নারী নয়, নুহূলের অস্তিত্বেরই আর এক প্রকাশ। একই অস্তিত্বের দুটি প্রকাশের এ সংলাপ ক্রমশ জটিল হয় – দর্শনের জটিল প্রশ্নকে আশ্রয় করে। প্রত্যেকের বক্তব্য দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। এবং নুহূলের দূর স্মৃতিতে যখন তার নিজের শৈশব স্পষ্টতর, কথকের দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বদর্শী লেখক নিজেই। ছেলেকে নিয়ে তারাবের স্বপ্নের কথা জানানোর পর আবারো কথকের ভূমিকায় নুহূল। নৌকায় চেতন-অবচেতনের দোলাচলে নুহূলের দার্শনিক ভাবনাগুলোর বিস্তার দীর্ঘতর, গভীর অনুসন্ধানী। যেমন:
“আমরা কথা বলছিলাম মানুষের শিকড়, মানুষের উৎসমূলের প্রসঙ্গ নিয়ে, তাই না? এখন আমাদের দৃষ্টিটাকে যদি আরো একটু গভীরে নিয়ে যাই, ব্যক্তিগত কিংবা জাতিগত মানুষের উৎসমূল থেকেই সামগ্রিক মানবসত্তার উৎসমূলে অর্থাৎ সেই অবস্থায় যেখানে নির্জিব বস্তু সজীব বস্তুতে অর্থাৎ প্রাণে পরিণত হয়েছিল। … এক কথায় বস্তুর মধ্যে চেতনার আবির্ভাব ঘটল। চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তথ্য বিনিময় ক্ষমতা। এই তথ্য বিনিময় ক্ষমতা যার যত বেশি সে তত বেশি চেতনা সম্পন্ন; এমনকি পারিপার্শ্বিকতায় তার প্রভাব বা প্রকৃতিতে তার অবস্থান তত সুদৃঢ়। বস্তুর অভ্যন্তরে চেতনার প্রগাঢ়তা, বিস্তৃতি কিংবা সক্রিয়তা অনুযায়ী বিন্যস্ত হয় তথ্য এবং এর উপরই নির্ভর করে একটা সজীব সত্তার শক্তি-সামর্থ-কার্য ক্ষমতা এমনকি দৈহিক আকার আকৃতিও। আবার এও বলা যায়, চেতনা বা তথ্য বিনিময় ক্ষমতা অর্থাৎ প্রকৃতিকে জানার ক্ষদতার ভেতর দিয়েই একটি সজীব সত্তা তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে কিংবা বিকাশ ঘটাচ্ছে। একটি সজীব বস্তু এই বিশ্ব প্রকৃতির অংশ, অর্থাৎ বিষয়টাকে কি এভাবে বলা যায় না যে, প্রকৃতিই প্রকৃতিকে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে জানছে একটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।” (পৃ. ৭১)
উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও তা এড়ানোর উপায় ছিল না। যেহেতু নুহূলের মূল প্রশ্ন দর্শনগত, যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সারা উপন্যাস জুড়ে নুহূল অক্লান্ত এবং পাঠককেও করে তার অনুসন্ধানের সহযাত্রী। সে নিজেও আমাদের জানায় যে সে আসলে তার লব্ধ জ্ঞানকে একটি গ্রন্থে উপস্থাপন করতে চায়।
উপন্যাসের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ ‘গোপন পদচিহ্নের ঐকতান’ এবং পূর্ববর্তী ভাগ ‘কংস-ভোরে নলুয়া’য় উপস্থাপিত তারাবের শৈশবের সমতালে নুহূলের শৈশব। সাধারণ নলুয়া সন্তান তারাবের মধ্যে যে অসাধারণত্বের প্রকাশ ঘটেছে, নুহূলে সে সকল অধিকতর শক্তিমান। অসাধারণ সুখপাঠ্য নুহূলের শৈশবকে নিয়ে লিখিত পৃষ্ঠাগুলো। ক্রমে তা কৈশোরের দিকে ধাবমান। ছোট সমাজটি সামগ্রিকতায় যেন উঠে আসে নুহূলের বর্ণনায়। সে অঞ্চলে খরা-বন্যার কথা, মুক্তা অনুসন্ধানী বাবার কথা। আমরা পেতে থাকি সেই সব মানুষদের যারা নির্মাণ করে নুহূলের কৈশোর। সহপাঠী সিদ্দিক যে কিনা নলুয়া আর বাঙালদের বাইরে একমাত্র ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ের । হরিদাশ বাবু যে কিনা নুহূলকে উপাধি দেয় ‘পঙ্খিরাজ’, পাখির সুর কণ্ঠে ধারণে নুহূলের সহজাত ক্ষমতার কারণে।
পরের ভাগে শিরোনাম ‘যে বয়স কোন গুরুত্ব বহন করে না’। যদিও তাতেই ঘটেছে সব গুরুত্বপূর্ণগুলো। কৈশোরের সে সময়েই তো চতুর্পাশের অভিঘাত বেশি। সে সময়েই তো প্রেম ও শরীর বিষয়ক প্রশ্নগুলো বেশি উচ্চকিত। ‘বাঙাল মেয়ে এক নলুয়ার হাত ধরে পালিয়েছে’ জানতে জানতে আমরা নুহূলের নিজের ঘটনার প্রত্যক্ষ করি। বড় চাচার সুন্দরী মেয়ে নার্গিস আপার সাথে অতীন্দ্রিয় এক যৌন সংসর্গ ঘটে যায় নুহূলের। নুহূল অনুধাবন করে আপা নুহূলের চাচার কামনার শিকার। নিজ পিতার সে অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতেই কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ে আপার আত্মহত্যা। আর এ ঘটনা পুরো নলুয়া সম্প্রদায়কে বাকি সমাজের সামনে হেয় করে তোলে। “সবার অলক্ষ্যে ঘটিয়ে যাওয়া একজনের পাপ কত দ্রুত পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিতে পারে অন্য সব দায়হীন মানুষদের” (পৃ. ১৪৭)।
বোধগত এমন সব ঘটনার সমানুপাতে চলতে থকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবৃদ্ধিও। সেখানে নুহূলের শিক্ষাগুরু হরিদাশ বাবু। কার্ল মার্ক্সের নামের সাথে পরিচিত হয় নুহূল। কলেজ পাঠের জন্য তার আগমন ঘটে ময়মনসিংহ শহরে। ‘জারিয়া ঝাঞ্জাইল লোকাল ট্রেন’ শিরোনামের অংশে নুহূল কলেজ জীবন, জীবনদর্শন নির্মাণ, সহপাঠী এবং রাজনৈতিক সহযাত্রী লিঙ্কনের উপস্থাপন ঘটে উপন্যাসে। এখানেও আছে নুহূলের পূর্ব কথিত দুই সত্তার কথোপকথন – যে কথনে এবারের প্রসঙ্গ হিসেবে উঠে আসে শ্রম, শ্রমব্যবস্থা, বন্টন ইত্যাদি সব মার্ক্সিয় প্রসঙ্গগুলো।
কলেজ জীবনকে আশ্রয় করে কাহিনীর পরিবর্ধিত খণ্ড দুটি হলো: ‘না পাঠানো চিঠি’ এবং ‘ক্রাইসিস মোমেন্ট’। নুহূল অনুধাবন করতে শুরু করে বাবার প্রত্যাশা থেকে তার দূরত্ব বাড়ছে। নুহূলের নিজের ভাষায়: ‘যে পথে নিজেকে প্রস্তুত করলে বৈষয়িক সাফল্য সহজতর হয় সে পথের হাতছানি উপেক্ষা করে নিজের দিকে, জীবনের দিকে বারবার নতুন উদ্যাম, নতুন কৌতুহল নিয়ে তাকাতে চেষ্টা করছি’ (পৃ. ১৯৭)। সমকালে যদিও একটি কলেজ পড়–য়া মেয়ে, যাকে সে শুধুমাত্র দেখেছে, কথাও হয় নি কখনো, তার প্রতি নুহূল এক অদৃশ্য আকর্ষণ বোধ করে। ‘ক্রাইসিস মোমেন্ট’ এ আমরা দেখি বাম রাজনীতিক লিঙ্কন নিহত।
আমরা বুঝতে পারি ইতোমধ্যে নুহূল দার্শনিক এক বোধে উপস্থিত; যে বোধকে একটি লেখায় প্রকাশ করতে সে ঐকান্তিকভাবে মনযোগী। আর তার তাই চাকরি সন্ধান না করে সে নিজ বাড়িতে থেকে সম্প্রদায়ের শিক্ষাহীন শিশুগুলোকে জ্ঞানদানে নিজেকে ব্রতী করে। খ্যাতিমান লেখক হওয়ার মোহে না থেকে জীবনের সত্যিকারের তাৎপর্যকে বানীবন্ধ করতে উৎসুক সে। কিন্তু সে কাজে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলোকে উপো করতে নুহূল নিজেকে নিরুদ্দেশ করতে বাধ্য হয়। ‘ছয়টি অন্ধকার গুহা’তে সে নিরুদ্দিষ্ট সময় এবং ষড়শত্র“ নিয়ন্ত্রণ সাধনা ঘটে নুহূলের। কাম, ক্রোধ, লোভ, অহংকার, হিংসা, নিন্দা নিয়ন্ত্রণে নুহূল পায় জটাধারী সন্ন্যাসীর সাহচার্য।
সাধুর গুহা থেকে ফিরে আসে যে নুহূল সে তো ভিন্ন মানুষ – ভেতরগত এবং বাহিরগত উভয়ভাবেই। সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে – আর তাই তাকে নিয়ে সমাজের মানুষদের স্পষ্ট হয় দুই ভাবনার। একদল ভাবে সে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, অন্যদল মনে করে ভণ্ড পাগল। ওদিকে অবচেতনে তাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে তার অন্তরজগতের সেই অপরিচিতা। তার প্রতি অনুভব করতে থাকে গভীরতম এক প্রেমাকর্ষণ। অপ্রতিরুদ্ধ সেই প্রেমাকর্ষণের টানে পুনরায় সেই ‘কামনাগুহা’য় ধ্যানমগ্ন হয় সে। উপন্যাসের দ্বাদশ ভাগের শিরনাম ‘মনচিত্র’। কামনাগুহার অন্ধকারাচ্ছন্ন এই অধ্যায়ে নুহূলের অন্তর্জগৎ প্রয়াস পায় সবোর্চ্চ আলোক প্রাপ্তির। উন্মোচিত হয় চেতনাসত্তা, শক্তিসত্তার ঘোর রহস্য। এসব সুউচ্চ প্রজ্ঞালব্ধ বোধের সঙ্গে আলোকোজ্জ্বল প্রেমবোধও স্ফুরিত হয়। “…সমস্ত জ্ঞান, বোধ, এমনকি নিজেকে বোঝা, এ জগৎকে বোঝা, শক্তিসত্তা, চেতনাসত্তা… সব কিছুই মূল্যহীন, এক সার্থকতাহীন বিষয়ে পযর্বসিত হতে বাধ্য যদি এসব বোধের মধ্যে সত্যিকার প্রেমবোধের ঔজ্জ্বল্য না থাকে” (পৃ. ৩২৭)। এবং সেই সাথে দেখি অতিন্দ্রীয় প্রেমে ঝলসিত হয়ে সেই কামনাগুহা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সংজ্ঞা হারায় নুহূল। সাময়িকভাবে হারায় তার পূর্বস্মৃতি। সূর্যের প্রথম কিরণের সাথে চোখ মেলে তাকায়। আত্মোপলবদ্ধির আলোয় ঝলসিত হওয়ার পর প্রথম চোখ মেলে তাকানো থেকেই প্রকৃত পক্ষে এ উপন্যাসের শুরু। আর যেটা ত্রয়োদশ অধ্যায় ‘আফাল’-এ এসে নুহূল তার পূর্ণআত্মপরিচয় উদ্ধারের সাথে পাঠকও উদ্ধার করে এ উপন্যাসের প্ররম্ভিক সূত্র। কিন্তু সাথে সাথেই আফাল নাম জলোচ্ছাসের কবলে পড়ে ভয়াবহ নৌকা ডুবির দৃশ্যে আবারো তার অস্তিত্ব অনিশ্চয়তায়র কবলে পড়ে যায়।
‘আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার জীবনের মূল দর্শন কী, কিংবা কী হওয়া উচিত? তাহলে আমি বলব, এ বিশ্বজগৎ এক নিখাদ ও অতলস্পর্শী ভালোবাসার প্রকাশ। ‘আমি’ প্রকাশের কারণও ঐ ভালোবাসাই; তাই এই ভালোবাসাকে গম্ভীরভাবে উপলব্ধি করতে এবং ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ, এজন্যই আমার আবির্ভাব। … একজন মানুষ ঠিক ততটুকুই বড়, ঠিক যতটুকু তার ভালোবাসার মতা ও ক্ষেত্র বড়’ (পৃ. ৩০১)। নুহূলের এ বোধ দীর্ঘলব্ধ। এ বোধের মত বহু সব বোধকে গ্রন্থিত করতেই নুহূল আপ্রাণ। আর সে গ্রন্থনের নির্মাণগল্প নুহূলের মনচিত্র। যেমনভাবে কাসিক সিনেমার নির্মাণগল্পও হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় এক গল্প, শেখ আলমামুনের এ উপন্যাসও তেমনই।
নুহূলের সম্ভাব্য গ্রন্থের বিষয়গুলো জীবনদর্শন – যে সকল প্রশ্ন শ্বাশত; চিন্তাশীল সকল মানুষকে যে প্রশ্নাবলী চিরকাল তাড়িত ও আপুত করেছে, তেমন সবই নুহূলেরও। ঔপন্যাসিক সে সকল উপস্থাপন করেছেন কখনো নুহূলের দুই সত্ত্বার কথোপকথনে, কখনো তার নিজের কণ্ঠের বর্ণনায়, কখনো বা ঔপন্যাসিকের নিজের কলমে। সন্দেহ নেই প্রথম এ প্রচেষ্টায় শেখ আলমামুন উপন্যাস শিল্পের ‘কথনশৈলী’ ব্যবহারে প্রকাশ ঘটিয়েছেন অসামান্য দতায়। বাংলা ভাষায় কথনশৈলীর নিপুণতায়, তিন সৈয়দ সর্বাগ্র: সৈয়দ ওয়ালিউলাহ, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ এবং সৈয়দ শামসুল হক। ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৫৩)এবং ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮), ‘অলীক মানুষ’ (১৯৮২) এবং ‘বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ’ (১৯৯২) কথনশৈলী প্রশ্নে বাংলা ভাষায় পৌনঃপূণিকভাবে উলেখের দাবীদার। বর্ণনায় প্রথম পুরুষে এবং তৃতীয় পুরুষের সংমিশ্রণ এবং সাথে সাথে আরও বহু কিছুর অনুপ্রবেশ আধুনিক উপন্যাসের অবিভাজ্য অংশ। ‘কিছু খসড়া ছেঁড়া পাতা’তে নুহূলের পূর্বকথিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ মুদ্রিত। যেগুলোর কিছু কিছু ঠিক যেন তার মূল পাণ্ডুলিপির অংশ নয়, যেন খসড়া, ভাবনাসমূহের অবিন্যস্ত প্রকাশমাত্র।
সহজপ্রবিষ্টতার প্রশ্নে বিদ্ধ উপন্যাস বাংলা ভাষার ইতিহাসে পূর্বেও ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৫-৬৫) ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’, কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-৭৯) প্রায় অধিকাংশ উপন্যাস, অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮-২০০১) কিছু বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-৯৭) ‘খোয়াবনামা’ও কি খুব বেশি প্রবেশযোগ্য। সে প্রবেশে বরং যোগ্য হয়ে উঠতে হয় পাঠককে – ক্রমে ক্রমে, অথবা দীর্ঘ পঠন ইতিহাসের ভেতর দিয়ে। বিংশ শতাব্দীর অসামান্য ঔপন্যাসিক জোশেফ কনরাডের (১৮৫৭-১৯২৪) ‘হার্ট অব ডার্কনেস’ এত বেশি সুসংহত সে অনেক পাঠকের পক্ষে তার মর্মোদ্ধার দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।
উপন্যাসের শ্রেণী বিচারের প্রশ্নে নুহূলের মনচিত্রকে দু ধরনের উপন্যাসের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। প্রথমত এটি দার্শনিক উপন্যাস, যে অর্থে উপন্যাসে লেখক তাঁর জীবন ভাবনাকে সরাসরি প্রকাশ করেন। দার্শনিক যে উপন্যাস বাঙালি পাঠকের কাছে তুলনায় অধিক পরিচিত সেটি হলো ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০) এর ‘লা নোজ’ বা ‘বিবমিষা’। ১৯৩৮ সালে মূল ফরাসিতে প্রকাশিত এ উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয় ১৯৪৯ সালে যেখানে প্রধান চরিত্র আঁতোয়ান রোঁকেতঁ ডায়েরি ধরনে রচিত উপন্যাসটিতে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার ভাবনার কথা বলে – শেখ আলমামুনের উপন্যাসে সে ভাবনার প্রকাশ ঘটে নূহূল ও তার মানসকন্যার কথপোকথনে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখা যেতে পারে যে, নুহূল নিজেও কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার জীবন বোধকে সে একটি গ্রন্থে উপস্থাপিত করবে, যেমনভাবে বিবমিষাতে নায়ক উপন্যাসের শেষে সিদ্ধান্ত নেয় একটি উপন্যাস লেখার।
এ ছাড়া নুহূলের মনচিত্রতে রয়েছে প্রধান চরিত্রের নির্মিতির চিত্রায়ন – শৈশব ও কৈশোরের যে নির্মিতির ভেতরে লুকিয়ে থাকে লেখকের নিজের জীবন অভিজ্ঞতা। জার্মান ভাষায় বিলগানস্রোমান অভিধার এ উপন্যাস বাংলা ভাষাতেও লভ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) এর শ্রেয়তর একটি উদাহরণ। হুমায়ুন আজাদের (১৯৪৮-২০০৪) ‘সব কিছু ভেঙ্গে পড়ে’ও (১৯৯৫) একটি উলেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। প্রধান চরিত্রের বিকাশের এমন উদাহরণ বাংলা ভাষায় যে সকল নারী ঔপন্যাসিকের লেখায় পাওয়া যায় তাঁরা হলেন সুলেখা সান্যাল (১৯২৮-১৯৬২) এবং আকিমুন রহমান (জন্ম ১৯৫৯)। স্বল্পপঠিত এই দুই ঔপন্যাসিকের ‘নবাঙ্কুর’ (১৯৫৫) এবং ‘রক্তপূঁজে গেথে যাওয়া মাছি’ (১৯৯৯) নিঃসন্দেহে শক্তিশালী প্রয়াস। ইংরেজি ভাষায় রচিত চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-৭০)-এর ‘ডেভিড কপারফিল্ড’ (১৮৪৯-৫০) ও ‘গ্রেট এক্সপেকটেশানস্’ (১৮৬০-৬১)-এর হাত ধরে পরিবর্তিত কালে রচিত ডি এইচ লরেন্সের (১৮৮৫-১৯৩০) ‘সান্স এন্ড লাভারস’ (১৯১৩ ), জেমস জয়েসের ( ১৮৮২-১৯৪১) ‘এ প্রোট্রেট অব দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান’ (১৯১৪-১৫) সহ বহু এমন আত্মজৈবনিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ‘বিলগানস্রোমানে’র তালিকায় ‘নুহূলের মনচিত্র’ উলেখযোগ্য সংযোজন।
একথা সত্য নুহূলের মনচিত্রতে প্রবেশে কোন কোন পাঠক খানিকটা বাধাগ্রস্ত হবেন। কেননা, প্রচলিতভাবেই পাঠক উপন্যাসে গল্পের অনুসন্ধানে অভ্যস্ত। প্রচলের বাইরে গিয়ে গল্প কাঠামোবিহীন তেমন একটি অনুক্রমনিকা দিতে শেখ আলমামুন দ্বিধা করেন নি, যদিও সে বাধাকে অতিক্রম করতে পারলে গল্পের সে কাঠামোটি ক্রমশ পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আর যে একটি বিষয় পাঠক কান্ত বোধ করতে পারেন তা হলো নুহূলের সাথে তার প্রতিতুল সত্ত্বার কথোপকথন। প্রশ্ন উঠতেই পারে উপন্যাস তো দর্শন নয়। সে প্রশ্নের খুব সহজ উত্তরে যদি বলা যায় কোন উপন্যাসই তো দর্শন ব্যতিরেকে নয়, তাহলে ‘নুহূলের মনচিত্র’তে আমরা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ ও সুখ বোধ করব। তবে শেখ আলমামুন যেটি করেছেন তা কিন্তু কোন বিশেষ দর্শনের প্রচারপত্র নয়, বরং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একজন সাধারণ মানুষের ভাবনাসমূহের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।
‘নুহূলের মনচিত্র’ বাংলা ভাষায় রচিত একটি অসম্ভব শক্তিশালী প্রয়াস। অচিন্তিতপূর্ণ এ গ্র্ন্থের প্রচ্ছদ থেকে শেষ ফ্লাপ পর্যন্ত একটি ঘোর পাঠককে আচ্ছন্ন করে। সব্যসাচী হাজরার শিল্পচিত্র শুরুতেই যে অতীন্দ্রিয় বোধে পাঠককে আহ্বান করে ক্রমে ক্রমে তারই গভীরতম রহস্যে যেন পাঠকের অগ্রযাত্রা। উৎসর্গপত্রে তিনজন মানুষ উল্লিখিত – দাদা, আব্বা এবং আম্মা। শুধু শব্দ দিয়ে নয় বাক্যে লেখকের জীবনে তাঁদের ভূমিকা দিয়ে। কিন্তু অভিনবত্ব এই যে জলছাপে আম্মা উপস্থিত যার দুঃসাহস বাংলাভাষী কোন ঔপন্যাসিক সম্ভবত করেন নি। ‘মুখবন্ধ’, ‘কৃতজ্ঞতা’তেও যেন ঘোর লাগার ছড়াছড়ি – যে ঘোরে উপন্যাসের প্রধান পুরুষ নুহূল আকণ্ঠ নিমজ্জমান। পনেরটি বিভাজন- প্রতিটির শেষে একটি করে লব্ধ চেতনাসমৃদ্ধ লিখন। কিন্তু বইয়ের শুরুতেই গল্প ও ভাবসূত্র বাণীবদ্ধ হয়েছে এভাবে ‘তার যাত্রা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী; সে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত; তার মধ্যেই অন্তর্নিহিত সমস্ত কিছু।’ বইটি পাঠন সম্পন্ন হওয়ার পরই এ বাণীর পরিধি স্পষ্ট হয়ে উঠে।
স্মরণযোগ্য সে সব বাক্যবন্ধের কয়েকটি এমন:
‘…হতে পারে সৃষ্টির আদি আবহে নিজেকে না চেনার ব্যকুলতা থেকেই তার যাত্রা শুরু। কিন্তু আমরা তো ঠিক জানি না, কী ছিল সেই শুরুর আবহ এবং জানি না চূড়ান্ত শেষের কথাও; তাহলে আমরা কীভাবে বলি প্রকৃত-সত্য আসলে কী… ’
‘…রাজনীতির উর্বর ভূমিতে বিবেক নামক কোন তৃণলতার অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক বিষয় সাধারণ মানুষের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। অথচ সবুজ বনানীর মতো বিবেকই হওয়া উচিত তপ্ত মরুময় বাস্তবতায় রাজনীতির মূল প্রাণ…’
‘…পরমসত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য প্রত্যেক মানবসত্তার গভীরে লুকিয়ে আছে নিখুঁত এক নকশা। গভীর প্রেম, পবিত্রতা, ভক্তি আর প্রজ্ঞাময় দৃষ্টি দিয়ে সে নকশার সন্ধান করতে হবে নিজের মধ্যেই…’
শেষ ফ্লাপে দীর্ঘ শশ্রু ও কেশ সমৃদ্ধ মানুষটির ঘোষণা ‘নিজেকে লেখক হিসেবে মানতে নারাজ’।
এত নির্ভূল বানানে পরিপাটি প্রকাশনার কৃতিত্ব অনুলেখিত অনেকের সাথে পারভেজ হোসেনেরও। প্রকাশনা শিল্পকে শৈল্পিক অভিধার যথার্থতা দিয়েছেন তিনি। লেখক ও প্রকাশককে বিনম্র সালাম জানাই।