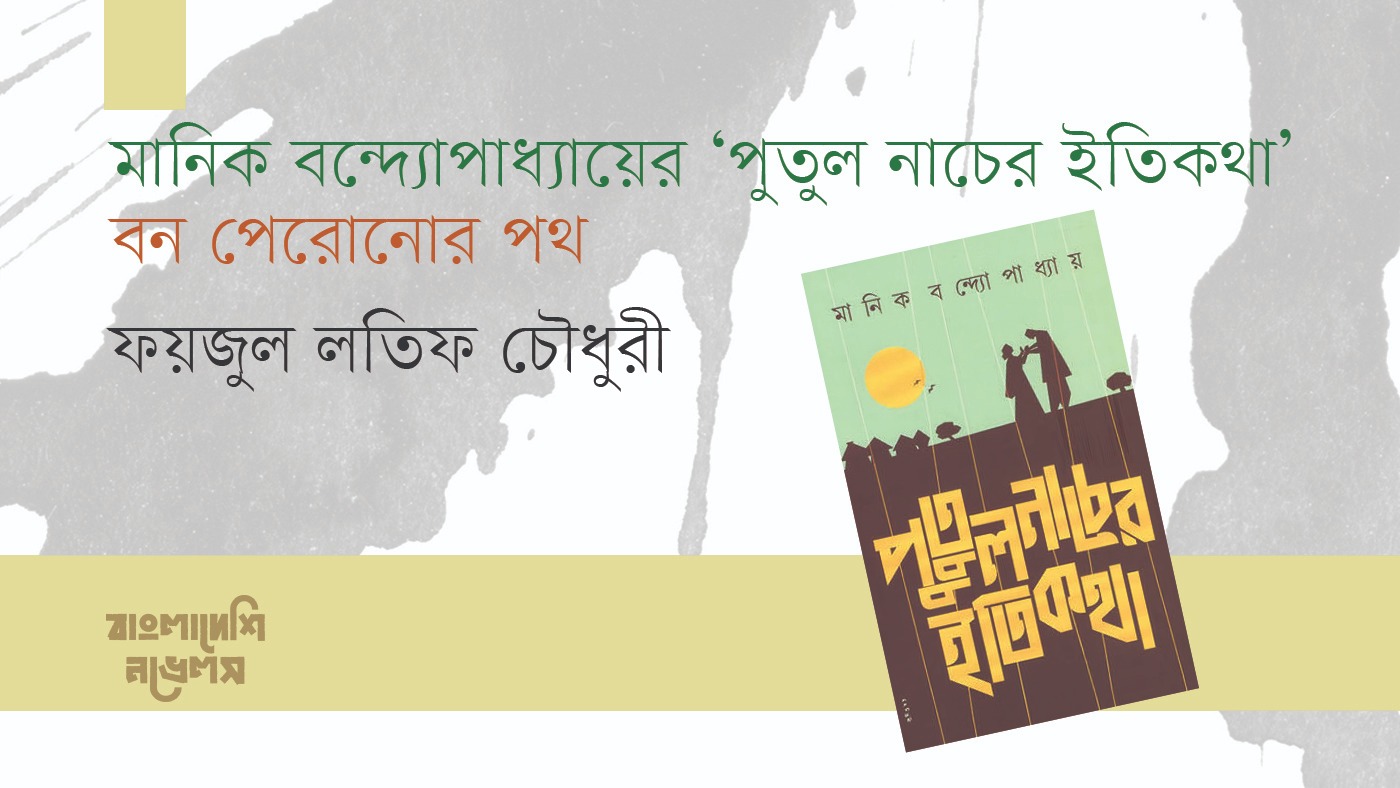ক.
‘আমলকীর মৌ’ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই লেখা একটি উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৯৭৮। রাজনৈতিকভাবে চরম অস্থিরতার মধ্যে রচিত হলেও, এটি কোনোভাবেই তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। ঔপন্যাসিক দিলারা হাশেম কৌশলে ও সচেতনভাবেই ঐ সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে এড়িয়ে সামাজিক-পারিবারিক জীবনকে উপজীব্য করে তুলেছেন এই উপন্যাসে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে যারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন কেবল তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দিলারা দেখিয়ে দিলেন একটা যুদ্ধের মীমাংসা হতে এখনো বাকী – যুদ্ধটা নারী স্বাধীনতার যুদ্ধ কিংবা আরও পরিষ্কার করে বললে, মানবতার মুক্তির যুদ্ধ। দেশ স্বাধীন হল, নারী স্বাধীন হয়েছে কি? মুক্ত হতে পেরেছে কি সমাজের বোধ-বুদ্ধি? এমন সব প্রশ্ন নিয়েই যেন হাজির হল ‘আমলকীর মৌ’। দিলারা হাশেম একটা নব্য স্বাধীন দেশের স্বাধীন কিছু বায়বীয় চরিত্র নিয়ে দেখিয়ে দিলেন, পুরুষকেন্দ্রিক সভ্যতাসৃষ্ট এথিকস, ভ্যালুস, – সর্বোপরি একটি আপাদমস্তক সমাজ ব্যবস্থা – তার হাতে যেমন নারীরা জিম্মি, জিম্মি তেমন পুরুষরাও। একটু আগে আমি যে এটাকে অরাজনৈতিক উপন্যাস বললাম এখন সেটা ফিরিয়ে নিচ্ছি। ‘আমলকীর মৌ’ চরমভাবে রাজনৈতিক একটি উপন্যাস। এখানে গেরিলা যোদ্ধার মতো একজন নারী যোদ্ধা যে জীবনযুদ্ধ শুরু করেছেন সেই যুদ্ধকে কোনভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।
খ.
আপাত দৃষ্টিতে এই উপন্যাসের মূল ইস্যু হল জেন্ডার বিভাজন। তাই আলাদা করে উপন্যাসটিকে নারীবাদী উপন্যাস বলায় যায়। নারী কেন্দ্রীক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক লেখা হয়েছে। তবে তসলিমা নাসরিনকে বাদ দিলে এরকম সাহসী উপন্যাস দুটো লেখা হয়েছে কি না সন্দেহ। সত্তর দশকে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী স্বামী-সন্তান ছেড়ে আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে বাস করছে, রাত নেই দিন নেই রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, ইচ্ছে হলে পান করছে তরল কিংবা ধূম। ব্যাচেলর বন্ধুর ফ্লাটে ঢুকে পড়ছে যখন তখন। এটা ভাবতেই অনেক মেয়ের গা শিউরে উঠবে। বিশেষ করে সময়ের কথা বিবেচনা করে তো বটেই। সারার মতো আত্মসচেতন, আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমতী ও উচ্চশিক্ষিত, চমতকার ইংরেজি বলা নারী চরিত্রও বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি নেই। মহিলা বিদূষী – তার ওপর রূপসী, এই তৃরত্ন যোগ ঘটেছে সারার ক্ষেত্রে। এবং এই যোগসাধনই তার কাল হয়েছে – নিজের জন্য, অন্যের জন্যেও। নারীরা রূপসী হবে যথার্থ, সাথে সারা যে গুণার্জন করেছে সেগুলো যে পুরুষালি! সারা তার যোগ্যতা বলে যোগ্য মানুষের মতো আচরণ করেছে। তৈরি সমাজকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়তে চেয়েছে। সম্পূর্ণ না পারলেও সমাজের কিছু মানুষকে অন্তত সে বোঝাতে পেরেছে, এভাবেও নারীরা বেঁচে থাকতে পারে। এবং এভাবেই বেঁচে থাকা উচিত।
সারা অস্তিত্ব সচেতন নারী। সে প্রশ্ন করেছে সমস্ত বৈষম্য নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজিতে মাস্টার্স এবং বিদেশ থেকে ডিগ্রি ফেরত। সে ইচ্ছে করলেই তার রূপের সাথে সাথে এই যোগ্যতাকে গুলিয়ে অন্যরকম একটা জীবন পেতে পারতো; কিন্তু সে তা করেনি। রূপচর্চা ও স্টাইল নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। কারণ সে বুঝে গেছে এটা তার অস্তিত্ব বিরোধী, নারীদের আরও নারী করে তোলার কারসাজি। ‘উপকরণ হিসেবে সে কোনমতেই ব্যবহৃত হবে না, এক্সপ্লয়টডও নয়।’ [পৃ.১২, ‘আমলকীর মৌ’, মুক্তধারা, ১৯৭৮] এটা তার সচেতন ভাবনা। প্রয়োজনে উল্টো সেই ব্যবহার করবে, এক্সপ্লয়টেডও। এটা ভেবে সারা তার সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে বন্ধুদের উপকার করে বেড়ায়। এক অর্থে বন্ধুরা তাকে ব্যবহারই করে, সারার মতো বুদ্ধিমান মেয়ে সেটা না বুঝে উঠবার কথা নয়। সারা এক্ষেত্রে বন্ধুদের উপকার হচ্ছে, এটা ভেবেই খুশি।
সারা গোড়া থেকেই সংসারের ছোটখাটো অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। প্রশ্নগুলো হয়ত আমাদের অজানা নয়, কিন্তু সারা সেগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। প্রশ্ন থেকে রেহায় পান না সংসারে তার অতি প্রিয় বাবাও। ‘যে লোকটি দিনের বেলায় আম্মা মানুষটার সাথে প্রায় সম্পর্কবিহীন দিন কাটায় – সে রাতে কোন সম্পর্কের দাবিতে এবং কিভাবে অতগুলি সন্তানের পিতৃত্বের অধিকারী হয়!’ [পৃ.২৩] সংসারে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা যে কোথায় তা সারার প্রশ্ন থেকে পরিস্কার হয়ে ওঠে। সারা তার বাবা-মার মধ্যকার অস্বচ্ছ দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতর থেকে তাবৎ নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভেতর একটা অস্বচ্ছতা দেখতে পায়। সারা এই ঘোলাটে সম্পর্কটা ধরতে পারে বলে সে তার স্বামী-সন্তান ফেলে চলে আসতে পারে। তার এই সাহসটার পেছনে ইন্ধন জোগায় তার অর্থনৈতিক সাবলম্বিতা। সারার বোন সালেহা নারী-পুরুষ সম্পর্কের এই ফাঁকটা ধরতে পারলেও চলে আসতে পারে না। জাগতিক মুক্তির বদলে তাকে চিরন্তর মুক্তির পথ বেছে নিতে হয় – সে আত্মহত্যা করে। কারণ সে সারার মতো অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী নয়। সালেহা স্বামী ছেড়ে আশ্রয় চেয়েছিল বাবার কাছে। বাবা সম্মান ও সমাজের ভয়ে তাকে আশ্রয় দেননি। সালেহাকে জোর করে ধরে রাখতে পারেনি সমাজ। ভার্জিনিয়া উলফ্ নারী স্বাধীনতায় নারীদের নিজস্ব একটি কামরার ওপর জোর দিয়েছিলেন। একবিংশ শতকে এসে নারীদের শুধু কামরা দিয়ে হচ্ছে না, দরকার হয়ে পড়েছে নিজস্ব একটি ব্যাংক একাউন্টও। নারী ক্ষমতায়ন বা স্বাধীনতার সাথে জড়িয়ে আছে অর্থনীতি। মার্ক্সের সেই অমোঘ বাণী – ‘একটা ক্লাশ ইকোনোমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কখনই খাঁড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না’ – সত্য হয়ে ওঠে নারীদের ক্ষেত্রেও।
আবার অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হলেই একক প্রচেষ্টায় সমাজের সব বিশ্বাস বা আচারকে ভাঙ্গা যায় না। তাই তো সারা খালার খাটুলি ধরতে চাইলে মামা বলেন, ‘তুই বয়ে নিয়ে যাবি? তুই তো মেয়ে মানুষরে। মুর্দায় কাঁধ দিতে গেলে পুরুষ হতে হয়। ওটা তোর কাজ নয়।’ [পৃ.২৮] এখানে এসেই আটকে যায় সারা। দিলারা হাশেম তসলিমা নাসরিনের মতো কোনো নগ্ন প্রতিবাদে নামান না তাঁর চরিত্রকে, তিনি খালি প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারেন।
সারার এই স্বাধীন জীবন তাকে সমাজ ও পরিবারের কাছে ‘মোস্ট আন-ওয়ানটেড’ করে তোলে। আবার রাতের অন্ধকারে এই সমাজেই সবচেয়ে ‘ওয়ান্টেড’ হয়ে ওঠে সারায়। ভণ্ড সমাজ তখন মাতাল হয়ে নারীর সুখ চায়। সারা উপলব্ধি করে, যে লোকগুলো তাদের পরিবারের নারীকে শক্ত করে আটকে রাখে সেই লোকগুলোই অন্য নারীকে বাইরে বের করে আনার জন্য আনচান করে! সারা বাইরে থাকে বলে যে সমাজ তাকে বলে, ‘মেয়েটার লজ্জা বলে কি কিছু নেই?’ ও ‘তোমার মত মেয়ের বাবা বলে পরিচয় দিতে আব্বার লজ্জা করবে।’ এ জাতীয় কথা। সারা কারু সাথে বিছানায় যেতে রাজি না হলে সেই সমাজই আবার সারাকে ‘কনজারভেটিব’ আখ্যায়িত করে বলে, ‘ইউ ডোন্ট নীড টু স্লীপ উইথ এভরি আদার বয় ইউ মীট, বাট ইউ মে স্লীপ উইথ ওয়ান অর টু – ইউ লাইক মোস্ট। কাম অন সারা – শরীর ছুঁলেই তোমার প্লেগ হয়ে যাচ্ছে না।’
এটা হল শিক্ষিত-বিত্তশালীদের ভণ্ডামি। এই ভণ্ডামির সাথে তাল মেলায় না সারা। সে বিয়ের আগে কারো সাথে বিছানায় যাবে না, এই তার প্রতিজ্ঞা। তার ইচ্ছে হলে সে পান করে, না হলে না। কারও মনোঞ্জন করার জন্য সে নেশা করে না। তার সবকিছু সম্পূর্ণ নিজের জন্য। ‘একমাত্র নিজের অন্তরের কাছে ছাড়া আর কারু কাছে জবাবদিহির জন্য সে প্রস্তুত নয়।’ [৪৯] বাংলা সাহিত্যে এমন চরম অস্তিত্ব সচেতন নারী খুবই কমই আছে।
পরিবারের কাছে সবসময় লাঞ্চিত হতে হয় সারাকে। পরিবারের নারীরাই সারার বড় শত্রু। মা থেকে শুরু করে বড় বোন, ভাবি ও বোনের মেয়েরা পর্যন্ত সারার স্বঘোষিত স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারে না। ছোট বোন নীলু সারাকে বলে, ‘তোমার মত মেয়ের বাবা বলে পরিচয় দিতে আব্বার লজ্জা করবে।’ [পৃ.৫০] মা যোগ করেন, ‘মেয়েটার লজ্জা বলে কি কিছু নেই?’ [পৃ.৫১] বড় আপা মেয়ের চুল কাটার বিষয়ে বলে, ‘হাঁটু-ধরা চুল নইলে চলবে কি করে, বর জুটাতে হবে না?’ [পৃ.৫২] পিতৃপরিচয় যে সমাজে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিও সারাকে বুঝিয়ে দেন বড় আপা, ‘পিতা যে আছেন, সেটুকুও কম কথা নয়রে। আছেন তাই টের পাচ্ছিস না। যেদিন সত্যিই থাকবেন না – সেদিন বুঝবি। নামটারও ত কিছু মাহাত্ম্য আছে।’ [পৃ.৫৬] ভাবী সেজেগুঁজে স্বামীর বন্ধুদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভোর থাকে, অথচ সারার কোন বন্ধু বাড়ি পর্যন্ত এলেই তার চোখ জ্বালা করে। বাড়ির সকলের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে। এ সংসারে ‘স্বামীর বন্ধু হলেই সাত খুন মাফ।’ [পৃ.৫৮] যেন সংসারে নারীর কোন বন্ধু থাকতে নেই। নারীরা সেটা মেনেও নিয়েছে, সারা মানেনি তাই তাদের সমস্যা।
এমনি করে প্রায় প্রতিদিনই ঘরে ফেরার পর সারাকে তীক্ষ্ম বাক্যের সম্মুখীন হতে হয়। সারা কখনও প্রতিবাদ করে কখনও করে না। সারার সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ তাদের কথায় নিজের জীবনের ছক থেকে তিল পরিমাণ নড়চড় না হওয়া।
তবে শেষপর্যন্ত সারা তার মুক্তির পথ খুঁজে পায় কি না সে সন্দেহ থেকেই যায়। সারা একজন মানুষ নয়, একজন নারী হিসেবেই সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। একজন পুরুষের জন্য যদি পুরুষ পরিচয়ই যথেষ্ট হয়, তবে কেন নারীকে আলাদা করে মানুষ হয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে? অলরেডি সে একজন নারী, এবং এইটাই সারার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সারা যখন বলে, ‘আই উইল ম্যারী এগেইন। আই মাস্ট গেট আউট অব ইট।’ তখন প্রশ্ন জাগে, সারা আসলে কোথায় থেকে বেরুতে চাইছে? মুক্তির জন্য সে আবার বিয়ের কথা ভাবছে কেন? কোনো পুরুষ তো মুক্তির জন্য বিয়ের কথা ভাবে না। তাহলে সারা কোন মুক্তির কথা বলছে? এসব প্রশ্ন আপনা আপনি চলে আসে।
উপন্যাসের শেষের দিকে এসে মনে হয়েছে দিলারা হাশেম তাঁর নারী ভাবনাটাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি সারাকে আলাদা করে উঠিয়ে এনে কী প্রমাণ করতে চাইছেন তা পরিষ্কার না। সারাকে তিনি নারীদের থেকে আলাদা করলেন, আবার সারাকে করে তুললেন সবচেয়ে পুরুষনির্ভর। নইলে সে শুরুতে দ্বারা, পরে বন্ধু হাসিব, প্রেমিক ফিরোজ এবং সবশেষে বড় ভাই মতিন – এদের ওপর এত বেশি নির্ভর করবে কেন! নারী স্বাধীনতার একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে ‘আমলকীল মৌ’ উপন্যাসটি।
গ.
স্বাধীনতার সমস্যা শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও। দিলারা হাশেম নারীদের মুক্তি নিয়ে কথা বলতে বলতে তাঁর হয়ত অবচেতনেই ধরা দিয়েছে অন্য এক সমস্যা, সমস্যাটা যদি সত্যি হয় তাহলে হতাশা নারীর জন্যই বেশি। যে পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে সারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে, সেই পুরুষই যদি মুক্ত না হয়, তাহলে পাল্লাটা কিসের সাথে?
সারা জন্মের পর থেকে যে পুরুষগুলোর সাথে পরিচিত হয়, যারা তার জীবনের সবচেয়ে কাছে আসে তারা সারার চেয়েও ব্যর্থ। সারা যেভাবে তার আপন সত্তাকে চিনতে পেরেছে তারা সেভাবে পারেনি। তারা মানুষ হিসেবে সারার চেয়েও নিম্নস্তরের।
সারার বাবা আজম খান অতি শিক্ষিত একজন মানুষ। তার সময় কাটে বই পড়ে নয়ত সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে। কি ইতিহাস, কি দর্শন, কি রাজনীতি – সবকিছুতেই তিনি সমান পণ্ডিত। তার সবসময়ের সঙ্গী হলেন – কান্ট, হেগেল, গেটে, স্পিনোজা, প্লেটো, রাসেলের মতো বিশ্ব পণ্ডিতরা। স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক কেবলই লিবিডোর। সারাদিন স্ত্রীর সাথে একদণ্ড কথা বলার অবকাশ হয় না তার। সময় দেন না সংসারেও। অথচ নিয়ম করে ঠিকই গর্ভবতী হয়েছেন সারার মা। পণ্ডিত হয়েও আজম খান সমাজের মানবতাবিরোধী কতক নিয়মকে অবজ্ঞা করতে পারেন না। কাজের মেয়ের সাথে বড় ছেলের প্রণয়ের ঘোর বিরোধী তিনি। শুধু তাই নয়, কৌশলে নিজের এক কর্মচারীর সাথে ঐ মেয়ের বিয়ে দিয়ে অন্যত্র বদলি করে দেন। যে লোকটার সংসার নিয়ে ভাববার সময় নেয়, সেই লোকটাই এত কিছু ভাবেন! স্বামীর অত্যাচারে সকিনা আত্মহত্যা করলেও ইনডাইরেক্টলি তার মৃত্যুর জন্য দায়ী আজম খানই। ‘সংসারে সকিনাকে সবই শেখানো হয়েছিল, শুধু শেখানো হয় নি লেখাপড়া, পাঠানো হয় নি স্কুলে। কেননা সেইটেই রীতি।’ [পৃ.২০১] এই রীতির বাইরে যেতে পারেননি কান্ট, হেগেল, গেটে, স্পিনোজা, প্লেটো, রাসেল হজম করা আজম খান। এক্ষেত্রে সেই রীতির খানিকটা বাইরে পা বাড়ালেও প্রেমিক মতিন শেষপর্যন্ত বাবার কথা মেনে নিয়েই আর বিয়ে করেনি সকিনাকে। মেজো মেয়ে সালেহা তার অত্যাচারী-বহুগামী স্বামী রশীদের সংসারে ফিরে যেতে না চাইলেও আজম খান সমাজে সম্মান হারানোর ভয়ে তাকে যেতে বাধ্য করেন। কিছুদিন পর সালেহা আত্মহত্যা করে। এ মৃত্যুরও পরোক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ান আজম খান। আজম খান শিক্ষিত হয়েও নিজের সবচেয়ে কম সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগেন। সমাজে তার বাজার দর কম, এ বিষয়টা অতি গুরুত্বের সাথে নেন তিনি। এমনি করে এই উপন্যাসের প্রতিটা পুরুষ চরিত্রই কম বেশি সমাজের চিরায়ত নিয়মের খাঁচায় বন্দি। এখান থেকে একমাত্র সারাই খানিকটা বেরুতে পেরেছে, আর কেউ পারেনি।
নারীকে শুধু জেন্ডার নয়, একটা শ্রেণি হিসেবেও কল্পনা করেছেন দিলারা হাশেম, যে শ্রেণির সঙ্গে প্রলেতারিয়েট সমাজের খুব বেশি পার্থক্য নেই। নারীরা পিছিয়ে পড়ার কারণ পুজির বিকাশের সাথে নারীদের বিকাশ সমানুপাতিক হারে ঘটেনি। অথবা ঘটতে দেওয়া হয়নি। পুরুষশাসিত সমাজ নানা বন্দোবস্ত করে এই বিকাশের পথকে শক্ত করে আটকে রেখেছে। আজম খানের মতো মানুষ জ্ঞানচর্চা করেছেন যন্ত্রের মতো, পুরুষশাসিত সমাজের দেমাগটা ঠিক রাখার জন্য। নারীরা একসঙ্গে সারার মতো নড়েচড়ে বসছে না কেননা সেই শক্তি তাদের দেওয়া হয়নি কিংবা তারা এখনো অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।
সাধারণ নারীবাদী উপন্যাসগুলোতে পুরুষদের বহুগামীতা উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে থাকে। থাকে নারীদের শরীরের রগরগে বর্ণনাও। পুরুষদের খুব খারাপভাবে তুলে ধরতে পারলেই যেন নারীবাদী উপন্যাস লেখার কাজ অর্ধেকটা হয়ে গেল। দিলারা হাশেম এই সস্তা ট্রেন্ডে হাঁটেননি। তাঁর উপন্যাসের বেশিরভাগ পুরুষ চরিত্রই নারীদের সম্মান দেখায়। সারার বড় ভাই সকিনাকে ভালবেসে বিয়ে করতে পারেনি বলে জীবনে আর কোন নারীর সংস্পর্শে আসেনি। চরিত্রগত ত্রুটি নেই সারার বাবা কিংবা অন্য দু’ভাইয়েরও। হাসিব সারাকে ভালবাসে। সে সারাকে দেহ-মন দিয়ে কামনা করে, অথচ সারা একা তার বাসায় রাত কাটালেও সে সারাকে অমর্জাদা করে না। সে সারার স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করে। ফিরোজ চরিত্রবান ছেলে। সুযোগ পেয়েও সে সারার শরীর পর্যন্ত এগোই না। সারার বন্ধু সাজিদ পরিবার ও স্ত্রীর কথা ভেবে সারার কাছে অন্যায় আবদার করলেও সারার মর্জাদা হানি সে করেনি। সারার বড়ভগ্নিপতী ছিলেন অতি ভালমানুষ। সালেহার স্বামীর মতো দু-একজন লম্পট হয়ত আছে তবে এ উপন্যাসে তাদের ভূমিকা খুবই খাটো।
উপন্য্যাসের শেষদিকে এসে সবকিছুই ভেঙ্গে পড়ে। সম্পর্কগুলো মৃত্যু বা চরম বিচ্ছেদের ভেতর দিয়ে সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠে। সারার মায়ের মৃত্যু, মেজো বোনের আত্মহত্যা, প্রেমিক ও বাগদত্তা ফিরোজের মৃত্যু; বড় ভাইয়ের প্রেমিকা সকিনার আত্মহত্যা – এতগুলো মৃত্যু এসে বদলে দেয় উপন্যাসের চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক। আত্মপোলব্ধিতে মৃত্যু গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। যে সারা কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করে না, শেষের দিকে এসে সে সারাই কপাল বা অদৃষ্টের লেখনকে ধ্রুব জ্ঞান করে। সে বলে, ‘অশ্রু ঢেলেই ফুল ফোটানো যে আমার ভাগ্য – সে আমি এড়াবো কেমন করে? আমি যে আমলকীল মৌ।’ [পৃ.৩৫৮] বিচ্ছেদ বেদনায় সে অস্তিত্ববাদী থেকে হয়ে ওঠে অস্তিত্ববাদ-বিরোধী।
ঘ.
উপন্যাসটির ভাষার বুনন শেষের দিকে এসে কিঞ্চিত ফেঁসে গেছে। শুরুর দিকে ভাষা ও উপমার প্রতি দিলারা হাশেম যতটা যত্মবান ছিলেন শেষের দিকে ততটা ছিলেন না। গল্পটা ঠিকঠাক বলাটাই যেন তার মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার একটি উপন্যাসে লেখকের সমান মনোযোগ দাবি করা বোধহয় উচিতও হবে না। উপমার ক্ষেত্রে উপন্যাসিকা বার বার প্রকৃতির কাছে ফিরে গেছেন। উপন্যাসের শুরু ও শেষটা হয়েছে প্রকৃতির হাত ধরেই।
শুরু: ‘রাস্তার দুপাশে ডালপালা ঝাঁপানো গাছগুলো যে পাতার মশারি। পথটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে আর সেই মশারির জালি ছেঁকে ঝরে পড়ছে জোছনার রেণু। সেই জোছনার আফসা গায়ে মেখে বড় বড় সেগুন পাতাগুলো বেদেনী মেয়েদের মত হাওয়ায় শরীর নাচাচ্ছে। সেগুন ফুলের মৃদু মিষ্টি ঘ্রাণ যেন তাদের দেহের বাসনাময় মদিরতা। জোছনার সাঝ পরে এই শহুরে রাতও পেয়েছে অভাবনীয় এক রূপের মাদকতা।’
শেষ: নদীর মত জীবনটা এখনও বইছে। কোন বড় ঝঞ্ঝায় এই বহমান জীবনের স্রোত কখনও থামতে জানে না। নিরবধি গতিই এর পরিণতি। বইতাই অস্তিত্ব। এখনও ঋতু পরিবর্তন হয়। মুকুল ধরে ফুল ফোটে, চন্দ্র, সূর্য, তারা ওঠে আপন নিয়মে।
ভাষার বিন্যাস ও উপমার প্রয়োগ কোথাও কোথাও কবিতার দোলা এনে দিয়েছে। দিলারা হাশেম তাঁর চরিত্রদের বিশদ বয়ান বা অতি ডিটেলিং-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রও যতক্ষণ বর্ণনার ভেতর থেকেছে মনে হয়েছে ঐ সময়ে সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বিস্তার যত কমই হোক না কেন সব চরিত্রকেই পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া যায়। পড়তে মনে হয়, পুরানা পল্টনের মোড়ে গেলেই হাসিবের বাসাটা দেখতে পাওয়া যাবে! রাত একটু গাড় হলেই মনে হয়, এ বুঝি সারা ঘণ্টা মিটিয়ে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো! এমন কত দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। চরিত্র ও পরিবেশ পরিস্থিতির এতটাই জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসটি জুড়ে।
একদা বাস্তববাদী উপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন হেনরি জেমস। তাঁর অভিযোগ ছিল, বাস্তববাদী লেখকরা কেবলমাত্র বাইরে থেকে চরিত্রাঙ্কান করে থাকেন। মানব চেতনার ভেতর যে নিরন্তর আলো-আধারের খেলা চলে সে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির কোনো পরিচয় তাদের চরিত্র সৃজনে ধরা পড়ে না। [সাহিত্যের রূপ-রীতি: কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, পৃ.২৯০] হেনরি জেমস-এর এ অভিযোগ এখানে খাটে না। ‘আমলকীর মৌ’ পুরোপুরি বাস্তববাদী উপন্যাস। এরপরও এই উপন্যাসে প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মনন জগতের পরিচয় মেলে। বিশেষ করে সারার তো বটেই। সারা তার ভেতরের কোন অনভূতিই পাঠকদের কাছে গোপন রাখে না। দিলারা হাশের তাঁর এই উপন্যাসে সরাসরি ‘চেতনাপ্রবাহ’ (স্ট্রীম অব কনসাসনেস) সাহিত্যরীতি অনুসরণ না করলেও তিনি প্রটাগনিস্ট সারার ব্যাপারে কোন ধরনের গোপনীয়তা বজায় রাখেননি। শুধুমাত্র চরিত্রগুলোকে একটা পরিস্থিতির ভেতর ছেড়ে দিয়ে তাদের বোঝবার ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে দেননি, সাথে একান্ত অনুভূতিগুলোও শেয়ার করেছেন দিলারা হাশেম। এখানে চরিত্রচিত্রনের কাজটি তিনি দুইভাবে করেছেন। তিনি নাটকীয় পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি দুইই অবলম্বন করেছেন।
ঙ.
সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ট শিল্প মাধ্যম হল উপন্যাস। বিশদ ও বিস্তৃত শিল্পমাধ্যম তো বটেই। মানব জীবনকে উপন্যাসায়ীত করার কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই। কাজেই লেখকরা খানিকটা নিজের ভাবনা থেকে খানিকটা পূর্বসূরীদের কাছ থেকে বলার বা বয়ানের ভঙ্গি বেছে নেন। এক্ষেত্রে দিলারা হাশেম বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের দুই পূর্বসূরী হেন্রি ফিল্ডিং ও থ্যাকারের দেখানো পথে হেঁটেছেন। ফিল্ডিং এক বিশাল আখ্যানবিন্যাসে ঘটনার পর ঘটনা সাজান। আর থ্যাকারে কাহিনীর মাঝখানে খানিকটা থেমে পাঠকদের সাথে কথা বলেন। দিলারা হাশেমের এই উপন্যাসটা যেমন কোথাও কোথাও ঘটনা নির্ভর তেমন কোথাও কোথাও বক্তব্য নির্ভর।
সাধারণত উপন্যাসের আখ্যানভাগের বর্ণনারীতি বা কোনো ন্যারেটিভে একজন ন্যারেটর থাকেন। সেই ন্যারেটর বাইরের কেউ অর্থাৎ লেখকও হতে পারেন আবার উপন্যাসের যে কোনও চরিত্রও হতে পারে। তবে ‘হার্ট অব ডার্কনেস’ এ তিনজন ন্যারেটরের উপস্থিতি ঘটেছে – একজন লেখক, একজন চরিত্র, অন্যজন বেনামি। জাপানি ক্লাসিক ‘রাশোমন’ এ প্রতিটা চরিত্র ন্যারেটর। একটি খুনের ঘটনা প্রতিটা চরিত্র আলাদা করে আদালতে ব্যাখ্যা করেন, ফলে প্রতিবারই ঘটনা যায় বদলে। বঙ্কিমের ‘রজনী’ উপন্যাসে আখ্যানভাগের বর্ণনা দিতে উঠে আসে চরিত্ররাই। রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটির তিনটি প্রধান চরিত্রের মুখ থেকে। দিলাশা হাশেমের ‘আমলকীর মৌ’ উপন্যাসে মূল কথক লেখিকা নিজেই, মাঝে মধ্যে কথকের ভূমিকায় চলে এসেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র সারা।
ভি এস নাইপল একবার সমালোচিত হয়েছিলেন এই বলে, পৃথিবীতে প্রথম সারির কোনো নারী কথাসাহিত্যিক নেই। তিনি জর্জ এলিয়ট থেকে শুরু করে ভার্জিনিয়া উল্ফ পর্যন্ত সবাইকে টেনে বলেছিলেন কেউ তাঁর মানেরও কথাসাহিত্যিক নয়। কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন, নারী সাহিত্যিকদের অতি আবেগ ও বিষয়বস্তুর স্থূলতাকে। আমি সে বিতর্কে যাবো না। প্রসঙ্গক্রমে চলে আসলো নাইপলের কথা। দিলারা হাশেমের এই উপন্যাসটা খুব ধরে পড়লে হয়ত বোঝা যাবে এটি কোনও নারী কথাসাহিত্যিকের লেখা তবে সেই বোঝা যাওয়াটা এখানে মোটেও দোষের ইঙ্গিত বহন করে না। দিলারা হাশেমের ভাষা যথেষ্ট আবেগবর্জিত। ঘটনার বয়ানে তিনি যতটা নির্বিশেষ থাকা সম্ভব তিনি থেকেছেন।
উপন্যাসটি চরিত্রায়ন, বিস্তার, ভাষা ও উপমার ব্যবহার সবদিক থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে উঠেছে। প্রতিটি চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তার বেশি জানার প্রয়োজন পড়ে না। তবে প্লট কোথাও কোথাও খানিকটা ঝুলে গেছে। সেটা হয়েছে ঘটনানির্ভর উপন্যাসকে চরিত্রনির্ভর করে তোলার কারণে। যৌগিক প্লট ও উপপ্লটে ৩৮০ পৃষ্ঠার উপন্যাসে মোট বিয়াল্লিসটা অনুচ্ছেদ আছে। সব অনুচ্ছেদ আয়োতনে সমান না। অনুচ্ছেদ বিন্যাসে দিলারা হাশেম চিরায়াত পথে হেঁটেছেন। একেকটা অনুচ্ছেদে একেকটা গল্প নিয়ে তিনি হাজির হয়েছেন। প্লট কোথাও শিথিল, কোথাও দৃঢ়পিনদ্ধ। উপন্যাসের গঠনের দিক দিয়ে প্লটটি বৃত্তাকার। একটি মূল ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাবতীয় ঘটনার অবতারনা ঘটে। উপন্যাসের সেটিং বা পটভূমি হল ঢাকা, সময় ৭০’র দশক। উপন্যাসের মূল কনফ্লিক্ট আপাত দৃষ্টিতে নারীর সাথে সমাজের মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সাথে সমাজের। আবার ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিরও। কোথাও কোথাও আবার নিজের সাথে নিজের।
উপন্যাসের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হল হাসিব-লাইজুর পরিচয় ও আকস্মিক দৈহিক সম্পর্ক হয়ে ওঠার পর্বটি। এ উপন্যাসে লাইজুর পাঠ অনর্থক। ফিরোজের উপস্থিতিও কোথাও কোথাও প্রশ্নবিদ্ধ। রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করতে যেমন প্রভাবক লাগে, এ উপন্যাসে তেমন প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে লাইজু-ফিরোজ। দুটো চরিত্রই আউটসাইডার। এদুটো চরিত্রকে আমরা নাটকের টার্মে ‘ডিউক্স এক্স মেসিনা’ বলতে পারি। শেষ করতে যেমন হঠাত করেই এটার নাটকে আগমণ ঘটে। এই উপন্যাসেও তেমনি ঘটেছে। উল্লেখ্য, ‘ডিউক্স এক্স মেসিনা’র উপস্থিতি নাটকের প্লটকে দুর্বল করে তোলে। এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই করেছে।
উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্র নির্বিশেষ বা টাইপ চরিত্র। চরিত্রগুলো ব্যক্তিপরিচিতি উপেক্ষা করে একটি সাধারণ পরিচতি তুলে ধরে। সবাই প্রচলিত ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার ম্যানারিজম বা মতবাদকে আকড়ে ধরে। এ ধরনের চরিত্রকে সমতল সদৃশ চরিত্রও বলে থাকেন কোন কোন সাহিত্য সমালোচক। একমাত্রিক হওয়ার কারণে আজম খান এত জ্ঞানী হওয়া সত্বেও যে দিক দিয়েই তাকে দেখা হোক না কেন তার কোনো রূপান্তর বা পরিবর্তন চোখে পড়ে না। আর উপন্যাসে ব্যক্তিক্রেন্দ্রিক বা বর্তুলাকার চরিত্র হল সারা, কিছুটা হাসিব, ফিরোজ ও সারার ছোটবোনও। সারা চরমভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রীক। সে নিজেকে বাদ দিয়ে সমাজকে কল্পনা করতে পারে না। তার কাছে টোটাল সমাজ থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন ও আলাদা। সমাজ নয় সে ব্যক্তির সন্ধানে মগ্ন থাকতে পছন্দ করে। এজন্য সারা বদলাতে থাকে, সকাল সন্ধ্যা তার রূপ বদলায়, তাকে কোনো নির্দিষ্ট মাফকাঠিতে মাপা যায় না। সমগোত্রীয় নারী চরিত্রদের মধ্যে পড়ে – জেন অস্টেনের এলিজাবেথ, তলস্তয়ের আনা কারেনিনা, ইবসেনের নোরা, ফ্লবেয়ারের এমা বোভারি, টমাস হার্ডির টেস প্রমূখ।