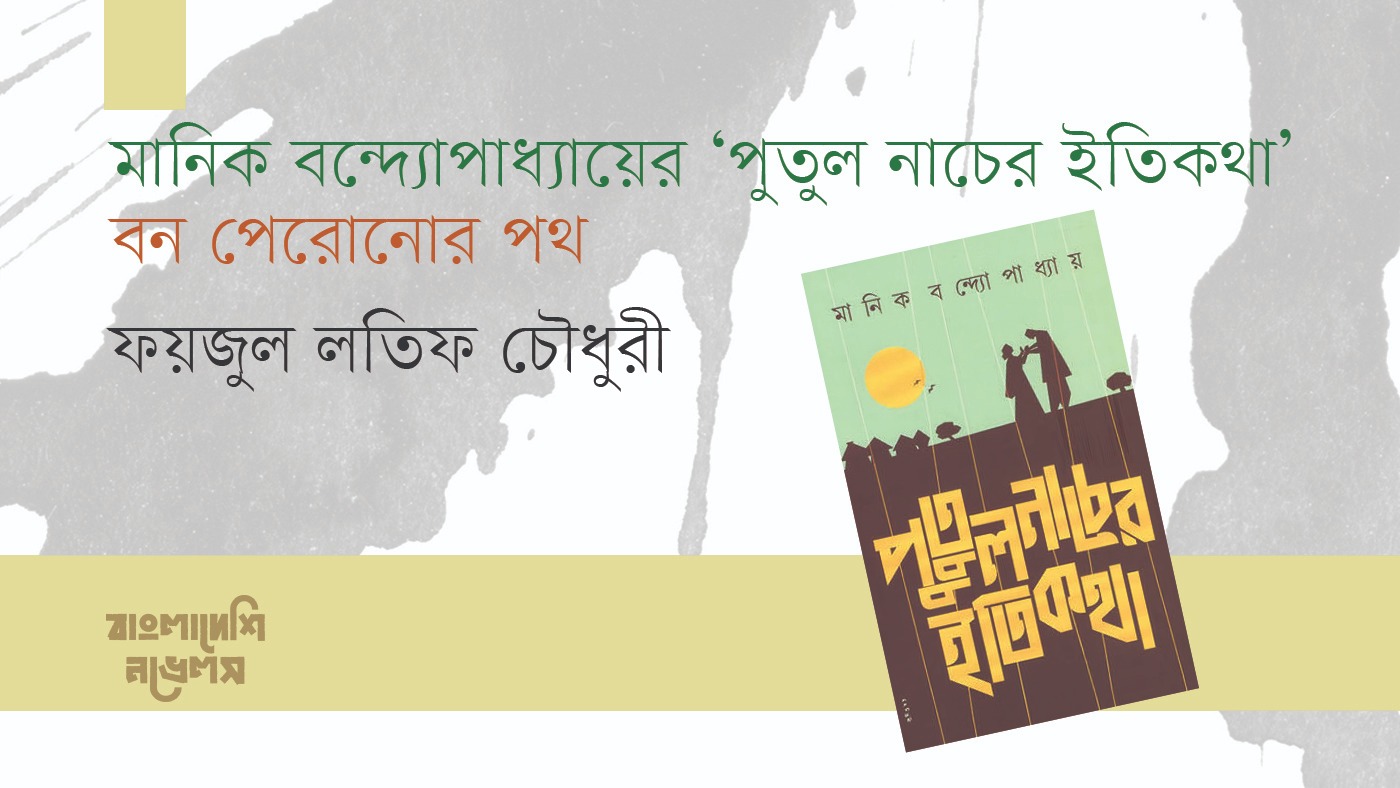উপন্যাসশিল্পের আধুনিক কৌশল রপ্ত করে লেখা হয়েছে ‘গোপনীয়তার মালিকানা’ উপন্যাসটি। ঔপন্যাসিক এই সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক হামীম কামরুল হক। তিনি প্রথম পুরুষের বয়ানে উপন্যাসের গল্প উপস্থাপন করেছেন। কোথাও ‘স্ট্রীম অব কন্সিয়াসনেস’ টেকনিক অবলম্বন করে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার ভেতর দিয়ে কাহিনী কিংবা ভাবনার জট খুলেছেন, কোথাও ড্রামাট্রিক মনোলগের মতো কল্পিত কিছু শ্রোতার সঙ্গে একপক্ষীয় আলাপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন গল্পকে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের সাথে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ডায়লগ থাকলেও এটি ডায়লগধর্মী উপন্যাস নয়। মায়াবাস্তবতার উপন্যাসে সেটির দরকারও পড়ে না। এ ধরনের উপন্যাসে একটি মাত্র চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে অনন্যা চরিত্রকে দেখা হয়। কাজেই উপন্যাস জুড়ে থাকে একটি সিঙ্গেল পয়েন্ট অব ভিউ। তবে মাত্র দুটি চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা হলেও দেখানোর মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকে, কেননা চোখের চেয়ে হৃদয় দিয়ে দেখা হয় বেশি। আর হৃদয় চোখকে ছাপিয়ে ওঠে বলেই দৃশ্যগত হয় হ্যালুসিনেশন বা মায়ার দুনিয়া। মানে বায়বীয় এবং বস্তুগত জগৎ মিশে একাকার হয়। এই উপন্যাসেও সেটা হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের যাপিত-জীবন, অযাপিত-জীবন, স্বপ্নপ্রসূত বা কল্পনাপ্রসূত-জীবন – সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। লেখক হামীম কামরুল হক যদি উপন্যাসের প্রটাগনিস্টয়ের ফিকশন্যাল অলটার ইগো হন, তাহলে উপন্যাসটিকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। যেভাবে আমরা জয়েসের ‘পোর্টেট অব দ্য আর্টিস্ট এজ অ্যা ইয়াং ম্যান’ উপন্যাসকে দেখে থাকি। জয়েসের এই উপন্যাসের মতো আলোচ্য উপন্যাসেও স্বপ্ন ও বাস্তবতা দ্বন্দ্ব আছে, দ্বন্দ্ব আছে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে। ‘পোর্টেট অব দ্য আর্টিস্ট এজ অ্যা ইয়াং ম্যান’ উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র কিশোর স্টিফেন ডেডালুসের ভেতর ধর্মীয়-দার্শনিক বোধের উন্মেষ ঘটে। অনুরূপভাবে এখানেও কিশোর প্রটাগনিস্ট আলো বা আলোপ্তগিনের ভেতর বুদ্ধিবৃত্তিক বোধের জাগরণ ঘটে। ডেডালুসের সন্ধানে থাকে স্পিরিচ্যুয়াল এসেন্স অব নেচার, আর এখানে এসে যেটা দাঁড়ায় সেক্সুয়াল এসেন্স অব বডিতে। এই যা পার্থক্য। পার্থক্য আরও আছে, তবে মূল পার্থক্য হল – ‘গোপনীয়তার মালিকানা’ ‘পোর্টেট অব দ্য আর্টিস্ট এজ অ্যা ইয়াং ম্যান’ এর মতো উপন্যাস হিসেবে পরিষ্কার ভাবে দাঁড়াতে পারেনি। অত ওয়েল রিটেন উপন্যাস এটি নয়। আরও দুটি উপন্যাসের সাথে গোপনীয়তার মালিকানার তুমূল তুলনা চলে। এক. স্টিফেন কিংয়ের ‘দ্য বডি’; দুই. রেইডার জনসনের ‘মাই লাইফ এজ এ ডগ’। উপন্যাস দুটিরই মূল বিষয় হল – Awakening to the body। দুটি উপন্যাসই মনোলগ ধাচে ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভে লেখা। তবে গোপনীয়তার মালিকানার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে নয়, বেশ গুছিয়ে।
গোপনীয়তার মালিকানা শুরু হয়েছে শুরুতে নামহীন কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্মৃতি আওড়ানোর ভেতর দিয়ে। অনেক পরে জানা যায় প্রটাগনিস্টের নাম আলোপ্তগিন, ডাকনাম আলো। মূলত উপন্যাসটি আলোর আত্মজীবনীই। আলো রাজশাহী শহরে ফেলে আসা তার কিশোরকালে আমাদের নিয়ে গেছেন – খানিকটা নিজেকে আবিস্কার করতে, খানিকটা নিজেকে পাঠকদের কাছে উন্মোচন করতে। কোথাও কোথাও সচেতনভাবে নিজেকে জাহির করার বিষয়টিও লক্ষ করা গেছে। এতে চরিত্রটি শুরুতেই তার গুরুত্ব কিছুটা হারিয়েছে। যেমন, উপন্যাসের এই অংশটা:
মামার কাছে জানলাম, তিনি আমার শিল্পসাহিত্যে আগ্রহ দেখে বলেছিলেন, ‘পৃথিবীর আধুনিক লেখা পড়তে হলে অন্তত দশজনের লেখা যেন পড়ি। কবিতায় ইয়েটস, ফার্নান্দো পাসোয়া, সি.ভি কাবাপি, হোর্সে লুই বোর্হেস, আর গল্প উপন্যাসে মার্সেল প্র“স্ত, টমাস মান, ফানৎস কাফকা, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ আর উইলিয়াম ফকনার।’ আমি বললাম মাত্র দশজন? ‘এদের পড়লেই তুমি দিনে দিনে এক হাজার জনের কাছে যেতে পারবে। কার কাছে নয় বল – শোপেনহাওয়ার কি নিৎসের। নিৎসের কাছে যদি তুমি যাও তুমি ফিরে আসবে জরথ্রুস্ত্রের কাছে আর জরথ্রুস্তের কাছ থেকে তুমি ফেরদৌসীর কাছে।’ বলে দিয়েছিলেন, ‘বাল্মীকি, ব্যাসদেব, হোমার, ভার্জিল, ওভিদ, দান্তে, ফেরদৌসী, সার্ভান্তেস, শেক্সপিয়ার, গ্যেটে, টলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ। দ্য গ্রেটেস্ট ডজন। ভারত দিয়ে শুরু ভারত দিয়েই শেষ। সাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদী বলতে যা বোঝায়। তারপর তোমার ইচ্ছামতো তুমি যা খুশি পড়ো, কিন্তু আগে ক্লাসিকস পড়া থাকলে বাকিসব জলের মতো বুঝে যাবে। …আমার কাছে মনে হয়েছে, উপন্যাসের যে গতিতে এই সময়ে আসার কথা ছিল, তার যোগ্য প্রতিনিধি তিনি (মিলান কুন্ডেরা)। কিন্তু আমরা এ সময় কুন্ডেরাকে ধরবো উপন্যাস তো চলে গেছে টমাস পিনশেনদের কাছে। তারপর মার্কেজ-ফুয়েন্তেসরা তো আছেনই, অন্যদিকে ডেভিড মালুফরাও আছেন।…’ [পৃ. ২২-২৩]
উপন্যাসে মামা হঠাৎ ঝটিকার মতো এসে তরুণ ভাগনার কাছে এমন সাহিত্যতত্ত্ব উগরে দিয়ে আবার চলে যান। উপন্যাসে তার ভূমিকা এমনই। এই অংশটুকু উপন্যাসে একেবারে অনর্থক একটি অংশ। না থাকলেই বরং ভালো হতো। এমন বেশকিছু ক্লান্তিকর বর্ণনা ডায়লগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। যেমন –
‘তা হয়। কিন্তু আসল বন্ধু তো সে, যার মনের কথাটা তোমার জানা, তোমার মনের কথা তার জানা, তুমি জীবনে কী চাও সে জানে, সে কী চায় তুমি জানো। এটা হল বন্ধুত্বের মিনিমাম লেভেল। তারপর বিপদে আপদে সাহায্য করা, সমস্ত কিছুতে থাকা – এটা তো আছেই। আমি একটা জিনিস ভেবে দেখেছি। ধরো, তোমার সঙ্গে কারো দশ বছরের সম্পর্ক, একদিন কোনো একটা কারণে সে এমন একটা কথা বলল, তাতে তোমার মনে হল, এই ছিল তাহলে ওর মনের কথা, এই হলো আসল চেহারা। এটা মনে করে তুমি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিলে। তাকে আর বন্ধু বলেই গণ্য করলে না। তাহলে ওই যে দশ বছরের এত আন্তরিকতা সৌহার্দ্য সব শেষ হয়ে গেল? তার কোনো মূল্য নেই? আমি মনে করি আছে। আমি মনে করি সবার মানবিক দুর্বলতা আছে। সবার ভেতরে শয়তান আছে, সবার ভেতরে বাস করে ভয়ঙ্কর খুনি একজন, পরশ্রীকাতর, হিংসুক, প্রতিশোধপ্রবণ একটা মানুষ – সেই মানুষটা দশ বছরে একবার বেরিয়ে আসতে চাইবে না? আর তার জন্যে বাদ বাকি সব কিছু শেষ? মানুষের দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে কি এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চনার মতো একটা কথা, একটা কাজই নষ্ট করে দিতে পারে? মানুষের সম্পর্ক কি সাদা শার্টের মতো? মানুষকে এইসব বস্তুগত তুলনা দিয়ে ব্যাখ্যার জায়গা থেকে যখন বের করে নিয়ে আসা যাবে তখনই মানুষের সঙ্গে বস্তুগত জায়গা থেকে দেখা পার্থক্যগুলো ধরা পড়বে। মানুষের মানবিক দুর্বলতা বাদে যেটুকু মানুষ তা-ই তার মনুষ্যত্ব।’ [পৃ. ২০]
এর চেয়েও লম্বা লম্বা ডায়লগ উপন্যাসে আছে। কোথাও কোথাও ডায়লগ হয়ে উঠেছে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের দেওয়া ভাষণের মতো ভীষণ বক্তব্যপ্রধান। ফলে সবমিলিয়ে শীর্ণকায় উপন্যাসটির সাধারণ গতি থেকে থেকে শ্লথ হয়ে এসেছে। কোথাও কোথাও আবার উপন্যাসটি প্রয়োজনের তুলনায় দ্রুত এগিয়ে গেছে; শুরুতে চরিত্রগুলো আসতে না আসতেই সরে গেছে। যেমন রাশু ও নিশিপর্ণার চরিত্রের বিস্তার আরও কিছুটা ঘটলে মন্দ হতো না।
উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেম-ভালোবাসা, তবে তথাকথিত শাশ্বত প্রেম বলতে যা বোঝায় সেই প্রেম নয় – কামনির্ভর মনস্তাত্ত্বিক প্রেম। যেমন – গুলশান খানের সঙ্গে আলোর মা কোহিনূরের প্রেম। একাত্তরে পাক-সেনা গুলশান খান অধঃস্তন সেনাদের মুখের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসে কোহিনূরকে। সে কোহিনূরকে বাগে এনে তারপর ভোগ করতে চায়। বাগে আনতে আনতে প্রেমে পড়ে যায় কোহিনূরের। কোহিনূরও একধরনের প্রেমে পড়ে যায় গুলশান খানের। বীণা আন্টি আলোকে জানায়, কোহিনূরের প্রেমে পড়ার কারণ হল গুলশান খান বিছানায় অতি দক্ষ ছিল। কোহিনূরের আরও অনেক প্রেমিক পুরুষ ছিল – যেমন সুবক্তগিন, ইলিয়াস আলী, হাদিদসহ আরও অনেকে, যাদের সঙ্গে তার প্রেমটা ছিল দেহের। মায়ের প্রতি আলোরও একধরনের ইনসেসচ্যুয়াল অনুভূতি ছিল। সেটা সে বীণা আন্টিকে জানানোর সাহস পায় না। আপন মনে আওড়াতে থাকে –
‘আমি মাঝে মাঝে মাকে খেয়াল করতাম। কখনো ব্রা পরা অবস্থায় বা খালি গায়েও তাকে দেখেছি। পরনে কেবল সায়া ছিল। ঠিক গোসল করার আগে বা পরে দু-একদিন। আমি কেমন একটা টান বোধ করেছিলাম। পরে নিজের কাছে নিজে মরমে মরে গেছিলাম। আমি এও দেখেছি, আম্মাও আমার দিকে মাঝে মাঝে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যখন আমি খালি গায়ে বা কাপড় বদলাচ্ছি। [পৃ ৩৩]’
মাও ছেলের প্রতি সেক্সুয়াল আকর্ষণ অনূভব করেন। সে কথা অবশ্য আলোর মা নিজে বীণা আন্টির কাছে স্বীকার করেছেন। বীণা আন্টি এবং আলোর ভেতরকার সম্পর্কও ছিল দেহ-সর্বস্ব। আলোকে যখন তার মা বীণা আন্টির বাড়িতে রেখে যায় তখন বীণা আন্টির কার্তিক মাস মানে রতিকাল যাচ্ছিলো! তাই ছেলের বয়সী একটা ছেলেকে তিনি কব্জা করতে ছাড়েননি। বীণা আন্টি আলোকে যৌনদাস বা ভোগের গিনিপিগ বানিয়ে ছাড়েন। সে কথা তিনি স্বীকার করেন গল্পকথক আলোর কাছে এই বলে যে, তার (আলোর) মন ও শরীরকে নিজের ল্যাবরেটরি বানানোটাই ছিল তার সজ্ঞানে করা এক এবং একমাত্র পাপ। বীণা আন্টির শরীরসঙ্গী আরও অনেকে ছিলেন, তাদের ভেতর উল্লেখযোগ্য হল অমিত। অমিতকে পেলে বীণা আন্টি চেটেপুটে খেয়ে ফেলতো। বর্ণনা সেভাবেই এসেছে। যারা ছিল রতিবাজ তাদের সঙ্গেই বীণা আন্টির যত সখ্য। সখ্য এই শর্তে যে, খালি শুতে হবে, বিয়ে নয়। বিয়েতে ঘোর আপত্তি ছিল বীণা আন্টির। একইভাবে আলোও বীণা আন্টি ছাড়া আর যে সব প্রেম করেছে সেগুলোও শরীরনির্ভর। যেমন, ব্রিটিশ পর্নোজগতের তারকা লিন্ডার সঙ্গে আলোর প্রেম। উপন্যাসের অন্যান্য মাইনর চরিত্ররাও শরীরনির্ভর প্রেমে সাড়া দিয়েছে। যেমন, কিশোরকালে বান্ধবী টিনা গল্পকথককে বিছানায় আসার জন্য বলেছিল। নিশিপর্ণাও প্রেম করেছিল দেহ দিয়ে। ছাত্রের ছোট বোন আরিয়ানা ক্ষণিক পরিচয়ের পরই যে কোনো মূল্যে গল্পকথকের সন্তানের মা হতে চেয়েছিল। এমনি করে উপন্যাসজুড়ে কেবল নারী-পুরুষের ভেতর শরীর লেনাদেনার সম্পর্ক। একমাত্র প্রকৃত ভালোবাসা ছিল কেবল রত্নদীপ আর শানুর ভেতর। যে ভালোবাসার জন্য শানু নিজের জীবন বিসর্জন দেন।
উপন্যাসে ছোট ছোট করে অনেক বিষয় এসেছে। যেমন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলো একজন ওয়ার বেবি বা যুদ্ধশিশু। তাই ঘুরে ফিরেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে পার্টিশনের কথা। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা। বাম রাজনীতির কথা। বিশ্বসাহিত্য ও দর্শনের কথা। অস্তিত্বের সংকটের কথা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা। প্রবাসজীবনের কথা। সম্পর্ক তৈরি ও সম্পর্ক ভাঙার কথা। আর খোলামেলা যৌনতা তো আছেই। আরও আছে আলোর মায়াজগতের গল্প। এত এত বিষয় মাত্র ৯৬ পৃষ্ঠার এক উপন্যাসে চেপেচুপে আটকে রাখতে গিয়ে উপন্যাসটি আর সুখপাঠ্য থাকেনি। খুব ঠাসা ঠাসা মনে হয়েছে। এমন সিরিয়াস প্লট আরও আরও বিস্তার দাবি করে।
উপন্যাসটির আর একটি সমস্যা আমার কাছে মনে হয়েছে সেটি হল: বীণা আন্টির চরিত্র। বীণা আন্টির সঙ্গে আলোর ইনসেসচুয়াল সম্পর্ক থাকে। মূলত বিণা আন্টিই এই উপন্যাসের নায়িকা। তার চরিত্র এখানে সেক্সুয়ালি এক্সট্রিম হিসেবে দেখানো হয়েছে। সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা হল তার সঙ্গে জড়িত টাইম এন্ড স্পেস নিয়ে। আশির দশকের শেষে এবং নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের ঢাকাতে বীণা আন্টির বাস। এ সময় তিনি সিঙ্গেল ওমান হিসেবে ঢাকায় থাকতেন। তাঁর ছিল অবাধ যৌনজীবন। তিনি এক একজন বিছানাসঙ্গীতে পালা করে বিছানায় ডেকে নিতেন। আর তার বিশেষ সঙ্গী হিসেবে অর্ধেক বয়সী সন্তান সম্পর্কের আলো তো ছিলই যাকে তিনি এনাল সেক্স সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি বাসায় পর্নো নায়িকাদের মতো ডিলডো পর্যন্ত রাখতেন! ঢাকায় ওই সময় কেন এখনও এমন একজন নারী বাস করবে আর কেউ কোনো নেতিবাচক কথা বলবে না, এটা ভাবা যায় না। আবার উপন্যাসটির সেটিং ঢাকা হওয়া সত্বেও ওই সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাবহুল রাজনীতির কোনো কথাই উঠে আসেনি। এসেছে বিশ্বসাহিত্যের কোথাই কী ঘটছে সেসব প্রসঙ্গ। তাহলে কি উপন্যাসিক সচেতন ভাবেই তার নিজস্ব বাস্তবতাকে এড়াতে চেয়েছেন? যেভাবে তিনি রাজশাহীর পদ্মা নদীর পার থেকে ছুটে এসেছেন সেভাবেই কি তিনি তার সময়ের বাংলাদেশ থেকে ছুটে পালাতে চাইছেন? স্কেপিজম স্বভাব কি তাকে শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে প্রবাসজীবনে? এবং তার এডিক্টেড টু বডিজ-কে কি আলটিমেট স্কেপিজম হিসেবে দেখা যায়? এমন নানা প্রশ্ন উঠে আসে। শেষপর্যন্ত আলোর অস্তিত্বের সংকটই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।
উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য হল, পদ্মা পারের দুটি দৃশ্য ও অন্ধকার গুহার ভেতরের দৃশ্যটি। এ কটি দৃশ্যতেই পরাবাস্তবতার ছোঁয়া আছে। এই দৃশ্যগুলো না থাকলে উপন্যাসটিকে হয়ত আর মায়াবাস্তবতার উপন্যাস হিসেবে দেখার সুযোগ থাকতো না। অতি মুন্সিয়ানার সঙ্গে উপন্যাসিক হামিম কামরুল হক এই বায়বীয় দৃশ্যগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষ করে এলিগরি অব কেভের দৃশ্যটি। এখানে এসে তিনি শতভাহ উৎরে গেছেন। পাঠক হিসেবে আমি মুগ্ধ হয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করেছি আসলে কী ঘটছে। খানিকটা বুঝেছি, খানিকটা বুঝিনি। আবার পড়েছি।
বাংলা সাহিত্যে এই ফর্মে খুব বেশি উপন্যাস লেখা হয়নি। কাজেই ফর্মটি অতি পরিচিত ফর্ম হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। হামীম কামরুল হকের এই উল্টোপথে যাত্রাটা শুভ হোক এবং তাঁর হাত ধরে আমরা অন্য বাস্তবতার আরো আরো উপন্যাস পড়ার সুযোগ পাই – এমনটিই প্রত্যাশা রইল।