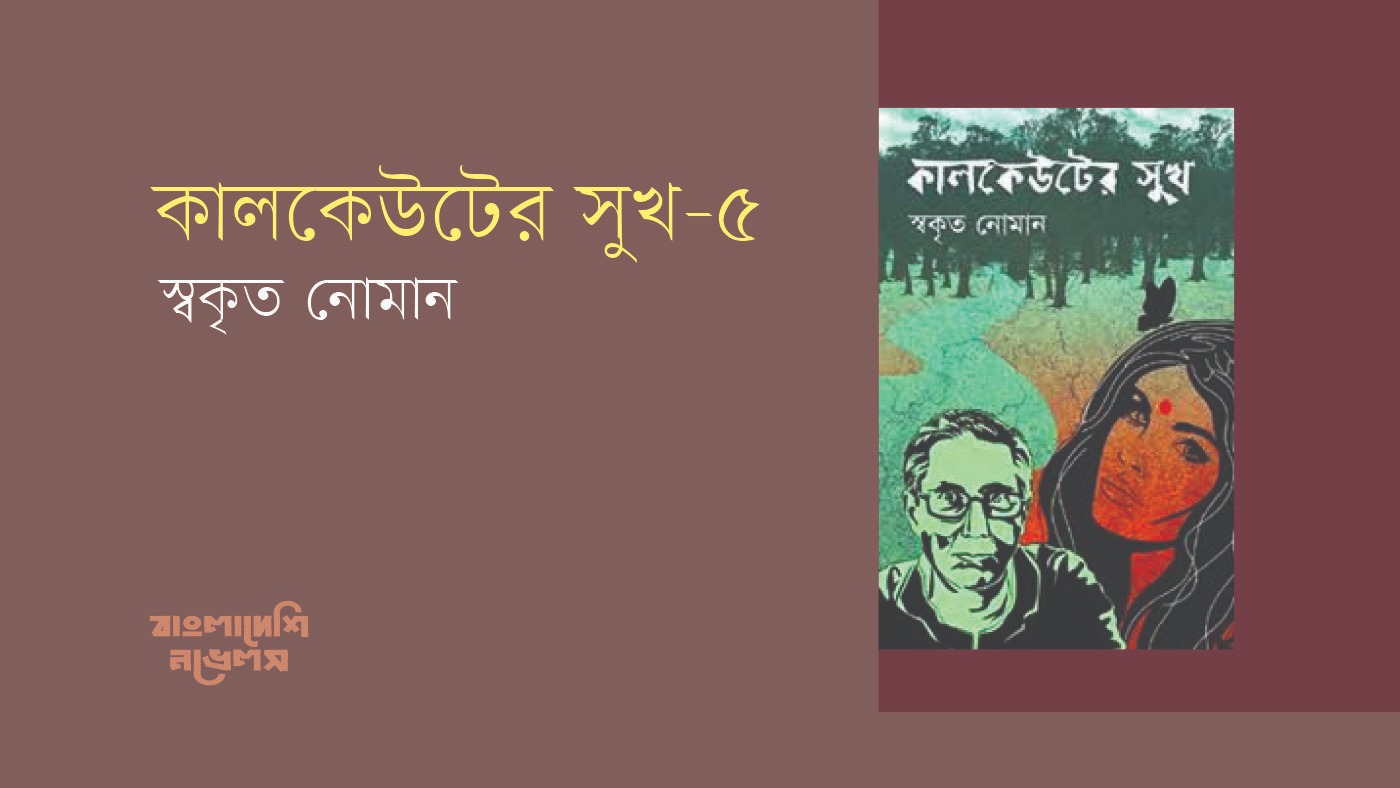কালকেউটের সুখ
স্বকৃত নোমান
পাঁচ.
এই চুনকুড়ি নদীর তীরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতে চেয়েছিলেন কেশব মাস্টার। বলেছিলেন জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান এমন এক অস্ত্র, এই অস্ত্র যার হাতে থাকে শত্রু তাকে সহজে ঘায়েল করতে পারে না। কিন্তু দুই মেয়ের অবাধ্যতা এবং আজানা শত্রুর একের পর এক শত্রুতা জ্ঞানের শক্তি সম্পর্কে তাকে সংশয়ী করে তুলল – কোথায় জ্ঞানের শক্তি? আমি তো সবসময় জ্ঞানচর্চার মধ্যেই আছি। নিজে যা শিখেছি মানুষের মধ্যে বিলাচ্ছি। ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়াচ্ছি। কই, জয় তো আমার হচ্ছে না। শত্রুর শত্রুতা আমাকে জেরবার করে দিচ্ছে, জীবনযুদ্ধে তো কেবল হেরেই যাচ্ছি। হারতে হারতে ঢুকে যাচ্ছি এক অতল অন্ধকার খাদে।
নমিতা ও দীপিকার ধর্মান্তর এবং তাদের হারিয়ে চারুবালার মনোদৈহিক অসুস্থতা মাস্টারকে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে। দুই মেয়ের শূন্যতা চারুবালার ভেতর গভীর এক হাহাকার তৈরি করে। বাইরে তাদের গালাগাল করে, জীবনে কখনো মেয়ে বলে স্বীকার করবে না বলে কত শপথ করে, কিন্তু ভেতরটা তার হাপরের মতো জ্বলে। সংসারের কাজ করতে করতে নিজ মনে অনর্গল বকে, ‘কুকুর-বাঁদর পেটে ধুরেলাম। আমাকে কষ্ট দেবার জন্যি তারা দুনিয়ায় আইয়েচে। নিজি না খাইয়ে খাওয়াইচি, না পুরে পরাইচি। এত নেমকহারাম হতি পাল্ল! দোষ আমারই, পেটেত্তে পড়ার সাতে সাতে গলা টিপে মাইরে ফ্যাললাম না ক্যানো।’
বকতে বকতে একসময় ফোঁপাতে শুরু করে। নোনাজল চোখের কোটর ছেড়ে গাল ছুঁলে পরে দুঃখ আরো উথলে ওঠে। কাজের চেয়ে কান্নাটা তখন জরুরি হয়ে পড়ে। কাজকাম ফেলে দুই পা মেলে ঘরের পৈঠায় বসে ফোঁপায় আর চোখের জলে ছিনা ভাসায়। কোন দুঃখে বেলা-অবেলায় সে এভাবে কাঁদে বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। মাস্টার তখন বাড়ি থাকলে বাশ্ঘরের চকির ওপর গুম মেরে বসে থাকেন। অসহ্য ঠেকলে চুপচাপ নদীর তীরে গোলপাতার মুড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। কামকাতর শঙ্খিনীর মতো ছুটে চলা সোতস্বিনীর উথালি-পাথালি ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার ভেতরেও উথাল-পাথাল শুরু হয়। যুদ্ধে স্বজন হারানোর যে বেদনা বহু বছর ধরে ক্ষণে ক্ষণে বুকের ভেতর বৈশাখী বাওড় হয়ে বয়ে যায় তা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। দিগন্তের বিশাল শূন্যতা ঢুকে পড়ে তার বুকের ভেতর। বেদনার চাপে চোখ দুটো ভারী হয়ে ওঠে। কেঁদেকেটে বুকটাকে হালকা করে তারপর ঘরে ফেরেন।
তখন আশ্বিন মাস। মুকনোলির প্রান্তরে তখনো হাঁটুজল। সাঁঝের বেলায় হেঁশেলে বসে তালের পিঠা বানাচ্ছিল চারুবালা। চালের গুঁড়ে রস মাখতে মাখতে গুনগুন করে গান ধরে –
বেলা দুই প্রহরের কালে
বাঁশি বাজলো রাই বলে
আমি কেমনে যাই বলো
ওই কদম্বের তলে।
কে জানে কী স্মৃতি লুকিয়ে ছিল গানটার মধ্যে, হয়ত দীপিকা প্রায়ই গানটা গাইত বলে, দারুণ স্মৃতিকাতর হয়ে উঠল চারুবালা। আহা, তালের পিঠা কী যে পছন্দ করত মেয়েটা। আশ্বিনের অকালবর্ষায় হেঁশেলে বসে চারুবালা গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে কলাপাতায় মুড়ে পিঠাগুলো যখন খোলায় ভাজতে দিত, আনন্দে হাত-পা নাচাত দীপিকা। তর সইত না তার। পারলে তো কাঁচা আঠা খেয়ে ফেলে। এই আদেখলামির জন্য কত মারই না খেয়েছে মায়ের। তবু যে বেহায়া সেই বেহায়া, খানিক পর পোষা বিড়ালের মতো আবার মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করবে, আঁচল ধরে কাঁইকুঁই করবে।
চারুবালার গুনগুনানি থেমে যায়। বুকের ভেতর হাপরের আগুনটা উস্কে ওঠে বুঝি। ডানে-বাঁয়ে কাকে যেন খোঁজে। না, কেউ নেই। তাপসী ও গোপেশ বাশঘরে বাবার কাছে উপনিষদের শ্লোক শুনছে। কেমন যেন লাগে তার, খুব একা মনে হয় নিজেকে। পৃথিবীতে যেন কেউ নেই তার, যেন এক নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে ভেসে চলা একটা শূন্য নৌকার পাটায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে যুগ যুগ ধরে। নৌকাটা চলছে তো চলছেই… গন্তব্যহীন।
আটামাখা হাতে হেঁশেল থেকে বেরিয়ে চুনকুড়ির আড়ায় এসে দাঁড়ায় চারুবালা। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ, নদীতে জোয়ার, ওপারের জঙ্গলে ভয়াল নীরবতা। থেমে থেমে ঝিল্লির ডাক আর মশাদের গুঞ্জরণ। বাশঘর থেকে ভেসে আসছে মাস্টারের গলা, ‘যস্তু সর্বাণি ভুতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি।’ আলো-অন্ধকারে দক্ষিণে যতদূর চোখ যায় অপলক চেয়ে থাকে চারুবালা। পথের একটা সাদা রেখা মিশে গেছে দক্ষিণ দিগন্তের দিকে। রেখাটা ধরে কে যেন আসছে, মনে হয় তার। হয়ত নমিতা, অথবা দীপিকা। তাদের গলা শুনতে পায় সে। এগিয়ে আনতে সে আরো সামনে এগোয়। হাট থেকে, ক্ষেত থেকে, বাদা থেকে মানুষেরা বাড়ি ফিরছে। চেনা-অচেনা কত মুখ দেখতে পায়, যে মুখ দেখার জন্য সে ব্যাকুল, অথচ সেই মুখের দেখা পায় না। বুকটা ভেঙে আসে তার। ভেতরে জ্বলতে থাকা হাপরটার আগুন আরো উস্কে ওঠে। জ্বলন্ত হাপরের তাপে গলে গলে দু-গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা নোনাজল গড়ায়। খুব ইচ্ছে করে এই নীরব রাস্তায় দাঁড়িয়ে দীপিকা-নমিতা বলে জোরে হাঁক দিতে। যদি তারা শুনতে পায়।
আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ধীর পায়ে আবার সে হেঁশেলে ফেরে। কিন্তু বুকের ভেতর জ্বলতে থাকা হাপরটা কিছুতেই নেভাতে পারে না, চোখের বাঁধভাঙা অনিরুদ্ধ জল কিছুতেই থামাতে পারে না।
হঠাৎ কী যে হলো তার, হাপরটার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল বুঝি, হেঁশেলের শুকনো খড়-পাতার ওপর ঢলে পড়ল। ওদিকে বাতাসের তোড়ে বাশঘরের হারিকেনটা নিভে যায়। আগুন ধরাতে হেঁশেলে এসে মাকে অচেতন পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে ওঠে তাপসী, ‘ও বাবা গো, মার কী হুলো।’
সারা বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যায়। মাস্টার ছুটে আসেন। পেছনে গোপেশও। ধরাধরি করে চারুবালাকে বাশ্ঘরের চকিতে এনে শুইয়ে দিল। মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালল। আলমিরা থেকে একটা শিশি বের করে মাস্টার ছিপি খুলে দু-ফোঁটা তরল পদার্থ বউয়ের জিবের আগায় ঢেলে দিলেন। ততক্ষণে পড়শিরাও ছুটে এলো। সবার মুখে সহানুভূতি, আহা, সারা দিন কত খাটাখাটনি করে বেচারি, অতিরিক্ত পরিশ্রমেই বুঝি এই দশা। কোন গোপন কারণে তার এই দশা কেউ জানে না, কেউ বোঝে না। কে রাখে কার মনের খবর? রাখেন তো কেবল একজন, তার শোয়ামি। বউয়ের চোখ দেখে তিনি বুঝতে পারেন কোন বেদনার উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার বুকে।
পরদিন শোয়ামিকে কিছু না জানিয়ে এক হাঁড়ি তালের পিঠাসহ গোপেশকে রতনপুর পাঠিয়ে দিল চারুবালা, ‘যা বাবা, তোর দিদিরে একবার দিকে আয়।’
গোপেশ তো যাবেই না। বাবা শুনলে আস্ত রাখবে? কিন্তু মায়ের মনের গতিক বুঝে রাজি না হয়ে পারল না। রোজ সাইকেল হাঁকিয়ে সে হরিনগর স্কুলে যায়। হরিনগর থেকে রতনপুর যেতে কতক্ষণই-বা লাগবে। প্যাডেলটা জোরে মারলে বিকেলের মধ্যে বাড়ি ফেরা তো কঠিন কিছু নয়।
বিকেল গড়িয়ে সাঁঝ নামল, সাঁঝ গড়িয়ে রাত, অথচ গোপেশের ফেরার নাম নেই। মাস্টার অস্থির হয়ে উঠলেন। কোথায় গেল ছেলেটা? বউকে বারবার জিজ্ঞেস করেন, ‘কই গেল ছাওয়ালডা? তোমারে কিচু বুলে যায়নি?’ চারুবালা এড়িয়ে যায়, না শোনার ভান করে থাকে। শোয়ামির অস্থিরতা দেখে শেষে সত্যি কথাটা স্বীকার না করে পারল না, ‘গোপেশরে আমি এট্টা কাজে পাঠাইচি।’ কোথায়, কী কাজ জানতে চাইলেন মাস্টার। চারুবালা জবাব দেয় না, মাথা নুইয়ে চুপচাপ আঁচলের কোণায় গিঁট পাকায়।
বউয়ের মুখের দিকে গভীর চোখে তাকালেন মাস্টার, কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হলো না, যা বোঝার বুঝে গেলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায়, রাগলে পরে তার গলাটা যেমন হয়, বউয়ের চোখে চোখ রেখে বললেন, ‘তারে তুমি রতনপুর পাঠাইচো?’
ধরা পড়ে গেল চারুবালা। অপরাধীর চোখে একবার শোয়ামির মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল। খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে মাস্টার গুম মেরে যান। বউয়ের মনের হাল বুঝে ছেলের ফেরা-না-ফেরা নিয়ে আর কোনো কথা বললেন না। বলার আছেই-বা কী? তিনি পুরুষ, মন তার পাথরের মতো কঠিন। কঠিন না হলেও চাইলেই কঠিন করে তুলতে পারেন। কিন্তু মায়ের মন তো পাঁক-কাদায় গড়া, সামান্য বৃষ্টিতেই থিকথিকে হয়ে যায়।
দুদিন পর তিন সের ওজনের মস্ত একটা কাতল আর এক হাঁড়ি পিঠাপুলি নিয়ে বাড়ি ফিরল গোপেশ। বোন-বোনাইয়ের আদর-আপ্যায়নে খুশি তার পেটে ধরছে না। পাঁটা মোরগ জবাই দিয়েছে, ডেগি মুরগির রোস্ট করেছে, চিকন চালের পোলাও তো ছিলই। সকালের নাশতার কথা কী আর বলবে। তেলে ভাজা, খোলায় ভাজা কত রকমের পিঠা যে বানাল। বানাবে না? জামাইবাবু কি তাদের চেয়ে কম ধনী? কত জমিজিরাত তাদের। বিরাট একখানা বাড়ি, বাড়ির সামনে বিরাট দিঘি – সাঁতরে পাড়ি দিতে গেলে দমে কুলোয় না। বড়শি ফেললেই বড় বড় রুই-কাতল ওঠে। ফেরার সময় দিদি জোর করে কাতলটা দিয়েছে। জামাইবাবু পকেটে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলেছে, ‘মারে নে আবার বেড়াতি আইসো ভাই।’
হঠাৎ চারুবালার আসল কথাটা মনে পড়ে গেল, ‘গরুর মাংসে হাত দিসনি তো বাবা?’
নাকমুখ কুঁচকিয়ে গোপেশ বলল, ‘তুমি পাগল হুলে মা? আমি গরুর মাংস খাব। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মায়দিও তো গরুর মাংস খাওয়া ধরিনি। জামাইবাবু তো বাড়ি গরুর মাংস প্রায় আনেই না।’
চারুবালার চেহারায় খুশির ঝলক ওঠে, চোখে পানি ধরে না তার। যাক, মেয়েটা তবে সুখেই আছে। একটিবার দেখার জন্য মনটা তার দারুণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গোপেশের হাতখানা চেপে ধরে রেখে বলে, ‘আহা, একন দেখতি কেরাম হুয়েছে আমার দীপু? শুকিয়ে গেচে বুঝি? নাকি বেশি খাইয়ে আবার মোটা হুয়ে গেচে! আচ্ছা, আমার কতা কী বুললো? তোর বাবার কতা কিচু জানতি চায়নি? নিচ্চই ম্যালা কান্নাকাটি কুরেচে। হ্যাঁ রে বাবা, তোর ভাগ্নে-বুনঝিরা দেখতি কার মতো হুয়েচে? ওরা দাদু-দিদিমার কতা বলে না?’
জবাব দিতে দিতে গোপেশ হাঁপিয়ে ওঠে। একই উত্তর বারবার দেয়, তবু চারুবালা ফের জিজ্ঞেস করে। বহুদিনের ভুখার মতো গোপেশের কথাগুলো সে গিলতে থাকে আর বারবার আঁচলে আনন্দের অশ্রু মোছে।
দ্রুত তার আনন্দ বিপুল বিষাদে রূপ নেয়। বাদার নির্জনে বসে বুঝি অনন্ত ম-ল, নাকি নরেন ম-ল তাকে কঠিন বিদ্রুপ করে, ‘ছি! ছি! ছি! তুমি মোল্লেবাড়ির বউ হুয়ে জাতির মুকি কালি দেয়া এট্টা বেজাত মাইয়ের জন্যি কানতি বুসলে?’
কে জানে, এ হয়ত তারই কণ্ঠস্বর। নিজেই হয়ত নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে সে, তার চৌদ্দপুরুষ বামুন, ঘরে কোনোদিন ম্লেচ্ছ যবনের পা পড়েনি, অথচ সে কিনা এখন জাতকুলহারা মেয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।
গোপেশকে একটা কথাও আর জিজ্ঞেস করে না সে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে, চেহারায় ফুটে ওঠে রূঢ় ছাপ। রতনপুরের দিকে ছুটতে থাকা মনটার রাশ টেনে ধরে। নমিতা বা দীপিকা নামে তার কোনো সন্তান নেই – পুরনো শপথটা মনে মনে আবার নতুনভাবে করে। তারপর গুম মেরে বসে থাকে। থাকে তো থাকেই। পুবের সূর্য পশ্চিমে ঢলে, তবু তার ওঠার নাম নেই।
কিন্তু মনের সঙ্গে কি লড়া যায়? তাও আবার মায়ের মন। তার কী সাধ্য সন্তানকে মন থেকে মুছে ফেলে। শপথের কথা সে আবার ভুলে যায়, আবার ভারী হয়ে আসে দুই চোখ। নীরব কান্না ধীরে ধীরে সরব হয়, তারপর রূপান্তরিত হয় সকরুণ বিলাপে – নমিতা ও দীপিকার আবেগভরা তামাদি স্মৃতির বিরক্তিকর বেসুরো পাঁচালি। দুঃখের মাত্রাটা বেশি মাত্রায় উথলে উঠলে বিলাপের ফাঁকে মাঝেমধ্যে মাটিও চাপড়ায়। তার এই টানা বিলাপ দেখে, এই মানসিক অবস্থার কথা ভেবে মাস্টারের পাথরে গড়া মনটাও বুঝি টলে যায়। পঁয়তাল্লিশ বছরের চারুবালা, আহা, কত না রূপ-যৌবন ছিল তার। যেদিন শুনল তার বড় মেয়ে তাকে না জানিয়ে মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে ফেলেছে সেদিন থেকেই যে শরীরটায় ভাটা পড়তে শুরু করল, ভাটা আর থামল না। তার শরীরটা এখন মরাগাঙ। দুই চোপার হাড় বেরিয়ে গেছে, চোখের নিচে কালিদাগ পড়েছে, টান টান শরীরটা কেমন বেঁকে গেছে। এই শোক না থামলে দু-তিন বছর পর তার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভেবে দারুণ বিচলিত বোধ করেন মাস্টার। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করেন। মন বলে, অনেক তো হয়েছে, আর কত? সন্তান তো তোমারই ঔরসের। ঈশ্বরও তো তার সৃষ্টির সব অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তুমি তো ঈশ্বর নও, রক্তে-মাংসে গড়া সামান্য মানুষ মাত্র। অহংকার তো তোমার সাজে না। অহংকার দূর করো কেশব, সব অতীত মুছে দাও, ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলো আবার জোড়া লাগাও। দুই মেয়ে এসে যদি তোমার কাছে ক্ষমা চায়, ক্ষমা করে দিয়ে তুমি তাদের বুকে টেনে নাও। তারা ধর্ম ছেড়েছে, মানুষ তো আছে এখনো। ধর্ম ছাড়লে মানুষ কুকুর-বিড়াল হয়ে যায় না। আচ্ছা, হলোই না হয়। কুকুর-বিড়াল কি মানুষের সঙ্গে বসবাস করে না? তুমি শান্ত হও কেশব, মনকে সহজ কর। আসুক তারা, হেসেখেলে বাবার বাড়ি দুদিন বেড়িয়ে যাক। মণ্ডলবাড়ি আবার হাসি-আনন্দে ভরে উঠুক।
কিন্তু চারুবালার বিলাপ যখন থেমে যায়, কেঁদেকেটে হয়রান হয়ে আবার যখন সে ঘর-সংসারে মনোযোগী হয়, চুনকুড়ির জল থেকে অনন্ত মণ্ডলের গুলিবিদ্ধ লাশ হামাগুড়ি দিয়ে আড়ার ওপর উঠে করুণকণ্ঠে বিলাপ শুরু করে, ‘আমার কোনো অপরাধ ছেলো না কেশু। কেবল বাপ-ঠাকুদ্দার ধর্ম ছাড়িনি বুলে তারা আমারে এই গাঙের ঠাণ্ডা জলে কান ধুরে দাঁড় কুরে রাকে, আমার স্বাদের ঘরটা জ্বালিয়ে দ্যায়, আমারই চোকের সামনে তোর মারে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। শুদু ধর্মের কারণে, আমি হিন্দু ধর্ম ছাড়তি চাইনি বুলে তারা বন্দুকের গুলিতে আমার বুকডা ফুটো কুরে দেচে।’
বৈশাখী বাওড়ের মতো মুহূর্তেই মাস্টারের মতি পাল্টে যায়। যে মন তাকে শান্ত হতে বলেছিল, সন্তানদের প্রতি সদয় হতে বলেছিল, সকল অতীত মুছে দিয়ে হাসি-আনন্দে ভরা এক সুন্দর ভবিষ্যতের কথা বলেছিল, সেই মনই আবার বেঁকে বসে – না, প্রশ্নই আসে না। বউ কেন, আমাকেও যদি মরতে হয় তাতেও আপত্তি নেই। নাকের ডগায় দম থাকতে কখনোই আমি জাতকুলহারা মেয়েদের নরেন মণ্ডল আর অনন্ত মণ্ডলের স্মৃতিঘেরা এই মণ্ডলবাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেব না।
দুই মনের নীরব লড়াই চলতে থাকে অবিরাম। এক মন হারে তো আরেক মন জেতে। নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে নিদারুণ বিষণ্নতা গ্রাস করল তাকে, সীমাহীন এক অস্থিরতা সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারেন না। না সংসারে, না স্কুলে। তার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা যাযাবর মানুষটা জেগে ওঠে। তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় দূরের পথে। সারা দিন হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ান। হরিনগরে ওষুদের দোকানে গেলে সাইকেলটা হাঁকিয়ে ফের বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না, কলা-রুটি খেয়ে দোকানেই শুয়ে থাকেন। কোনো কাজে একবার দূরে কোথাও গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। কত জায়গায় কত চেনাজানা মানুষ তার, কারো বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে দেন। জীবনের সুখ-শান্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, পথে পথে ঘুরে তিনি তারই সন্ধান করে বেড়ান। আট পুরুষের স্মৃতিঘেরা মণ্ডলবাড়িটার জন্য একদিন খুব টান ছিল তার। যেখানে যত দূরেই যেতেন তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য মনটা চটফট করত। অথচ এখন, ভগবানের কী লীলা, বাড়িটার প্রতি তার বিন্দুমাত্র মায়া নেই। কেমন অচেনা লাগে বাড়িটা। কেবলই মনে হয়, না, এ বাড়ি তার নয়, অন্য কারো সম্পত্তি। তিনি এখানে আশ্রিত মাত্র। যেকোনো দিন পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে পড়তে হবে।
তার এই উদাসীনতায় ছন্নছাড়ার পথ ধরল সোনার সংসার। গোপেশ বড় হয়েছে। সংসারের হাল ধরার মতো বয়স যদিও হয়নি, তবু যতটা পারে ধরে। ওদিকে স্কুলের ছাত্রছাত্রী কমতে থাকে। দু-তিন মাসের বেতন বাকি পড়ায় মাস্টার দুজনও আসা বন্ধ করে দিয়েছে। অগত্যা স্কুলটার হাল ধরতে হয় তাপসীকে। এবার সে ম্যাট্টিক দিয়েছে, রেজাল্ট বেরোতে বেশি দেরি নেই। ফলাফল ভালো হলে কলেজে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে। এই অবসরে সে স্কুলের প্রতি মনোযোগী হলো।
স্কুলটা চালু রাখতে মেয়ের চেষ্টা দেখে মাস্টারের মনে বুঝি কিছুটা শান্তি ফিরল। নমিতাকে নিয়ে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, যে স্বপ্ন দেখেছিলেন দীপিকাকে নিয়ে, সেই স্বপ্ন বুঝি পূরণ করবে তার ছোট মেয়ে। ভেবে শান্তির সুবাতাস দোলা দিয়ে যায় তার বিক্ষিপ্ত মনে। দু-এক মাস আর কোথাও যান না, হাটে-বাজারে গেলে ঠিক সময় বাড়ি ফেরেন। ভেতরের যাযাবর মানুষটা বুঝি আবার ঘুমিয়ে পড়ে। মেয়ের সঙ্গে মিলে স্কুলটা আবার চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন। চাঙ্গা হয়ও। ছাত্রছাত্রীরা আবার ফিরতে শুরু করল। নিষ্পাপ শিশুদের মুখের দিকে তাকালে তার মনে হয়, না, পৃথিবীতে কোনো শোক নেই, দুঃখ নেই। এই গরানপুর যেন এক স্বর্গভূমি। এই গ্রাম ছেড়ে তিনি আর কোথাও যাবেন না। কোনোদিনও না।
কিন্তু চারুবালার তামাদি শোক আবার যখন উথলে ওঠে, আবার যখন আগের মতো দুই মেয়ের জন্য বিলাপ শুরু করে, মাস্টারের মনটা তখন আবার উতলা হয়ে ওঠে, ঘুমন্ত যাযাবর মানুষটা আবার জেগে ওঠে, তাকে আবার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘর থেকে পথে। আজ মুন্সিগঞ্জ তো কাল গাবুরা, পরশু শ্যামনগর তো তরশু কাশিমারি। অথবা সীমান্তের চোরাইপথ পাড়ি দিয়ে সন্দেশখালী। সেখানে তার দিদি আছে, জামাইবাবু আছে, ভাগ্নে-বোনঝিরা আছে, আছে কত আত্মীয়-স্বজন। তাদের সঙ্গে দেখা হলে ভারী মনটা হালকা হয়।
না, শেষ পর্যন্ত তাপসীর একার পক্ষে স্কুলটা চালু রাখা সম্ভব হলো না। স্বভাবে সে ঠাণ্ডা মেজাজের, গম্ভীর। চালচলনেও ধীরস্থির। কথা বলে কম, যা বলে ভেবেচিন্তে বলে। অল্প বয়সেই তার মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, অনেকটা বাবার মতো, যার কারণে গ্রামের ছোট-বড় সবাই তাকে অন্য চোখে দেখে। মানুষের মুখে মুখে তার সুনাম। মোল্লেপাড়ার হিন্দুরা বলে, দুই মেয়ে তো মাস্টারের মান-সম্মান সব খেয়েছে, কিন্তু এই মেয়েটা আলাদা। মাস্টারের স্বপ্ন-স্বাধ পূরণ করলে তাপসীই করবে। ভগবানের আশীর্বাদ আছে মেয়েটার ওপর।
কিন্তু সে তো মেয়ে, আশীর্বাদ থাকলে আর কতটাই আছে। তবু চেষ্টায় তার কমতি ছিল না। কিন্তু আশ্বিনে ঝড়ে স্কুলের ছাওড়াটা উড়ে যাওয়ায় মনোবল ভেঙে গেল বেচারির। তুফানটাও ছিল ভয়ংকর। বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় আশি থেকে নব্বই মাইল। বাতাসের এমন তোড়ে কারো ডেরা-চালা কি আর আস্ত থাকে? কত ঘরের চাল যে উড়ে গেল। স্কুলের চালটা উড়ে কোথায় গিয়ে পড়ল পাত্তা থাকল না। ভোরে ঝড় থামল, কিন্তু বৃষ্টি থামল না। পরদিনও না। তারপর দিনও না। আশ্বিনের বৃষ্টি উজাতে উজাতে কার্তিকে গিয়ে ঠেকল। টানা দশ দিনের তুমুল বৃষ্টিতে জনপদে সমুদ্র হানা দিল। ভিটা-নাবাল সব জলে একাকার। মুকনোলির প্রান্তরের কাশবনও ডুবে গেল। যেদিকে চোখ যায় কেবল জল আর জল। দিদিকে দেখার নাম করে সন্দেশখালী গেছেন মাস্টার। তিন দিনের মধ্যে ফেরার কথা, কিন্তু ঝড়বৃষ্টির কারণে পারলেন না। প্রায় পনেরো দিন পর বাড়ি ফিরে তার স্বাধের স্কুলের দশা দেখে মনের অবস্থা তো বেহাল। শূন্যভিটার দুই কোণায় শুধু দুটো কাঠের খুঁটি কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে। দেশ স্বাধীনের পর বাড়ি ফিরে পোড়া ভিটার যে হাল দেখেছিলেন, অনেকটা তাই। তখন পুড়েছিল আগুনে, এখন উড়ে গেছে তুফানে – ফারাক শুধু এটুকু। ব্ল্যাকবোর্ডটা উল্টে আছে পেয়ারাগাছটার তলায়, পায়া ভাঙা হাতলচেয়ারটায় শ্যাওলা ধরে আছে, কাদায় উঁকি দিচ্ছে চকের প্যাকেটটা।
দুই খুঁটির একটি ধরে দাঁড়িয়ে উদোম ভিটার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন মাস্টার। বুকের ভেতর শোকের পাথরটা নড়েচড়ে ওঠে। যেন বা সন্তান হারানোর শোক। দুই গণ্ড বেয়ে জল গড়াতে থাকে। নিঃশব্দের কান্না। বুঝ হওয়ার পর তাপসী সেদিন প্রথম বাবাকে কাঁদতে দেখল। দু-হাতে বাবার দু-গাল মুছে দিতে দিতে তারও কান্না পায়। ওড়নায় চোখ মুছে কাঁপা গলায় সে বাবাকে শাসায়, ‘দ্যাকো শরীলডার কী হাল কুরেচে। ইস্, সারা গায় কী মশার কামড়ের দাগ! রাত্তিরি মশারির খোলে শুউনি? পিসির বাড়ি কি মশারি নি? আর কোনোদিন তুমি সন্দেশখালী যাবার কতা বলবা না। হাঁটো, ঘরে হাঁটো।’
মাস্টার নড়েন না। শোক তার আরো উথলে ওঠে, চোখের আড়ভাঙা স্রোত আরো বাড়ে। বাবার হাত ধরে টানতে থাকে তাপসী, ‘ওটো বাবা ওটো, ঘরে হাঁটো।’ কিন্তু একচুলও নড়ানো যায় না তাকে, দু-হাতে খুঁটিটা আঁকড়ে ধরে তিনি আগের মতো নিঃশব্দে কেঁদে চলেন। তাপসী আর কী করে, বাবার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সেও ফোঁপাতে থাকে।
: নমির বাবা!
পেয়ারগাছটার তলায় চারুবালার গলা শোনা যায়। মাস্টারের অশ্রুভেজা ঝাপসা চোখ সেদিকে ফেরে। বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, যে মুখ তার সারা জীবনের আনন্দ-বেদনার সাক্ষী, বুকটা ফেটে যেতে চায় তার। নিঃশব্দের কান্না সশব্দে বিস্ফারিত হয়। শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে তিনি হাঁটু মুড়ে ভেজা মাটিতে বসে পড়েন।