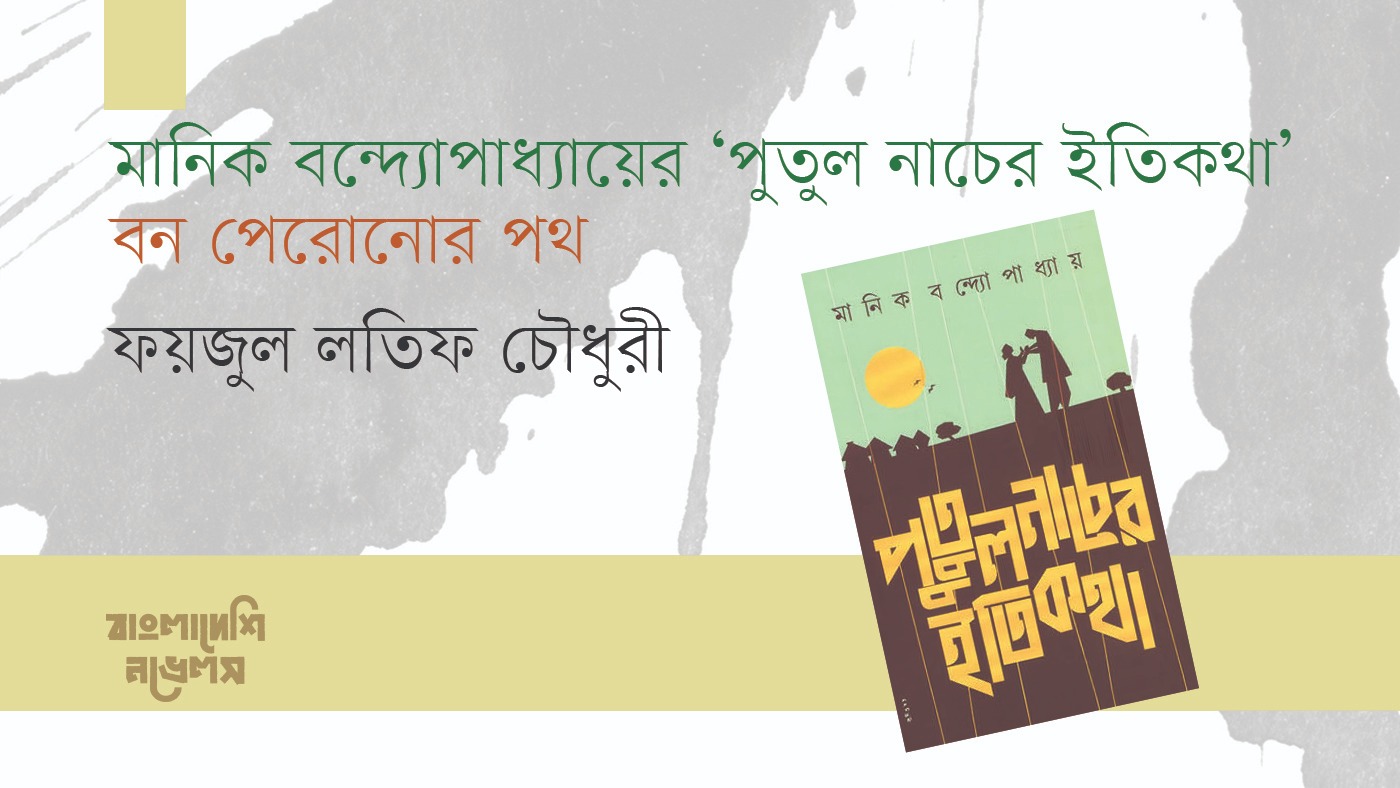ইমদাদুল হক মিলন (জন্ম: ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, তৎকালীন ঢাকার বিক্রমপুরের লৌহজঙের পয়শা গ্রামে) পেশায় লেখক ও সাংবাদিক। চারপাশে ঘটতে থাকা অবিরাম নেতিবাচকতার ভেতরেও শেষপর্যন্ত তিনি আশাবাদের প্রতি দায়বদ্ধ। প্রশান্তি তাঁর কাম্য। শিল্পের উদারতা আর সহমর্মিতার ওপর ভর করে তিনি শোনেন মানবতার আর্তনাদ। সমৃদ্ধ ও মনোমুগ্ধকর সংস্কৃতির ঘন রস পান করে তিনি নিজের, পরিজনের আর পরিচিত মানুষের দুশ্চিন্তার শব্দগুলো প্রকাশ করে চলেছেন। জ্ঞান-পিপাসায় মানবিক চেতনার প্রতি প্রবল আস্থাশীল এই সাহিত্যশিল্পী প্রার্থনা, আত্মনিবেদন আর শুভবোধের দিকে আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। নিরলস লেখক মিলনের সদা-চিন্তাশীল মন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি ও সংগ্রামের দিকে সরাসরি তাক করা। প্রথম উপন্যাস ‘যাবজ্জীবন’ (বাংলা একাডেমির সাহিত্যপত্রিকা ‘উত্তরাধিকার’-এ ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬) থেকে শুরু করে বৃহৎ-কলেবর আর বিপুল ক্যানভাসের উপন্যাস ‘নূরজাহান’ (প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫)-এর নিবিড় পাঠে আমরা সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি নিমগ্ন একজন সাধক লেখককেই আবিষ্কার করি। মিলনের উপন্যাসের বিষয়, ভাষা ও পরিবেশনশৈলীর দিকে নজর দিতে গিয়ে মনে পড়ে গেল দেশকাল-সমাজ বিষয়ে প্রায় ৫০০ উপন্যাসের লেখক পার্লের একটি ভাষণের কথা। জন্মসূত্রে মার্কিনি চীনা ঔপন্যাসিক, ১৯৩৮ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী, পার্ল এস বাক (১৮৯২-১৯৭৩) নোবেল বক্তৃতায় চীনের উপন্যাস বিষয়ে বলেছেন:
আমিও বিশ্বাস করতাম, প্রকৃত সাহিত্যের সাথে উপন্যাসের কোনো যোগ নেই। বিদ্বানরা এই রকমটিই শিখিয়েছিলেন আমাদের। আমাকে আরো শেখানো হয়েছিল, সাহিত্যে নান্দনিকতা যুক্ত করতে পারেন শুধু বিদগ্ধ মানুষেরাই। জীবনের গভীরতর উৎস থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঝরনাধারার মতো প্রতিভাগুলোকে ঠেকিয়ে রাখতেই যেন বিদ্বানদের মস্তিষ্ক এসব আইনকানুনের জন্ম দিত। প্রতিভা, তা সে যে-মাপেরই হোক না কেন, তার ভূমিকা সবসময় স্রোতস্বিনীর মতো; অন্যদিকে শিল্প, আধুনিক ধ্রুপদী যা-ই হোক-না কেন, তার ভূমিকা খোদিত অবয়বের, যার ওপর স্রোতস্বিনীর জল নেমে আসে অঝোর ধারায়। চীনের উপন্যাসও সেই স্রোতস্বিনী নদীর মতোই, যার নেমে আসাকে স্বাগত জানায় প্রকৃতির পাথর আর বৃক্ষরা, প্রাকৃত মানুষেরা তার জল পানে শীতল হয়, ছায়া আর বিশ্রাম পায় তার আশ্রয়ে। চীনে তাই উপন্যাস মাত্রই ছিল সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে উঠে আসা এক অদ্ভুত সৃষ্টি, এ ছিল তাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। এ উপন্যাসের ভাষাও ছিল তাদের নিজস্ব রীতির,…। (হায়াৎ মামুদ, ভূমিকা ও সম্পাদনা, ‘নোবেল ভাষণ: বাক্ থেকে পামুক: পাঁচ মহাদেশের দশ সাহিত্যরথী’, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, প্রকাশকাল: ২০০৮, পৃষ্ঠা: ১২-১৩)
‘নূরজাহান’ যেন এক চিলতে বাংলাদেশ। ‘শেষ হেমন্তের অপরাহ্ণবেলায় উত্তুরে হাওয়াটা একদিন বইতে শুরু করল’ এই কবিতাপ্রতীম বাক্যটির ওপর নির্ভর করে তৈরি হতে শুরু করেছিল ‘নূরজাহান’, প্রায় দুইদশক আগে। বইটিতে লেখকের স্বপ্নময়তা-কল্পনা আর পরিকল্পনার প্রকাশ পাঠককে নিশ্চয়ই বিস্ময়ের দরোজায় নিয়ে যাবে বারবার। বিক্রমপুরের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাস সাংস্কৃতিক-সামাজিক বাংলাদেশের মিনিয়েচার। উত্তরের হাওয়ায় বিক্রমপুরের আলী আমজাদের কিছু না হলেও ‘নূরজাহানের কিশোরী শরীর অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে ভরে’ যাওয়ার যে গল্প, তা পাঠককে পাঠ করতে হয় দীর্ঘ সময় ধরে প্রতীক্ষার প্রহর পার হতে হতে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে মৌলভীবাজারের ছাতকছড়ায় দ্বিতীয় বিয়ের অপরাধে গ্রাম্য মসজিদের ইমাম মান্নান মাওলানা ফতোয়াবাজি করল, নূরজাহানকে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে তার ওপর ১০১টি পাথর ছুড়ে মারা হলো। অপমানে আত্মহত্যা করলো মেয়েটি। সমকালে মিডিয়ায় তোলপাড় তোলা এই ঘটনাটি ‘নূরজাহান’ উপন্যাসের প্রেরণাভূমি। নারীর ওপর ফতোয়ার প্রভাবকে কেন্দ্র করে গড়েওঠা ‘নূরজাহান’-এ আছে এক বিশেষ সময়কালের কোনো রাষ্ট্রভূমির সার্বিক পরিস্থিতি ও প্রার্থিত প্রতিবাদ। লেখকের এক জবানবন্দির খানিকটা তুলে ধরছি:
মেদিনীমণ্ডল গ্রামে জীবনের অনেকগুলো বছর আমার কেটেছে। ওই গ্রামের পবিত্র জল হাওয়া আর মানুষের ভালোবাসায় আমি বড় হয়ে উঠেছিলাম। আমার বুজি (নানি) আমাকে তাঁর আঁচলের ছায়ায় রেখে বড় করেছিলেন। ওইরকম মহীয়সী নারী এই জীবনে আমি আর দেখিনি। তাঁকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলাম ‘কেমন আছো, সবুজপাতা’। আর আমার ‘নূরজাহান’ শেষপর্ব সেই মহীয়সী নারীকে উৎসর্গ করলাম। আর নূরজাহান আসলে এক প্রতীকী চরিত্র। বাংলাদেশের যে-কোনও গ্রামেই তাকে নিয়ে আসা যায়। (‘লেখকের বক্তব্য’, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১০৭৪)
মেদিনীপুর গ্রামের বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক। আবাদি জমির মাটি ভেদ করে তৈরি হচ্ছে সভ্যতার নতুন মাত্রা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। মাটিয়াল আর কন্ট্রাক্টাররা ব্যস্ত। গ্রামবাসীর আগ্রহ-উদ্বেগ-আনন্দের শেষ নেই। বাস্তব-কল্পনা, ভাষা-প্রয়োগে আঞ্চলকিতার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব, বিক্রমপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাধারণ মানুষের জীবনধারা, ঘোরলাগা-স্বপ্নবাজ মানুষের কলমের কালি বেয়ে নেমে এলো উপন্যাসের পাতায় পাতায়। ‘শুধু সংলাপে না, লেককের বর্ণনায়ও ঢুকে গেছে ওই অঞ্চলের শব্দ, সুর।’ সেই সুর যেমন কথায়, তেমন পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিবরণে; চরিত্রগুলোর নিজস্ব আলোয়; চলমান রাজনীতি-সমাজনীতি-সংস্কৃতির প্রতিফলনে-প্রক্ষেপণে। ধর্ম, নারীর অধিকার, পারিবারিক আইন, নিরপেক্ষতা, মানবিকবৃত্তি, কূট-কৌশল, গ্রাম ও শহরের জীবনচিত্রের প্রভেদ, প্রেম-হিংসা-লোভ-প্রতিশোধ, দারিদ্র্য, সরলতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-হতাশা আর আশাবাদের এক বিরাট মিলনমেলা মিলনের এই উপন্যাস। ‘নূরজাহান’-এর ক্যানভাস মহাকাব্যের মতো, বিশালতার ব্যাপ্তি মহাসমুদ্রের মতো।
গরিব দবির গাছি-হামিদা দম্পতির ১৩ বছরের বাড়ন্ত মেয়ে নূরজাহান। পাখির মতো চঞ্চল, আনন্দময়ী, সাহসী, সরলমনা ও প্রতিবাদী। গ্রামের মতোই পরিবর্তমান। ‘সারাদিন এই বাড়ি ওই বাড়ি, সড়ক চকমাঠ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরে চেহারায় তার রোদের কালিমা, হাত পায়ে কাদামাটি, মাথার ঘন কালো চুল ধুলায় ধূসর’ (পৃষ্ঠা ৩৮)। নূরজাহানের জীবনের চলমানতার ইঙ্গিত মেলে উপন্যাসের একটা বিবরণ থেকে: ‘বিরাট একটা কারবার হচ্ছে দেশগ্রামে। কত নতুন নতুন চেহারা যে দেখা যাচ্ছে! নানান পদের মানুষে ভরে গেছে গ্রামগুলি। একটা মাত্র সড়ক রাতারাতি বদলে দিচ্ছে বিক্রমপুর অঞ্চল। শহরের হাওয়া লেগে গেছে গ্রামে। যেন গ্রাম এখন আর গ্রাম না, যেন গ্রাম হয়ে উঠছে শহর।’ গ্রাম আর শহরের মিশ্রণে এক নতুন সভ্যতার আভাস পেয়েছিলাম চল্লিশের দশকে আহসান হাবীবের কবিতায়। প্রবল আশাবাদী হাবীব লিখেছিলেন: ‘নতুন নতুন গ্রাম বানাবো, নতুন নতুন শহর গড়বো।’ এই মিশ্র সভ্যতায় মানুষের মনে তো পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পাখি ডাকা শিশিরভেজা গ্রামের মানুষের গায়ে লেগেছে শহরের হাওয়া। নদীরা মরে যাচ্ছে। দখল হচ্ছে নদীর জমি। আমন-আউসের জায়গা দখল করেছে ইরো-বোরো ধানের চাষ। অধিকার আর মর্যাদার প্রশ্নে তারা অনেক বেশি অগ্রসর। মিডিয়ার ক্যামেরার লেন্স এখন সর্বত্র প্রসারিত। সংবাদকর্মী আর উন্নয়নকর্মীরা দিনরাত ব্যস্ত মানবাধিকারের বিষয়ে। মেয়েরা এখন আর কেবল ‘সংসারের লক্ষী’টি নয়। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে তারা। আর্থিক-সামাজিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরতা কমেছে। বেড়েছে শিক্ষিতের সংখ্যা। অন্যায় যেমন বাড়ছে, প্রসারিত হচ্ছে প্রতিবাদের নানান ধরনও। এমন প্রেক্ষাপটে নূরজাহারের আবির্ভাব-বিচরণ, প্রভাব ও অন্তর্ধান। শরীরে-মনে জেগে উঠছে নূরজাহানরা। ইমদাদুল হক মিলন দেখছেন নূরজাহানকে:
বিকালবেলার চমৎকার এক টুকরো আলো এসে পড়েছে নূরজাহানের মুখে। সেই আলোয় অপূর্ব লাগছে মেয়েটিকে। তার শ্যামলা মিষ্টি মুখখানি, ডাগর চোখ, নাকফুল আর স্বপ্নমাখা উদাসীনতা কীরকম অপার্থিব করে তুলেছে তাকে। কুতকুতা চোখে মুগ্ধ হয়ে নূরজাহানকে দেখছে আলী আমজাদ। দেখতে দেখতে কোন ফাঁকে যে ভিতরে তার জেগে উঠতে চাইছে এক অসুর, খানিক আগেও আলী আমজাদ উদিস (টের) পায়নি। ঠিক তখনই হা হা করা উত্তরের হাওয়াটা এল। সেই হাওয়ায় আলী আমজাদের কিছু হল না, নূরজাহানের কিশোরী শরীর অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে ভরে গেল। কোনওদিকে না তাকিয়ে ছটফট করে সড়ক থেকে নামল সে। শস্যের চকমাঠ ভেঙে, ভ্রুণ থেকে মাত্র মাথা তুলেছে সবুজ ঘাসডগা, এমন ঘাসজমি ভেঙে জোয়ারে মাছের মতো ছুটতে লাগল। (প্রথম অখণ্ড আনন্দ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৮)
মাছে-ভাতে বাঙালির এককালের সুখের সংসারের ছবি আছে ‘নূরজাহান’ উপন্যাসে। পিঠা-পুলি, ঢেকিতে আটা কুটার শব্দ, শীতের উৎসব, বর্ষাকালের গল্পময় রাত, বাড়ির আনাচে-কানাচে শাক-সবজির বাগান, বাড়ির খেয়ে বড় হওয়ার যে ঐতিহ্য বাংলাদেশের। পুকুরের মাছ, জমির সরিষায় তেল, ঘরের মুরগির ডিম এগুলোতো চিরচেনা ছবি। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া কিংবা বিকেলবেলা মেয়েদের এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরে বেড়ানো আমাদের সামাজিক ইতিহাসের কথা বলে। সম্পন্ন গৃহস্থ বাঙালির এক সামাজিক বিবরণের কাহিনি এই উপন্যাস। অবশ্য এখন ওসবের অনেক কিছুই কেভর স্মৃতি। গ্রামের সেই স্থিরজীবনের, রঙিন জীবনের নির্মলতা-পবিত্রতা আর আনন্দময়তার কথা জানাচ্ছেন মিলন তার কাহিনির পাতায় পাতায়। একটা উদ্ধৃতি টানছি: ‘রান্নাচালার পিছনে ঝাপড়ানো একটা জামগাছ। সকালবেলার রোদে চকচক করছে জামপাতা। একটা টুনটুনি পাখি লাফাচ্ছে গাছের ডালে। এই ডাল থেকে ওই ডালে যায় টুনটুনি, ওই ডাল থেকে সেই ডালে। জামগাছটার দিকে তাকায় মরনি ঠিকই দেখেও দেখে না। মনের ভেতরে অতীত দিনের স্মৃতি। চোখ জুড়ে অতীত দিনের প্রিয় মানুষের মুখ’ (পৃষ্ঠা ১৬)। কেবল সড়ক-মহাসড়ক ধরে যোগাযোগের উন্নতি নয়, গামেন্ট শিল্পের বদৌলতে আর্থিক অগ্রগতিও হয়েছে বাংলাদেশের। নূরজাহারে বাল্যবন্ধু মজনুর মতো হাজারো কিশোর-যুবক এখন শহরে খলিফা হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বস্ত্রবালিকারা এখন বড় বড় শহরে দল বেঁধে চলাফেরা করে। কাজ করে সংসারের চাকা যেমন ঘুরাচ্ছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে নারীর প্রতি নির্যাতনও চলছে। বন্ধ হয়নি বাল্যবিবাহ। যৌতুকের যন্ত্রণায় কেঁদে মরছে হাজারো নারী। নূরজাহান এই আধুনিক বিশ্বে ধর্মান্ধতা আর পুরুষতান্ত্রিকতার অসহায় শিকার। গ্রামীণ কাইজ্জা, দেওয়ানের দেহতত্ত্বের গান, ফেরিওয়লাদের ঘুরাঘুরি সবই আছে। নতুন করে যুক্ত হয়েছে অপরাধের ভিন্ন ভিন্ন কৌশল।
সমাজের বিরাট পরিসরে মানুষ এক অসহায় প্রাণি মাত্র। কত বিচিত্র সমস্যা আর বিপত্তির মধ্যে যে মানুষের জীবন অঅবদ্ধ, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ‘নূরজাহান’-এর ক্যানভাসে মিলন মানুষের সেইসব অসহায়তার ছবি এঁকেছেন নানান কৌশলে। যেমন মজনুর খালার বাড়িতে আশ্রয়-নিতে-যাওয়া মজনুর বাবার যখন তার পরিচয় গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, সেই সময়ের লেখকের অভিব্যক্তি-বিবরণ। পাঠ নিচ্ছি:
পলোর ভিতর মুরগির ছাওটা তখন কোনওরকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। উঠে একসময় দাঁড়াবে ঠিকই, বেঁচেও যাবে কিন্তু তার চারপাশে থাকবে পলোর বেড়া। পলো তুলে নেওয়ার পর বেড়া একটু বড় হবে। এই বাড়ির উঠান পালানই হবে তখন আর একটা পলো। সেই পলোর বৃত্ত ভেঙে একমাত্র মৃত্যুই পারবে তাকে মুক্তি দিতে। (পৃষ্ঠা: ৯৮)
প্রবাদের দেশ বাংলাদেশ। এখানে দারিদ্র্য, অসহায়তা আর আশাবাদের মতো প্রবাদও আমাদের নিত্যসঙ্গী। ‘নূরজাহান’-এর বিপুল ক্যানভাস জুড়ে ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়েছে প্রবাদের আলো, আছে লোক-সংস্কার আর লোকবিশ্বাসের উপস্থিতিও। যেমন: ‘পেডে খিদা লইয়া মান ইজ্জত দেহন যায়নি’ (পৃষ্ঠা ২৯), ‘পয়লা দিনের রস একজন মানুষরে খাওয়ান লাগব’ (পৃষ্ঠা ৮৬), ‘এরকম দুপুরে ভাত না খেয়ে বাড়ি থেকে বোরোয় কোন গিরস্ত’ (পৃষ্ঠা ২৬৬), ‘সেই দিন নাইরে নাতি/ খাবলা খাবলা খাতি’ (পৃষ্ঠা ৭৭০)।
কাহিনিতে স্থান-পাওয়া চরিত্রগুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল-প্রাণবন্ত। ছনুবুড়ি, তছি পাগল, আজিজ গাওয়ালি, আমুদে স্বভাবেরর হামেদ, বিশ-একুশ বছরের কাহিল মেয়ে কুট্টি, জোঁকের মতো তেলতেলা শরীরের বাঁধা কামলা আলফু, মজনুর বাবা আদিলউদ্দিন, ফুর্তিবাজ পবন, দীর্ঘকালের বিধবা দেলোয়ারা, আহাতার, মোতালেবের কাহিল বউটা, মাকুন্দা কাশেম, মরনি, দেশগ্রামের সাতেপাঁচে না-থাকা আজিজ, হাসুর বাপ কানা দলিল, নিখিল, মাওয়া বাজারের সেলুনওয়ালা দুলাল, ইব্রার বউ জহুরা, দেলোয়ারার পালিয়ে-যাওয়া ‘সুপুরুষ’ স্বামী আব্দুল মজিদ, ‘উপরে এক ভিতরে আরেক’ আলী আহম্মদ, বছর বছর বাচ্চা-প্রসর-করা বানেছা, পাখির মতন মানুষ আলা’র মা, আজিজ গাওয়াল, মাওলানা মহিউদ্দিন, ভাঙ্গারি কাকা, প্রায় নিশ্চুপ নাদের, মুকসেদ, মোতাহারের মা তহুরা বেগম, মোতাহারের বউ শরীরভরা চাহিদা নিয়ে রাত জেগে-থাকা পারু, হাসুবালা, মতিমাস্টার, মাওলানা মান্নানের মুখে নূরজাহানকে বিয়ে করার প্রস্তাব শুনে চমকেওঠা বারো ঘাটের পানি খাওয়া ল্যাংড়া বসির ঘটক, চা-মিস্টির দোকানদার সেন্টু, লেপ-তোশকের কারিগর কাম হাজাম আব্দুল, তামাক-বিড়ির নেশায় আচ্ছন্ন ফইজু, গণেশ নাপিত, রামদাস, ফুলমতি, রব্বান শিকদার, বিড়ি খাওয়া লোক মতলিব, মনির সর্দার সকলে মিলে যেন তৈরি করেছে এক চিলতে বাংলাদেশ। সবচেয়ে প্রভাবশালী চরিত্র মান্নান মাওলানা। তার পরিচয় দিচ্ছেন ঔপন্যাসিক: ‘চোখ দুইটা মান্নান মাওলানার ষাঁড়ের মতন, যেদিকে তাকান তাকিয়েই থাকেন, সহজে পলক পড়ে না চোখে। যেন কথা বলবার দরকার নাই, হাত পা ব্যবহার করবার দরকার নাই, দৃষ্টিতেই ভস্ম করে ফেলবেন শত্রুপক্ষ। এইজন্য মান্নান মাওলানার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না কেউ। ভুল করে অচেনা কেউ তাকালেও দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে পলকেই সরিয়ে নেয় চোখ।’ (পৃষ্ঠা ৪৪) এই মাওলানা ‘নূরজাহান’ উপন্যাসের কেন্দ্রে থেকেছেন বরাবর। তিনিই হয়ে উঠেছেন সমাজের কুটিল চরিত্রের প্রধান প্রতিনিধি। আর তাকে অতিক্রম করার জন্যই কিশোরী নূরজাহানের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। কাহিনিকার মিলনও চেয়েছেন মান্নান মাওলানার প্রতিপত্তির কথা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়ে একটি সমাধানের সিঁড়ি নির্মাণ করতে।
কাহিনি এগোতে থাকলে, নূরজাহানের শরীরের বৃদ্ধির সাথে সাথে নিজেই যেন নিজের শত্রু হয়ে ওঠে সে। প্রকাশ হতে থাকে তার বিদ্রোহী চেতনাও। মাওয়া মহাসড়কের মাটির কাজের সাব-কন্টাক্টর আলী আমজাদে চোখ পড়ে নূরজাহানের কিশোরী শরীরের দিকে। প্রায়শই কথোপকথন হতো নূরজাহান-আমজাদের। কিন্তু সখ্যতার চেয়ে দূরত্বই বাড়তে থাকে ক্রমাগত। বৃদ্ধ শ্রমিকের সাথে আমজাদ দুর্ব্যবহার করলে নূরজাহান অনায়াসে তাকে বলে ফেলে: ‘আপনে মানুষ না।’ অতঃপর কাহিনির ক্যানভাসে প্রবেশ করে মান্নাম মাওলানা। নূরজাহানের বাবার নাম বিকৃত করে ‘দউবরা’ বললে মান্নানের ওপর ক্ষিপ্ত হয় সে। নূরজাহানের গ্রামময় ঘুরে বেড়ানোতে আপত্তি তোলে মাওলানা। মাওলানা তাকে শাস্তিও দিতে চায়। বলে: ‘খাড়ো মসজিদখান বানাইয়া লই, এই গ্রামের বিচার শাল্লিশ বেবাক করুম আমি। শরিয়ত মোতাবেক করুম। তর লাহান মাইয়ারা বরকা (বোরখা) না ফিনদা বাইতথন বাইর অইতে পারবো না। চুদুর বুদুর (এদিক ওদিক, ইতরামো ফাজলামো অর্থে) করলে গদে (গর্তে) ভইরা একশো একহান পাথথর ফিক্কা (ছুঁড়ে) মারুম’ (পৃষ্ঠা ৪৬)। তখনও আমরা দেখি নূরজাহানের প্রতিবাদী কণ্ঠ। এই কিশোরী যেন চলমান সমাজের কঠোর দরোজায় কড়া নাড়ে প্রবল হাতে। পাঠক চমকে ওঠে নূরজাহানের কথা বলার ভঙ্গি দেখে। মিলনের বর্ণনা: ‘ডানহাতের বুড়া আঙুল মান্নান মাওলানার দিকে উঁচিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে নূরজাহান বলল, আপনে আমার এইডা করবেন। পচা মলবি, কিচ্ছু জানে না খারি বড় বড় কথা! জানলে তো খাইগোরা (খানেরা) আপনেরঐ ইমাম বানাইতো, অন্যদেশ থিকা ইমাম আনেনি! মাওলানা কারে কয়, ইমাম কারে কয় খাইগো বাড়ির মসজিদের হুজুররে দেখলে বোজবেন। দেখলেঐ ছেলাম করতে ইচ্ছা করে। ফেরেশতার লাহান মানুষ। আর আপনে, আপনেরে দেখলে মনে অয় খাডাস (খাটাস), রাজাকার’ (পৃষ্ঠা ৪৬)। মাওলানার সমস্ত অপকর্মের প্রতিবাদে একদিন লোকালয়ে নূরজাহান তার মুখে থু থু ছুঁড়ে মারে। সে দৃশ্য তাকিয়ে দেখে স্তব্ধ জনতা। সমাজে প্রতিবাদের ভাষা নীরবে-নিভৃতে কেঁদে ফিরছে বহুকাল ধরে। যে যার মতো সুবিধা ভোগ করতে ব্যস্ত। পৃথিবীর কোনো কোনো প্রান্তে কখনো কখানো ডাক দিয়ে ওঠে কোনো প্রতিবাদী গলা। হাত উঁচিয়ে পরিবর্তনের অঅহ্বান জানিয়ে যায় কেউ কেউ। নজরুল-ম্যান্ডেলা-সুচিরা তাই অনন্য ব্যক্তিত্ব। আপসকামিতা নয় বিজয়ই যাদের লক্ষ্য। এটা ব্যতিক্রম। যেমন নূরজাহান। নূরজাহানের প্রতিবাদ আর জনতার মৌনতা বিষয়ে মিলন লিখছেন: ‘তখন প্রকৃতি ছিল প্রকৃতির মতন উদাস, নির্বিকার। শীতের বেলা তেজালো হচ্ছিল। তীক্ষ্ণ রোদ উষ্ণ করে তুলছিল দেশগ্রাম। স্বচ্ছ আকাশ ছুঁয়ে দূর নদীচরের দিকে উড়ে যাচ্ছিল ভিনদেশি পাখি। পথপাশের হিজল ছায়ায় বসে একাকি ডাকছিল এত ডাহুকি। আর বহুদূরের কোন অচিনলোক থেকে আসা উত্তরের হাওয়া বইছিল হু হু করে’ (পৃষ্ঠা ২৪৯)।
নূরজাহান কেবল শক্তি নিয়ে সামনে এগিয়েছে, তা নয়। কিছুটা ভয়ও যেন তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। আর তার চারপাশের লোকগুলোতো ভয়ের একেকটা আখড়া। মিলন জানাচ্ছেন সে কথা: ‘বাইরের গড়িয়ে যাওয়া দুপুরের নির্জনতায় তখন ঝিমধরা ভাব। গয়াগাছের ওদিক থেকে ভেসে আসছিল ক্লান্ত এক কাকের ডাক। থেকে থেকে ডাকছিল কাকটা। সেই ডাকের মাঝখানেই যেন নিজের মধ্যে ফিরে এল মরনি। কাঁথার তলায় লুকিয়ে থাকা নূরজাহান তখন কেমন স্থির হয়েছে। শরীরের কাঁপনটা নাই। ভয়ে আতঙ্কে ফেলা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ বদলে গেছে। এখন শব্দটা কেমন ধীর, গম্ভীর। গভীর ঘুমে ডুবে যাওয়া মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দের মতন’ (পৃষ্ঠা ২৭৮)।
কেবল লোভ-প্রতিহিংসা আর প্রতিবাদ নয় ভালোবাসা-ভালোলাগার বর্ণনাও দিয়েছেন কাহিনিকার মিলন। খানিকটা পাঠ নিচ্ছি: ‘মজনুকে এভাবে তাকাতে দেখে জীবনে এই প্রথম শরীরের খুব ভিতরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ হল নূরজাহানের। অদ্ভুত এক লজ্জায় চোখ মুখ নত হয়ে গেল। চট করে মজনুকে ছেড়ে দিল সে। চোখ তুলে কিছুতেই আর মজনুর দিকে তাকাতে পারলো না। মজনু তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নূরজাহানকে দেখছে। চার মাসে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে নূরজাহান। মুখটা ঢলঢল করছে অপূর্ব এক লাবণ্যে। চোখে আশ্চর্য এক লাজুকতা। পিঠের ওপর ফেলে রাখা বেণি দুইখানা যেন হঠাৎ করেই তার চপলতা হরণ করেছে’ (পৃষ্ঠা ৫৮)। অন্য একটি ছবি: ‘নূরজাহানের চোখের দিকে তাকাল কুট্টি। ধীরে ধীরৈ বেশ গুছাইয়া গাছাইয়া পুরা ঘটনা বলল। সেই যে জ্বরের রাইতে আলফুর কাছে সে গেল, তারপর দিনে দিনে কী থেকে কী হয়ে গেল, শরীর মন সব দিয়া দিল আলফুরে, কিচ্ছু বাদ দিল না। সব বলল। ওই যে এক দুপুরে নাইয়া ধুইয়া আসনের পরও তারে পাথালি কুলে কইরা চাউলতাতলার নাড়ার বিছানায় নিয়া গেছিল আলফু, সেইসবও বলল। শুনতে শুনতে নূরজাহান নিজের শরীরে কী রকম একটা কাঁটা দেওয়া ভাব টের পাইল। মনটা কেমন যেন হয়ে গেল তার। একজন মানুষের কথা মনে পড়ল। সেই মানুষটার নাম মজনু। মজনুর কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হইয়া গেল সে’ (পৃষ্ঠা ৭৯৭)। স্বামী ঘরজামাই রব্বান আর প্রাণ-পুরুষ মনজুর প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের ব্যাপারাদির কথা লিখেছেন কথানির্মাতা মিলন: ‘যতই মন জুইড়া থাউক মজনু, রব্বানের জন্যও একটা মায়া মমতা ভাল লাগা নূরজাহানের তৈরি হইছে। এইটা ভালবাসা কিনা কে জানে! তবে মায়াটা রব্বানের জন্য লাগে। দুপুরবেলা দেরি কইরা বাড়িতে আসলে অপেক্ষার একটা কষ্ট হয়। রাতের বেলা দেরি কইরা আসলে মনের ভিতর তৈরি হয় অদ্ভুত এক ছটফটানি। সব মিলায়া সম্পর্কটা মায়া মমতার, ভাললাগার, হয়তো বা এও এক রকমের ভালবাসা। মজনুর জন্য যেমন তেমন না, অন্যরকম’ (পৃষ্ঠা ১০১৮)। ধর্ম-কাহিনির পাশাপাশি আধ্যাত্ম্যচিন্তারও প্রবেশ ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কিছু ফকিরি-মুর্শিদি গানের ব্যবহার তাঁর সেই অভিলক্ষ্যকে স্পর্শ করে বটে। যেমন:
আমারে সাজাইয়া দিয়ো নওসারও সাজন
হুইলে পরে মাগো আমার বিয়ারও লগন
কাঁচা বাঁশের পালকি করে মাগে আমারে নিয়ো! (পৃষ্ঠা ৪৮৩)
দেশ-গেরামের বিস্তর জীবনের বিবরণ আছে ‘নূরজাহান’-এ। জীবন যেখানে যেমন, মানুষগুলো জীবনকে যেভাবে উপভোগ করে, ভোগের নেশায় কাতর হয়, দুঃখ-বেদনায় নত হয়ে যাদের জীবন, তারা সকলে প্রতিবেশ-পরিবেশ নিজে হাজির হয়েছে ইমদাদুল হক মিলনের এই উপন্যাসে। যেন তিনি বিক্রমপুরের মেদিনিমণ্ডলে পুরে দিয়েছেন গোটা বাংলাদেশ। জীবনযুদ্ধের পাশাপাশি মানুষের সৃজনশীলতা এবং শিল্পীসত্তাও প্রকাশ পেয়েছে প্রাসঙ্গিক পরিসরে। আমরা যেন তার এই ‘ঝুলে-পড়া’ লম্বা কাহিনিতে দেখতে পাই চিরন্তন বাংলাদেশের এক নিটোল চিত্র। যৌতুকপ্রথা, একটি ছেলের প্রত্যাশায় অনেক মেয়ে জন্ম-দেওয়ার প্রবণতা, কিশোরী কণ্যাকে ঘরে আটকেরাখার রীতি, গ্রামের সম্ভ্রান্ত বাড়ির পায়খানা ঘরের বিবরণ প্রভৃতি নানান প্রসঙ্গ খাড়া করেছেন কাহিনিকার উপন্যাসের বিপুল ক্যানভাস জুড়ে। মানুষগুলো যেন যে-কোনো গ্রামের যে-কোনো এলাকার। সিলেটের ঘটনা কেবল কাহিনির প্রয়োজনে বিক্রমপুরে আসেনি, তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশের মাটি আর আকাশের সীমানায়। গ্রন্থটিকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ভেতর দিয়ে নির্মিত হয়েওঠা একটি প্রামাণ্যচিত্র। ‘চারদিক থেকে মার খাওয়া নিরীহ কুত্তা বিলাইয়ের মতন দিশাহারা’ মানুষেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। তাদের চোখে-মুখে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়। নতুন জীবনের প্রত্যাশা। ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে, ইতিহাসের পাঠের ভেতর দিয়ে নতুন জীবনকে স্বগত জানানোর এ এক নবতর কৌশল। মিলন যেন আজকের প্রজন্মকে ওই মহামিলনের উৎসবের পথে পারি জমাতে সহায়তা করতে চান। ‘শীতের বেলা ফুরাতে সময় লাগে না। দুপুর শেষ হওয়ার আগেই বিকাল হয়ে যায়।’ কিন্তু উত্তরের হাওয়া গায়ে মেখে এগোতে থাকা ‘নূরজাহান’ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। দূরে এবং দূরে প্রসারিত হতে থাকে এর কাহিনি-উপকাহিনি। চরিত্রগুলো নিজের নিজের জায়গা থেকে ঘোষণা করতে থাকে অস্তিত্ব ও অবস্থান। জীবনবোধে মানিক-জীবনানন্দ আর প্রকৃতি-বর্ণনায় বিভূতির মতন নির্মল-নির্মোহ মিলন মহাজীবনের নিবিড় কারিগর।
ইমদাদুল হক মানুষের জীবনবোধকে রূপ দিয়েছেন ঐতিহ্য ও চিন্তার আলোকশিখায়। মানুষের চলমানতা ও বিবর্তনের ছায়াটাকে ধরতে চেয়েছেন ক্যামেরার লেন্সে। একটি বর্ণনা দেখে নিতে পারি: ‘হারিকেনের আলোয় সাদা থান পরা দোলোয়ারাকে অচেনা মানুষ মনে হয়। যেন এ দুনিয়ার কেউ নন তিনি, যেন অন্য কোনও দুনিয়া থেকে হঠাৎ করেই চলে আসছেন মেদিনীমণ্ডল গ্রামের তিন মেন্দাবাড়ির এক বাড়িতে, যে বাড়ির আরেক নাম সারেঙ বাড়ি। তিন ভাইয়ের দুইজন ছিলেন জাহাজের সারেঙ আর একজন কেরানি। যেন কোনও এক দূরগামি জাহাজে করেই বাপ-চাচারা কেউ অচেনা কোনও দেশ থেকে আজ এই সন্ধ্যায় দোলোয়ারাকে নিয়া আসছেন এই বাড়িতে, এই ঘরে। বহুদূর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে বলেই বুঝি চোখের চশমায় তাঁর জমেছে দুনিয়ার সব ধুলা’ (পৃষ্ঠা ৩১২) এই বিবরণে যেন সহজেই ছায়া ফেলে প্রখরচেতন কবি জীবনানন্দের ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে’র সন্ধান-অনুসন্ধিৎসু কোনো পথিকের দৃষ্টি। যুগ-যুগান্তর ধরে যিনি খুঁজে ফেরেন সভ্যতার আলো-অন্ধকার এবং অসীম সব রহস্য। কথানির্মাতা মিলন আমাদেরকে সেই অনুভবের জায়গা নিয়ে হাজির করেন হয়তো। আর কাহিনি গড়াতে থাকে উত্তরের হাওয়া থেকে ‘চৈতালি ঘূর্ণি’র দিকে; ঘূর্ণি পেরিয়ে বর্ষার আর্দ্র বাতাসের পানে; শ্রাবণের মেঘ গলিয়ে আবার উত্তরের হাওয়ায়। গ্রাম-বাংলার চিরায়ত ছবি এঁকেছেন কলমের কালিতে। বর্ণনা: ‘পুকুরঘাট বলতে এখন আর কিছু নাই। বর্ষার পানিতে পুকুর ডোবা সব ভেসে গেছে। এখন চারদিকেই পুকুর, চারদিকেই ডোবা। যেদিকে চোখ যায় শুধুই পানি।’ (পৃষ্ঠা ৬৫৯) বিল-হাওরের বাংলাদে, নদীময় বাংলাদেশ, গাছগাছালির নিবিড় ছায়ায় ঘেরা গ্রাম মিলনের ‘নূরজাহান’ উপন্যাসের বিরাট ক্যানভাস জুড়ে বর্তমান।
আধুনিক বিশ্বে নারীমুক্তির জন্য বহু মানুষ ও সংগঠন প্রবলভাবে সোচ্চার। কিন্তু তারপরও কি নারীরা পেয়েছে কাক্সিক্ষত মুক্তি। স্বাধীনতার জন্য তাদের হাহাকার কি কমেছে কিছুটা হলেও? সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মিলন জানেন নারীর পরাধীনতা শেষ হয়নি আজও। শেকলে বাঁধা নারীর পা। নূরজাহানের বাবা দবির গাছির ভাষ্যে মিলনের কথা শোনা যাক: ‘দবির মন খারাপ করা গলায় বলল, হ। মাইয়াডার কথা চিন্তা করলে আমার খালি মালেক দরবেশ সাবের কথা মনে অয়। দরবেশ সাবে কইতো, দুনিয়া ভইরা আল্লায় খালি জেলখানা বানাইয়া থুইছে।… নূরজাহানের লগে আমরা যেইডা করতাছি হেইডা শাসনের জেলখানা। … মাইয়া মাইনষের এমুন জেলখানায় থাকনঐ ভাল। তয় বেশি তেড়িবেড়ি করতে পারে না।’ (পৃষ্ঠা ৪৯৩-৯৪) মিলন বুঝতে পেরেছেন ‘মানুষের জীবন তো আসলে এক ছোট নদীই। বাঁকে বাঁকেই তো চলছে জীবন’ (পৃষ্ঠা ৮৩৩)। যে নূরজাহানকে নিয়ে এতকথা এত কিচ্ছা-কাহিনি, কাহিনিকার শেষপর্যন্ত একটা প্রশ্ন ছুঁড়েছেন পাঠকের দিকে: ‘নূরজাহানের জীবন যদি হত তছির জীবন। বদ্ধ পাগলের জীবন। তা হলে কি মান্নান মাওলানা তার পিছনে লাগতো? পাগল হয়ে সে যদি মান্নান মাওলানার মুখে ছ্যাপ ছিটাত তা হলে কি কেউ কিছু মনে করত’ (পৃষ্ঠা ৯০৭)।
নূরজাহানের স্বামী রব্বান কোনো এক জ্যোৎস্নাভরা রাতে পুরানা ব্যাগে কাপড়চোপড় নিয়ে পালিয়ে যায়। ততোদিনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাজও শেষ হয়েছে। রাস্তার পাশে বেড়ে উঠছে সারি সারি বাবলাগাছ। বাস-ট্রাক-টেম্পু চলছে। কোথায়ও রব্বানের সন্ধান মিলল না। স্বামীর চিন্তায় ‘নূরজাহান শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে।’ অবশ্য রব্বান পরে পূর্বের স্ত্রী শেফালিকে নিয়ে হাজির হয় নূরজাহানদের গ্রামে। শেফালি স্বামীর এরকম অন্যায়ের জন্য মাফও চায়। আগের সংসার ছেড়ে এসে তথ্য গোপন করে নূরজাহানকে বিয়ে করে সংসার করছিল রব্বান। অবশ্য রব্বানের অনুতাপও আমরা টের পেয়েছি। লেখক জানাচ্ছেন সেই অনুতাপের কথা:
রব্বান বলল, আমার অহন কী করতে ইচ্ছা করতাছে জানো?
কী?
জ্যাটিঙ্গা পাখি হইয়া যাইতে।
জ্যাটিঙ্গা পাখি আবার কোনডা?
হেই পাখি আমাগো দেশে থাকে না। থাকে আসামের জঙ্গলে।
তোমার আথকা হেই পাখি হইয়া যাইতে ইচ্ছা করতাছে ক্যা?
এই জ্যোৎস্না রাইত দেইখা, পূর্ণিমা রাইত দেইখা। আর ওই যে ইট্টু আগে যেই আনন্দটা পাইলাম সেই আনন্দে আমার জ্যাটিঙ্গা পাখি হইয়া যাইতে ইচ্ছা করতাছে। তোমারে কইলাম না জ্যাটিঙ্গা পাখিরা থাকে আসামের গভীর জঙ্গলে। ভরা পূর্ণিমা রাইতে চান্দের আলো দেইখা, জ্যোৎস্না দেইখা হেই পাখির মাথা খারাপ হইয়া যায়। জঙ্গল থিকা দলে দলে বাইর হয় পাখিডি। বাইর অইয়া কী করে জানো?
কী?
আত্মহত্যা।
কী?
আত্মহত্যা করে। দলে দলে আত্মহত্যা করে।
একটু থামলো রব্বান। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, আমার অহন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করতাছে। (পৃষ্ঠা ১০১৯-২০)
রব্বানের সাথে সংসার হলো না নূরজাহানে। পরে বিয়ে হলো তিনকন্যার পিতা মতলিবের সাথে। কিন্তু পেছনে তো লেগে আছে মান্নান মওলানা। সে যেহেতু নূরজাহানকে পায়নি, তাই কঠিন প্রতিশোদ নিতে চায় অপমানের। নেয়ও শেষ পর্যন্ত। ‘মতলিব আর নূরজাহানি যে সংসার করতাছে, ওইডা সংসার না, ওইডা জিনা, জিনা। ব্যাভিচার’ (পৃষ্ঠা ১০৫৪) এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে নূরজাহানকে শাস্তি দেয় প্রবল প্রতাপশালী মান্নান মাওলানা। নিজের ফতোয়া অনুযায়ী মাটির গর্তে ফেলে নূরজাহানের ওপর নিক্ষেপ করা হয় শত শত ইটের টুকরা। মিলন লিখছেন তখনকার পরিস্থিতির কথা:
নূরজাহান তখন আল্লাগো আল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বলে চিৎকার করছে। মান্না মাওলানা একটা কইরা ইটের টুকরা ছোড়েন আর নূরজাহান আল্লাহ বইলা চিৎকার দেয়। মিনারে বসা মোতালেবের পালা একটা সাদা কবুতর স্তব্ধ হয়ে আছে। ওড়ার ক্ষমতা যেন হারায়া ফেলছে কবুতরটি। মাঘমাসেও পদ্মার দিক থেকে আসে নরম একটু হাওয়া। সেই হাওয়া বন্ধ করেছে তার চলাচল। গাছের পাতারা নিথর হয়ে আছে, চকেমাঠে আর গিনস্থ বাড়ির উঠানে পড়া রোদ যেন রোদ না, রোদ যেন আসলে গভীর এক অন্ধকার। দিনের বেলাই যেন নেমে গেছে অন্ধকার রাত। মাথার ওপর আছে যে নীলসাদায় আশমানখানি, ওরকম সাতখান আসমানের উপরে আছে মহান আল্লাহপাকের আরশ, মান্নান মাওলানা একটা কইরা ইটের টুকরা ছোড়ে, নূরজাহান আল্লাগো আল্লাহ বলে চিৎকার করে, তার সেই চিৎকার সাত আশমান ভেদ করে চলে যায় আল্লাহপাকের আরশের কাছে। আল্লাহর আরশ কাঁইপা কাঁইপা ওঠে। (পৃষ্ঠা ১০৬৩)
ঔপন্যাসিকের কল্পনা হয়ে উঠতে পারে ক্ষমতাবান, মুক্তিকামী শক্তি যদি তা প্রয়োগ করা যায় আমাদের প্রত্যেকের মাথার মধ্যে অনুরণনরত অন্যকে, আগন্তুককে, শত্রুকে জাগিয়ে তোলার জন্য। ২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেলবিজয়ী তুর্কি কথানির্মাতা ওরহান পামুক বলেছেন: ‘যখন আমি একজন লেখকের কথা চিন্তা করি, আমি তেমন একজন ব্যক্তির কথাই ভাবি যিনি নিজেকে একটা ঘরে তালাবদ্ধ করেছেন এবং ধৈর্যের সাথে কথার মালা গেঁথে চলেছেন নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে, ঠিক যেমন করে একজন রাজমিস্ত্রি পাথর দিয়ে সেতু বানায়।’ (সূত্র: নাজিব ওয়াদুদ, নোবেল বিজয়ী অরহান পামুক, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৪৫) ‘নূরজাহান’ পড়তে গিয়ে মিলনকে সেতু বানানোর কারিগরই মনে হয়েছে মাঝে-মধ্যে। তিনি আমাদের সবচেয়ে আদিম ঘৃণা-ভয় এবং উদ্বেগ নিয়ে হাজির থেকেছেন আর ঐতিহ্যের আলোয় নির্মাণ করেছেন আধুনিকতা। উপন্যাসটি সচেতন পাঠকের মনে একটা গভীর ও বিভ্রান্ত আবেগের জন্ম দেয়। আর তা হলো লজ্জা। অবশ্য এটা অনুমান করা যায় যে, যখন কোনো জনগোষ্ঠী অপমানিত বোধ করে, তখন একটা অহংকারী জাতীয়তাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ‘নূরজাহান’-এ তেমনটাই ঘটছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি। যেহেতু উপন্যাস কোনো জনগোষ্ঠীর বিশেষ ইতিহাস অনুধাবনের সবচেয়ে বড় ভরসাস্থল, তাই তা পাঠ করার ভেতর দিয়ে কল্পনায় অস্তিত্ববান হয়েওঠা একটি জাতির ছবি সামনে চলে আসে।
ইমদাদুল হক মিলন গল্প বলার জন্যে লেখেন না, বরং গল্প নির্মাণ করেন তিনি। লেখার কৌশল ও প্রকরণ তাঁর আয়ত্বে আছে। আর লেখালেখির প্রতি মিলনের গভীর নিবেদন আমাদের চোখে পড়ে। তিনি জীবনলগ্ন কাহিনি নির্মাণ করেন। ‘প্রতিদিনকার সাহিত্য-ডোজ’ গ্রহণ করেন মিলন। সবচেয়ে ভালো নিরাময় আর সুখের বৃহৎ উৎস হিশেবে তিনি বেছে নিয়েছেন প্রত্যেক দিন কিছু-না-কিছু লিখে ফেলার রুটিন। তিনি উপযোগী দৃশ্য ও প্রতিবেশ-পরিবেশ স্থাপন করেছেন বর্তমান উপন্যাসে। ডিটেইলসের ভেতর দিয়ে তিনি পাঠককে নিয়ে গেছেন বাতাস ও অনুপ্রেরণা, মনের অন্ধকার নিভৃত কোণ আর কুয়াশা ও নিশ্চলতার মুহূর্তগুলোয়। ‘নূরজাহান’ পাঠ করতে করতে আমরা ভাব-ভালোবাসা-উন্মাদনা ও আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি। প্রেমাস্পদকে আনন্দ দিতে, শত্রুকে তুচ্ছ-তাচ্চিল্য করতে, শ্রদ্ধেয়দের কিছু বলতে, অজানা বিষয়ে জ্ঞানবানদের মতো কথা বলার ফুর্তি পেতে, হারানো ও স্মরণীয় অতীতের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করতে, ভালোবাসার স্বপ্ন দেখতে, বিশেষ কোনো দুঃখ কিংবা অসীম রহস্যের ভেতর দিয়ে পথ চলতে ‘নূরজাহান’ যেন অবশ্যপাঠ্য এক উপন্যাস হয়ে উঠেছে।
লেখক : শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ।