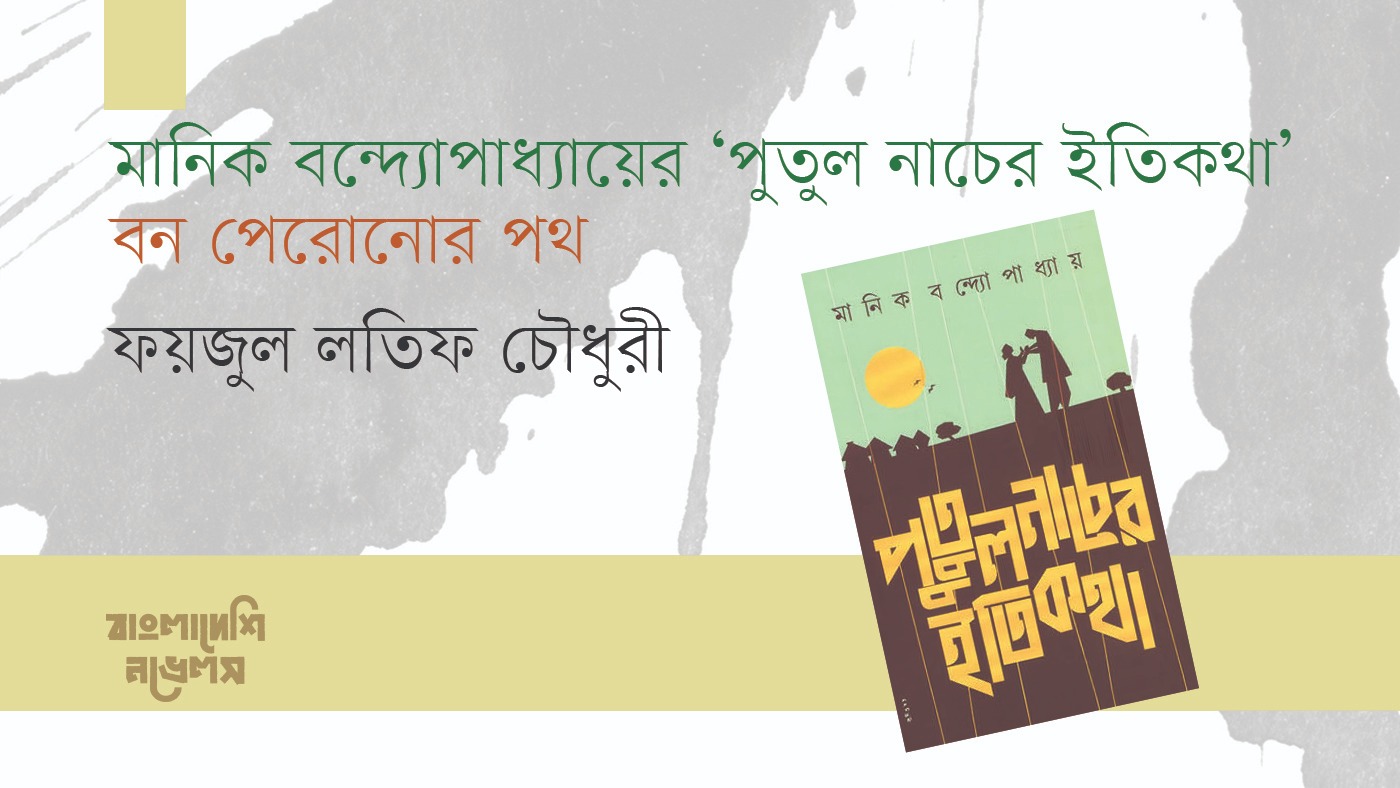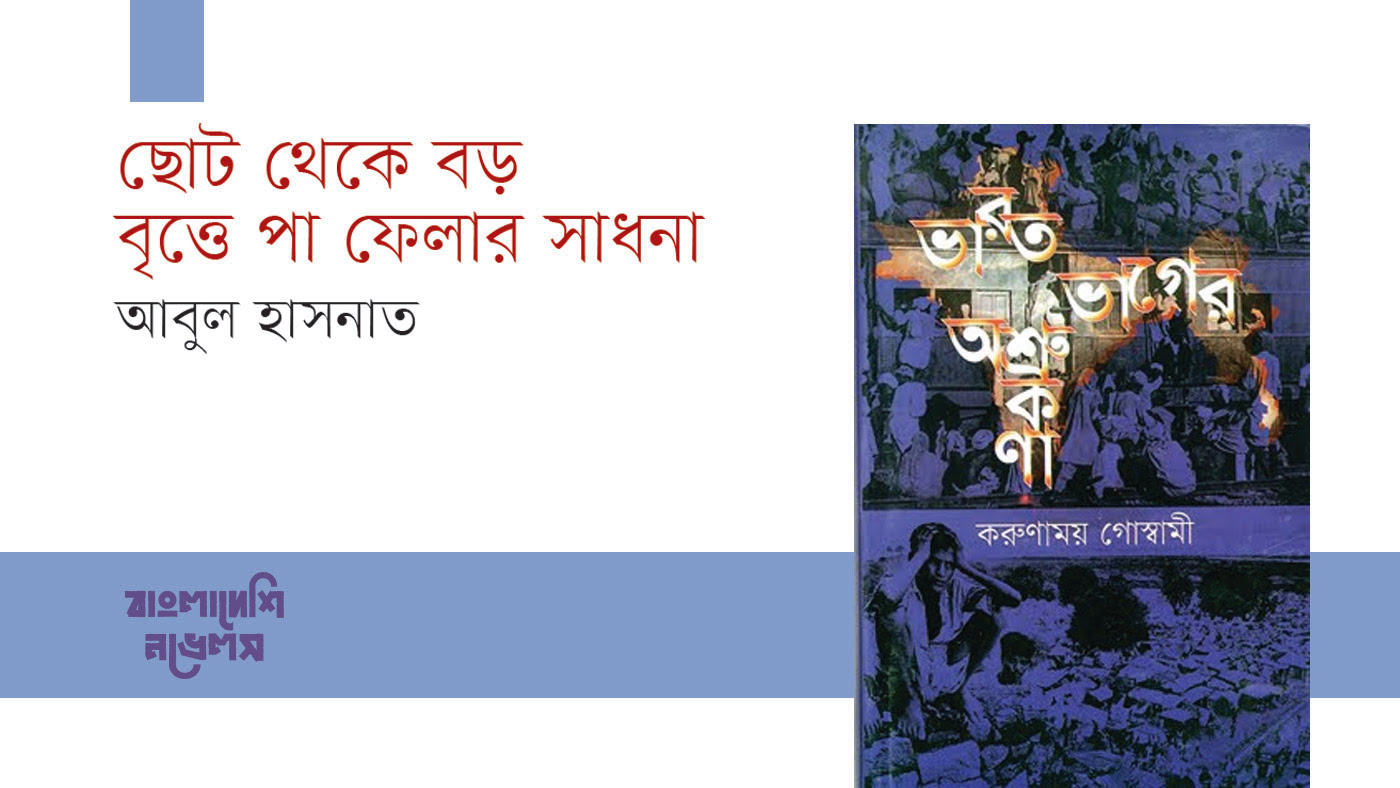বাংলাদেশের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর অন্যতম নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩) প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালের মার্চে সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখলের কিছুদিন আগে। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু-হত্যার পর থেকেই চলছিল সামরিক শাসন। সেলিনা হোসেন তখনো তরুণ। তাঁর প্রথম বই গল্পের সংকলন; উৎস থেকে নিরন্তর বের হয় ১৯৬৯ সালে। ১৯৮৩ সালের আগে প্রকাশিত তাঁর দুটি গল্পের বই ‘জলবতী মেঘের বাতাস’ (১৯৭৫) ও ‘খোল করতাল’ (১৯৮২)। সাড়া জাগানো চারটি উপন্যাস ছিল তখন তাঁর: জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২), হাঙ্গর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), মগ্নচৈতন্যে শিস (১৯৭৯) ও যাপিত জীবন (১৯৮১)। এরপরই ১৯৮৩ সালে নীল ময়ূরের যৌবন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমকালের রাজনীতিকে প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট করে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্ভর উপন্যাস হিসেবে এটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
তখন গল্প উপন্যাস নিয়ে কাজ করব বলে আমি এগুলো খুব মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করি। পড়তে-পড়তে কৌতূহলবশত একটি দীর্ঘ আলোচনাও লিখি। প্রকাশের জন্য তা একদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের হাতে দিই। সেলিনা হোসেন আমাকে চেনেন না। লেখাটি ‘লোকায়ত’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা (জুলাই ১৯৮৩)য় প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে সেলিনা হোসেনের ১১৪টির মতো বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নীল ময়ূরের যৌবন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসকে লেখক বলেছেন ‘কনটেম্পোরারি প্যারালাল’; অতীতের সময়টাকে সমসাময়িক করে লিখিত। এতে তিনি চর্যাপদের সময়কে ধারণ করে সাম্প্রতিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ভাষিক ও সাহিত্যিক সংকটের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।
মনে রাখা দরকার বঙ্গবন্ধু-হত্যার পরে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি নতুন করে সংকটের আবর্তে নিপতিত হয়। ১৯৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর একুশে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে ‘শহীদ দিবস’ পালনের পরিবর্তে, কুলখানি ও কোরআন তেলাওয়াতের রেওয়াজ চালু করতে চেয়েছিলেন। এই পটভূমিতে চর্যাপদের কবি সাহিত্যিক ও তাঁদের সৃষ্ট চরিত্র ও কাব্যভাবনা অবলম্বন করে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সমসাময়িক জনবিরোধি কালা কানুনের।
উপন্যাসের বিষয়বস্তুর জন্য লেখক পিছু হটে চলে গিয়েছেন একেবারে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে, বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জাতির উন্মেষের যুগে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে সাধক চর্যাকারগণ আধো-আধো গড়ে-ওঠা ভাষায় সে-কালের জীবন, জীবিকা এবং সামাজিক অবস্থাকে ধরে রেখেছেন গুটিকয় বিক্ষিপ্ত পদে। রচনাসমূহে আবহমান কালের আবেদন-যুক্ত যে খন্ড খন্ড জীবন-চিত্র ফুটে উঠেছে টীকাকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ শতকের শেষার্ধে দাঁড়িয়ে সেগুলোকেই একত্র এবং একীভূত করেছেন নীল ময়ূরের যৌবনে। আপন কল্পনার এবং শিল্পকলার সংমিশ্রণে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে শুরু করে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েকশ’ বছরের বাঙলার অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনালেখ্যের পটভূমিতে ক্ষুদ্র পরিসরে এক মহাকাব্যিক আবহ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এ-উপন্যাসে।
প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সেলিনা হোসেন আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বল ভুবনে অবস্থান করে উপন্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন ফিরে গেলেন হাজার বছরের পুরনো পটভূমিতে। লেখকের অভীষ্ট এবং অন্বিষ্ট কী ? প্রশ্ন-কাতর মন নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, এ-গ্রন্থে কেবল ঐতিহ্যের পুনরালোচনা এবং পুনর্মূল্যায়নই নেই, এতে প্রকটিত হয়েছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব-সচেতন অভিজ্ঞতা-পীড়িত এক মানব-সত্তা।
চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, মঙ্গলকাব্যে এবং পরবর্তী বাঙলাসাহিত্যে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে, পুরনো অতি-পুরনো বাঙলাদেশের এবং তার অধিবাসীদের যুগান্তরেও তাতে তেমন কোন পরিবর্তন নেই। আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক সংঘাত এবং বর্ণপ্রথা বা সামাজিক মানুষের উঁচু-নীচু শ্রেণীকরণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঘৃণা-বিদ্বেষ অত্যাচার অনাচার প্রতিবাদ সে-যুগে যেমন ছিল, এযুগেও তেমনই আছে। সত্য প্রকাশের সুযোগ এবং মত ও পথের স্বাধীনতা সেকালে যেমন ছিল না, একালেও তেমনি নেই। তবু তৎকালের শিল্পী-কবিরা গোপনে ঝুঁকি নিয়ে অন্তরের কথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেলিনা হোসেনও সামাজিক মানুষ হিসেবে অভিন্ন উপায়ে বলতে চেয়েছেন আপন শ্রেণীর মানুষের কথা। আর ব্যক্তিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে তিনিও কণ্ঠ মিলিয়েছেন চর্যাপদের কবিদের সঙ্গেই।
নীল ময়ূরের যৌবনের শ্রেণীনির্ণয় করতে গিয়ে এটিকে ঐতিহ্যিক উপন্যাস বলা হয়েছে। কিন্তু এতেই সব কথা বলা শেষ হয়ে যায় না। একালে কোন গ্রন্থকে কেবল ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যিক, সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক–এরকম কয়েকটি অভিধায় নির্দেশ করলে তার দ্বারা বিশেষ কিছুই বোঝানো যায় না। একটি উপন্যাস একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। নীল ময়ূরের যৌবনে ঐতিহ্য অবলম্বনে প্রকাশ পেয়েছে বর্তমানের বহুকৌণিক সঙ্কট ও সম্ভাবনা। উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে লেখক প্রায় দশবার ব্যবহার করেছেন চর্যাপদের একটি বহুল উদ্ধৃত চরণ : ‘অপণাঁ মাংসে হরিণা বৈরী’। চর্যাকার ভুসুকু ৬ সংখ্যক চর্যায় লিখেছেন : কাকে নিয়ে, কাকে বা ছেড়ে, কেমন করে যে আছি। আমার চারপাশ ঘিরে হাঁক পড়েছে আমাকে মারবার জন্য। দুঃখানুভূতিময় এই চর্যাটির মধ্যদিয়ে হরিণের রূপকে তৎকালীন সমাজের একটি বেদনাঘন পরিবেশের কথা তুলে ধরা হয়েছে। হরিণের দুঃখ এবং বিপদের চরম অবস্থা এটি। একটি বিপদাপন্ন অসহায় জীবনের সকরুণ অবস্থার কথা তুলে ধরার জন্য এই একটি চর্যাই যথেষ্ট। তৎকালীন সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস তপ্ত-হাওয়ার মতো চোখেত্বকে তীরের মতো বেঁধে ! প্রতিটি অধ্যায়ের শীর্ষে, কিংবা অধ্যায়-পরিকল্পনা ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশেও ব্যবহৃত হয়েছে এ চরণটি। বস্তুত এ-চর্যার যে অন্তর্নিহিত ভাব তা উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায় চরিত্র ঘটনা এবং বক্তব্যের অভ্যন্তরে গভীরভাবে বিধৃত।
হরিণের মাংসের জন্যই জগতের সকলে তার শত্রু। শিকারী সারাক্ষণ তাকে অনুসরণ করে, এক মুহূর্তও ছাড়তে চায়না। হরিণ তাই তৃণ স্পর্শ করছে না। এ অবস্থায় হরিণা তাকে উপদেশ দিচ্ছে : শোন হরিণ, তুমি এ বন ছেড়ে চলে যাও। লাফ দিয়ে দ্রুত চলে যাবার জন্য হরিণের ক্ষুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন, এই তত্ত্ব মুঢ় ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করে না। খন্ড খন্ড ভাবে এরূপ যেসব চিত্র ফুটে উঠেছে চর্যাপদে, সেগুলোতে সে-কালের সমাজ-জীবনের একটা গভীর শূন্যতাবোধ এবং দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানব পরিবারের চিত্রই ভেসে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি চর্যাতেই এই বেদনা-ভারাক্রান্ত অবস্থা থেকে মুক্তির আকুতি ধ্বনিত হয়েছে। চর্যাটির ভাববস্তু অনুধাবন করলে দেখা যায় গীতিকারগণ ইন্দ্রিয়কে চিত্তকে বিনষ্ট করার কথা ঘোষণা করেছেন। কারণ যে ট্রাজিক পরিস্থিতির মধ্যে কবিদের বসবাস তাতে কোন আকাঙ্ক্ষাই চরিতার্থ করার উপায় নেই। অতএব তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বিনষ্ট করাই উত্তম। একথার মধ্যে-যে কত বড় বেদনা লুক্কায়িত তা কেবল ভুক্তভোগীই অনুভব করতে পারেন। মানুষের না-পাওয়ার বেদনা অপরিসীম। চেয়ে না-পাওয়ার বেদনায় সঙ্কুচিত হওয়ার চেয়ে না-চাওয়ার বৈরাগ্যকেই অনেক সময় শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। উপন্যাসের প্রতি অধ্যায়ে হরিণের প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকায় প্রতিটি অধ্যায়ের মর্মার্থের জন্য এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। হরিণের মাংস সুস্বাদু বলেই সকলে হরিণের শত্রু। এই বাহ্য অর্থের আবরণে সেকালের চর্যাকারগণ যে বিষয়াতিরিক্ত বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এ-কালের সেলিনা হোসেন তাকেই আশ্রয় করেছেন। যখন তিনি চর্যার প্রেক্ষাপটে ভাষাগত সমস্যা, স্বাধীনতা-কামীর দুর্ভোগ, শ্রেণীপার্থক্যের গ্লানি ১৯৮৩ সনের বাঙলাদেশে বসেও নির্দ্বিধায় ব্যাখ্যা করতে পারেন না, তখন তিনি চর্যাকারের সাঙ্কেতিক ভাষার গল্প-কাহিনীর অবতারণা করবেন না তো কি করবেন ?
মানুষের মন স্বভাবতঃই স্বাধীনচেতা। সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, কিন্তু মনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। মনের শত্রুই তাই বড় শত্রু প্রগতিশীল মানুষের, বিপ্লবী মননই তার দুর্ভোগের কারণ হয়। অন্তরের তাগিদে কাজ করতে গিয়ে মানুষ কত বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবু তা থেকে বিরত হয় না। স্বাধীনদেশের নাগরিকও আজ ন্যায্য দাবীর কথা অকপটে বলতে পারে না। সেলিনা হোসেন একটা মানব গোষ্ঠীর প্রেম-কাহিনীর অন্তরালে হরিণের মাংসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এই অবরোধের অব্যক্ত বেদনাই প্রকাশ করেছেন মূলত।
কবি ভুসুকু বাণিজ্যে গিয়ে আর ফিরে আসছে না। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। পতিব্রতা রমণী সুলেখা আর কতদিন আশায়-আশায় সংযমে বুকে পাষাণ বেঁধে থাকবে। দীর্ঘ বিচ্ছেদে তার অন্তর স্বামীর স্মৃতি ভুলে যায়। তাছাড়া সুলেখার শরীরে হরিণের মাংসের ন্যায় লোভনীয় যৌবন অটুট রয়েছে। সুদামও তার সাথে ভাব জমাতে চায়। সুলেখা এই শরীর মন নিয়ে সুদামকে বেশি দিন উপেক্ষা করতে পারে না। একদিন বিপত্নীক সুদামকে সে জীবনের নতুন সঙ্গী করে নেয়। কিন্তু ভুসুকু ফিরে আসে একদিন। সব শুনে প্রেমিক ভুসুকুর বেদনার্ত কবি-মন উচ্চারণ করে চিরন্তন সত্য : অপণাঁ মাংসে হরিণা বৈরী। সান্ত্বনা পায় এই বলে : সুলেখার দোষ কি? এ-যে কালের বিধান।
গ্রন্থে ব্যবহৃত এই চরণের আপাত-সার্থকতা এভাবে দেখানো হলেও হরিণকে অবলম্বন করে যে গূঢ়-ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে তা মানুষের মন। চর্যাপদে ‘হরিণ’ ব্যবহৃত হয়েছে ‘মন’ অর্থেই। সদাচঞ্চল পৃথিবীর দিকে মন সর্বদাই প্রসারিত হতে চায়। কিন্তু বস্তু সংস্পর্শে তাকে বারবারই আহত হতে হয়। কেননা মনের তৃষ্ণা যেখানে তৃপ্ত হয় না, দুঃখ সেখানে আসে অবধারিত রূপে। এইসব দুঃখই মনকে ব্যাধের মত চেপে ধরে। হরিণের স্থানে মনকে না বসিয়ে যদি এর রচয়িতা ভুসুকুকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজে বিচরণশীল কোন মানুষকে কল্পনা করা যায় তাহলে এরকম একটা চিত্র দাঁড়ায় :
কবি-লোকটিকে মারবার জন্য চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছে। নিজের গুণের জন্যই তার এই বিপদ। তাই মনের দুঃখে সে পানাহার ত্যাগ করেছে। কিন্তু মুক্তির পথ সে জানে না। মুক্তির প্রেরণা তাকে বলছে, এই এলাকা ছেড়ে কোথাও চলে যেতে হবে। সেই প্রেরণাতেই সে দ্রুত ছুটে চলেছে। তৎকালীন সমাজের যে চিত্র এবং নিম্নবর্ণের লোকেদের প্রতি উচ্চবর্ণের লোকেদের যে অনুদার ব্যবহারের পরিচয় চর্যাপদে পাওয়া যায়, তাতে ভুসুকুর মুক্তির প্রেরণাকে বিন্দুমাত্র অসঙ্গত মনে হয় না। আর সেই একই প্রেরণাবশে সেলিনা হোসেনের এই উক্তির ব্যবহারও অযথার্থ বলে মনে হয় না। এই একটি চরণের নিপুণ ব্যবহারই জানিয়ে দেয় কেমন পরিস্থিতিতে সেকালের এবং একালের বাঙালি জনসাধারণ কালাতিপাত করেছে এবং করতে বাধ্য হচ্ছে।
দুই
নীল ময়ূরের যৌবনের গল্প-কাঠামো তৈরি হয়েছে শবরী এবং কাহ্নপাদের দাম্পত্য জীবনের প্রেমবিধুর জীবননাট্যের ভিত্তিতে। উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে বৌদ্ধ যুগোত্তর কালের সমাজব্যবস্থায়। বিশাখা চরিত্রটি অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন : “ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরের চত্বরে সময় আর কাটতে চায় না বিশাখার। কাল সন্ধ্যায় দেশাখ ওকে আসতে বলেছিল।—আস্তে আস্তে কেমন ভয় করতে থাকে বিশাখার। কতকাল আগের বৌদ্ধ মন্দির কে জানে ? এখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। লোকজন ইচ্ছেমত ইট কাঠ খুলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। রাজা কোন গরজ করে না। এ ধরনের তিনটে মন্দির আছে। সব ভাঙা।”
শবরী কাহ্নুপাদের নবপরিণীতা স্ত্রী। কাহ্নু বৌদ্ধ রাজা বুদ্ধমিত্রের রাজদরবারে পাখা-টানার চাকুরী করে আর শবরী স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে পাহাড়ের টিলার উপর চাচর বেড়ায় ঘেরা এক দরিদ্র কুটিরে। কর্মক্লান্ত দয়িতকে উপহার দেবার জন্য শবরীর রূপ-পরিচর্যার যে চিত্র পাওয়া যায় সেলিনা হোসেনে, তা ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক চর্যার অনুসরণেই অঙ্কিত। উঁচু উঁচু পর্বতের উপর শবরী যুবতী এবং কাহ্নুপাদের সংসার জীবন, ঘর-গেরস্থালী স্থাপিত। পাহাড়ের মাথায় বাঁশের চেচাড়ী দিয়ে তারা চমৎকার ঘর বানিয়েছে। ঘরের পাশে কার্পাস ক্ষেত, তাতে সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। শবরী মাথায় ময়ূরপুচ্ছ ; কানে কুন্তল গলায় গুঞ্জারমালা ও মুখে চন্দন-প্রলেপ প্রভৃতিতে অপরূপ সুন্দরী–আদিম রমণীর নৈশবিহারের আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব। কঙ্গুচিনা দিয়ে হাড়িয়া তৈরি করে রেখেছে রাতে মদ্য পানের আনন্দ অনুষ্ঠানে মত্ত হবার বাসনায়।
শবরী ও কাহ্নুর জীবনে রয়েছে অন্তহীন জ্বালা-যন্ত্রণা এবং দুঃখ-বেদনা–রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক কারণে। তবু স্বাধীন বন্যজীবনের প্রেক্ষাপটে সুখী যুবতী গৃহবধূ রোমান্টিক স্বরূপেই প্রথম চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সমাজের মধ্যে শবরী এবং কাহ্নুর সংসারটাই যেন অপেক্ষাকৃত সুখের। কারণ ওরা সংসারে মাত্র দুজন, আর কাহ্নুপাদই কেবল রাজদরবারে চাকুরী করে। সমাজের সকলের দৃষ্টিতে সে এজন্য একজন শ্রদ্ধা ও সমীহযোগ্য গণ্যমান্য ‘কবি-মানুষ’।
রাজা বুদ্ধমিত্রের কাদা-নিমজ্জিত ঘোড়ার গাড়ির চাকা তুলে দিয়ে একদিন সে এই চাকুরী পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। ‘নইলে ব্রাহ্মণদের প্রচন্ড প্রতাপে রাজার কাছে যাবার সাধ্য কারো নেই।’ এজন্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এবং পারিষদদের কেউ-ই ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখে না। অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি লোককে এত দূর নিয়ে আসার কোন যুক্তি তারা খুঁজে পায় না। অহরহ সকলে কেবল তার ক্ষতি করার জন্য পেছনে লেগে থাকে। তাই সকাল সন্ধ্যায় একটুও বিরাম নেই কাহ্নুপাদের। রাজা দরবারে উপস্থিত না-থাকলেও কাহ্নুকে পাখা টানতে হয়। হাত যখন অবশ হয়ে আসে তখন তার মনের মধ্যে কবিতার পংক্তি গুনগুনিয়ে ওঠে। সে পংক্তি কখনও ভালোবাসার, কখনও প্রতিবাদের। কিন্তু প্রতিবাদ সরাসরি করতে পারেনা বলেই তার গায়ে আবরণ দিতে হয়। শবরীকে সে বলে : ‘চারদিকে ভীষণ অন্ধকার, শবরী। পথ বন্ধ। এগুতে পারছি না।’ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সে ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
প্রতিদিনের ন্যায় আজও কাহ্নুপাদ কাজে চলেছে রাজ দরবারে। পথে দেখা হয় ছুটকীর সাথে। সে অন্যান্য ছেলেদের থেকে স্বতন্ত্র। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যরা তখন শিকারের ট্রেনিং নেয়। ছুটকী ভাবুক। কখনো উদাসীন। মনে হয়, ওর আলাদা কোন চেতনা আছে যা ওকে অন্য পথে পরিচালিত করে। ছুটকীর ইচ্ছা, সেও রাজ দরবারে যায় কাহ্নুর সঙ্গে। কিন্তু সে অধিকার নিম্নশ্রেণীর এই বালকটির নেই। “জন্মগতভাবেই ও সেখানে যাবার অধিকার অর্জন করেনি। রাজাদেরও যে তাদের প্রজাশ্রেণীর জন্য কোন দায়ভার নেই। ছোটলোকদের জন্য অত সময়ই বা কই” সরকারের ? নিজেদের দারিদ্র্য আর অভাবের কথা স্মরণ হলে কাহ্নুপাদের মনের মধ্যে এক দারুণ তাড়নার সৃষ্টি হয়। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে তার অন্তরে। —
“রাজসভায় কত ঐশ্বর্য। কত বিলাস। কত অপচয়, কত অনাচার। কোন কিছুরই লেখাজোখা নেই। ব্রাহ্মণেরা কাহ্নুকে কেন্দ্র করে যে ছুঁক ছুঁক করে, তা তাকে মোটেই স্বস্তি দেয় না। ধর্মে, কর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে, বিধি-নিষেধের খতিয়ান প্রণয়নে হোতা সেজে বসে আছে ঐ ব্রাহ্মণেরাই। ওদের প্রতাপকে অস্বীকার করে কার সাধ্য! অন্তরে যতো ক্ষোভ, যতো জ্বালাই থাকনা কেনো, কাহ্নুপাদকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে এই ব্যবস্থা। নইলে তো প্রাণে বাঁচাই দায়।” -এসব ভাবতে ভাবতে কাহ্নুপাদ দরবার অভিমুখে নদীর পথে অগ্রসর হয়। এভাবে কাহ্নুপাদের চরিত্রের ক্রমাগ্রগতিকে অবলম্বন করেই উপন্যাসটির ঘটনা এবং অন্যান্য চরিত্র বিকশিত হয়েছে।
নায়ক কাহ্নুপাদ বিবাহিত পুরুষ। সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর মুখপাত্র হিসেবে সকলের বেদনা তার অন্তরে দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে- অথচ সে অবৈধ প্রণয়াসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ। সুযোগ পেলেই সে যুবতী নারীর শরীর কেন্দ্র করে প্রেমভাবে তন্ময় হয়ে পড়ে। অতি প্রত্যুষেই ইন্দ্রিয়ের প্রচাপে মদ-বিক্রেতা দেবকীর শরীরী প্রতিচ্ছবি তার মানসচোক্ষে ভেসে ওঠে। দেবকী পছন্দনীয় রমণী। সব সময় মুখে তার হাসিটা লেগেই থাকে। দারুণ সতেজ এবং স্নিগ্ধ দেবকী। গত রাতেই শবরীর সাথে কাহ্নুর কামগ নৈশ-বিহারের অনুভূতি এবং মদ্য-পানের প্রতিক্রিয়া সার্থক হয়েছে, সেসবের কোন স্মৃতিই এখনও ম্লান হয়নি; তবু তার দেবকীর কথা ভাবতে ভালো লাগে। দেবকী তার মগজের মধ্যে বসে খুনসুটি করছে। তার চেহারা মনের মধ্যে লালন করে কাহ্নুর সুখ বাড়ে। দেবকী কিংবা ডোম্বীর কথা মনে হলে সে জগতের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরস্ত্রীর রূপ-যৌবন তার মনের মধ্যে হাহাকার তোলে, অন্তর তার ডুকরে মরে ; নৌকার মাঝি ডোম্বীকে তাই সে আত্মরতির ও দৃষ্টি-মৈথুনের সামগ্রী করে।
প্রতিদিন রাজ দরবারে চাকুরীতে যাবার পথে সে ডোম্বীকে একবার দেখতে পায়। কাহ্নু কবি বলে, ডোম্বী তাকে ভালোবাসে। কাহ্নুও ডোম্বীকে ভালোবাসে। তবে শবরী এবং ডোম্বী তার মননে দুটি ভিন্ন প্রতীক। শবরী মন্দিরার মতো মৃদু সুরলহরী, ডোম্বী নদীর উত্তাল স্রোতের মতো উর্মীমুখর। ডোম্বী নিমিষেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় কাহ্নুকে শবরীর ক্রোড় থেকে- কূল থেকে অকূলে। শবরী ওর বিয়ে করা বৌ, কিন্তু ডোম্বীর জন্যই ওর অনুরাগ বেশি। এ মুহূর্তে কাহ্নুর মনে হয়, এই উদারমুক্ত নিসর্গ নদী নারী, সবই তাদের। কিন্তু “রাজ সভায় গেলে টের পায় কিছুই তাদের নয়। সব ওদের, যারা উঁচু বর্ণের। ওরা (উঁচু বর্ণের লোকেরা) ভোগ করবে, খাবে, ছিটোবে, ফেলবে। যেটুকু কাঁটাকুটো তা ওদের (কাহ্নুদের) জন্য। এইটুকু চেটে চুটে ওদের খুশি থাকতে হবে, কোন কিছুই চাইতে পারবে না।”
কাহ্নুপাদের চরিত্রকে বিকশিত করে তুলতে আরো কটি চরিত্রের সংযোগ ঘটেছে এ-উপন্যাসে। দেশাখ এবং তার বৌদি সুলেখা, দেশাখের প্রণয়িনী বিশাখা, ভৈরবী এবং তার স্বামী ধনশ্রী উপন্যাসের আরও কতিপয় চরিত্র। কাহ্নুপাদের স্ত্রী হলেও শবরী এ-উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকটাই নিষ্প্রভ। তার পাশে ডোম্বী উজ্জ্বল চরিত্র। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে বাঙময় করে তোলার জন্য কাহ্নু ব্যতীত ডোম্বী, দেশাখ, ছুটকী উল্লেখ্য চরিত্র। গ্রন্থের নায়িকা কিন্তু ডোম্বী। সে কাহ্নুকে ভালোবাসে। কারণ কাহ্নু কবি, ভবিষ্যত-দ্রষ্টা, জাতির কণ্ঠস্বর ও বিপ্লবী। ডোম্বী নিজে দেশ-হিতৈষিণী এক বিপ্লবী রমণী। চর্যাপদে মনে হয় ডোম্বীকে নিয়ে কাব্য রচনা করেই কবিরা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রতি বিদ্রোহ ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। বস্তুত ৩৩ সংখ্যক চর্যার ভাব অবলম্বন করেই লেখক ডোম্বী চরিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। ডোম্বী সমাজের অত্যন্ত দরিদ্র, স্বামী-পরিত্যক্তা এক নারী। জীবিকার জন্যে সে খেয়া পারাপার করে। প্রয়োজনে রাতে টাকার বিনিময়ে যৌবনের মধু বিতরণ করে। তার প্রতি এক কাহ্নুপাদ ব্যতীত অন্য কারো সহানুভূতি নেই। অন্যেরা (রাজার লোকেরা) ডোম্বীর দারিদ্র্যের সুযোগে লাম্পট্য-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য রাতে তার বাড়িতে ভীড় জমায়। চর্যাকার কাহ্নুপাদ ১০ সংখ্যক চর্যায় গেয়েছেন : নগরীর বাহিরে রে ডোম্বী তোমার কুঁড়ে ঘর। সেখানে ব্রাহ্মণ আর নেড়েরা যে যাওয়া আসা করে, তুমি তাদেরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও। ওগো ডোম্বী, আমি তোমাকে সাঙ্গা করবো। আমি কানু কাপালিক, নিঘৃণ এবং উলঙ্গ যোগী, তোমার জন্যই নলের পেটরা পরিত্যাগ করলাম। এখানে সমাজের উচ্চ কোটির লোকেদের নিম্নসম্প্রদায়ের প্রতি যে নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তাকে সেকালের সমাজের খাঁটি প্রতিচ্ছবি মনে করতে কোন বাধা নেই।
সমাজের অবহেলিত এই নারীকে বিয়ে করতে চেয়ে কবি সমাজের বিধিবদ্ধ রীতির প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কারণ, ডোম্বী এমনই এক নারী যে তাকে বিয়ে করতে চাইলে সমাজের প্রতি কঠিনতম অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। এই কাব্যভাবটুকুকে অবলম্বন করেই লেখক কল্পনারস সহযোগে ডোম্বীকে এক বিদ্রোহিনীর চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। ডোম্বীর কাছে তাই সব পুরুষই গতানুগতিক কেবল কাহ্নু ব্যতীত। কাহ্নুর মতো একটি পুরুষের ভালোবাসাই কেবল ডোম্বীর মন উদার করে দিতে পারে। ডোম্বী কাহ্নুকে বিনা পয়সায় নদী পার করে দেয় । কিন্তু অন্য কাউকেই সে বিনা পয়সায় পার করে না। কারো হাজারো মিনতিতেও ডোম্বীর হৃদয় গলেনা । কাহ্নু সেখানে নিজে থেকে পয়সা দিতে চাইলেও ডোম্বী তা নেয় না। দুটো কারণ এর জন্য অনুমিত হতে পারে : হয় ব্যক্তিগত ভালোবাসা, না-হয় জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা বলেই কাহ্নুর প্রতি ডোম্বীর এই ভালোবাসাময় ব্যবহার। ডোম্বী, ছুটকী, দেশাখ, ভৈরবী এবং ধনশ্রী কাহ্নুপাদকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শ্রেণীভেদের তীব্র নিষ্ঠুরতা।
ছুটকী হচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতের প্রতীক। তাকে কেন্দ্র করেই বর্তমানের বৃদ্ধ, অক্ষম, ভীরু সব জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাপ্নিক মনোভূমে লালিত ও আবর্তিত। সমাজের শ্রেণীবদ্ধ রূপের প্রকাশ পেয়েছে মন্ত্রী দেবলভদ্রের সংযোজিত আরো দুটি সামাজিক আইনে। এক. ব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে-কোন ধরনের মেলামেশা করতে পারবে, সে নারী যদি তার বিবাহিতা স্ত্রী নাও হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এমনকি সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের কোনো রমণীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলেও কেবল সংসর্গদোষ ছাড়া তাদের কোনো অপরাধ বোঝাবে না।
দ্বিতীয়ত: বিবাহিতা নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যাভিচার করা কমদোষের হবে। তবে নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। এই সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে চর্যাপদে বিধৃত সমাজের নৈতিক অধঃপতনের প্রতিচ্ছবির। ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, রাজারাইতো এই আইন প্রণয়ন করেছেন। কিংবা ব্যবহারিক জীবনে নানা প্রকারে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ পূর্বক তারাই দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে অলিখিত আইনে পরিণত করেছেন এই ব্যভিচারী যৌনাচারকে। ফলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বাৎসায়নের কামসূত্রের খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের এই চিত্র চর্যাপদেও আছে, সেলিনা হোসেনেও এসেছে।
পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান হলো দেশাখ। দেশাখ বীর শিকারী স্বভাবে বোহেমিয়ান অন্তরে প্রেমিক। “শিকারের বাইরে কোন কাজ খুব একটা করতে চায় না। তার উপর কোন কিছু মনোমতো না হলে সবাইকে গালগাল করে সে আস্ত রাখেনা। ওর রুগ্ন চেহারায় কোথাও কোনো মায়া-দয়া নেই বলেই মনে হয়। দেশাখের সংসারের প্রতিও কোন টান নেই।” কিন্তু পঙ্গু বৃদ্ধ বাবা আর মা ভাইবোন, বৌদি সুলেখা- এতগুলি মানুষের অভাব এবং দারিদ্র্যে ভরা সংসার যন্ত্রণাদায়ক। সংসারের প্রয়োজনে তাই তাকে খাটতেই হয়। সে সজারু ঘুঘু হরিণ এসব শিকার করে আনে। তা নিজেরা খায়, এবং বিক্রী করে দু’পয়সা পায়। তাছাড়া বৌদি সুলেখা বাঁশের চাঙ্গারী বুনে তা বিক্রি করায় কিছু আসছে বলে কোনো রকমে দিন চলে যাচ্ছে। বড় ভাই ভুসুকু পরের নৌকায় বাণিজ্যে গেছে কড়ি রোজগারের জন্য। কিন্তু সেই যে কবে গেছে, আজও ফিরে এলোনা। আসবে কিনা তাও কেউ জানে না। “ভাগ্য ভালো হলে নির্ঝনঝাটে ফিওে আসা যায়। নইলে একদিকে যেমন রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির ভয়, তেমনি অন্য দিকে আছে জলদস্যুর উৎপাত। সামনে পড়লে নিঃস্ব করে দেয়।’’
দেশাখকে চাঙ্গারী বিক্রি করার জন্য শহরে যেতে তাগিদ দেয় সুলেখা, আর বলে : দাদার খোঁজটাও যেনো সে নিতে চেষ্টা করে। দেশাখ জানে, খবর আনা যাবেনা দাদার। এসে মিথ্যে করে বৌদিকে বলতে হবে। কিন্তু একটা কথা মনে করে দেশাখের হাসি পায় : “দাদাকে ছাড়া বৌদির দিন যেনো আর কাটে না । তার শরীর মন দাদাকে পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তার বাবা মার কথোপকথনে দেশাখ এবং সুলেখার মুখ দিয়ে মানবীয় মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বৃদ্ধ বাবার গায়ে জোর নেই। শয্যাশায়ী বলে মা তাকে সবসময় গালাগালি করে এবং তার মৃত্যু কামনা করে শুনে দেশাখ এবং সুলেখা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাবা অথর্ব বলে মা তাকে সহ্য করতে পারেনা। অথচ সুলেখা ভুসুকুর বাড়ী-ফেরার দিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে। ভুসুকু জোয়ান উপার্জনক্ষম, সুলেখার সর্বপ্রকার প্রয়োজনে লাগে। এজন্যই কি সুলেখার ভালোবাসা ? দেশাখ বৌদিকে বলে : “প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তুমিও মার মতো দাদাকে গালাগালি করবে। জোর করেও ভালোবাসতে পারবেনা।”- দেশাখের এ প্রণয়-সঙ্কটতত্ত্ব ব্যাখ্যায় লেখকের তীব্র আবেগপূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই ব্যখ্যা তাঁর সৃষ্ট সুলেখার জীবনে এবং কাজে অন্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
ধনশ্রী এবং ভৈরবীর চাচর-বেড়ার ঘরে পাতা সংসারেও রয়েছে একই রকম আর্থিক দৈন্যদশা। ‘দু বছর আর তিন বছরের ছেলে দুটো একটানা কাঁদছে। গরু দুইয়ে তিন সের দুধ পেয়েছে ধনশ্রী। বিক্রি করে চাল আনবে।’ ‘স্বামী কখন আসবে ঠিক নেই, তবু ভৈরবীর আক্ষেপ নেই। ভীষণ শান্ত স্বভাব ভৈরবীর। কথা বলে সুন্দর করে। সেজন্যে সকলে পছন্দ করে’ ওকে। কিন্তু ভৈরবীর সংসারের অভাব তাকে কামোদের দোকানে গিয়ে ধার আনতে বাধ্য করে। সংসারে ছেলেমেয়েই নয়, অতিথিও যে রয়েছে। বিশেষত অতিথিকে উপোস রাখলে বড় পাপ হবে। চর্যাপদে আছে : হাড়িতে ভাত নেই, নিত্য অতিথি। চর্যার সঙ্গে আরো একটা সাদৃশ্য- ভৈরবী বাকীতে সওদা আনতে গেলে কামোদের মনে প্রেম জাগ্রত হয়। দারিদ্র্যের সুযোগে সে-যুগে এবং এ-যুগেও অর্থবান লোকেরা দরিদ্র-রমণীর দেহোপভোগের বাসনা প্রকাশ করে।
দেশাখ, রামকী, ধনশ্রী, দেবেন, সাধন, কামোদ, কাহ্নুপাদ সকলে মিলে হরিণ শিকারের আয়োজনে মেতে উঠেছে। শিকার শেষে বসবে ওদের হরিণ-উৎসব। এ অধ্যায়টি তৎকালীন সমাজ-চিত্রকে উম্মুক্ত করে দেয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য। শিকারী-প্রধান জনগোষ্ঠীর এই ছবি বাঙলাদেশের বৌদ্ধ-যুগের শেষ পাদের পাল আমলের সমাজজীবনের ছবিই তুলে ধরেছে। এখানে খাদ্যদ্রব্যের প্রধান সামগ্রী হরিণ, সজারু, শামুক, কাগনী ধানের চাল, নদীর মাছ প্রভৃতি। শিকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কবি কাহ্নুপাদও। তাকে দেখে ডোম্বী জিজ্ঞেস করে : ‘গীত লেখা ছেড়ে দিয়ে শিকারে যে ?’ উত্তরে কাহ্নুপাদ বলে: ‘কেবল গীত লিখে কি পেট ভরে?’ জীবন-জীবিকার নিষ্ঠুর তাড়নায় মানুষকে কতো রকমের কাজ করতে হয়! এ-সমাজে এবং সেকালের সমাজেও যাঁরাই শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করেছেন, তাঁরা প্রায়শই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আরাম-আয়েসকে পরিহার করে কেবল নিজের চেষ্টাতেই তা করেছেন। উপরোক্ত সংলাপ দুটিতে জীবন-জীবিকার প্রেক্ষাপটে শিল্প-সাহিত্যের অবস্থান ফুটে উঠেছে। চর্যার সমাজের সাধারণ পুরুষের দল শিকার করতে যাবার পথে দেখতে পায় জেলেরা নদীতে মাছ ধরছে। সে মাছ দেখে সকলের জিহ্বায় পানি চলে এসেছে। এতে বুভুক্ষু সমাজের অনাহারী মানুষের আর্থিক দশার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। আবহমানকালের বাস্তব বাঙলাদেশের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র এটিই। এই মাছ দিয়ে শুধু দুটো ভাত খেতে পারলেই যেনো তারা যথেষ্ট খুশি হতে পারত। এর বাইরে জীবনে চাওয়ার আর খুব একটা কিছু তাদের ধারণায় নেই। কিন্তু এক সময় ওরা অনুভব করে যে, এই মাছ তো সবই রাজ-দরবারে চলে যাবে। এই মাছ কখনো ওদের জন্য নয়। দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ উপাদান উৎপাদকদের বৃদ্ধ আঙুল দেখিয়ে সমাজপতি-রাষ্ট্রপতিরাই তা ভোগের জন্য নিয়ে যায় রাজ-দরবারে আর চাষী-জেলে-শিল্পী-শ্রমিক থাকে অভুক্ত অনাহারী। তদুপরি সমাজের কৃষকেরাও জমি হারিয়ে দিন দিন ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হচ্ছে। রাজা বুদ্ধ মিত্রের আমলেও দেখা যায় : ‘পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধান চাষ করেছে রাজার লোকেরা। এগুলো রাজা বুদ্ধ মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্রী দেবলভদ্রের নিষ্কর জমি। এখানে আগে বিশাখার বাবার জমি ছিল। জমি ছিল ধনশ্রীর ও আরো অনেকের। একদিন দেখা গেল সেটা আর ওদের নেই। রাজা খুশি হয়ে মন্ত্রীকে দান করেছেন। কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কেউ কোন আপত্তিও করতে পারবেনা। কেননা রাজা দেশের ভূমির একমাত্র মালিক।’
কিন্তু এই নিঃসম্বল মানুষদের মনে প্রেম আছে, আছে জৈবিক তাড়না এবং আনন্দ উৎসবের ঘনঘটা। তাই নিঃস্ব জনগোষ্ঠী শিকার করে আনে বন থেকে হরিণ সজারু আর খরগোশ, তারপর উৎসবে মেতে ওঠে। উৎসবে জোড়া জোড়া যুবক-যুবতী নারী-পুরুষেরা নাচে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সে উৎসবের মধ্যমণি বারাঙ্গনা ডোম্বী, আর তার শরীরী-নৃত্যই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। তবে তাতে আরো নতুন নতুন নারী-পুরুষের জুটিও প্রায়ই নাচতে নামে। এবারও নাচ-অনুষ্ঠনে এসেছে কাহ্নু শবরী দেশাখ এবং তার প্রেমিকা-কিশোরী বিশাখা। দেশাখ আবার সাথে করে নিয়ে এসেছে তার বৌদি সুলেখাকে। সুলেখা প্রথমে আসতে চায়নি। তার স্বামী বিদেশ গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তা ছাড়া শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও রয়েছে ঘরে। দেশাখ বৌদির দ্বন্দ্ব-ভারাক্রান্ত মনকে বুঝতে পেরে জোর করেই তাকে নিয়ে এসেছে উৎসবে।
: চলো বৌদি! সারারাত উৎসব হবে আর তুমি একলা মন খারাপ করে বসে থাকবে কেনো? সুলেখা বলে : তোমরা হাড়িয়া খাবে। জোড়ায় জোড়ায় নাচবে। আমি কি করবো বলতো? দেশাখ বলে : তুমিও সঙ্গী জোগাড় করে নাচবে। তারপর সুলেখা সঙ্গী করে নেয় সদ্য বিপত্নীক জোয়ান পুরুষ সুদামকে। তারপর এক সময় আর সুলেখাকে খুঁজে পাওয়া যায়না। আজ সুলেখা দেশাখের চোখের আড়ালে থাকতে চায়। তাই থাকুক।”
পরবর্তী অধ্যায়টি সবচেয়ে আকর্ষণীয় এ কারণে যে এখানে এসেছে বাঙালীর মুখের ভাষার সমস্যা। বাঙালী হাজার হাজার বছর ধরে শাসিত হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিজাতিদের দ্বারা। যদি কখনো স্বজাতির লোক হয়েছে রাজ্যশাসক, তবু সেখানে রয়েছে উচ্চ জাতি আর নিম্নজাতির ভেদাভেদ রেষারেষি। সমাজে উচ্চশ্রেণী আর নিম্ন-শ্রেণীতে দেখা দিয়েছে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব। একালে বসেও সেলিনা হোসেন কি কারণে-যে ‘অপণাঁ মাংসে হরিণা বৈরী’ শিরোনাম দিয়ে হাজার বছরের পুরাতন চর্চাগীতিকায় বিধৃত সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে এ-উপন্যাসের রূপচিত্র এঁকেছেন তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, যখন বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও বর্ণবাদী সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হতে দেখা যায়। সেকালের মানুষ কিংবা কবিরা হয়তো ঠিক এভাবেই বলেননি কথাগুলি কিংবা সামাজিক রাষ্ট্রিক আর্থিক জীবনকে অবলম্বন করে রচিত হয়নি কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য। কিন্তু চর্যার সমাজের খন্ড খন্ড ছবি নিয়ে কল্পনাশক্তির সাহায্যে শৈল্পিক সত্তার সংমিশ্রনে সেলিনা হোসেন রচনা করেছেন বিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের চিত্ররূপ-উপাখ্যানকে।
ভাষা সমস্যা নিয়ে সে যুগের সামাজিক ছবিকে পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেলিনা হোসেন একালের ভাষা-সমস্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণা প্রসূত উপলব্ধি সহযোগে। বারবার এসেছে বাঙালীর মুখের ভাষা বাঙলার উপর দেশী বিদেশী অভিভাবক ও শাসক গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর আঘাত। সেকালে ‘স্বভাবতই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়া কর্মের হোতা হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণেরা। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের গভীরে এর শেকড় গ্রোথিত ছিল। আর এ আধিপত্যের শিকার হয় নিম্নবর্ণের মানুষ। রাজা বুদ্ধমিত্র এবং মন্ত্রী দেবলভদ্র দুজনেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি। ইন্দ্রিয় কর্তৃক চালিত হতে বড় ভালোবাসে তারা। এজন্য বিভিন্ন গোত্র থেকে যুবতী নারী সংগ্রহ করে তারা ইন্দ্রিয়ের লালসাকে পরিতৃপ্ত করে থাকে।
নানা উৎসবে সেসবের অব্যবহারের তো কোন কথাই নেই। আর গুণগ্রাহী বেপরোয়া সাঙ্গ-পাঙ্গরা সাধারণত জোগায় এসব নারী-সামগ্রী। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মেয়েদেরকে তারা ধরে আনে জোরপূর্বক। তাতে কারো কিছু বলবার থাকেনা। একালের সমাজেও কি এই চিত্র বহু পুরাতন ? না, এসব অনাচারের বিরুদ্ধে কেউ কোনদিন প্রতিবাদ করে না, করতে পারেনি, কখনই পারেনা কেউ। করলেও তা ঢাকা পড়ে যায় সহস্র কন্ঠের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও গুঞ্জরণে।
কাহ্নুপাদের কাছে রাজসভার এ ধরনের পরিবেশ ভীষণ শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে ওঠে। অথচ মুখটি খোলার জো নেই। কিন্তু সে-যে একজন কবি সে-কথাও সে ভুলতে পারেনা। মনই তার প্রধান শত্রু । অন্তরের ভেতর প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র হয়, তখন ঐ রাজসভা তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছা করে কাহ্নুপাদের। ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের রাশভারী সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি ওর লৌকিক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ওরা ওকে নিয়ে যতই হানাহানি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করুক না কেন। কারণ এটাই-যে তার বুকের ভাষা। ওরা শত শত লোক যে ভাষায় কথা বলে তার কি কোন মূল্য নেই? ভাবতে ভাবতে কাহ্নুপাদের মাথাটা ঝিম ধরে আসে। কিন্তু ধৈর্য না ধরলে সকলের মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না কিছুতেই। অনেক অনুনয় বিনয় করে রাজা বুদ্ধমিত্রের কাছ থেকে রাজ সভায় কবিতা পাঠের অনুমতি পেয়েছে কাহ্নুপাদ। ডোম্বীর কাছে গিয়ে সে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে : ‘এতদিনে আমার ভাষার মর্যাদা হবে মল্লারী। আমি দেখাবো ওদের ওই তালের মতো শব্দগুলো কেবল ভাষা নয়। আমাদের ভাষা ঝরঝরে, প্রাণ আছে।’….কাহ্নুপাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভাষা প্রশ্নে লেখক উচ্ছ্বাস-প্রবণ হয়ে উঠেছেন। আবেগায়িত সংলাপ প্রকাশ পায় ডোম্বীর কন্ঠ থেকে : ‘তোমার হাতে যাদু আছে কানু। মুখের ভাষা তুমি বুকের ভাষা করে দাও।’- কাহ্নুকে উদ্দেশ্য করে ডোম্বীর কথা যেনো সমগ্র লেখকসম্প্রদায়কে সম্বোধন করে অভিব্যক্ত ঔপন্যাসিকের এক আকুল আবেদন।
কিন্তু, কাহ্নুপাদ শেষ পর্যন্ত তার কবিতা রাজসভায় পড়তে ব্যর্থ হয়। ছোটমুখে নাকি বড়কথা বা কাব্য-চর্চা মানায় না। কাহ্নুপাদ প্রতিজ্ঞা করে : ‘ঐ রাজ সভায় গীত গাইতেই হবে। যত যন্ত্রণা, যত কষ্টই হোক।’ তারপর কাহ্নুপাদ কাব্য-চর্চায় মনোযোগী হয়। আগামী সভায় সে যে কবিতাটা পড়বে তাই রচনায় সে মেতে উঠেছে। ঐ কাব্য-চর্চার মুহূর্তটিকে লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে : এদিকে কাহ্নুপাদ ক্রমাগত নিজের ওপর বিরক্ত হচ্ছে। কোন পংক্তিই পছন্দ হচ্ছেনা। পুরোটা তো পরের ব্যাপার। কখনো মনে হয়, নিজের জ্বালার কথা উচ্চস্বরে বলে। পরক্ষণে চুপসে যায়। তাহলে ওরা ওকে মেরে ফেলবে। পড়তে দেবেনা। কুক্কুরীপাদ এজন্যেই বলে ‘রুখের তেন্তলী কুম্ভরী খাঅ।’ সরবে বলতে পারেনা বলে কুক্কুরীপাদ এমন আবরণ দিয়ে বলে। চমৎকার কথা বলে কুক্কুরী। ওদের জীবন-গাছের তেতুল ঐ দেবলভদ্রের মতো হোতকামুখো কুম্ভীরে খায় বলেইতো ওদের এত যন্ত্রণা সমাজে। ঠাঁই নেই, মুখের ভাষার দাম নেই। ঘরে প্রতিদিনই অভাবের গরম খোলায় উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। নইলে এত ধান এত কার্পাস, ওদের কিসের অভাব? সব ঐ রাজার গোলায় যায়। ছোট লোকদের জন্য কেবল নেড়াকুটা। আর কি? ওদের জন্য ঐটুকুই যথেষ্ট। এতেই ওদের বর্তে যাওয়া উচিত। কাহ্নু একবার ডোম্বীকে নিয়ে রচনা করে : নগর বাহিরে ডোম্বী তোহরী কুড়িআ। ছুই ছুঁই যাইসি ব্রুাহ্মণ নাড়িআ।।- কিন্তু পরক্ষণেই কেটে দেয়। দরবারে বসে ঐ কবিতা পড়লে রাজার লোকেরা ওখানেই ওকে হত্যা করে ফেলবে। কারণ, যতো অনাচারই হোক, শাসকদের জন্য, উচ্চ বর্ণের লোকদের জন্য সবশুদ্ধ, ছোট লোকেরা তা বলতে পারবে না। তারপর আপাতত পড়বার জন্য লেখে: আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা। তা দেখি কাহ্নু বিমণা ভইলা।’
ভীষণ অন্ধকার পথ। তা দেখে কাহ্নু বিমনা হলো। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর রচনা শেষ করে ওঠে কাহ্নুপাদ। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। যদিও ঐ গীতটা লেখার পর ওর একটা আত্ম-বিশ্বাস জন্ম নেয়। কিন্তু ‘দ্বিধামুক্ত হতে পারে না। পন্ডিতেরা বাঘের মতো বসে থাকে। সুযোগ পেলেই হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেবল। এমনিতেই ওরা কেউ ওর ওপর খুশি নয়। জোর করে অহরহ নিজের দাবী জানাতে হয়।’ লেখকের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এ-উক্তি একালের সমাজ-রাষ্ট্র এবং সাহিত্য-সমাজের প্রেক্ষিতে একটি চমৎকার রসঘন মন্তব্য। সমাজ-মনকে মুক্তভাবে প্রকাশ করতে দেয় না। তার বিরুদ্ধে লেখকের কাঁক্ষ- মৌন প্রতিবাদ : ‘মন না থাকাই ভালো। মন থাকার যন্ত্রণা অনেক। হাজার বছর আগেকার সামাজিক অবস্থা যেনো আমাদের সমাজে এখনও বিদ্যমান। কবি কাহ্নুপাদের আর একটি বিক্ষোভ সংস্কৃত পন্ডিতদের জীবন বিচ্ছিন্ন সাহিত্যের বিরুদ্ধে। জীবনবাদী গীত রচনা করে কাহ্নুপাদ রাজসভায় হাজির হলো। কিন্তু যখন দেবলভদ্র শোনে যে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ কাহ্নুপাদ কবিতা পড়বে, তখন তার বিস্ময় এবং ক্রোধ চরমে পৌঁঁছে : ‘তুই কি গীত লিখিস ? তুই সংস্কৃতের কি জানিস ?/ : সংস্কৃত জানবো কেনো ? আমার ভাষায় লিখেছি। /: ও ছুঁচোর কেত্তন ? বেরো এখান থেকে।’ কাহ্নুপাদ অপমানের জ্বালা অন্তরে নিয়ে বের হয়ে পড়ে। দেবকীর মদের দোকানে ঢুকে আকণ্ঠ মদ পান করে। রঙ্গ-কৌতূকে এবং রমণীর দেহ ভোগে মনটা হালকা করতে চায়। তারপরও কিন্তু মনের আগুন নেভে না। শবরীর কাছে না গিয়ে সে যায় ‘মনের মানুষ’ ডোম্বীর কাছে। ডোম্বী সব শুনে রেগে ওঠেঃ ‘তুমি কি করলে ?/: কিছু করিনি।/ : কিছু করলে না? মাথা ফাটিয়ে দিতে পারলে না ?/ : তাহলে কি আমাকে আস্ত রাখতো ?/: না রাখলে মরতে। আমরা সবাই জানতাম তুমি মুখের ভাষার জন্যে মরেছ। কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যদি আসবে তবে গেলে কেন ওখানে?’ এখানে বায়াান্নর ভাষা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে গাঠকের। লেখকের বাস্তব সমাজের স্বকালীন চিত্র এটি। ডোম্বী যেনো ভাষা-আন্দোলনের অগ্নি-প্রেরণা। কবি কাহ্নুপাদ জাতীয় জাগরণের বীর, জাতির নয়নমণি স্বপ্নদ্রষ্টা কবি-রত্ন। ডোম্বী বলছে : ‘মরলে কি হয় কানু ? যাকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাস তার জন্যে মরতে পারো না ? কাহ্নুপাদের বুকের গভীর থেকে উঠে আসে প্রতিজ্ঞার ধ্বনি। পারি, আমি পারি মল্লারী। এই চেতনা অত:পর মূলত স্বাধীনতার চেতনা। এই চেতনাকে উপজীব্য করে চলে অন্ত্যজ শ্রেণীর অস্পৃশ্য মানুষদের মুখের ভাষার অধিকার আদায়ের প্রতিরোধ এবং সংগ্রাম। বাধা যদি আসে, প্রতিহত করতে হবে। সংগ্রাম করার জন্য তৈরি হতে থাকে সকলে। ব্রাহ্মণেরা যদি কাহ্নুদের সে অধিকার না দেয় তবে নীচ শ্রেণীর লোকেদের নিয়েই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করবে তারা। নিজেদের সার্বভৌম ভূখন্ডে স্বাধীনভাবে তারা মুখের ভাষার চর্চা করবে; নাটক প্রবন্ধ ও সংস্কৃতির চর্চা করবে।
গ্রন্থের বাহাত্তর থেকে শেষ একশ আশি পৃষ্ঠায় ঘটনাপ্রবাহ উত্তরিত হয়েছে এই চেতনাকে কার্যকর করার লক্ষ্যেই। শেষ পর্যন্ত কাহ্নুপাদ সাহসী এবং দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছে সেকথাই। কিন্তু তার আগে ডোম্বীকে প্রাণ দিতে হয়েছে রাজার আইনে। রাজশক্তি কাহ্নুকে পঙ্গু করে দিয়েছে দু’হাত কেটে।
তিন
দেশাখ এ-গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে বিশাখাকে ভালোবাসে। দেশাখ প্রেমিক মুক্তিকামী সন্ত্রাসবাদী বীর-যোদ্ধা, ভবিষ্যত সংগ্রামের জন্য সে দল গঠন করেছে। তৎপরতা চালায় গোপনে-গোপনে। নারী শিশু সকলকে সে তীঁর চালনা শিক্ষা দেয়। বিশাখা কিশোরী প্রেমিকা। দেশের জন্য তারও দরদ রয়েছে। স্বত:স্ফূর্তভাবে সংগ্রামের মধ্যে সে দেশাখকে মেনে নিয়েছে। শ্রেণীভেদের আগুন তীব্র হলে তা থেকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে দেশাখ কাহ্নুপাদকে বলে : ‘কানুদা এসো তাহলে আমরা ছোট লোকেরা আলাদা হয়ে যাই। আমাদের ভেতর থেকে একজনকে রাজা বানাই, একজনকে মন্ত্রী বানাই, তারাই আমাদের কথা ভাববে আমাদের উপকার করবে।’
ডোম্বী আগাগোড়া প্রতিবাদে এবং প্রতিশোধ-কামনায় স্থির অচঞ্চল। ডোম্বী দেবলভদ্রের এক ভাগ্নেকে হত্যা করেছে জোর করে তার দেহোপভোগের এক উত্তেজনাময় মুহূর্তে। সেই অপরাধে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো। বন্দী হবার আগে সে দেশাখকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে : তাকে কেউ ভুলে যাবে না তো ? দেশ ও জাতির জন্য যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেল অকাতরে, তাকে ভুলে যেয়োনা তোমরা। দেশাখ স্বীকার করে, তার সোনার মূর্তি বানিয়ে রাখবে তারা। একালের শহীদ মিনার ও ভাস্কর্য-চেতনার কথা এখানে স্মরণ হয়। শহীদদের ভুলে যাবার, ডোম্বীকে ভুলে যাবার বা ভুল বোঝবার প্রতি কটাক্ষ হানা হয়েছে এখানে। ডোম্বী উগ্র-স্বভাব রমণী, বেপরোয়া। কাহ্নুপাদ নির্বিবাদে কারাবরণ করেছে বলে তার ক্ষোভের অন্ত নেই। কাহ্নুকে তারা হাত কেটে ছেড়ে দেয়। কিছুদিন পর রাজার লোকেরা তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়। মানুষজন মারা যায় অসংখ্য। যেমন বাঙলাদেশে ২৫ মার্চ কালোরাত্রিতে (১৯৭১) ঘটেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা, ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালের সমস্যা সব একীভূত হয়েছে এখানে।
সুলেখা এবং ভুসুকু গ্রন্থে ব্যবহাত ‘অপণাঁ মাংসে হরিণা বৈরী’ প্রবাদের সার্থকতা সূচক দুটি চরিত্র। ভুসুকু কবি। সে-ই উক্ত কবিতার রচয়িতা। কাব্য প্রেরণায় একদিন সে যা উচ্চারণ করেছিল। তা-ই ভুসুকুর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাণিজ্য থেকে এসে সে দেখে সত্যিই জীবনোপভোগের কামনায় স্ত্রী সুলেখা অন্যত্র ঘর বেঁধেছে।
আর সুলেখা চরিত্রকে ঔপন্যাসিক চর্যাপদের প্রণয়িনী গৃহবধূর মনন-বৈশিষ্ট্যে আঁকার প্রয়াস পেয়েছেন। চর্যার আমলের সামাজিকতায় গৃহস্থবধূর অপরের সঙ্গে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ গ্রন্থেও এই তথ্যের প্রতিফলন রয়েছে। স্বামী নয় এমন পুরুষের সঙ্গে সুলেখা প্রণয়-কল্পনায় ঘর ত্যাগ করেছে। অথচ দিনের বেলা বধূ কাকের ডাকেও ভয় পায়। বিচ্ছেদে স্বামীর প্রতি তার আকর্ষণ মলিন হয়ে গেছে। সেকালে যেতো একালেও যায়। স্বামী থেকে দূরে একাকী জীবনে স্বৈরাচারী যৌন-চেতনা নীতিবোধকে ক্ষুণ্ন করে থাকে। আজকের সমাজের প্রেক্ষিতেও এ বক্তব্য কৃত্রিম নয়। কেবলমাত্র শবরী চরিত্রটি এখানে অকলঙ্কিত। কাহ্নু তাকে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছিল। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী শবরীকে রেখে কানু আবার অন্য নানা নারীর সাথে প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করে- যার অধিকাংশ পরিণতিই সফল দৈহিক-প্রণয়ে। কিন্তু এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শবরীর বিরূপ মনের প্রতিচ্ছবি উপন্যাসে অঙ্কন করা হয়নি।
তাছাড়া গুণী এবং লোকীকে কেন্দ্র করে লেখক নবোদ্ভীন্না কিশোরী মেয়েদের যৌনজীবনের ভাবনা-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। মহাভারত-রামায়ণের প্রভাবে তিনি সমাজে কুসংস্কারের দুটি চিত্র তুলে ধরেছেন ধনশ্রী এবং অরণীর জীবনে স্ত্রী-বিয়োগের সূত্র ধরে। লোকমুখে স্ত্রীর কলঙ্কের কথা শুনেই স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে অরণী। অথচ সে জানে তার স্ত্রী ‘নির্দোষ’। আবার অন্য ধরনের কুসংস্কারও আছে। সমাজব্যবস্থাই কুসংস্কারের জন্ম দেয়, কারণ অশিক্ষা। কোন রমণীর গর্ভে একসঙ্গে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করলে দুই পুরুষের স্ত্রী-দোষে কলঙ্কিত বলে তাকে ছাড়তে বাধ্য করায় রাজা তার রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা। সমাজের এই অবক্ষয়ের মধ্যেও রমণীরা তাদের পেটে ‘বীর-সন্তান’ ধারণ করতে চায়। একারণে সজারুর মাংস তারা ভক্ষণ করে। সন্তান ভীরু হবার আশঙ্কা মায়েদের সারাক্ষণ তাড়িত করে। তবে বলা আবশ্যক, সমাজে অনাচার বা যথেচ্ছ যৌনাচার থাকলেও প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা সেকালেও ছিল। ভৈরবী চাল ডাল বাকী কিনতে যায় কামোদের দোকানে। কামোদ সুযোগ পেলেই নিজের কামনা-বাসনার কথা ভৈরবীকে বলে। কিন্তু ভৈরবী সেসব কথা শুনেও শোনে না। কামোদ এবং ভৈরবী ছোট বেলায় কত উজ্জ্বল মুহূর্ত একসঙ্গে কাটিয়েছে। ওকে ছাড়া কামোদের এক মুহূতর্ও কাটতো না। কিন্তু সেই সব স্মৃতিকে এখন ভৈরবী ভয় পায়। কখনোই স্মৃতির বাক্স মেলে ধরে না। ধনশ্রী ওকে ভীষণ ভালোবাসে এবং বিশ্বাস করে। ধনশ্রী স্ত্রীকে ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারেনা। কোনদিন স্ত্রীকে অবহেলা করেনি। সেজন্যেই ধনশ্রীর গন্ডীর বাইরে যেতে পারে না ভৈরবী। মনটা এদিক-ওদিক করলেও সে স্বামীর কথা মনে করে তা ভুলে যেতে চায়। অর্থাভাবে ভালোবাসা বেচে বেড়াতে হয়, ভালোবাসার অভিনয় করতে হয়, অর্থ-সংকটে অনেক কিছুই বিসর্জিত হয়। ডোম্বী কড়ির জন্যে ঘরে লোক ঢোকায়। কিন্তু কাহ্নুপাদকে সে অকপটে সে কথা বলতে পারে না।- ‘তুমি রাগ করোনা কানু, বামুনগুলোকে সারাদিন ঢুকতে দেই না। যেদিন কড়ি থাকে না, উপোস করতে হয়, সেদিনই কেবল দেই।’ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কাহ্নু উচ্চারণ করে : ‘আমার যদি অনেক কড়ি থাকতো মল্লারী ? /তাহলে বুঝি পথে পথে ছিটিয়ে বেড়াতে ?/না পথে নয়। ভালোবাসা বাঁচাতাম।’ এরকম অবস্থাও এ-কালে দেখা যায় হরহামেশাই। অর্থ নীতিকে গ্রাস করে।
কাহ্নু চরিত্রের বিকাশের সাথে সাথে এ-গ্রন্থের পরিসমাপ্তি এবং দেশাখ ও সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ গড়ার প্রেরণা ছড়িয়ে কাহ্নু চরিত্রের সার্থকতা। রাজ দরবারের চাকুরী কাহ্নুপাদ ছেড়ে দিয়েছিল। পরদিন থেকে শুরু হয় তার জীবনের বাঁক বদলের সূচনা। কাহ্নু বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান গায়। কিন্তু চাকুরী রাজা তাকে ছাড়তে দেবে না। মন্ত্রী ব্যঙ্গ করে বলেছিল এসব কথা। তারপর হুঙ্কার ছেড়ে হুকুম জারি করে যায়। কাহ্নু অবশ্য মন্ত্রীর হুকুম আহকাম পরোয়া না-করেই চাকুরি ছেড়েছিল। কিন্তু রাজার লোকেরা তাকে রেহাই না দিয়ে বন্দী করে নিয়ে চলে যায় এবং শাস্তি দেয় অমানুষিক। দেবলভদ্র অবশ্য কাহ্নুকে এক শর্তে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। কাহ্নু যদি মুক্তি পাবার পর রাজার প্রশস্তি লিখতে রাজী থাকে তবে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। বুদ্ধিজীবী এবং লেখক কেনা-বেচার সাম্প্রতিক কালের নমুনার সাথে এর অসঙ্গতি নেই। কিন্তু সকল কবি এবং সকল মানুষই নিজেকে বিকিয়ে দিতে রাজী থাকলেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাঁরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে রাজী থাকেন, কিন্তু আপোস করেন না কখনও স্বজাতি এবং স্বধর্মের বিরুদ্ধ-শক্তির সাথে।
দেশাখ তার প্রেমিকা বিশাখাকে সুযোগ পেলেই বলে : ধরো এই বনটা আমাদের রাজ্য। গাছপালা গশুপক্ষী সব প্রজা । তুমি আমার রানী আর আমি রাজা। এটি একটি প্রেমিকের স্বপ্ন-কামনা প্রেম-লীলার মুহূর্তে। কিন্তু সুচিন্তিত এবং স্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যায় কাহ্নুপাদের কণ্ঠেই। কাহ্নুপাদ জেল প্রত্যাগত হবার পর তার শরীরের করুণ পরিণতি দেখে সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লে কাহ্নু বলেছিল : ‘তোরা কেউ দুঃখ করিস না দেশাখ। আমাদের তেমন একটা জায়গা একদিন হবে। আমরাই রাজা হবো। রাজা প্রজা সমান হবে। আমাদের ভাষা রাজ-দরবারের ভাষা হবে। তেমন দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে দেশীখ।’ একথায় সকলের মুখে স্বস্তি ফুটে ওঠে। দম নিয়ে আবার কাহ্নুপাদ বলে : ‘একটা ছোট্ট ভূখন্ড আমাদের দরকার। সে ভূখন্ড-টুকু সবুজ শ্যামল আর পলিমাটি ভরা হলেই হয়। দক্ষিণে থাকবে একটা সুন্দর বিরাট বন, আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে সাগর।’ কাহ্নুপাদ থামতেই দেশাখ চেঁচিয়ে ওঠে, আহ্ কানুদা কেমন করে যে মনের কথা বলো! তুমি না থাকলে আমরা স্বপ্ন দেখতেই পারিনা। তখুনি চামড়া পোড়া গন্ধটা বাতাসের প্রবল ঝাপটায় ওদের সবার নাকে মুখে গলগলিয়ে ঢোকে। সে গন্ধ প্রাণ ভরে বুকে টেনে হো হো করে হেসে ওঠে ভুসুকু, ‘কাহ্নিলারে আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলি।’
উপসংহার
ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক বাঙলাদেশ, রাষ্ট্রভাষা যে দেশের বাঙলা, সেই স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী পটভূমিতে যে সচেতনতা গড়ে উঠেছিল দেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতির প্রেক্ষাপটে, সেলিনা হোসেন তারই ছবি আঁকতে চেয়েছেন দেড় হাজার বছর আগের পটভূমিতে। অথবা বলা চলে এই চেতনাই হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালিরা কামনা করে আসছিল, পথ খুঁড়ে আসছিল সে উদ্দেশেই। উপন্যাসে চরিত্র নির্মাণকলায় কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে। কাহ্নুপাদ ‘ভালোবাসা’কে বাঁচাবার কথা বলেছিল। সেই কাহ্নুপাদকে প্রেমের প্রতি নিষ্ঠাহীন চরিত্রে রূপান্তরিত করা সঙ্গত হয়নি। একটি চরিত্রকে আদর্শ রূপ দেবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লেখিক তা গ্রহণ করতে পারেননি। এ-গ্রন্থে যে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি তৈরি হয়েছিল, একটা চরিত্রও মহৎ না থাকার কারণে তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আর যদি সর্বত্রই তিনি সেকালের মানুষের বিশেষ জৈবিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেই সচেষ্ট হয়ে থাকেন, তবে অন্যত্র চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর স্বাধীনতা গ্রহণ করা সঙ্গত হয়নি। জৈবিক ক্রিয়াাকর্মের ছবি আঁকায় আবেগের তীব্রতা আছে, অথচ মহৎ চরিত্র আঁকার আকাঙ্ক্ষা নেই-এটা লেখকের শিল্পদৃষ্টির পরিশীলনের অভাব প্রমাণ করে। কাহ্নুপাদের চরিত্রের একটি ত্রুটি তার রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদহীন কারাবরণ। কাহ্নুর তুলনায় ডোম্বী অনেকটাই এক-রৈখিক এবং বিদ্রোহিনী-রমণী। কাহ্নুপাদের চরিত্রের এবং কার্যকলাপের স্ববিরোধী ভূমিকাও চরিত্রটিকে কিছুটা নিষ্প্রভ করেছে। বারবারই সে কর্মপথ বিচ্যুত, নীতি-বিবর্জিত ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত। শবরী তার সুন্দরী স্ত্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডোম্বী ও অন্য নারীর প্রতি তার দেহলিপ্সা তাকে মহত্ত্ব থেকে স্খলিত করেছে।
সেলিনা হোসেনের ভাষা সহজ ও সরল। বিদগ্ধ পাঠককে অধিকক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখার মতো শৈল্পিক-বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষায় ও রচনারীতিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে এবং ঘটনা-সংস্থানেও একই রকম সরলতার পরিচয় বিধৃত। এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশী উপন্যাস-সাহিত্যে ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের গুটিকতক উপন্যাসের একটি হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।