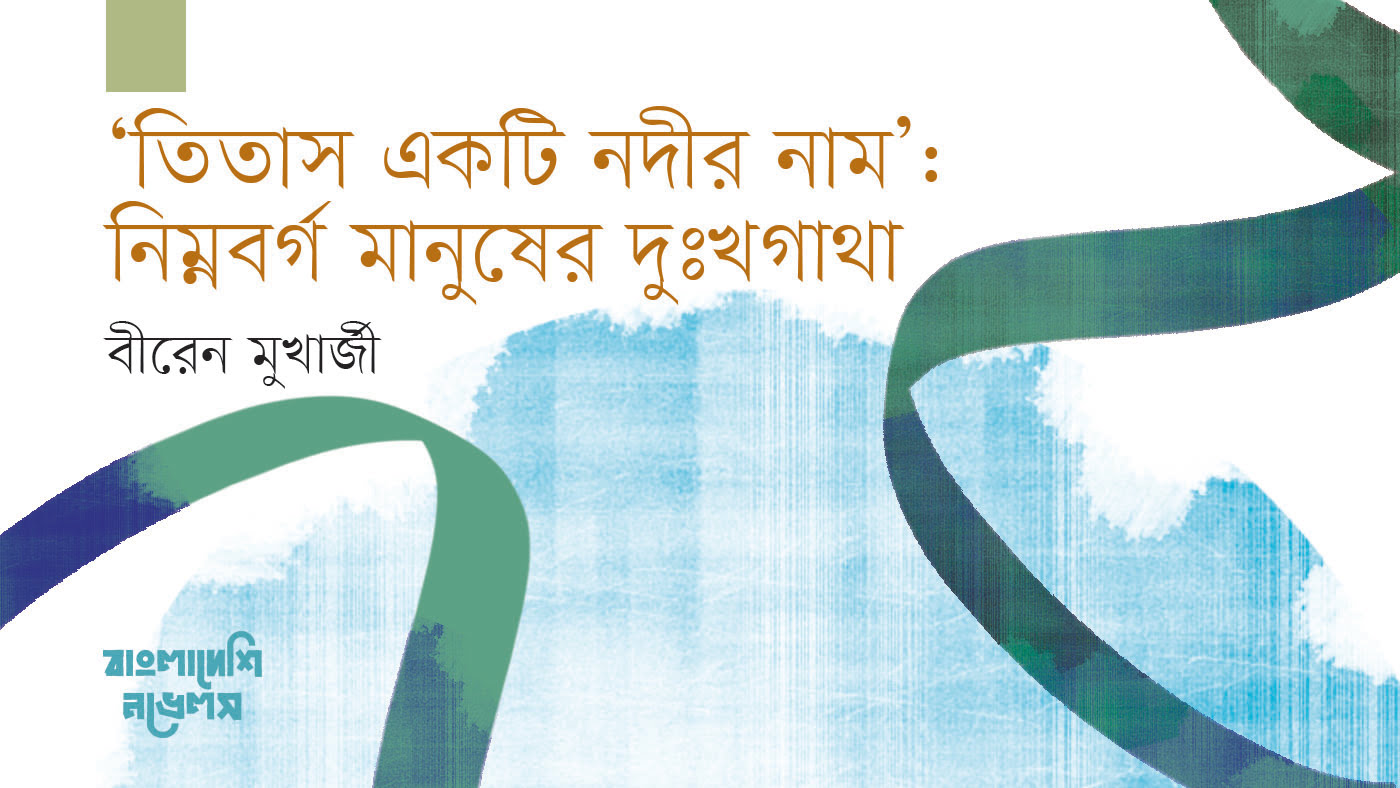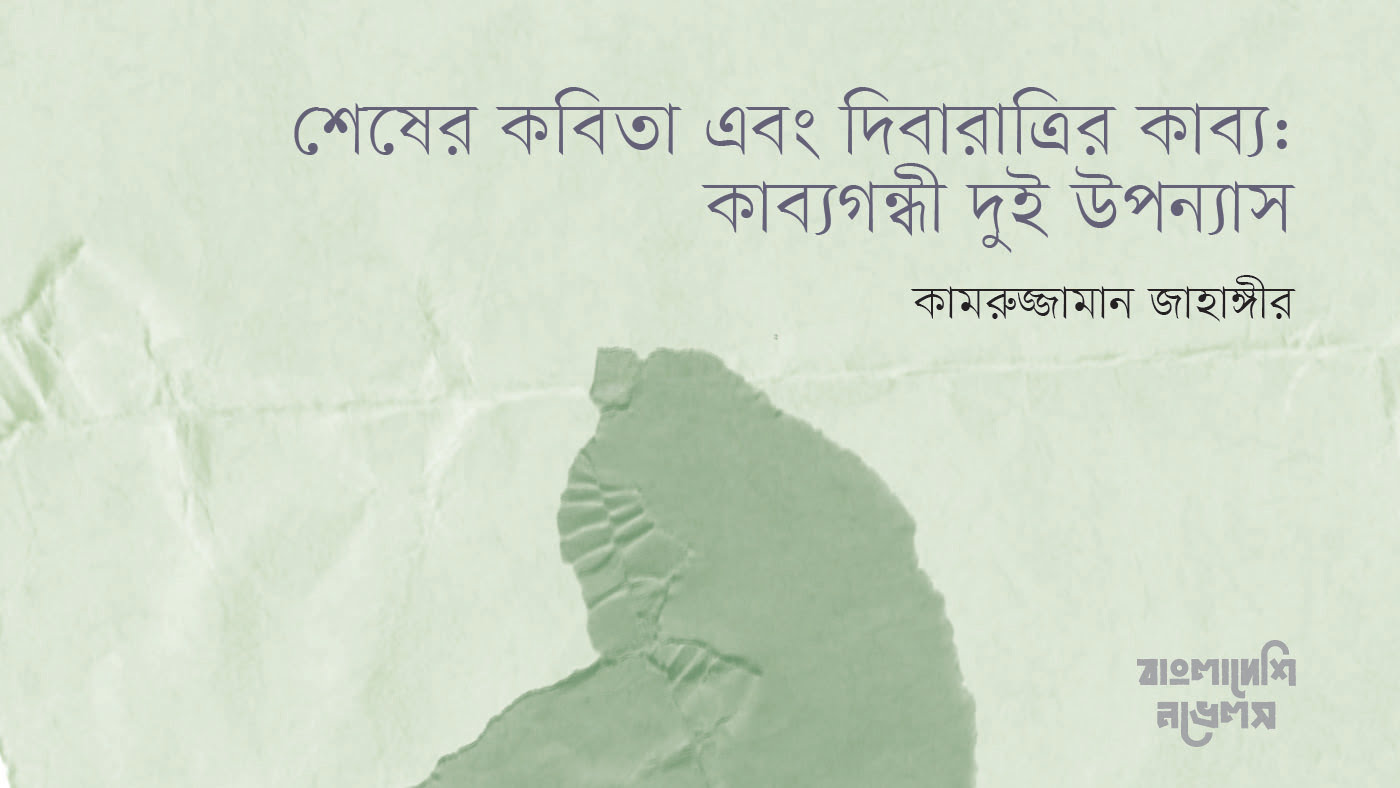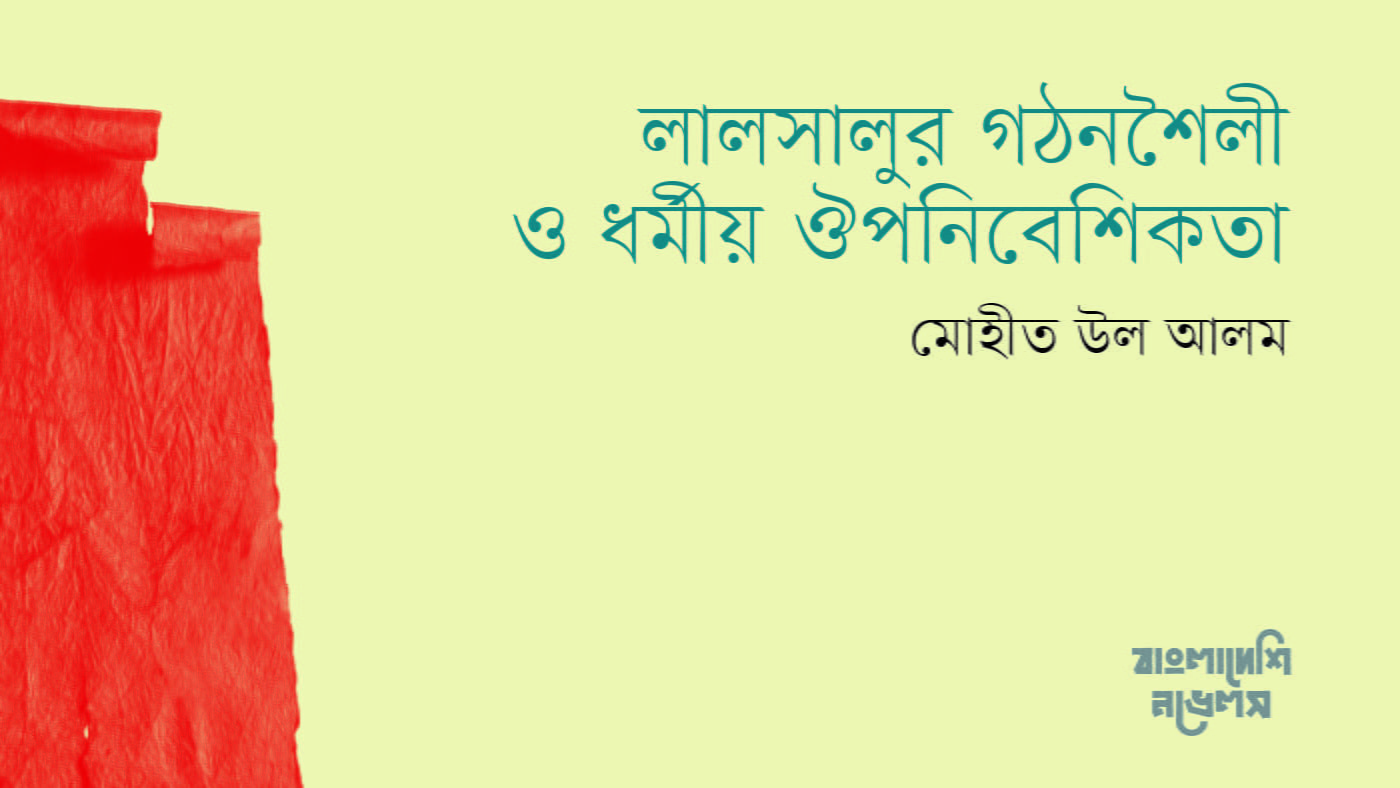ল্যান্সডাউন রোডের ফুটপাতের দোকান মালিককে জিজ্ঞাসা করি- ‘এটা কি ১৮৩ নম্বর বাড়ি?’ বলেন- ‘হ্যাঁ’। কাউকে খুঁজছেন? ‘আমি বলি- ‘না ঠিক কাউকে খুঁজছি না। এমনি বাড়িটা দেখতে এসেছি।’ দোকান মালিক মুহূর্তে যেন রহস্য বুঝে যান। ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে বলেন- ‘ও বুঝতে পেরেছি দাদা। অনেকেই দেখতে আসেন। এখানে কবি জীবনানন্দ দাশ থাকতেন একসময়। অনেক বড় কবি ছিলেন। শুনেছি নোবেল প্রাইজ পাবার কথা ছিলো, ষড়যন্ত্র করে দেয়া হয়নি।’ তিনি তার ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আরো খানিকটা বিষদ করবার পর জীবনানন্দ এ বাড়ির নীচতলার যে অংশে থাকতেন সেটা দেখালেন। সরু নির্জন গলি দিয়ে সেখানে গিয়ে সবুজ রঙের কাঠের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াই। দরজার মরচে পড়া লোহার কড়াটি স্পর্শ করি। অনেক রাতে কলকাতার ফুটপাত থেকে ফুটপাতে হেঁটে, আদিম সাপের মত ছড়িয়ে থাকা ট্রাম লাইন মাড়িয়ে জীবনানন্দ ফিরতেন এই বাড়িতে। এসে হাত রাখতেন এই কড়ায়। কাকে ডাকতেন তিনি? সম্ভবত স্ত্রী লাবন্যকে নয়, হয়তো নীচু গলায় ডাকতেন মেয়ে মঞ্জুকে। ল্যান্স ডাউন রোড থেকে যাই কাছের শম্ভুনাথ হাসপাতালে। সেখানকার ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে গিয়ে উঁকি দেই। ভেতরে একজন রক্তাক্ত রোগী গোঙাচ্ছে। তাকে ঘিরে কয়েকজন ডাক্তার, নার্স। এক নার্স এসে আমাকে বলেন, রোগী কি আপনার? বলি – না। সরে আসি সেখান থেকে। হাসপাতালের করিডোরে হাঁটি। ভাবি নার্সকে বলতে পারতাম, আমার এমন রক্তাক্ত রোগী একজন ছিলেন এখানে, ঐ ইমার্জেন্সি বেডেই ষাট বছর আগে। ট্রামের ধাক্কায় আহত হবার পর জীবনানন্দ দাশকে এই হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছিলো, এখানেই মৃত্যুবরন করেছেন তিনি। আমি হাসপাতালের করিডোরে হাঁটি আর যেন দেখতে পাই সেখানে ছোটাছুটি করেছেন জীবনানন্দের পান্ডুলিপি উদ্ধারকরী ভুমেন্দ্র গুহ, ফলের ঝুড়ি নিয়ে বেঞ্চে নিঝুম বসে আছেন তার বোন সুচরিতা।
জীবনাননন্দ দাশের জীবনকে ভিত্তি করে ‘একজন কমলালেবু’ নামের বইটি লেখার এক পর্যায়ে গিয়েছিলাম কলকাতায় তার স্পর্শ লাগা জায়গাগুলো দেখতে, গিয়েছিলাম বরিশালেও যেখানে কেটেছে তার জীবনের সিংহভাগ। জীবনানন্দ দাশ আমার উপর ভর করেছেন কৈশোরেই। আমি তখন আধা সামরিক বিদ্যালয় মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। খাকি পড়ে প্যারেড করি, পিটি করি। কিন্তু মন ভেসে বেড়ায় কঠোর নিয়ম ঘেরা খাকি চত্বরের বাইরে। মায়াকোভস্কির কথা ধার করে নিজেকে তখন মনে হয় খাকি পড়া মেঘ। পড়ার জন্য নির্ধারিত প্রেপ টাইমে কেমিস্ট্রি বইয়ের নীচে লুকিয়ে পড়ি কবিতার বই। আমাদের সেই খাকি চত্বরে এক নতুন বাংলা শিক্ষক ক্লাসে এসে আমাদের সিলেবাসে না থাকা সত্ত্বেও একদিন আবৃত্তি করে শোনালেন জীবনানন্দের ‘আট বছর আগে একদিন’ কবিতাটি। কবিতাটির অর্থ সেইসময় বোধগম্য না হলেও আমাদের সেই শিক্ষক রফিক কায়সারের আবৃত্তি শুনে একধরনের ঘোর লাগে। পরদিন মার্চপাস্ট করি আর আমার মাথার ভেতর ঘোরে সেই পংক্তি- ‘চমৎকার! ধরা যাক দু একটি ইঁদুর এবার।’ এরপর জীবনানন্দের ঐন্দ্রজালিক কবিতাগুলো আমার সঙ্গী হয়ে ওঠে এবং আমাকে ছেলে ধরার মতো বস্তাবন্দী করে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যায় ঐ আধা সামরিক চত্বরের বাইরে। কবিতা না লিখলেও কবিতার পাঠক আমি বরবার এবং জীবনানন্দ আমাকে দখল করে রেখেছেন আকৈশোর। যখন গল্প লিখতে শুরু করি লক্ষ্য করি জীবনানন্দের আবহ, ভাষা ব্যবহার চোরাগোপ্তাভাবে আমার গদ্যকেও প্রভাবিত করছে। আমার ‘কয়েকটি বিহবল গল্প’ বইয়ের কিছু গল্প কবিতা হিসেবেও আবৃত্তি করা হয়েছে মঞ্চে। জীবনানন্দ আমাকে বিশেষভাবে আক্রান্ত করেন যখন আমি তার কথাসাহিত্যিক পরিচয়টি পাই। জীবনানন্দের জীবৎকালে অপ্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, ডায়েরীর সাথে পরিচিত হয়ে মনে হয় যেন তুতেনখামেনের গুপ্তধনের মুখোমুখি হয়েছি। তার গদ্যও আমাকে দখল করে ভীষণভাবে। ‘মারাত্মক নিরুপম আনন্দ’ নামে আমার একটি গল্প আছে, ‘পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ’ নামে আছে একটি গল্পগ্রন্থ, এ দুটোই জীবনানন্দের গদ্যেরই লাইন। আমার আরেকটি গল্পগ্রন্থ ‘অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প’ জীবনানন্দের একটি গল্পকে কেন্দ্র করেই। আমি ক্রমশ টের পাই জীবনানন্দ আমার উপর যেন খানিকটা সিন্দাবাদের মতো ভর করেছেন। আমি এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেই জীবনানন্দের এই ভারমুক্ত হবার জন্য তাকে নিয়েই পুর্নাঙ্গ একটি বই লিখব। এরপর তার যাবতীয় লেখাপত্রের ভেতর ডুব দেই। জীবনানন্দ যা লিখেছেন তার সামান্য মাত্র প্রকাশ করেছেন বাকী তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন কালো ট্রাঙ্কে। মৃত্যুর পর সেই গোপন ট্রাঙ্ক থেকে বেরিয়েছে প্রায় আড়াই হাজার কবিতা, গোটা বিশেক উপন্যাস, শ দেড়েক গল্প, চার হাজার পৃষ্ঠার ডায়েরী, অসংখ্য চিঠিপত্র। এছাড়াও রয়েছে তার অগনিত প্রবন্ধ। এক এক করে খুঁটিয়ে পড়ি সেসব। পড়ি তাকে নিয়ে লেখা বহু মানুষের স্মৃতিচারন, আলোচনা, বিশ্লেষণ। ঘুরে আসি তার যাপিত জীবনের জায়গাগুলো। তাকে নতুন করে আবিষ্কার করি। আবিষ্কার করি তিনি শুধু অনন্যসাধারণ শব্দশিল্পী নন, এক এনসাইক্লেপেডিক ভাবুক, গভীর অ্যাথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষক। তিনি কাকের বাসা থেকে শ্যাওলার উপর খসে পড়া ডিম যেমন লক্ষ্য করেন, তেমনি গভীর জ্ঞান রাখেন নিলস বোরের কোয়ান্টাম থিয়োরীরও। দেখি তিনি বিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে অতি দূর ইতিহাস আর অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে টের পেয়ে গেছেন আধুনিকতা আর বিশ্বায়নের ঘোর পরিণতির ঘ্রান। জীবন, জীবিকা, দাম্পত্য, স্বপ্ন, বাস্তবতার ঘূর্ণিঝড়ে ডানা ঝাঁপটিয়েছেন একটি আহত পাখির মতো। সাহিত্যের হাঙর ভরা সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে প্রবল আত্মবিশ্বাসে যাদুকরের মতো দেখিয়ে গেছেন ভাষা আর ভাবনার মায়াবী খেলা।
লক্ষ্য করি জীবনের নানা বাঁকে নতুন, নতুন ভাবনা মোমের মতো জ্বলে উঠেছে জীবনানন্দের মনে, সেই ভাবনা তিনি সমান্তরালে নাড়াচাড়া করেছেন তার কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, ডায়রীতে, চিঠিতে, প্রবন্ধে। ‘একজন কমলালেবু’ বইটিতে আমি এই প্রহেলিকাময় মানুষ জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের সমান্তরালে তার নানা ধারার এই লেখাগুলোকে কোলাজের মতো স্থাপন করে অনুসন্ধান করেছি তার হৃদয়ের সেই পথচলাকে। জীবনানন্দকে ঘিরে আমার এই ব্যক্তিগত অভিযাত্রা শুরু করেছি এই জিজ্ঞসার উত্তর খুঁজতে যে ট্রামের আঘাতে তার এই মৃত্যু কি কোন দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি একটা হত্যাকাণ্ড? কমলালেবুর সঙ্গে জীবনানন্দের সম্পর্ক জীবনানন্দের গভীর পাঠক আঁচ করতে পারবেন। জীবনানন্দকে নেহাতই কাব্যিক, নির্জন, প্রাকৃতিক ইত্যাদি অভিধায় বোঝার চেষ্টা আমাদের এক অভ্যাস। অথচ আমি টের পেয়েছি জীবনানন্দ জটিল, বহুমাত্রিক মানুষ। তার ভেতর আছে ডার্ক হিউমারও। তাকে নিয়ে বইয়ের নাম দিতে গিয়ে কিম্বা বইয়ের কাঠামো নির্মাণ করতে গিয়ে তাই খড়ির গণ্ডির বাইরে আসতে হয়েছে আমাকে। ‘একজন কমলালেবু’ বইটি জীবনী গ্রন্থ না উপন্যাস এটি আমার কাছে খুব জরুরী প্রশ্ন নয়। এটি আমার কাছে একটি সাহিত্যকর্ম যা ফিকশন এবং নন ফিকশনের মাঝামাঝি এক ধূসর এলাকায় দাঁড়ানো। আমার কাছে জরুরী আজকের সাহিত্য বাস্তবতায়, রাজনৈতিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে জীবনানন্দকে নিংড়ে বুঝে উঠবার আমার এই আকুতি। জীবনানন্দ বিষয়ে ইতিপূর্বে আরো বিস্তর লেখা হয়েছে, তাদের প্রতি ঋণ স্বীকার করেই ‘একজন কমলালেবু’তে আমি আমার নিজস্ব বয়ানে জীবনানন্দকে সার্বিকতায় উপস্থাপন করেছি। আমার আগের বিবিধ লেখাতেও গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, প্রবন্ধ, কবিতার উপাদান মিলিয়ে ফেলবার চেষ্টা আছে। সেইসব লেখাকে কখনো অভিহিত করা হয়েছে ডকু ফিকশন, মেটাফিকশন বা ক্রিয়েটিভ ননফিকশন অভিধায়। বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও সাহিত্যের সংজ্ঞাকে ক্রমশ বিস্তুৃত হতে দেখছি। নোবেল বিজয়ী বেলারুশের লেখিকা সলভিয়েনা আলেক্সেভিচের সাংবাদিকতার রিপোর্টগুলো যখন উপন্যাস হয়ে ওঠে, বব ডিলানের গানগুলো যখন বিবেচিত হয় কবিতা হিসেবে, মিলান কুন্ডেরা যখন উপন্যাসকে নিৎশের দর্শন আলোচনার পাটতন করেন, জুলিয়ান বার্নেস যখন ফ্লবেয়ারে সাহিত্য সমালোচনাকে উপন্যাস হিসেবে উপস্থিত করেন তখন আমি রস এবং জ্ঞান কাণ্ডের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে যেতে দেখি, অনুপ্রাণিত হই।
তবে কথা এই যে একটি বই প্রকাশিত হয়ে গেলে সেটি আর লেখকের অধিকারে থাকে না। পাঠক/পাঠিকা হয় তার সঙ্গে সংযোগ বোধ করেন নয়তো করেন না। লেখকের তখন আর কোন ঢাল নেই। লেখক হিসেবে আমার অর্জন শুধু এই যে এই বইটি লিখতে গিয়ে জীবনাননন্দের মতো এক আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে অভূতপূর্ব একটা সময় কেটেছে আমার। টের পেয়েছি আজকের পৃথিবীতে কি দুর্দান্তভাবে প্রাসঙ্গিক তিনি, জেনেছি লেখক হিসেবে নতজানু হয়ে কত কিছু শেখার আছে তার কাছে। ফরাসী লেখক গুস্তাফ ফ্লবেয়ার তার বন্ধু আর্নেষ্ট ফেদিউকে বলেছিলেন, তুমি যদি কখনো আমাকে নিয়ে কোন বই লেখ তাহলে এমনভাবে লিখবে যেন তুমি আমার হয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছ। প্রতিশোধ? কার বিরুদ্ধে? জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লিখতে গিয়ে যেন একটু একটু করে বুঝতে পেরেছি ফ্লবেয়ার আসলে কী বলতে চেয়েছিলেন।