
জটিলতার ভাষারীতির লেখক কমলকুমার মজুমদারের ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যেমন সর্বাগ্রে বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষা-পরিক্রমাটির উপর আলোকপাত প্রয়োজন তেমনি প্রচলিত ভাষারীতি থেকে কোন্ কোন্ কথাসাহিত্যিক কীভাবে ‘না-প্রচলিত’ ভাষার অনুসন্ধান করেছেন সে সম্পর্কে জানাটাও প্রাসঙ্গিক। বাংলা কথাসাহিত্য রচনায় না-প্রচলিত ভাষা তৈরি এবং তা ব্যবহারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পীদ্বয় হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও সেই সাথে একথাও উল্লেখ করে রাখা দরকার ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরই বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মত কমলকুমারও যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি সুষম, নিজস্ব ভাষা গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ভাষা-নির্মাণে যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন সেটি পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছিল বলেই তারা অপঠিত থাকেননি কমলকুমারের মত। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে প্রথম ছটি গল্পের পর্যায়টির পরই কমলকুমার ভাষা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এবং আমৃত্যু তাঁর মধ্যে এই ক্রিয়ার ব্যাপারটি বর্তমান ছিল। ভাষা-নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্রমবিবর্তনের ভাবনা থেকে তিনি কখনই পশ্চাদপদ হননি। এবং বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বিষবৃক্ষ রচনার সময় থেকে তাঁর নিজস্ব ভাষারীতিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন বা রবীন্দ্রনাথ যেমন ঘরে-বাইরে উপন্যাসে এসে চলিত গদ্যরীতির সুষম একটি রূপে পৌঁছান, কমলকুমার তেমনি সুহাসিনীর পমেটম-এ তাঁর নিজস্ব একটি ভাষারীতি গঠনে পূর্ণতা অর্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উদ্ভাবিত স্ব-স্ব ভাষায় পাঠকের সহজবোধ্যতায় সাহিত্যকে উপস্থাপন করেছিলেন; কিন্তু কমলকুমার ক্ষেত্রে সেটি হয়ে বিপরীতে – স্ব-উদ্ভাবিত স্বাভাবিক বোধ্যতার সীমা অতিক্রম করায় কমলকুমার হয়ে পড়েন বাংলা সাহিত্যের দূরাগত এক অতিথি – যাঁর স্থান স্পর্শযোগ্যতার বাইরে।
যে কোন মহৎ সাহিত্যকই ভাষা নিয়ে নিরীক্ষা চালিয়ে থাকেন – সমাজ ও সময় সদাপরিবর্তনশীল বলেই নিরীক্ষার তাঁর জন্যে অত্যাবশ্যকও হয়ে দাড়ায়। প্রার্থিত বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থিত করার জন্যে শুধু কথাসাহিত্যেই নয় সাহিত্যের যে কোন শাখাতেই এ প্রয়োজনের উপলব্ধি স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের ভাষীরীতির অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছিলেন তাঁর সাহিত্যরচনা এবং অধিকতর উপযোগী একটি ভাষা-প্রয়োজন উপলব্ধি করেই এক পর্যায়ে যে ভাষাতে তাঁর নিজস্বতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী ভাষা দিয়ে কথাসাহিত্য রচনা শুরু করলেও সে ভাষাকে যথেষ্ট উপযোগী বিবেচনা না করার কারণেই উদ্যোগী হন কথাসাহিত্যের অধিকতর উপযোগী একটি ভাষা নির্মাণ করায়। ত্রিশোত্তর কথাসাহিত্যিকরা সে ভাষায় যথেষ্ট গ্রহণ বর্জন করেছেন, পরিমার্জনা করেছেন ঠিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষারূপ থেকে বৈপ্লবিক কোন উত্তর তাঁরা ঘটাতে পারেন নি। এঁদের পর থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে ভাষার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হলেও ঐ ভাষাভঙ্গির মূলরূপটি রয়ে গেছে অক্ষুণ্ন। কেউ কেউ আঞ্চলিক ভাষাকে ডায়ালগে এনেছেন, পরবর্তীকালে কেউ কেউ সেটি মূল বর্ণনাতেও নিয়ে আসেন। শব্দ ব্যবহারে কেউ কেউ দেখিয়েছিলেন বিশেষত্ব, কারও কারও রচনায় আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে নিঃসঙ্কোচে। একাধিক ক্রিয়া, বিশেষণ ইত্যাদি পদকে পাশাপাশি ব্যবহার করে কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন নতুন আবহ সৃষ্টির। আবার কয়েকজন সাহিত্যিক বাক্যকে দীর্ঘ, হ্রস্ব ইত্যাদি করে নতুন মাত্রা সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এসব কিছুকেও ছাপিয়ে কমলকুমারের কৃতিত্বটি উজ্জ্বল – কমলকুমার ভাষার মূল রীতিটিকে ভেঙে ফেলে তৈরি করতে পেরেছিলেন একটি নতুনতর ভাষাভঙ্গী যা বাঙালির কাছে সম্পূর্ণতই অপরিচিত, যা বাংলা সাহিত্যের পাঠকের স্বাভাবিক পরিচিতির বাইরে।
ভাষা নিয়ে ভাঙাগড়ার এই যে খেলার মূল লক্ষ্য কিন্তু সবসময়ই এক – লেখকের ভাবনাকে যথার্থভাবে আরও বেশি অনুভবযোগ্য করে পাঠকের কাছে তুলে ধরা, লেখকের আপন সত্তায় অনুভূত ভাবনাটি অধিকতর স্পর্শযোগ্য করে পাঠককে উপহার দেয়া।
দুই
বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) প্রকাশ বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ্য এক মাইলফলক; বাংলা সাহিত্য রচনা এরও অল্প কিছু আগে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষাতে শুরু হলেও পরবর্তীকালে পণ্ডিতজনেরা সবাই মেনে নিয়েছেন আলালী ভাষা বাংলা কথাসাহিত্যের উপযোগী কোন সাহিত্য-ভাষা ছিল না; এটি ছিল নিছকই ভাব আদান-প্রদানের ভাষা মাত্র। আলালী সে ভাষারীতিটি স্থায়ীত্ব লাভ করলে কেমন হ’ত বর্তমান প্রসঙ্গে সে বিতর্কের অবকাশ নেই। সামগ্রিকভাবে বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষা-পরিক্রমায় প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তদনুসারে রবীন্দ্রনাথের যে অগ্রসরণ এবং সে পথকে অবলম্বন করে বাংলা কথাসাহিত্যের বতমানকাল পর্যন্ত যে একশ’ ত্রিশ বছরের ইতিহাস স্বভাবতই আমাদের আলোচনার পটভূমি সেইখানে নিহিত। এখানে বলে রাখা দরকার বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাষারীতির মূলটি গ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃতানুসারী বলে অভিযুক্ত করলেও নিজের ভাষাতে তিনি অবলম্বন করেন বিদ্যাসাগরকেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘বাঙ্গালা ভাষা’ প্রবন্ধে ‘বিষয়ানুসারে রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত’ বলে যে মন্তব্য করেছিলেন সেটি বিদ্যাসাগারের রচনাতেও ক্রিয়াশীল। বিদ্যাসাগরই প্রথম সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করে, বাংলা ভাষায় ইংরেজি বিরামচিহ্নের ব্যবহার ঘটিয়ে বাংলা ভাষাকে একটি সৌন্দর্যমণ্ডিত সাহিত্য ভাষায় পরিণত করেন।
দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমগৃহীত ভাষায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদ, তৎসম শব্দ ব্যবহারের আধিক্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে বর্তমান থাকলেও বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) উপন্যাসে এসে তাঁর ভাষার এ ভারভাবটি খানিকটা হ্রাস পায় এবং সাথে সাথে বঙ্কিমের গদ্যরীতি লাভ করে অন্তঃসলিলা এক শক্তি। বিষবৃক্ষ থেকে কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) পর্যন্ত বঙ্কিমের ভাষা সাধুরীতিকে অবলম্বন করে থাকলেও বাংলা কথাসাহিত্য রচনায় সাবলীল এবং সংঘবদ্ধ ভাষার একটি রূপ-সন্ধান তিনি এসব গ্রন্থে দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে এর খানিকটা ব্যত্যয়ও হয় – বিষয়গত কারণটিই এর মূলে ছিল বলে ধারণা করা যায়।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনে ভাষা নিয়ে গ্রহণ-বর্জন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম করেননি। সাধুরীতিতে রচিত তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাসগুলোতে বঙ্কিমী ঢঙটি বেশ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলো অধিক মননশীলতার কারণে বেশী গতিশীল হওয়ায় বঙ্কিমী প্রভাবকে অতিক্রম করে খানিকটা এগিয়ে যেতে সক্ষম হয। চতুরঙ্গ (১৯১৬) উপন্যাসে এসে সে রীতিতে লক্ষিত হয় একটি ভিন্ন মাত্রা। সর্বনাম এবং ক্রিয়ারূপ সেখানে সাধুভাষার হলেও তা এসে যায় অনেকখানি চলিত ভাষার কাছাকাছি। একই সালে প্রকাশিত ঠিক পরের উপন্যাস ঘরে-বাইরেতেই ঘটে যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চলিত রীতিতে রচিত এ উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদটি এমন –
‘মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথির সিঁদুর, সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দু’টি চোখ – শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছিল আমার চিত্তাকাশে ভোর বেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা বেড়িয়েছিলেন। তারপরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখলা না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই যে ঊষা-সতীর দান, দুর্যোগ সে ঢাকা পড়ে, তবুও সে কি নষ্ট হবার?’
ঘরে-বাইরের এ ভাষা পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথে পেয়েছে নতুনতর গতি। শব্দ ব্যবহার, বাক্যের শ্রুতিমধুরতা প্রভৃতি ব্যাপারে সর্বদা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন বলেই তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন শেষের কবিতাতে (১৯৩০) – কিন্তু চলিত ভাষা রীতির এ কাঠামোটি থেকে গেছে প্রায় একই রকম, বরাবরই। রবীন্দ্রনাথের এ ভাষারীতিতে পরবর্তীকালে বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় যে কথাসাহিত্য রচিত হচ্ছে – রবীন্দ্রনাথের এ বাকভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে কথাসাহিত্যের জীবনলাভ।
ত্রিশোত্তরকালে বাংলা কথাসাহিত্যে ঢেউ লাগে ‘চেতনাপ্রবাহ’ ধারায়। মনুষ্য-মনের অবচেতন স্রোতটিকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে তাঁদের ভাষায় এসে পড়ে এক নতুন রূপময়তা। বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু এ সময়ে কথাসাহিত্যের ভাষায় চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতির মেজাজ আনতে সবচেয়ে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। একটু জ্যেষ্ঠ জগদীশ গুপ্তও ভাষারীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবীদার। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও সংযত ভাষণের উত্তরসুরি হিসেবে আমরা পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু সামগ্রিক চিত্রটি এরূপ থেকে যায় যে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষাভঙ্গীটি নির্মাণ করে গিয়েছিলেন সেটিই বহমান থাকে বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষার মূল কাঠামো হিসেবে। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যের ভাষারীতিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তন আসে তা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার। প্রধানত সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার প্রথম দিকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও পরে স্বাভাবিকতার একটি অঙ্গ হিসাবে সেটি প্রতিষ্ঠা পায়। একসময়ে তা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় যে, বর্ণনাকারীও আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করে ফেলেন – অন্তত যখন আঞ্চলিক ভাষার কোন চরিত্র গ্রহণ করে বর্ণনাকারীর ভূমিকাটি। আর আঞ্চলিক শব্দকে লেখকের নিজের বর্ণনায় ব্যবহার তো বেশ স্বাভাবিক একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। অসীম রায়ের গল্প ও শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলোকে বা হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে এ ব্যাপারটি বেশ লক্ষণীয়। অন্যদিকে বিমল কর, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কথাসাহিত্যে কাটাকাটা বাক্যের সাবলীল একটি স্রোত তৈরি হয় যা পাঠকের চিত্তে তৈরী করে কাব্যিক এক অনুরণন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, দেবেশ রায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখের ভাষা নির্মাণে লক্ষ করা যায় বলিষ্ঠতার এক ছাপ যা তাঁদের সাহিত্যকর্মকে দেয় সিরিয়াস সাহিত্যের ভঙ্গীমাটি।
একথা বলা অযৌক্তিক হবে না রবীন্দ্রনাথের পর কমলকুমারের মধ্যেই আমরা প্রথম দেখতে পাই প্রচলিত বাংলা ভাষার কাঠামোকে ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা। খুব ধীর গতিতে শুরু করে তিনি সুহাসিনীর পমেটম-এ (১৯৬৫) পৌঁছে এমন একটি ভাষাশৈলী নির্মাণ করতে সক্ষম হন যা সম্পূর্ণতই তাঁর নিজস্ব। সে ভাষার শব্দ ব্যবহার এবং বাক্য গঠনরীতি এমন নিয়মে চলে যা বাংলাভাষী পাঠকের একেবারে অজানা। ব্যাপারটি এমন নয় যে, কমলকুমার একটি বিশেষ সাহিত্যকর্ম রচনার জন্যেই এমন একটি ভাষাকে সাময়িকের জন্য তৈরি করে নেন (যেমনটি আমরা দেখতে পাই শওকত আলীর উপন্যাস প্রদোষে প্রাকৃতজন-এ (১৯৮৪) যেখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে নির্মিত কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে শওকত আলী ধারণ করেন তৎসম শব্দবহুল একটি ভাষারীতিকে)। কমলকুমারের ভাষা-নির্মাণ প্রক্রিয়াটি ক্রমশ পৌঁছে যায় একটি চূড়ান্তে এবং তা বিষয়-নির্বিশেষে তাঁর যে কোন গ্রন্থ রচনার জন্যই অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিককালে অমিয়ভূষণ মজুমদারে আমরা অনুরূপ একটি নিরীক্ষার সাক্ষাৎ পাই।
মধু সাধুখাঁ (১৯৮৮) উপন্যাসের পূর্বে অমিয়ভূষণের ভাষায় পরীক্ষা থাকলেও মধু সাধুখাঁতে আমরা প্রথম দেখতে পাই বাক্য গঠনে ভিন্ন একটি রীতি যে রীতিতে কমলকুমার মজুমদারের ছায়া পাঠক লক্ষ করেন এবং সে রীতিটি ফ্রাইডে আইল্যান্ড বা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর (১৯৮৮) উপন্যাসে অর্জন করে অনেক দৃঢ়, অনেক বেশি সংহত একটি রূপ। কমলকুমার মজুমদারের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষা-নির্মাণে যে দীর্ঘ পরিক্রমাটি আমরা লক্ষ করি অমিয়ভূষণে কিন্তু তা ঘটে না। এমনকি অমিয়ভূষণ তাঁর ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর উপন্যাসের পরে পুনরায় ফিরে আসেন তাঁর নিজস্ব ভাষারীতির পূর্বরূপে – যে ভাষাতে তিনি অধিক অভ্যস্ত। তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস গড় শ্রীখণ্ড, নয়নতারা, রাজনগর প্রভৃতি অসামান্য গ্রন্থে তিনি যে ভাষাভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন তাতেই রচিত হয় তাঁর পরবর্তী উপন্যাস বিবিক্ত (১৯৮৩)। এমনকি তার চাঁদবেনে (১৯৯৩) উপন্যাসে প্রয়োজনানুযায়ী খানিকটা ভাবগাম্ভীর্য এলেও তিনি তাঁর স্বাভাবিক ভাষাতে এখানে স্থিত।
তিন
পাঠকের কাছে কমলকুমারের গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত সেটি গচ্ছে তাঁর ভাষা-জটিলতা। একটি নিজস্ব ভাষাভঙ্গী নির্মাণে তাঁর পারদর্শিতা যেমন অনেক পাঠককে আগ্রহী করেছে তাঁর রচনা সম্পর্কে, তেমনি আরও বেশি পাঠককে তাঁর রচনা থেকে বিমুখও করেছে। তাঁর ভাষাভঙ্গীর এ ভিন্নতা বহুল আলোচনা লাভের কারণেই কমলকুমারের সাহিত্যের অন্য সব অনুসঙ্গ হয়ে পড়েছে অনালোচিত। বিষয়কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভাষারীতি নিয়ে কথাবার্ত দিয়েই কমলকুমারের সাহিত্য দিয়ে আলোচনা শেষ হয়ে যাচ্ছে।
কমলকুমারের গল্প-উপন্যাসে কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করা কষ্টকর। ‘লালজুতো’তে কিশোর প্রেমের যে আখ্যান তিনি দিয়েছেন তা অসাধারণ। এত মর্মস্পর্শী করে দুই কিশোর-কিশোরীর ভবিষ্যত সন্তান-বাসনা, সে সন্তানের জন্য একজোড়া লালজুতো ক্রয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত কমলকুমারের রচিত প্রথম এ গল্পটি যে কোন পাঠককে আকর্ষণ করতে সক্ষম। এবং বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে – কমলকুমারকে আপাতদৃষ্টিতে আমরা মান-কমলকুমার হিসেবে চিহ্নিত করি সে সময় তিনি এক পা-ও সেপথে বাড়ান নি। যদিও সকল বড় সাহিত্যিকের রচনার মত কমলকুমারের ক্ষেত্রে কোন একক বিষয়কে নির্দিষ্ট করে কোন রচনার মধ্যে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। প্রেম নিয়ে তাঁর যেমন বেশ কিছু গল্প রয়েছে তেমনি অবস্থান নিয়েছে কমলকুমারের রচনায়। কমলকুমারের মোট রচনার হিসেব কষলে দেখা যাবে মোটামুটি সাতাশ/আটাশটি গল্প এবং গোটা পাঁচেক উপন্যাসের ভেতর দিয়ে তার কথাসাহিত্যিক পরিচয়টি প্রকাশিত।
এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার ব্যক্তিজীবনে কমলকুমার শুধুমাত্র একজন কথাসাহিত্যিকই ছিলেন না, তাঁর কলম দিয়ে একইসাথে রচিত হয়েছিল বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং অন্তত দুটি নাটক। তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বিবিধ বিচিত্র বিষয় নিয়ে। বিশ্বসাহিত্য নিয়ে রচিত ‘নাতুরালিজম’, ‘মার্সেল প্রুস্ত বিষয়ে কিছু’, বা বাঙালি লোকঐতিহ্য নিয়ে রচিত ‘বাংলার মৃৎশিল্প’ ইত্যাদি ছাড়াও ‘ভাব প্রকাশ বিষয়ে’, ‘কথা এক ইশারা বটে’, ‘সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন’, ‘কলকাতার গঙ্গা’, প্রতীক জিজ্ঞাসা’, ‘পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে’ প্রবন্ধগুলোর বিভিন্ন বৈচিত্রময় বিষয়ে কমলকুমারের আগ্রহেরই পরিচায়ক। আর নাটক রচনার ব্যাপারে শুধু এটুকুই বলা যায় অদ্যাবধি তাঁর দুটি নাটকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে: ভূখণ্ড ও দানসা ফকির। এতো গেল সাহিত্যিক কমলকুমারের প্রসঙ্গ। কিন্তু এছাড়াও ব্যক্তি কমলকুমারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল আরও বহু গুণ, বৈশিষ্ট্য। সিনেমা এবং নাটকের ব্যাপারে তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। এ দুটো মাধ্যমেই নির্দেশনা ছাড়াও চিত্রনাট্য রচনা, সিনেমা পত্রিকা সম্পাদনা, ছবি আঁকা ইত্যাদি ব্যাপারেও তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ ও আন্তরিকতা। চিত্রশিল্পী হিসেবে যদিও সামান্যতম প্রতিষ্ঠা তিনি পান নি কিন্তু সারাজীবন ধরেই সুযোগ পেলেই রং-তুলি নিয়ে তিনি বসেছেন। অমৃত-কথা নামে যে গ্রন্থটি কমলকুমারের স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদার পরবর্তীকালে প্রকাশ করেন সেটি কমলকুমারের আঁকিবুঁকিকে আশ্রয় করে গ্রন্থিত। অথবা যারা কমলকুমার কর্তৃক সংকলিত ছড়ার বই পানকৌড়ি দেখেছেন তাঁরা বুঝবেন এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা খুব ছোটদের জন্য একগুচ্ছ ছড়াকে কমলকুমার কেমন পাতাজোড়া ছবি দিয়ে সাজিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। এছাড়াও বহু গ্রন্থের তিনি প্রচ্ছদও করেছিলেন বলে জানা যায়। নিভৃতে কবিতা চর্চাও করতে বলে তার কোন কোন পরিচিত সমবয়সী লেখক উল্লেখ করেছেন।
চার
বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাষারীতিতে কমলকুমারের অবস্থান কোথায় সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা কমলকুমারের ব্যক্তিজীবনের উপর খানিক আলোকপাত করে নিতে চাই।
১৯১৪ সালের ১৭ নভেম্বর কলকাতার তার জন্ম, পিতা প্রফুল্লচন্দ্র এবং মাতা বেণুকাময়ীর চার ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম তিনি। কমলকুমারের পৈত্রিক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা। মা চেয়েছিলেন ছেলেরা শিল্পী হোক, চরিত্রবান হোক। বাবা ছেলেদেরকে যুক্তিবাদী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বাবা-মার এসব অভীপ্সার ছাপ কমলকুমারের চরিত্রে বর্তমান। প্রথমদিকে পড়াশোনা করেন মিশনারী স্কুলে। পরে এসে ভর্তি হন সংস্কৃত টোলে। কিশোরকাল থেকেই কমল-নীরদের (কমলকুমারের ভাই বিখ্যাত চিত্রকর নীরদ মজুমদার) দূর দূর এলাকায় বেড়ানোর অভ্যাস গড়ে ওঠে। গিয়েছেন লক্ষ্ণৌ, এসেছেন রাজশাহী। ১৯৩৮ সালের দিকে শুরু করেন ব্যবসা। হয়ে ওঠেন প্রচণ্ড সাহেবী। ১৯৩৯ সালে এফ.এ পাস করেন। ১৯৪৭-এ বিয়ে করেন পুর্ব পরিচিতি দয়াময়ীকে। চূড়ান্ত সাহেবী কমলকুমার একসময় বাবুগিরি ছেড়ে শুরু করেন সাধারণ জীবনযাপন। ব্যবসা ইত্যাদি সব একসময় বন্ধ হয়ে যায়। নেমে আসে প্রচণ্ড দারিদ্র্য। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি নিঃসন্তান কমলকুমারের মৃত্যুর পূর্ব অবধি এ দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।
কমলকুমারের সাহিত্য আলোচনার জন্য ব্যক্তি কমলকুমার অত্যাবশ্যক – যে কোন মহৎ সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে থাকে। একজন মহৎ সাহিত্যিক পাঠকের দোরে পৌঁছানোর জন্যে সমালোচনার ভূমিকাও কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কমলকুমারকে নিয়ে এতদিনেও খুব বেশি গ্রন্থ রচিত হয় নি। ১৯৮১ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত রফিক কায়সারের কমলপুরান এবং ১৯৮৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার গ্রন্থ দু’টি ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কোন পূর্ণ গ্রন্থ রচনার খবর পাওয়া যায় না। এবং উল্লেখ্য যে, এ দু’টি গ্রন্থের প্রথমটি সম্প্রতি দ্বিতীয় মূদ্রণ পেলেও দ্বিতীয়টি বর্তমানে বাজারে সহজলভ্য নয়। কিছু লিটল ম্যাগাজিনেই মাঝেমাঝে তিনি আলোচিত সমালোচিত। এছাড়া অশ্রুকুমার সিকদারের বহুল প্রশংসিত আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস নামক সমালোচনা গ্রন্থে ‘অন্তর্জলী যাত্রার ঘোর বাস্তবতা’ প্রবন্ধটি কমলকুমার-চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ব্যক্তি কমলকুমারসহ তাঁর সহিত্যকর্মকে জানার জন্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবিতীর্থ পত্রিকার ১৮, ১৯, ২০, ২১ সংখ্যায় হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত ‘কমলকুমার মজুমদার: মুখ ও মুখের দ্বন্দ্ব’ প্রবন্ধটি উৎসাহী পাঠকের জন্যে অতীব প্রয়োজনীয় একটি সংগ্রহ বটে।
পাঁচ
“সে আপনকার অতীব শ্রীযুক্ত মুখমণ্ডলের খাসা সীম বীজ নাসার বেসর যেখানে ঝুটাপান্না – মনলোভা পান্নার ইহকালের অচীন সুদীর্ঘতা বহু সন্তরণে অতিক্রম করত আসিয়া স্থির মূর্ত্ত, উহাতেই দোমনা অঙ্গুলি প্রদান করে এবং এই অঙ্গুলিতেও নির্ঘাত, অবশ্যই, তাহার, সুহার-সুহাসিনীর দগ্ধ তীক্ষè রাত্র যাহা মেঘগর্জনের উন্মাদ দাপট ও যুগপৎ ভেককুল আর ঝিঁঝির পরস্পরা ডাক মিশ্রিত ত্রাহি করা দুর্যোগ ফলে, এ কারণে, এহেন ঘোরঘটা যামিনীর মাড়ি পীড়নজনিত যখন এমনও যে উহার, বালিকার ডাগর কালীয়া চতুর দেহ সুতপ্ত – এখন, যদ্যপি যে অল্পবয়সী তত্রাচ তাহার শরীর বৈভব সুকুমার লাল, পুরুষ অভিমানী – আরও যে এই অবয়ব যাহার কক্ষস্থ লণ্ঠনের হেতু দশাসই রুদ্র মখমল পট্টছায়া, মশারি তবু, দর্শনে প্রকৃতই বিশেষ মীনগন্ধবৈধ বাসনায় উচ্ছ্বসিত হওয়া স্বভাবত যে সম্ভব, যে তথাপিও কোনক্রমেই বুঝে না – উপরন্তু, অথচ এই হয় যে, পার্শ্ববর্তী ভাঁড়ার ঘরের, যাবতীয় কিছুর মধ্য হইতে ছোটলোক, নিম্নশ্রেণীর, মাথার কিটকিটে সুলভ বাসের সহিত শিকে-তোলা হাঁড়িতে জাওলা মাছের ক্বচিৎ চাঞ্চল্য প্রসূত ঘর্মাক্ত তৃপ্তিদায়িনী রতিসুখ আপ্লুত শব্দ উত্থিত হয়, তৎব্যতিরেকেও; তাই নিজেকে-সে – ভাবে দংশিত যন্ত্রনায় মৃদুহাস্যে জড়াইয়া শুইবার প্রোষিতভর্ত্তিকা ঘুমাইবার ঔৎসুক্যে জিহ্বাও পালট করে নাই, উহা সরসিত নহে, কেননা সে হয় ম্লান, সে বড় অসহায়; সে এই অমানিশীথিনীর সর্বক্ষণব্যাপী তিক্ত নিম্ব গন্ধ পাইয়াছে, তাহার পেলব গাত্রময় মারিগুটিকার বেদনা তাহাকেই আপন নৈকট্য হইতে অপসারিত করে – পুনরায় নিম্বশাখা পত্রযুক্ত বাজনে সে কাতর আর্ত্ত বেচারী…।”
উদ্ধারচিহ্নের সর্বশেষ তিনটি ডটের দৈর্ঘ্য একশত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ ‘সে আপনকার’ দিয়ে যে বাক্যটি শুরু হয়েছে একশত একান্ন পৃষ্ঠার উপন্যাস সুহাসিনীর পমেটম-এ সেটি বিরামচিহ্ন হিসেবে ড্যাশ, হাইফেন, সেমিকোলন, কমা, ডট, ব্রাকেট, উদ্ধারচিহ্ন প্রভৃতিকে গ্রহণ করলেও একটি পূর্ণ বিরামচিহ্নে পৌঁছোয় উপন্যাসটির সর্বশেষ বাক্যে। কমলকুমার মজুমদারের সাধারণ পরিচিতি এটা হলেও অবশ্য উল্লেখ্য যে, প্রথম গল্পে তিনি ছিলেন রীতিমত সহজ, স্বাভাবিক। ১৯৬৫-তে প্রকাশিত সুহাসিনীর পমেটম ১৯৩৭-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প ‘লালজুতো’ থেকে আঠাশ বছর পরের সৃষ্টি। ‘লালজুতো’র কমলকুমার আটাশ বছর ধরে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার ক্রমান্বয়ে এগুতে এগুতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ভাষায় লিখিত সুহাসিনীর পমেটম-এ পৌঁছোন।
ভাষাগত পরীক্ষায় কমলকুমার মজুমদারের শিল্পনিষ্ঠ স্বতন্ত্র পদচারণা শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষণীয়। বাক্যের বিন্যাসে তিনি যে ওলট পালট করেন, বিশেষণে তিনি যে তাৎপর্য আনেন, তা কমলকুমারের ইপ্সিত চিত্রময়তাকে সাহায্য করে বলে শিল্পসঙ্গত। নতুবা তা হয়ে যেত চূড়ান্ত রীতিবিলাস। আধুনিক চিত্রকলায় শিল্পী যে দুঃসাহসিক স্বাতন্ত্র্যের চর্চা করেন কমলকুমারের গদ্যের সঙ্গে সেই স্বাতন্ত্র্য-চর্চার স্বভাবাত্মক মিল আছে। অথচ বর্ণে, বিশেষণে বিন্যাসে এ অন্তত এর উত্তম মুহূর্তে কখনো উপন্যাসাতিরিক্ত নয়। বাঙালি লেখকের হাতে লৈখিক ক্রিয়া যে এখনো সম্পদ বলে পরিগণিত হতে পারে, কমলকুমারের লেখায় তার প্রমাণ আছে। অমিয়ভূষণের ভাষাশৈলী কমলকুমারের মতো স্বতন্ত্র পথচারী নয়। কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্রোপন্যাস ‘মধু সাধুখাঁ’র ভাষায় অন্তত সংলাপের ভাষায়, কমলকুমারের প্রথাবিরোধী বিন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অমিয়ভূষণের ‘গড় শ্রীখণ্ড’ অবশ্য কমলকুমারের উপন্যাসহসমূহের পূর্ববর্তী রচনা। সে উপন্যাসেও অমিয়ভূষণের ভাষার শান্ত, ধীর চাল, সুসমঞ্জস্য গঠন এবং অনাবিষ্ট ভঙ্গি উপন্যাসের বিষয় গাম্ভীর্যের উপযুক্ত আধার হয়েছিল। [সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ. ৫৭]
বাংলা উপন্যাসের বিশেষ ভাষারীতির উপর আলোকপাত করতে গিয়েই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপরের কথাগুলো বলেন। আমরা সবাই জানি বিশেষ ভাষারীতির জন্যে বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত। অমিয়ভূষণের প্রথম গ্রন্থ গড় শ্রীখণ্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬০ বঙ্গাব্দে যেটি ১৯৫৭-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এবং সে গ্রন্থটির ভাষায় ভিন্নতা আসলেও সেটি কোনক্রমেই কমলকুমারের সাথে তুলনীয় নয়। তাছাড়াও ১৩৬০ বঙ্গাদের আগেই ১৯৪৫-৪৬ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত কমরকুমারের গল্প ‘জল’, ‘তেইশ’, ‘মল্লিকা বাহার’-এই কমলকুমারের ভাষানিরীক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসিক জীবনের প্রথম যেটি করেছিলেন সেটি হচ্ছে উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার। যদিও অমিয়ভূষণ নিজেই একে একেবারে আঞ্চলিত ভাষা আখ্যা দিতে নারাজ। যেমন গড় শ্রীখণ্ড প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,
… আমি সেই ডায়ালগটাই দেব যাতে মনে হবে যেন একটা লোকাল কালার আছে, কিন্তু কোন লোকালিটির নয়, সেটা সর্বজনবোধ্য হবে। যেমন Wessex Novel-এ হার্ডি যে ডায়ালগ ব্যবহার করেছেন – এক নম্বর, Wessex বলে কোন জায়গাই নেই, দু’নম্বর সেটা কোন প্রদেশের ভাষাও নয়। সেটা একটা ডায়ালেক্ট যেটা সবাই বুঝতে পারে। আমার ‘গড় শ্রীখণ্ড’তে ডায়ালগ দেওয়া আছে, মনে হবে পাবনার ডায়ালেক্ট, কিন্তু একচুয়ালী তা পাবনার নয়। [সাক্ষাৎকার/১, বিজ্ঞাপনপর্ব, দশম বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮২ – জানুয়ারি ১৯৮৩]।
যদিও নিজের রচনার উপর অমিয়ভূষণের মন্তব্য কতখানি যথার্থ তা ভেবে দেখা দরকার। কেননা, পাবনার আঞ্চলিক ভাষাটি এমন নয় যে তা হুবহু বললে কোন বাংলাভাষীর কাছে তা বিদেশি ভাষা বলে মনে হবে। আর ডায়ালগ ব্যবহার – অর্থাৎ ডায়ালগের শব্দ ব্যবহার ও বাক্য গঠনে তো অমিয়ভূষণ পদ্মতীরবর্তী পাবনা ফরিদপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা থেকে একটুও সরেন নি। এ এলাকার ভাষার সাথে পরিচিত নন এমন কোন বাংলাভাষীও বইটি পড়তে গেল ডায়ালগের স্থানগুলোতে গিয়ে হোঁচট খাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। তা না হলে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত দুখিয়ার কুঠির ভূমিকায় লেখকের দরকার হতো না স্বাভাবিক বাংলারীতির বাইরে উপন্যাসের পটভূমির ভিন্ন অঞ্চলের গৃহীত ভাষার সর্বনাম, ক্রিয়া পদ ও অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর ব্যবহৃত ভাষার ব্যাখ্যা দেয়ার। তবে ডায়ালগের বিশেষ ব্যবহারের বাইরেও অমিয়ভূষণ বিশেষ ভাষারীতির সন্ধানী যার পরিচয় ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ মধু সাধুখাঁ এবং ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর উপন্যাসদ্বয়ে পরিলক্ষিত। পাঠকের সম্যক ধারণা লাভের প্রয়োজনে এ দু’টি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার অংশ বিশেষ আমরা উদ্বৃত করছি:
মদু-সা সাতিশয় হারামজাদা ছিলো – সন্দেহ কি? চিকন ঠাণ্ডা কালো রঙ, টিকলো নাক, টানা চোখ, বলে চক্ষু; সে-চোখের প্রান্তগুলি আবার লাল; দাঁতগুলি সুগঠিত, কিন্তু কষ ঘণ্টার-ঘণ্টায় পানরসে লাল; চলেও যেন সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি। গায়ে মোটা তসরের মেরজাই অর্থাৎ কুনুই পর্যন্ত হাতা, বোতামের বদলে নিচে ডোরে বাঁধা ছোটো ঝুলের পাঞ্জাবি, পরনে দু-আঙুলে চওড়া পাড়, খাটো কিন্তু সূক্ষ্ণ ধুতি।
লক্ষ করলে দেখা যায় টিকলো নাকের উপরো চুলের মতো সূক্ষè ক’রে টানা রসকলি। পাড়ে চামড়ার কট্কি। তার নৌকার মাঝি-মাল্লারা হিন্দু, কিন্তু বদর এবং বলা? তার জন্য পাক করে তোপদার, জাতে যে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে বলার সঙ্গে একত্র পানাহার করে, বদরের ছোঁয়া খায়। বদর সম্ভব মুসলমান, আর বলা ফিরিঙ্গি। মদু-সা-ই নাম দিয়েছে, অর্থাৎ সে কানাই আর ফিরিঙ্গি বেটা বলাই। হারামজাদা সন্দেহ নেই। (মধু সাধুখাঁ, পৃ. ১)।
পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারছেন অমিয়ভূষণের বাক্য গঠনের ভিন্নতা। তার এ ভিন্নতা আরও প্রকটতা লাভ করেছে পরবর্তীকালে যেমন:
সে বিষয়ে নানা মত যে প্রচলিত আছে স্বীকার করি এবং যে যাহা খুশি প্রামাণ্য মনে করায় ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। কেহ বলে দ্বীপের, যাহা দ্বীপ তাহা দেশ, ট্যুরিস্ট ব্যুরোর প্রচার, কেহ বলে বেনিফিকো ক্যাস্টিগলিনোর ক্যারিবকাব্য আন্দোলন, বলে ইহা সবই জন জোয়াকিম ফ্রেডা এবং সেই মাত্র। (ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর, পৃ. ১)।
যদিও অমিয়ভূষণ ভাষাগত এ নিরীক্ষা থেকে পরবর্তীকালে কোথায় স্থিত হন তা বিতর্কের। যেহেতু ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস বিবিক্তা স্বাভাবিক, প্রচলিত ভাষারীতিতে রচিত। আর অমিয়ভূষণের ভাষারীতি যেহেতু আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, তাই আমরা আমাদের আলোচনার কেন্দ্র কমলকুমারের ভাষারীতিতে ফিরে যাচ্ছি। তবে এখানেই বলে রাখা দরকার যেহেতু কমলকুমারের অধিকাংশ রচনাই যথাসময়ে গ্রন্থাকারে আসেনি তাই তাঁর যেসব রচনার সন-তারিখ আমরা উল্লেখ করছি সেগুলো পত্রপত্রিকায় রচনাটির প্রথম প্রকাশের সময়কার।
১৯৩৭ সালে প্রকাশিত প্রথম গল্প থেকে ১৯৭৯ সালে কমলকুমারের মৃত্যু অবধি ভাষায় তাঁর যে ক্রমঅগ্রসরণ ঘটেছে – যেটি এক পর্যায়ে তাঁর নিজস্ব রীতিতে পূর্ণতা পায় তা স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য কমলকুমারের সকল রচনার কালানুক্রমটি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ ব্যাপার সমস্যা হচ্ছে কমলকুমারের সকল রচনা গ্রন্থাকারে তাঁর মৃত্যুর পনের বছর পর এতদিনেও পাঠকের হাতে পৌঁছায় নি। যেগুলো বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থরূপে এসেছে সেগুলোও সহজলভ্য নয়। তাছাড়া বাদবাকি যেসব রচনা বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে তিনি দিয়েছিলেন এবং যেগুলো পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি তার পরিমানও একেবারে নগণ্য নয়। এ সকল ব্যাপারে কবিতীর্থ পত্রিকায় প্রকাশিত হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি আমাদেরকে মোটামুটি একটি চিত্র দিতে পারে। অন্যদিকে কমলকুমার মজুমদার: গল্পসমগ্র নামে তাঁর সহজলভ্য সকল গল্প নিয়ে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সেটিকেও আমরা প্রয়োজনে উল্লেখ করব। ব্যক্তি জীবনে কমলকুমারের পরিচিত হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিতে কমলকুমারের রচনাসমগ্রের যে কালানুক্রম দেয়া হয়েছে সেটি অনেকখানিই গ্রহণযোগ্য, যদিও সেখানে ‘শ্যাম নৌকা’, ‘স্বাতীনক্ষত্রের জল’, ‘বাগান দৈববাণী’ ও ‘আত্মহত্যা’ শিরোনামের চারটি গল্পের কথা বলা হয়েছে যা কমলকুমার মজুমদার: গল্পসমগ্রতে নেই। এছাড়াও উক্ত প্রবন্ধে আরও কয়েকটি গল্পের উল্লেখ রয়েছে যেগুলোর পাণ্ডলিপির খোঁজ পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায়নি, যেমন ‘খেলার তারিখ’, ‘সখারাম’, ‘খেলার অপ্সরা’, ‘খেলার মীমাংসা’ ও ‘বাগান যক্ষিণী’। অন্যদিকে হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিতে ‘জাসটিস’ ‘প্রেম’ ও ‘বাবু’র উল্লেখ নেই যেগুলি পূর্বোক্ত সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যদিও গ্রন্থ ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানে গল্পগুলি রচনাকাল অনুযায়ী সজ্জিত। কিন্তু উপরিউল্লিখিত তিনটি গল্প ‘জাসটিস’ ‘প্রেম’ ও ‘বাবু’ যেখানে সংস্থাপন করা হয়েছে তা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। সচেতন পাঠকের চোখ এড়াবে না যে ১৯৩৭ সালে রচিত কমলকুমারের প্রথম তিনটি গল্প ‘লালজুতো’, ‘মধু’, ‘প্রিনসেস’-এর বৈশিষ্ট্যগুলি ঐ তিনটি গল্পে বর্তমান। তাই হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের কালানুক্রমটিকে প্রধান আশ্রয় করে যদি আমরা কমলকুমারের কথাসাহিত্যের একটি তালিকা নির্মাণ করতে চাই তাহলে সেটি এমন হবে:
| প্রকাশকাল | রচনার নাম | রচনার শ্রেণি |
| ১৯৩৭ | লালজুতো | গল্প |
| ” | মধু | ” |
| ” | প্রিনসেস্ | ” |
| ” (অনুমিত) | প্রেম | ” |
| ” (অনুমিত) | জাসটিস | ” |
| ” (অনুমিত) | বাবু | ” |
| ১৯৪৫-৪৬ | জল | ” |
| ” | তেইশ | ” |
| ১৯৫১ | মল্লিকাবাহার | ” |
| ১৯৫৭-৫৮ | মতিলাল পাদ্রী | ” |
| ” | তাহাদের কথা | ” |
| ১৯৫৯ | অন্তর্জলী যাত্রা | উপন্যাস |
| ১৯৬০ | নিম অন্নপূর্ণা | গল্প |
| ” | ফৌজ-ই-বন্দুক | ” |
| ” | কয়েদ খানা | ” |
| ” (অনুমিত) | পিঙ্গলাবৎ | ” |
| ১৯৬১-৬২ | কঙ্কাল এলিজি | ” |
| ১৯৬২ | গোলাপ সুন্দরী | উপন্যাস |
| ১৯৬৪ | অনিলা স্মরণে | ” |
| ১৯৬৫ | সুহাসিনীর পমেটম | ” |
| ১৯৬৮ | রুক্ষিনীকুমার | গল্প |
| ১৯৬৯ | পিঞ্জরে বসিয়া শুক | উপন্যাস |
| ১৯৭১ | কালই আততায়ী | গল্প |
| ১৯৭২ | লুপ্ত পূজাবিধি | ” |
| ১৯৭৪ | দ্বাদশ মৃত্তিকা | ” |
| ” | অনিত্যের দায়ভাগ | ” |
| ১৯৭৫ | খেলার দৃশ্যাবলী | ” |
| ” | আর চোখে জল | ” |
| ১৯৭৭ | খেলার প্রতিভা | উপন্যাস |
| ১৯৭৮ | খেলার বিচার | গল্প |
| ” | খেলার আরম্ভ | ” |
| ” | বাগান কেয়ারী | ” |
| ” | বাগান পরিধি | ” |
এ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির গল্পগুলো, বর্তমানে সহজলভ্য নয় এমন গল্প যেমন ‘শ্যামনৌকা’, এবং অসমাপ্ত গল্প ‘মামলার শুনানী’ ও ‘কশ্চিত জীবন চরিত: তিনটি খসড়া’র নাম। উপরোক্ত কালানুক্রমকে সামনে রেখে এখন আমরা একটি সম্পর্ক তৈরি করতে পারি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত তার প্রথম গল্প ‘লালজুতো’ ও ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত সুহাসিনীর পমেটম-এর মধ্যে এবং দেখানোর চেষ্টা করতে পারি কীভাবে কমলকুমার ‘লালজুতো’র স্বাভাবিক ভাষারীতি থেকে ধীরে-ধীরে সুহাসিনীর পমেটম-এর জটিল, দুর্বোধ্য, একান্তভাবে নিজস্ব ভাষারীতির পূর্ণতায় পৌঁছান।
এই যে না-প্রচলিত একটি ভাষায় কমলকুমার ধীরে ধীরে ডুবে যান যেটি সবশেষে গিয়ে প্রায় সব পাঠকের কাছেই একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে সেটি কেন হয়? ছোটখাট কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চলিত ভাষা থেকে সাধু ভাষায় পদার্পন। মোটামুটিভাবে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত ‘পিঙ্গলাবৎ’ গল্পেই তিনি সাধু ভাষা প্রথম ব্যবহার করেন। পূর্বে প্রচলিত এবং বর্তমানে প্রচলিত নয় এমন শব্দ গ্রহণও কমলকুমারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এক সময়। একদম শেষ পর্যায়ের গল্পে এসে তিনি ক্রিয়াবাচক শব্দের পুরোনো রূপ যেমন – সিঞ্চিড়িয়া, সম্বোধনিয়া, উত্তরিলেন, অবলোকিলেন, মন্ত্যবিল, গ্রহনিয়াছেন, সাক্ষাতিয়াছেন, অবলোকনিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করা শুরু করেন। সংযোজন অব্যয়ের দ্বিত্ব ব্যবহার তাঁর ভাষাকে অপরিচিতি করে তুলতে ভূমিকা রাখে। ‘যেহেতু কেননা’র ব্যবহার তাঁর রচনার অনেক। এছাড়া ‘যে’ অস্বাভাবিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর লেখায় বহুবার। বিরাম চিহ্নের ব্যবহার তাঁর রচনায় ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। ‘লালজুতো’তে ড্যাশ, ‘মধু’ ‘প্রিনসেস্’ গল্পে ড্যাশ ( – ) ও ত্রিবিন্দুচিহ্নের (…) ব্যবহার রীতিমত নজর কাড়ে। ত্রিবিন্দুচিহ্নের ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে সারাজীবন ধরে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কমলকুমার যেন পাঠকের উপলব্ধিতে এ বোধই দিতে চান যে তিনটি বিন্দুর মধ্যে অনেক কিছু অব্যক্ত। আর সুহাসিনীর পমেটম তো পূর্ণ বিরতি অর্থাৎ দাঁড়ি চিহ্ন পেয়েছে উপন্যাসটির শেষ লাইনে। ভাষাগত ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও উপস্থাপনাগত কিছু বিষয়ও কমলকুমারের ভাষাকে দুর্বোধ্য করতে ভূমিকা রেখেছে। গল্পে বক্তার উপস্থিতি অস্পষ্ট হওয়া এগুলির মধ্যে একটি। এমনকি পরবর্তীকালে তৃতীয় ও প্রথম পুরুষে তিনি একই গল্পের ভিন্ন ভিন্ন অংশ রচনা করেন। ‘লুপ্ত পূজাবিধি’ এর একটি প্রথম উদাহরণ। ‘খেলার বিচার’-ও এ বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে রচিত। কিন্তু ‘খেলার দৃশ্যাবলী’ ও অনিত্যের দায়ভাগ’-এর প্রসঙ্গে একথা বলতেই হবে যে সেখানে বক্তার উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট। একদম শেষপাদে কমলকুমার তাঁর গল্পে চরিত্রের নাম ব্যবহার করা একদম বন্ধ করে দেন। বিভিন্ন সর্বনাম দিয়ে তিনি চরিত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে শুরু করেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম জটিল হওয়ার পেছনে আরও যেসব কারণ রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে গল্পের অস্পষ্ট কাঠামো। জীবনের একটি পর্যায়ে এসে তিনি কোন রকমে দু’একটি আঁচড়ে সারা গল্পটিকে খাড়া করতে শুরু করেন। গল্পের কাঠামো বা প্লটের চেয়ে, চরিত্রায়ন বা লেখকের বক্তব্যের চেয়ে বেশি স্থান দখল করে পটভূমি বা চরিত্রের তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুঙ্খানুপঙ্খ বর্ণনা এবং এসকল বিষয়কে অতঃপর আমরা পৃথক পৃথক গল্পের নিরিখে আলোচনা করার চেষ্টা করব।
প্রথম গল্প ‘লালজুতো’তে কমলকুমার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন চলিতকে এবং উল্লেখ্য সে সময়ে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধান পুরুষেরা তখনও অব্দি সাধু ভাষার নিগড় থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেননি। ‘লালজুতো’সহ এই সময়ে রচিত তাঁর অন্যান্য গল্পেও দেখা যায় ড্যাশ ও ত্রিবিন্দু চিহ্নের ব্যাপক ব্যবহার। এ সকল গল্পে ভাষা ও উপস্থাপনাগত জটিল কমলকুমারের কোন স্পর্র্শ নেই।
১৯৪৫-৫১ পর্বে কমলকুমারের আর তিনটি গল্প প্রকাশিত হয় এবং পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ করেন প্রথম গল্পগুলির ভাষা, আঙ্গিক থেকে এ তিনটি গল্পের ভাষা ও আঙ্গিকে ঘটে গেছে এক সূক্ষ পরিবর্তন। ড্যাশ, ত্রিবিন্দুচিহ্ন ও সংলাপের ব্যবহার প্রথম গল্পগুলির মত এগুলিতেও বর্তমান থাকলেও পরিবর্তত হয়েছে উপস্থাপনা ভঙ্গি। এ গল্প তিনটিতে লক্ষিত হয় এমন কিছু বাক্য যাতে ভাষা ব্যবহারে কমলকুমারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠকের নজর কাড়ে। যেমন, ‘ইদানিং তারা দুজন ভেড়ির উপরে উঠল …’ (‘জল’) ‘কৃতার্থ হয়েছে যেমন এরূপ ফজল কিছুক্ষণ পরে নিজেকে ঠিক করে বললে…’ (ঐ) ‘বারম্বার যখন তাকে কয়েকটি কথা ধাক্কা দিতে থাকল, যদি দিতে থাকল অথচ সে হতকিত হয়েছিল…’ (ঐ), ‘যেহেতু কেননা সে চাষী…’ (ঐ), ‘যেহেতু সে সুরেন সাঁপুই জাতিতে ওরা উগ্র ক্ষত্রিয় হলেও পয়সা আছে…’ (‘তেইশ’) ‘বদরোদ্দীর একটু খটকা লাগল, গুড়ের ব্যাপারী সে, তার খটকা লাগল…’ (ঐ), ‘যখন মল্লিকার কষ্ট হল, কিন্তু আনন্দের যে সে হাঁফ ছাড়ল…’ (মল্লিকা বাহার), ‘এরপর আনন্দ তার সাজ হয়েছিল…’ (ঐ), ‘মল্লিকা এমন যেমন সে বেয়াকুল…’ (ঐ) ‘বাণী মেয়েটি সে হয় জন্মরুগ্না…’ (ঐ) ইত্যাদি।
প্রায় এগারো বছর পর ১৯৫৭ সালে আঙ্গিক ও ভাষার আরও অনেক ভিন্নতা নিয়ে প্রকাশিত হয়, ‘মতিলাল পাদ্রী’। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এ পর্যায়ে কমলকুমারের ছোটগল্পের সংখ্যা সাত এবং উপন্যাস একটি। হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে পত্রিকায় কমলকুমারের রচনা প্রকাশের সালকে অনুসরণ করায় অন্তর্জলী যাত্রা উপন্যাসটিকে আমরা এ পর্যায়ভুক্ত করেছি। যেহেতু সেটি সাধু ভাষার রচিত তাই অনুমান হয় চলিত ভাষায় রচিত পরবর্তী আরও তিনটি গল্প ‘নিম অন্নপূর্ণা’, ‘ফৌজ-ই-বন্দুক’ ও ‘কয়েদখানা’ পরে এটি রচিত হয়েছিল। এ পর্যায়েই পরিলক্ষিত হয় কমলকুমার উপস্থাপনাতেও একটি ভিন্নতা সৃষ্টি প্রয়াসী। ঘটনা, মানসপট বা দৃশ্যপট বর্ণনার পুঙ্খনুপুঙ্খ হতে গিয়ে স্বাভাবিক গদ্য রচনারীতি থেকে তিনি দূরে চলে যেতে থাকেন। স্পষ্ট উপলব্ধির জন্যে এ পর্যায়ের রচনাগুলোর কয়েকটি থেকে আমরা প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি:
আতা গাছটির পাশেই জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল। এখন পড়ন্ত বেলা, পাতা ছিঁড়ে বিকালের আলোর ছিনিমিনি তার মুখম-লে, অধিকন্তু পাতার সবুজতা; এতে করে তার মনের অধৈর্য আরও যেন বেশি করে প্রকাশ পায়। সে ক্ষুৎপিপাসাকাতর, না অন্য কোন যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু সে নিজেই জানে না। সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তা, জ্যোতি তাকাল। [তাহাদের কথা]
যুথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখিটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভুতভাবে উঁচু করা ছিল, একারণ যে-ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারিকে সর্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরার সময় তার আপনকার হাত দু’টিকে উঁচু করে রাখতেই হয়, এতে করে মনে হয় তার ভারি আনন্দ হয়েছে – সে খুসী, অন্যথা অর্থাৎ যদি ভুল হয়, যদি সে নামায, ঝটিতি ফ্রকটি গা বেড়ে ঝরে পড়ে, খুলে পড়ে; তখন সে যুথী সখেদ একটি ‘আরে’ বলে, পুনরায় ঠোঁট চেপে জোর পটুত্বের সঙ্গে, ফ্রকটি আপনার কাঁধে তুলে দিয়ে থাকে। [নিম অন্নপূর্ণা]
লক্ষণীয় এ পর্যন্ত কমলকুমারের ভাষা স্বাভাবিক বাংলা বাক্যরীতিকে অনুসরণ করেই চলে। যদিও তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই দ্বিতীয় পাঠ আবশ্যক হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে কমলকুমার সাধু ভাষার রচনা শুরু করেন যেখান থেকে তাঁর আর পশ্চাদপসারণ ঘটে নি। পাঠক তাঁর রচনায় প্রবেশে পেতে শুরু করেন প্রবল বাধা। এ পর্যায়ের প্রথমদিকে সে বাধাকে অতিক্রম করা সম্ভব হলেও সুহাসিনীর পমেটম-এ তা যে অসম্ভব বলে প্রতিভাত হয়। যেমন:
আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে। [অন্তর্জলী যাত্রা]
বিলাস অন্যত্রে, কেননা সম্মুখেই, নিম্নে আকাশে, তরুণসূর্য্যবর্ণ কখনও অচিরাৎ নীল, বুদ্বুদসকল, যদৃচ্ছাবশত: ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি আর একটি এইরূপে অনেক অনেক – আসন্ন সন্ধ্যায়, ক্রমে নক্ষত্র পরস্পরা যেমন দেখা যায় – দূর কোন হরিত ক্ষেত্রের হেমন্তের অপরাহ্ন মন্থনকারী রাখালের বাঁশরীর শুদ্ধনিখাদে দেহ ধারণ করত সুডৌল দ্যুতিসম্পন্ন বুদ্বুদগুলো ইদানীং উঠানামা করে, এগুলো সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী আশ্চর্য্য! এ কারণেই বিলাস, চমৎকার যাহার রূপ, যে বেশ সুস্থ্য, এখন অন্যদিকে আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল কেননা এ সকল বুদ্বুদ সম্মুখে থাকিয়াও পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু এ-দৃষ্টিতে তাহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না, এ কথা সত্য যে, তাই মনেতে নিশ্চয় সে কুণ্ঠিত কেননা ইতঃপূর্ব্বে অজস্র দিনের আত্মসচেতার কুজ্ঝাটিকার মধ্যে সে একা বসিয়া কবিতা লিখিবার মনস্থ করে – কবি হইবার নয়, যেহেতু, সম্ভবত রূপকে রূপান্তরিত না করিয়া ভালবাসার শুদ্ধতার দিব্য উষ্ণতা ক্রমে অস্পষ্ট অহঙ্কার পর্য্যন্ত, তাহার ছিল না যদিও – তাহার, নিঃসঙ্গতা নাই শুধুমাত্র স্বতন্ত্রতা ছিল। [গোলাপ সুন্দরী]
লাবণ্য দেবীর মনে সহসা নির্ভরতা আসিয়াছিল, কেননা এখন বৃষ্টি হয়; বৃষ্টি পরিবর্তনের চক্রবৎ সূত্র বৈচিত্র্যের নিত্য হেম অনেকখানির পরেও – সেখানে জানালা আছে এবং দূরত্ব সকলই বাঁকা রেখা – আর একদিকে ষোড়শী, মৌন আবেগ; ইহা অনায়াসে ঘরে আসে, ইহা কাজরী, ইহা মোহউচ্ছল, উহা ময়ূর আমোষ বাস্তবতার রূপান্তর হওয়ার বীর লহমা; এবং এই, ইহাই ধ্রুব হেনা সুক্ষতম অজস্্র সুহউদর সুকুমারী গোপনতা যেখানে ধুলা নাই। [অনিলা স্মরণে]
উপরের তিনটি উদ্ধৃতি থেকে পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারছেন কমলকুমার মজুমদার এ সময়ে এসে তীব্র বেগে বাঁক নিয়েছেন জটিলতার আবর্তে যেখান তিনি আর ফেরেন নি। শব্দ ও বাক্য ব্যবহার ছাড়াও প্রেক্ষিত নির্মাণ এবং দৃশ্য বা ভাবনা বর্ণনা করতে গিয়ে দুর্বোধ্য উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার তাঁর রচনাকে করে তোলে পর্বতপ্রতিম দুর্ভেদ্য। গল্পের মূলসূত্র খেই হারিয়ে ফেলে এ সকল কারিকুরিতে। কমলকুমারের নিজস্ব এ রীতিটাই জীবনের শেষ গল্প পর্যন্ত হতে থেকেছে আরও বেশি দৃঢ়, আরও বেশি সংহত।
তাঁর গোলাপ সুন্দরীর ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,
কমলকুমারের ভাষা একেবারেই অন্য রকম। কেন এরকম ভাষায় তিনি লিখেন, সে প্রশ্ন অনেকবার করেছি। এক এক সময় এক এক রকম উত্তর দিয়েছেন তিনি। যেমন, বাংলা গদ্যের বাক্য বিন্যাস তৈরী হয়েছে ইংরেজির অনুকরণে। কমলকুমারের মতে, যদি, বিদেশি রীতি নিতেই হয়, তবে ফরাসী বাক্ভঙ্গী অনেক বেশি কাম্য। তিনি ইংরেজি-প্রভাব অস্বীকার করে ফরাসি-রীতিতে বাংলা গদ্য লেখেন। আবার কখনও বলেছেন, হাটে-বাজারে, বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, সে ভাষায় সাহিত্য রচনা উচিত নয়। সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলা, তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন ভাষা তৈরি করে নিতে হয়।
তবে এগুলোও বোধ হয় সঠিক যুক্তি নয়। আধুনিক বাংলা গদ্য অনেকখানিই রবীন্দ্র-অনুসারী। গদ্যে এই রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর তেমন মনঃপুত ছিল না, তিনি পছন্দ করতেন বঙ্কিমের গদ্যের দৃঢ়তা এবং মনে করতেন, বাংলা গদ্য বঙ্কিম-দৃষ্টান্তেই চলা উচিত ছিল। তবুও সাধু ক্রিয়াপদ আঁকড়ে ধরে থাকলেও, কমলাকুমারের গদ্য ঠিক বঙ্কিমী গদ্য নয়, এ তাঁর নিজস্ব তৈরি করা ভাষা।
কমলকুমার ফরাসী-বাকরীতি ব্যবহার করেছেন কি না তা নির্ধারনের দায়িত্ব গবেষকের তবে তিনি যে বঙ্কিমী ধরনকে নকল করেন নি সে বিষয়ে সন্দেই নেই। তাঁর ভাষাটি সম্পূর্ণতই তাঁর নিজস্ব। সর্বশেষে দুর্বোধ্য হলেও প্রথম থেকেই তা প্রকৃত পক্ষে দুর্বোধ্য নয়। ক্রমান্বয়ে তিনি ঐ পর্যায়ে পৌছোন এবং সেটি হয় শিল্পের প্রয়োজনেই। ‘…কেউ যদি কমলাকুমারের ঐ ভাষা নকল করে চর্চা করে, কিন্তু তার ভিতর যদি কমলকুমারের অনুভূতির ঐ গভীরতা, চিন্তার মৌলিকত্ব ঐ বর্ণাঢ্যতা না থাকে, তখন শুধু ঐ language টা তাকে কি সাহায্য করবে? আসলে language টা হচ্ছে, কমলকুমার মানুষটি যা বলবার কথা, সেটা বলতে গেলে যে ভাষাটি তৈরী হয় তাই। সেজন্য ওটা একেবারে তাঁর’ (সাক্ষাতকার: হাসান আজিজুল হক, বিজ্ঞাপনপর্ব, হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৫, পৃ. ৭৩)। এমনকি কমলকুমারের এই ভাষা তাঁর জীবৎকালে যত দুর্বোধ্য ছিল বর্তমান প্রজন্মের কাছে খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতে ‘কমলকুমার পড়ে আমার যে কষ্ট হচ্ছে, আমার ছেলের তা হবে না – যদি কমলকুমারের রচনার চর্চা হয়। রবি ঠাকুরকে আজকে আমি বুঝছি। কিন্তু কালীপ্রসন্নর মতো কাব্যবিশারদ, যিনি মহাভারতের তর্জমা করেছেন, বলেছিলেন – এটা একটা পায়রা, বকবক করছে, কবিতাই হয় না। আজকে যারা কমলকুমারকে বলছে লিখতে পারেনি, আমি যদি বলি তোমরা ঠিক তাদের মতো যারা রবীন্দ্রনাথকে বোঝেনি…।’ কমলকুমারের রচনা মোটামুটি কালানুক্রমে পড়লে দুর্বোধ্যতার কুয়াশা কেটে গিয়ে তাঁর শিল্পীপরিচয় মূর্ত হওয়া সহজসাধ্য বলে মনে হয়।
ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা সুন্দরম-এর গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪০২-এ প্রথম প্রকাশিত। ২০০২ সালে প্রকাশিত লেখকের বই বাংলা কথাসাহিত্য: যাদুবাস্তবতা এবং অন্যান্য-তে (ঐতিহ্য, ঢাকা) অন্তর্ভুক্ত।


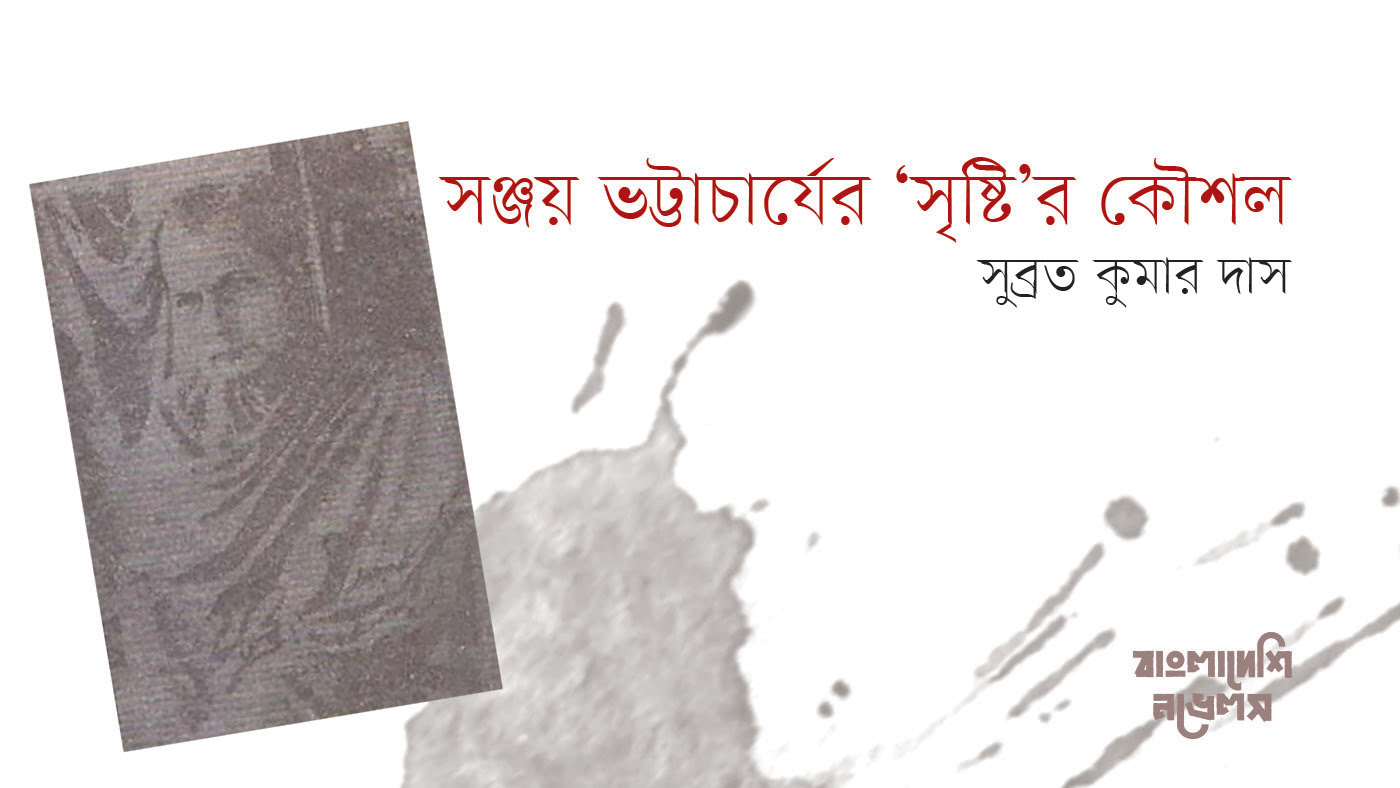






1 Comments
Debashis
কমলকুমার: রেখাব লী বইটি দেখতে পারেন। দেবাশিস তরফদার রচিত। প্রকাশক ভাষালিপি ২৪ রাজা লেন কলকাতা ৭০০০০৯