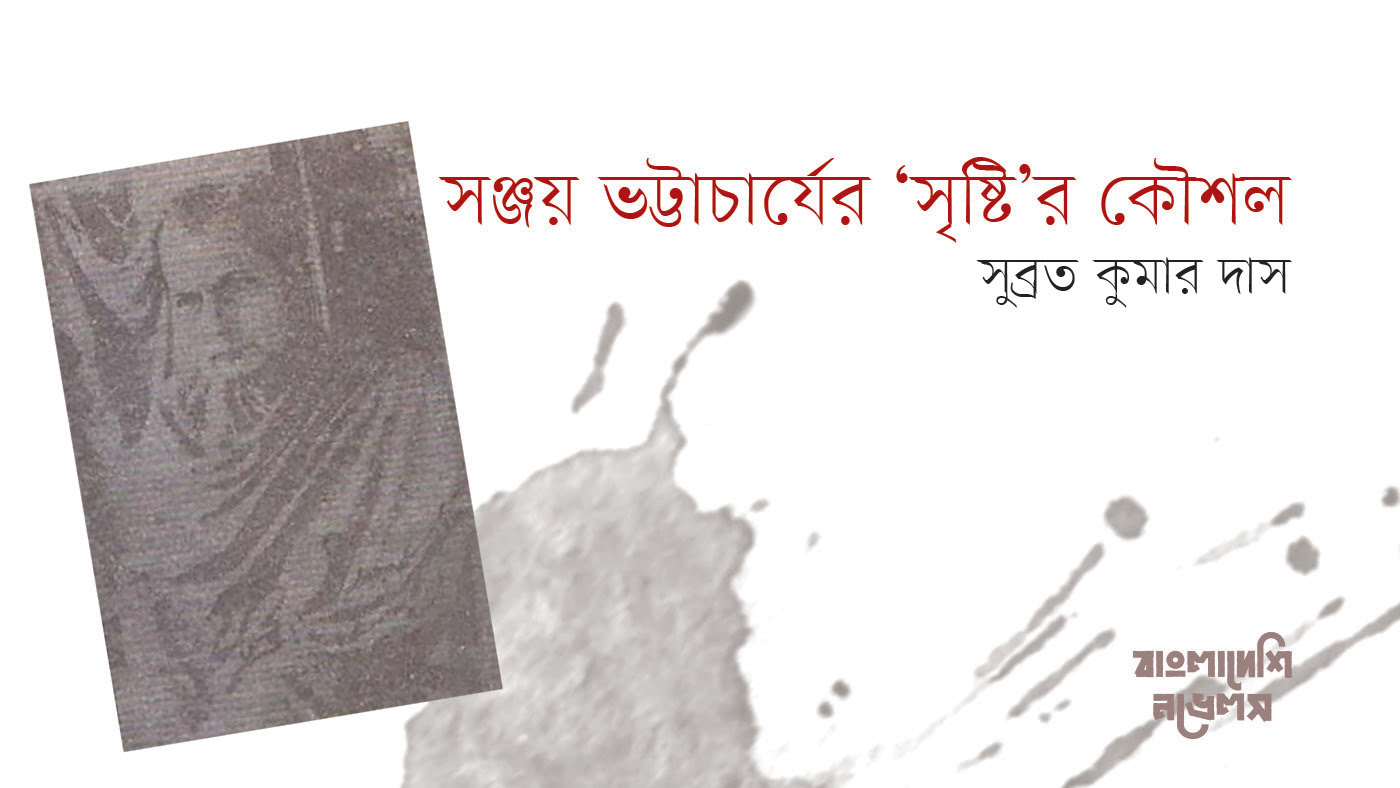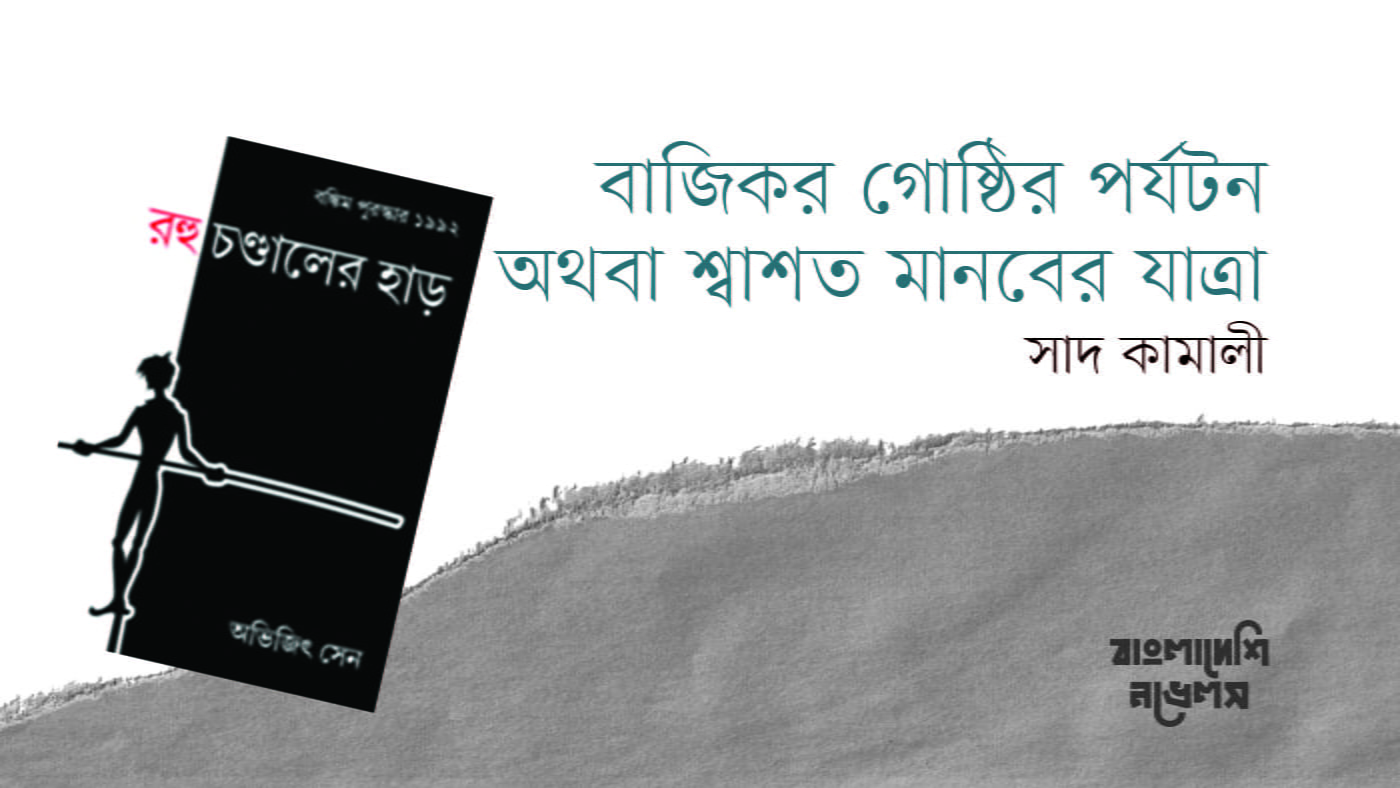‘ঘাম ঝরিয়ে’ নিজেকে ক্ষয় করে’ কী পায় মানুষ? কী পায় মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা লেখক কিংবা পাঠক? শ্রমের ওই বিস্তারে কতটুকু পাওয়া যায় জীবনের বৈভব, হৃদয়ের বৈভব? শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পড়তে পড়তে এই প্রশ্ন আসে। আর দেখি, গতানুগতিক পাঠ থেকে নয়, শ্যামলের সাহিত্যকে অনুভব করা যায় কেবল প্রাত্যহিক পাঠাভ্যাসের বাইরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে পড়তে পারার মধ্যে দিয়ে, বোধগম্যতার সঙ্গে হৃদয়ের সংশ্লেষ ঘটিয়ে। কেননা তিনি জানেন এবং পাঠককেও জানাতে চান ‘ঘাম ঝরিয়ে, নিজেকে ক্ষয় করে’ পাওয়া ভাবনা থেকে উৎসারিত হয় তার শিল্পের বিষয়আশয়। তাই গতানুগতিক পাঠ্যাভাসে তাঁকে স্পর্শ করা যায়-কিন্তু অনুভব করা সম্ভব নয় অত সহজে। শ্যামলের ভাষা আর ব্যবহৃত শব্দ আমাদের অপরিচিত নয়; কিন্তু পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে থেকেও তিনি এমন এক জীবনপ্রবাহে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকেন যে, পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দের সমবায়ে গড়ে ওঠা বাক্যের অর্থও পাল্টে যেতে থাকে। জীবনপ্রবাহের ওই ধারায় যুক্ত করে তিনি আমাদের প্রাণিত করেন শব্দ ও বাক্যের প্রচলিত অর্থবোধকতার বাইরে দাঁড়াতে এবং সহজের মধ্যে থেকেও দুর্বোধ্যতার আরোহী হতে। তখন আমরা অনুভব করি, নিয়ম ভাঙতে প্রলুব্ধ করছেন তিনি, যেমন করেছিলেন কৃত্তিবাসের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। কৃত্তিবাস তখন মধ্যগগণের গণগণে সূর্য, আর সুনীল তার নিজের বিবেচনাতেই ‘বেশ কঠোর সম্পাদক’। ২০০১ সালে বিভাব–এ ছাপা হওয়া ‘অতিজীবিত শ্যামল’ নামের এক নিবন্ধে সুনীল লিখেছিলেন, প্রবন্ধ ছাড়া গল্প কিংবা অন্য কোনও ধরণের গদ্য ছাপানোর ক্ষেত্রে খুব কঠোর ছিলেন তিনি, কৃত্তিবাসের প্রথম দিকে কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না। ওই সিদ্ধান্ত ভাঙতে নারাজ ছিলেন তিনি। কিন্তু সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। সুনীল বাধ্য হয়েছিলেন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে, যেমন পাঠক হিসেবে আমরাও বাধ্য হই ব্যতিক্রম ঘটাতে, আমাদের ধরাবাধা জীবনের বাইরে অপর এক জীবনপ্রবাহের উল্লাস ও টানাপোড়েনকে নিজেদেরই ভাবতে এবং সেই জীবনে ভেসে যেতে। শ্যামলের বেশ কয়েকটি লেখা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সুনীল। লেখার দুর্বলতার কারণে নয়, নিয়ম মেনে চলার তাগিদ থেকে তা করতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু তারপরও শ্যামল অভাবনীয় চমৎকার এমন সব গদ্য সুনীলকে শোনাতে থাকেন যে শেষ পর্যন্ত সুনীল প্রলুব্ধ হন সেরকম গদ্য ছাপানোর কৃতিত্বের ভাগীদার হতে। এরকম প্রকাশনায় বন্ধুদের আপত্তি থাকলেও নিয়ম তাই চুলোয় যায় এবং কৃত্তিবাসে ছাপা হয় রম্য রচনা, ছাপা হয় গল্প, যেসবের শুরু শ্যামলকে দিয়ে।
বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সেই গল্প, যা দিয়ে কৃত্তিবাসের ওই নিয়ম ভাঙার শুরু। কিংবা আমাদেরও শুরু নিয়ম ভেঙে পড়ার, প্রাত্যহিক পাঠাভ্যাসের বাইরে গিয়ে পড়ার। ডায়েরির এলোমেলো পাতা থেকে, টাটার সাফল্যের কাহিনী আর চিত্রিত পৃষ্ঠার পাশে উদ্বাস্তু অথচ লম্বা কাপড়ের গাজিয়াভর্তি ১০ টাকার নোট নিয়ে যাওয়া মানুষের হিজিবিজি লেখা থেকে আমরা বিদ্যুৎচন্দ্র পালকে উদ্ধার করতে থাকি বিবিধ সংকেতের মধ্যে দিয়ে। আর দেখি, কী করে একজন মালিক হয়ে পড়ে কর্মচারী। দেশবিভাগ যাকে উদ্বাস্তু করতে পারেনি, দেখি, নতুন স্বাধীন একটি রাষ্ট্র কী করে তাকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলে।
একেবারে কম লেখেননি শ্যামল। উপন্যাসই আছে তার প্রায় ৭৫টি, গল্প আছে আড়াইশ’রও বেশি। প্রতিদিন কতকিছুই তো পড়া সম্ভব, কিন্তু শ্যামল তার লেখার মধ্যে দিয়ে আমাদের ক্রমাগত হাতছানি দেন সেই জীবনের দিকে, যা আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তারপরও আমরা অপরিচিত সেসব জীবনের সঙ্গে, অপরিচিত সে জীবনের অভিজ্ঞতা ও দিনযাপনের সঙ্গে। সর্পবিষের বিচ্ছুরণে তিক্ত থেকে তিক্ততর হতে হতে রহস্যময় শ্যাওলা পড়েছে সেই জীবনের গায়ে। দিব্যজ্ঞানীর মতো শ্যামল সেই শ্যাওলার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া আনন্দ আর নিরেট তিক্ততা তুলে এনেছেন। অনেক চড়াইউৎরাই পেরুনোর মধ্যে দিয়ে তিনি তার আস্বাদ পেয়েছেন, তাই তার লেখাতে উঠে এসেছে বন্ধুর পথপরিক্রমার ছাপ, উঠে এসেছে পথচলার অভিজ্ঞতার নির্যাতন। উদ্বাস্তু হওয়ার কষ্ট, তারও বেশি জন্মভূমিতে অধিকার হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে তিনি থিতু হওয়ার চেষ্টা করেছেন পশ্চিম বঙ্গে। তখন যে কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স পড়তে গিয়েছিলেন, সেই আশুতোষ কলেজ থেকেও তাকে বিতাড়িত হতে হয় ছাত্র রাজনীতি করার ‘অপরাধে’। তারপর দিনের পর দিন ইস্পাতের এক কারখানাতে ইস্পাত গলানোর কাজ করেছেন তিনি। এইভাবে আড়াই বছর পর তিনি আবারও সক্ষম হন লেখাপড়া শুরু করতে। কিন্তু জীবন তো কেবল লেখাপড়ার নয়, জীবন এমন যেখানে হঠাৎ হাওয়ায় হ্যারিকেনের আলো নিভে যায় গাঁয়ের ঘরের বারান্দাতে পাতা টেবিলচেয়ারে বসে পাওনাদারের জন্যে চেক লিখতে গিয়ে। তারপর জীবনভর শুধু মনে হয়, মা এসে কি ফুঁ দিয়ে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়েছিলেন!
এই স্মৃতি, এই মনে হওয়া কোনও কল্পলোকের কল্পনা নয়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বোধহয় চম্পাহাটি পর্বের ঘটনা এটি। কলকাতার কাছে গাঁয়ের দিকে বাড়ি করেছেন তিনি। তখনও বিদ্যুৎ যায়নি সেখানে। সন্ধ্যার পর এই ঘটনা ঘটে, পাওনাদার আসে, সামনের বারান্দায় বসে হ্যারিকেনের আলোয় তার জন্যে চেক লিখতে বসেন শ্যামল, হঠাৎ হাওয়ায় হ্যারিকেন নিভে যাওয়ার আগে তিনি ঘড়িতে দেখেন সোওয়া আটটা বাজে। ঢলেপড়া অন্ধকারে কিছুক্ষণের জন্যে শ্যামলও ঘুমিয়ে পড়েন টেবিলে মাথাটা রেখে। ওদিকে তখন বৃষ্টিও নামছে। মিনিটপাঁচেক পর তার ঘুম ভেঙে যায়, তিনি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আবারও চেক লিখতে বসেন। পরদিন সকালে তিনি খবর পান, আগের রাত সওয়া আটটার দিকে আচমকা সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে তাঁর মা মারা গেছেন।
সেই থেকে বাকি জীবন শ্যামলের মনে হয়েছে, মা এসেই হয়তো ফুঁ দিয়ে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়েছিলেন।
এরকম অনেকরকম মনে হওয়া, মনে হওয়ার মতো সত্যকথা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে সারা জীবন তাড়িয়ে ফিরেছে। আর কেবল শ্যামল তো নয়, তার পাঠক হওয়ার যোগসূত্রে এখন আমাদেরও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দরিদ্রতারই চালচিত্র আঁকেন তিনি, কিন্তু দরিদ্রতা নয়, দরিদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রামও নয়, মানুষের জীবনের ঐশ্বর্য যে অন্য কোনওখানে, মানুষের জীবনের সেই ঐশ্বর্য যে বার বার অবসাদের মধ্যে দিয়ে ফিরে ফিরে আসে, সে কথাই জানান তিনি নানা রূপে, নব নব রূপে। কখনও নিজস্ব জীবনের আখ্যান দিয়ে, কখনো বা তার সাহিত্য দিয়ে। জীবনের নির্জন হয়ে পড়া, রাতের নীরবতা মাখা পথগুলোর ছায়াচ্ছন্নতা খুঁজতে খুঁজতে শ্যামলের গল্পের মানুষগুলো মরবিড হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও সেই মানুষগুলোর দিকে আমাদের তিনি ফিরে তাকাতে বাধ্য করেন রুদ্ধশ্বাস, সহজ আঁকুতি দিয়ে। তিনি আমাদের ওপর জোর করেন না, তিনি আমাদের তাকাতে বাধ্য করেন উদ্বেগ জড়ো করে। বন্ধুদের মধ্যে থেকেও বন্ধুহীন হয়ে পড়ার কথা, পৃথিবীতে থেকেও অন্য এক পৃথিবীর গভীর গহনে বাস করার কথা শোনান তিনি, যেমন শুনিয়েছেন তিনি তার উপন্যাস নির্বান্ধব-এ। ইস্পাত কারখানায় কাজ করার অভিজ্ঞতা এখানে আছে অবশ্য, কিন্তু তারপরও নির্বান্ধব অভিজ্ঞতাভিত্তিক লেখা নয়, অভিজ্ঞতা এ উপন্যাসে এসেছে অতৃপ্তির অনুষঙ্গ হয়ে, অভিজ্ঞতা ও সাফল্য শ্যামলের মানুষদের পরিতৃপ্ত করে না, বরং আরও বেশি নিঃসঙ্গ করে তোলে। নির্বান্ধব সেই নিঃসঙ্গতার কাহন। যদিও উপন্যাসের শুরুতেই তিনি লেখেন, ‘সব চরিত্রই কাল্পনিক’, কিন্তু তা হয়ে ওঠে চোরের সাক্ষী গাঁটকাটার মতো, আর সেটিকে তিনি আরও পাকাপোক্ত করেন তারপরেই এইসব বাক্যগুলি লিখে, ‘একদিন গভীররাতে সুনীলের- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায় ‘…আতর গোলাপ/সাবান খরচ প্রত্যহ’ শুনেছিলাম।’
বুকের দু ইঞ্চি নিচেই আত্মার নীলচে আলো জ্বলতে দেখা নিবারণ পাকড়াশি অনেককেই চেনে, জানে; কিন্তু তাদের কেউই বন্ধু নয় তার। স্ত্রীর মধ্যে সে বন্ধুকে খুঁজে ফেরে, কিন্তু স্ত্রী বার বার কেবলই স্ত্রী হয়ে যায়। আর নিবারণ মনে মনে নিজেকেই বলে চলে, ‘আমার যে আর ভালো লাগে না। ছেলেমেয়ে, বাড়িঘর, বউ-সব নিয়ে যে আমি নগর বসিয়েছি। আমাদের গরম কাপড়ের ট্রাংকে তুমি ন্যাপথালিন রাখো ফি’বছরে। এর পর আর পারা যায়?’ নিবারণ মদ খায় নিরুপায় হয়ে, পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে বন্ধুতা খুঁজে পেতে। কিন্তু বন্ধুরাও তার আর বন্ধু হয় না। ‘নির্বান্ধব’কে কি তা হলে বিচ্ছিন্নতার গল্পই বলব, যেখানে অবসাদগ্রস্ত নিবারণ একা একা ভেবে চলে, স্ত্রী রেবাকে সে একটা অনুরোধ কোনওদিনও করতে পারে নি, ‘একখানা স্টেনলেস স্টিলের চামচ ওর বুকের ভেতর বসিয়ে দিয়ে সুধা, ভালোবাসা বা আত্মা অর সোল, যাই হোক-তাই খানিকটা আমি ওপরে আলোয় তুলে এনে দেখার ইচ্ছে রাখি। মানে রাখতাম। কিন্তু কোনওদিন তা করা হয়নি।’ নিজের কাছে স্বীকৃতি দিয়েছে সে, বউকে তার ‘…গলা টিপে মেরে ফেলার ইচ্ছে হয়েছে। পরে আবার ভীষণ কষ্টও হয়েছে। অথচ তুমি কিছুতেই আমার বন্ধু হলে না। হবার কোনও চেষ্টাই ছিল না তোমার। কেবল বউ হয়েই থাকতে ভালোবাসলে। তোমার সঙ্গে মেশা গেল না। আমি মেশামেশির জন্য এক একদিন পঁচাশিটাকার ট্যাক্সি দাবড়ে কলকাতা চষে ফেলেছি-যদি কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। প্রায় দিনই হয়নি। সেসব দিন ডবল বিষণ্ন হয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছি-তখনও তুমি পুরনো কথা বলে আমাকে খুঁচিয়ে আনন্দ পাচ্ছ। আমি হুইস্কি খাই না। খেতে ভালোবাসি না। যেটুকু খেয়েছি, তার জন্য তুমি দায়ী। ইচ্ছে করলেই তুমি আমার বন্ধু হতে পারতে।’
কিন্তু রেবা বন্ধু হবে কেমন করে, যে-রেবার মনে হয়, নিবারণ দুঃখ খুঁজে বেড়াতেন! রেবার বুকের মধ্যে একটা স্টেনলেস স্টিলের চামচ বসিয়ে দিয়ে নিবারণ সুধা, ভালোবাসা বা আত্মা তুলে আনতে পারে নি, কিন্তু ঠিকই নিখুঁতভাবে টেবল্ ফর্ক বসিয়ে দিয়েছে তাকে সাফল্যের মুখ দেখানো কলিগ-বস অনিল দত্তের বুক বরাবর। কেন দিয়েছে? কেবল লতাই কি খানিকটা বুঝতে পেরেছিল? আর তাই সে বলে, ‘নিবারণের তো কোনও বন্ধু নেই। ও তো সারাজীবন এ টেবিলে সে টেবিলে বন্ধু খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে-কোথাও ওর হয় না।’ লতা যে তাকে খানিকটা উপলব্ধি করে, কিন্তু তারপরও নিবারণের কাছ থেকে সরে যেতে হয়েছে অনিল দত্তের কাছে – সেটা কি নিবারণও অনুভব করেছিল? আর তাই সে শেষ পর্যন্ত হন্তারক হয়ে ওঠে তার শুভানুধ্যায়ী কলিগ-বসের? কিংবা রেবাও কি বুঝতে পেরেছিল নিবারণের সঙ্গে তার দূরত্ব আর লতার সঙ্গে নৈকট্য, তাই লতাকে সে পাঠায় নিবারণের সঙ্গে দেখা করতে ‘উইথ দি ইনটেনশন-যদি লতা আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরাতে পারে।’ কাঠগড়ায় লতা বলতে পারে বটে, ‘তুমি তো কাউকে কোনওদিন খুন করার লোক নও।’ কিন্তু যা সে বলতে পারে না, তাও লিখে দিয়েছেন শ্যামল, ‘আমি মেয়েছেলে। আমাদের পুরুষমানুষের সঙ্গে অমন এক আধবার হয়। আমরা ঘাটের জল। ফিরে ফিরে বদল হয়ে আসি। তুমি কেন অনিল দত্তের জন্যে বরবাদ হবে। টেক ইট ইজি।’ এইখানে এসে টলোমলো জলরেখা কি খানিকটা স্থির হতে থাকে, তাই খানিকটা স্পষ্ট আভা ফুটে ওঠে – যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল, তার হাতবদল হয়েছিল! কিন্তু তাই কি সব? তা হলে কেন নিবারণের মনে হবে যে, ‘শরীর ধরে এগোলে তবে ভালোবাসাবাসি হয়। তাই তা এত ঠুনকো। অথচ শেষ অব্দি ভালোবাসাবাসির পথে এই শরীরখানাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।’ তা হলে নিবারণের কেন মনে হবে, যে বিরাট তুঁতে গাছের ছায়ায় সে আর মৃত অনিল দত্ত বসে আছে তার পত্রস্পন্দন, তার ছায়াচ্ছন্ন নিবিড়তার মধ্যে সে খুব মূল্যবান একটা চাবি খুইয়ে বসে আছে, যে চাবি থাকলে মৃত অনিল দত্ত আজই এখনই নিবারণের হাত ধরে লোকালয়ে চলে যেতো।
নির্বান্ধব-এর লেখক হিসেবে যদি ‘আলব্যেয়ার কামু’ বা এরকম কোনও নাম লেখা থাকত, তা হলে তা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হতো, চায়ের কাপে ঝড় উঠতো এবং সংস্করণের পর সংস্করণ হতো। কিন্তু লেখক তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, তাই নির্বান্ধব নিয়ে আলোচনা হয় না! অবশ্য আমাদের রশীদ করিম এ বইটি নিয়ে অক্টোবর ১৯৭৩-এ ‘দৈনিক বাংলায়’ একটি আলোচনা লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ‘উপন্যাসটিতে কামুর দি আউটসাইডার-এর প্রভাব আছে, এবং ‘নির্বান্ধব’ নামেই বোঝা যায়, লেখকের তা গোপন করবার এতটুকু ইচ্ছে নেই। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু এইটুকুই দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, কিভাবে সম্পূর্ণ মৌলিক উপন্যাস রচনা করতে হয়।’ এই আলোচনা যত প্রশংসাময়ই মনে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত নির্বান্ধব-এর জন্যে ভালো হয় নি। তাতে অবশ্য শ্যামলের কিছু আসে যায়নি। তিনি নিজে বিচ্ছিন্নতা ও অবসাদের নির্মেদ একটি ধারাবাহিকতা তৈরি করতে পেরেছেন তার বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য নির্বান্ধব-এরও অনেক আগেই কুবেরের বিষয়আশয় থেকে শুরু হয়েছে ওই বিচ্ছিন্নতা। এবং কুবেরের বিষয়আশয় বেশ স্পষ্টই বলে দেয়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্লীন বিচ্ছিন্নতা কাম্যুপ্রভাবিত হওয়ার চাইতে নিজস্ব অর্জন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। স্বর্গে তিন পাপী বলি আর হিম পড়ে গেল যেটার কথাই বলি না কেন, তাতেও রয়েছে বিচ্ছিন্নতার ওই ধারাবাহিকতা। এমনকি পরস্ত্রীর শেষ মুহূর্তে আমাদের চোখের নিচের ভাগে আশার সামান্য আলো জ্বললেও পুরো উপন্যাসে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতাই খেলা করে। ফিরোজা তার সদ্য স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের আখ্যান, যেখানে পাওয়া যায় স্বাধীনতাউত্তর টাটকা বাংলাদেশকে। কিন্তু সেখানেও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে আমরা যে ভবিষ্যৎ জেগে উঠতে দেখি, লেখক হিসেবে তা শ্যামলের শক্তিমত্তার পরিচয় দিলেও রাষ্ট্রের নাজুক উত্তরকালেরও ইঙ্গিত দিতে থাকে। রশিদকে বাঁচানোর জন্যে যে আয়োজন মুক্তিযোদ্ধার সংগঠক, আওয়ামী লীগের এম এল এ লতিফের স্ত্রী ফিরোজা করতে থাকে, ভারতবিভক্তির কারণে উদ্বাস্তু হয়ে চলে যাওয়া খোকনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কিংবা বিধ্বস্ত দেশের চেহারার আন্তরিক বয়ানও তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে না। লতিফ বাসায় নেই, রাজাকার রশিদকে বাঁচানোর জন্যে গভীর রাতে খোকনকে নিয়ে ফিরোজা চলে যায় গল্লামারির খাল পেরিয়ে হাড়গোড় ছড়ানো মাঠে। তখন মুক্তিযোদ্ধা ছেলে কয়েকজনকে দেখে খোকনের অনুভূতি চিন্তা করার মতো, ‘আস্তে আস্তে মনও খারাপ হয়ে উঠল। এদের কি হবে? এই এরা? কে সামলাবে? মুজিবের কোনো খবর নেই এখনো।’ এদের দেখে তার মন খারাপ হলেও এমএলএ লতিফের স্ত্রী হওয়ার অধিকারে ফিরোজার আবেগি গলার জেরাকে অবশ্য অসঙ্গত মনে হয় না তার।
তাই বলে অজ্ঞান মানুষটাকে সারা মাঠ ছেচড়ে টেনে যাবে জীপে বসে বসে, তোমরা কি? তোমরা কি? ফিরুর গলা বুজে এল।
জাফর টং করে লাফিয়ে উঠল, শেফালির দিদিকে কি করেছিল ওরা? জিজ্ঞেস করুন না। ভাদ্দর মাসের দুপুর বেলায়, ঠিক বারোটায় ডাকবাংলোর মোড় থেকে বিমলাদিকে লরির পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে স্টেশন অব্দি ফুলস্পীডে চালায়নি, আমি রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এটা এখন অর্থহীন বোঝা মাত্র।
ফিরু দেখলাম জাফরদের বাড়ির সবাইকে চেনে, তোর বাপকে গিয়ে সব বলছি।
তেনারে পাবেন কোথায়! নভেম্বরের বারো তারিখ ওই রশিদের খালু আর ফুপারা সবাই মিলে চাঁদমারি করিছিল,
এখান থেকেই দেখলাম, ফিরু ছোট করে ওঃ! বলেই ঢোঁক গিলল।
তারপরও সেই রশিদকে আর মারা হয় না, মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মারতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে, যুদ্ধের ঘোরে থাকা প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি মানুষ এখন জেগে উঠতে শুরু করেছে নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সেই আকাঙ্ক্ষার কাছে দেশের কোনও গুরুত্ব নেই, আছে কেবল অবনত হওয়ার অধিকার। ‘যদি বেঁচে ওঠে আমরা আবার তুলে আনব’ বলে চলে যেতে হয় জাফরদের। ফিরোজাদের বাঁচিয়ে রাখা সেই রাজাকারদের এখনও টানতে হচ্ছে বাংলাদেশকে, আর জাফররা দূরে সরে যাচ্ছে, ফের চেষ্টা করছে তাদের তুলে আনতে।
সুখি কোনও মানুষের কথা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের কখনো শোনাতে পারেননি তার গল্পের মধ্যে দিয়ে। শোনাতে চেয়েছিলেন কি? তাও তো মনে হয় না। তিনি শুনিয়েছেন তেমন সব মানুষের কথা যারা অতৃপ্তির মধ্যে দিয়ে জীবনের গভীর এক আস্বাদ নিতে থাকে-যেমন নিয়েছে কুবের, শ্যামলের সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ কুবেরের বিষয়আশয়-এ। শাহজাদা দারাশুকো আর আলো নেই লেখার মধ্যে দিয়ে শ্যামল চেষ্টা করেছেন বৃহৎ এক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইতিহাসকে পুনর্নিমাণ করতে, সেদিক থেকে ও দুটো অবশ্যই বড় উপন্যাস। কিন্তু তার একটিমাত্র উপন্যাসের কথা তুললে মানুষ বোধহয় কুবেরের বিষয়আশয়-কেই বেছে নেবে। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও মানুষ কীভাবে তার স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় কুবের তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তারপরও আমরা দেখি, কুবেরের বিষয়আশায় আসলে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আখ্যান নয়, দারিদ্র্য এখানে কুবেরের প্রধান শত্রু নয়, তারও বড় শত্রু কুবেরের নিয়তি-ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের রাতে জন্ম নিয়েছে সে, তাই মৃত্যুর গায়ে মাথা রেখে শোয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে তাড়িয়ে ফেরে নানা বিপর্যয়। দেবেন্দ্র লাল সাধু খাঁর পারিবারিক বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র এক কুবেরকে জেগে উঠতে দেখি আমরা। আভা আর বুলুর চেয়েও বড় তার অন্য কোনও টানাপড়েন- পুরুষের নিজস্ব স্বপ্নই কি তৈরি করে সেই টানাপড়েন? দ্বীপের যে স্বপ্ন কুবের দেখে, তা কি তাকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারে? যদিও মনে হয়, ওই স্বপ্নের আবেগেই সে কেড়ে নিয়েছিল আভাকে ব্রজের কাছ থেকে আর তাকে রেখে দিয়েছিল তার স্বপ্নের দ্বীপে। যেখানে শুধু স্বপ্ন নয়, গোখরোও আছে। আভাকে সে হত্যা করে, কিন্তু তাকেও মরে যেতে হয় ওই উদ্যত গোখরোর ছোবলে। কুবের মরে যায়, মৃত্যুর আগে ব্রজকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় রেলেশ্বরের শিব। কিন্তু সে কি নিজেও প্রস্তুত ছিল সেই মৃত্যুর জন্যে? না আভাকে হত্যা করা থেকে শুরু করে শিব ফিরিয়ে দেয়ার আয়োজন, সবই সেই মৃত্যুকে পরাস্ত করবার জন্যে? কুবেরের ছায়াই কি পড়ে না নির্বান্ধব-এর নিবারণ পাকড়াশির মধ্যে? তিলে তিলে তারা দু জনেই অর্জন করেছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার স্বাতন্ত্র্য ও ঔদার্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুবেরকে ঘুমিয়ে পড়তে হয়। ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিভ্রমের এক জগতে ঘুরতেই থাকে সে। নস্টালজিয়া, অবসাদ, সম্পর্কের গভীর আস্বাদ সব কিছুই ভিড় করে তার উপন্যাসে। বুলু ছুটতে থাকে কুবেরের পিছু পিছু যেন বা রক্তগলিত পুঁজের মধ্যে দিয়ে, আগলে রাখার পরম সুপ্ত ইচ্ছে নিয়ে। কুবের যখন তার স্বপ্নের দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়, বুলু যখন স্নান করতে থাকা কুবেরকে দেখতে দেখতে ভাবে, ‘চাষবাসে এত বড় একটা মার খেয়েও লেকাটা গান গায়’ তখন আপনাআপনিই আমাদের মনে পড়ে যায় শ্যামলের জীবনের চম্পাহাটি পর্ব। কি উপন্যাস, কি আত্মস্মৃতি সবখানেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জড়িয়ে থাকেন নস্টালজিয়ার ফাঁদে-জীবনের যাবতীয় তিক্ততা মহৎ মাত্রা পায় তার ওই নস্টালজিয়ার গুণে, আর আচানক বেরিয়ে আসা এক সাপের বিষের বিচ্ছুরণে।
জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখার বিষয়আশয়ের এইসব যোগ ও রূপান্তরযজ্ঞ আত্মস্থ করেই বোধহয় শ্যামল লিখেছিলেন,
নিজের জীবন, শরীর, সম্মান, অস্তিত্ব, নিরাপত্তা বার বার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মত বিপজ্জনক জুয়ায় তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে উঠে ঢেউয়ের ফেনায় যেটুকু খড়কুটো ধরা যায়, সেটুকুই শিল্প। নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে যা জানা যায়তা শুধুই জানা যায়-বোধিও বটে। এই বোধিকে আমি এভাবে বলি যে চিন্তা ঘাম দিয়ে আয় না হয়-সে চিন্তার কোনও দাম নেই।
ঘাম ঝরিয়ে-নিজেকে ক্ষয় করে যে ভাবনাকে পাই তাই হোক শিল্পের বিষয়।
এবং সারা জীবন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সে চেষ্টাই করে গেছেন। নিজেকে ক্ষয় করে করে চারপাশের জীবনকে গ্রন্থিত করেছেন তিনি। আবার পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এ-ও লিখেছেন,
আমাকে আমার পাঠক তৈরি করতে করতে এগোতে হয়েছে। তাঁরা আমাকে চেনেন। আমিও তাঁদের চিনি। গল্পের বেলপানা দিলে তাঁরা ওয়াক থু করে ফেলে দেবেন। আমাকে তাই মাঝে মাঝে এক চামচ মহাকালের জিজ্ঞাসা, দু চামচ জীবনরহস্য, কে যেন সাতসকালে যেকে ছিল-ইত্যাদি জিনিস লেখার ভেতর গুঁজে দিতে হয়। এই মিশেল গোজামিল হয়ে দাঁড়াতে পারে-যদি না তা আমার শরীর ও মনের ভেতর দিয়ে চোলাই হয়ে আসে।
নিজেকে বারবার বকযন্ত্রের ভেতর তরল করে ঢালি। বাষ্পে, অশ্রুতে একাকার হয়ে পরিণামে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়ি। এই পাতন প্রণালী আমার সারা লেখায় ছড়িয়ে আছে।
এরকম লেখা বেশি লেখা যায় না। সেই কম-লেখাও আমি লিখে উঠতে পারছি না।…
আত্মজীবনকেন্দ্রিক লেখা ‘এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি’র এক স্থানে শ্যামল লিখেছিলেন,
সময়ের দূরত্বে সাধারণ কথাই রূপকথা হয়ে যায়। জীবনে কেউ তো আর বিশিষ্ট হওয়ার জন্য গুছিয়ে ঘটনা ঘটায় না। বহতা নদীর মতই জীবনটা নাচতে নাচতে ঢেউ তুলে কালের তীর ধরে কথা-কাহিনী ছড়াতে ছড়াতে বয়ে যায়।
আমাদেরও তাই মনে হয়, আমরাও তাই ভাবি। কিন্তু শাদা চোখে আরও যা দেখি, তা হলো সময়ের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আগেই আমাদের চারপাশের সাধারণ কথাগুলোকে, সাধারণ জীবনগুলোকে তিনি রূপকথা করে তুলেছেন। এইখানে তিনি ত্রিকালদর্শী। কুবের থেকে শুরু করে নিবারণ পাকড়াশি, বিপিনচন্দ্র পাল, সন্তোষ, আশু, দাক্ষী কিংবা তার গল্পে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা আরও সব জীবনজাগানিয়া সাধারণ জীবনগুলো সেই রূপকথার জনক। মা যাকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকারে ঘুম পাড়িয়ে দেন মৃত্যুর আগে ফুঁ দিয়ে হ্যারিকেন নিভিয়ে, সেই শ্যামল জীবনের এ গলি ও গলি মাড়াতে মাড়াতে যেসব জীবন কুড়িয়ে পান, কুড়িয়ে নেন তার সবই কেমন স্বল্প সময়ের দূরত্বেও রূপকথা হয়ে যায়।
আর আমরা সেই রূপকথার সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকি, শুনতে থাকি।