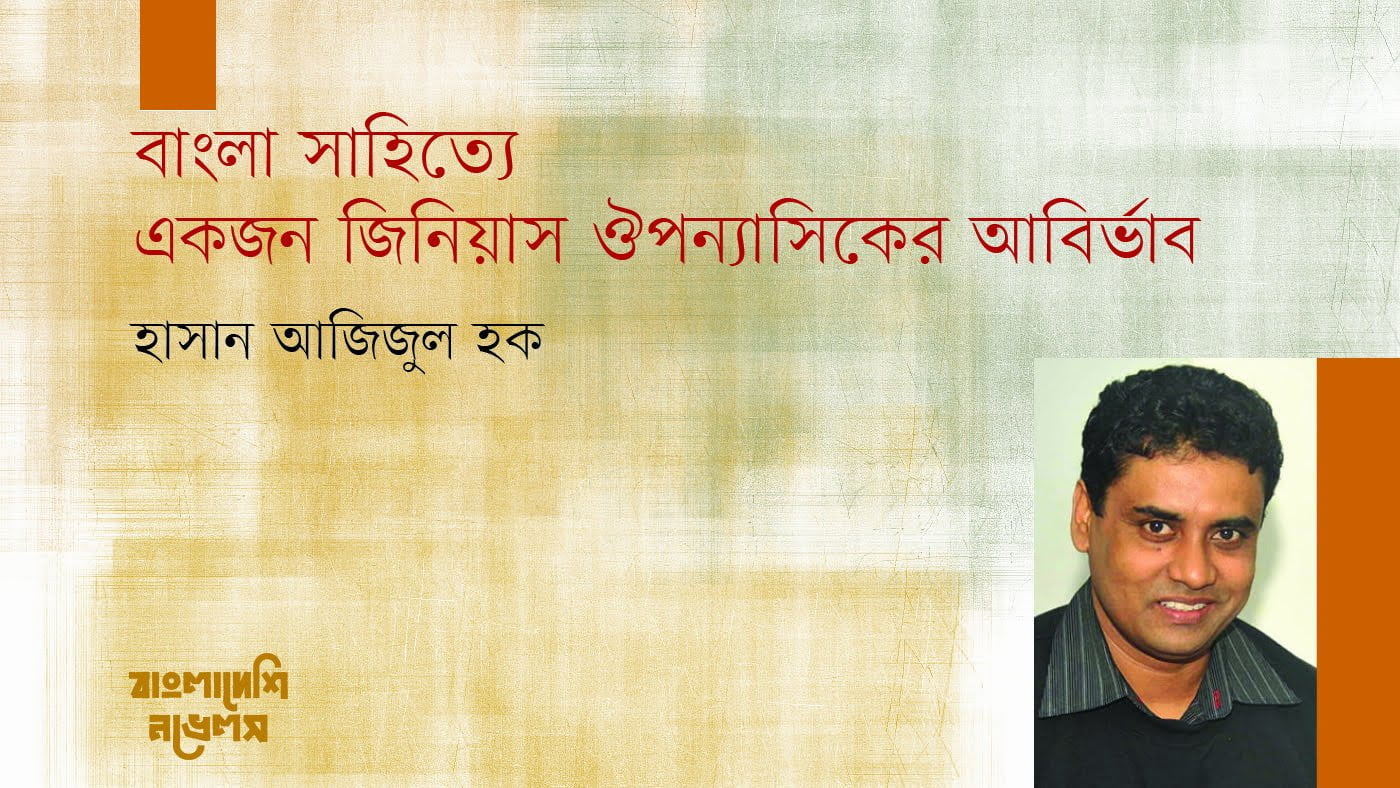হয়তো এমনি বলা অত্যুক্তি হবে না যে হুমায়ূন আহমেদ (জন্ম ১৯৪৮) বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) চেয়েও তিনি বেশি জনপ্রিয় কি না তা হয়তো গবেষণার দাবি রাখে তবে হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা যে কোন বাংলাভাষী সাহিত্যিকের জন্য বিস্ময়ের তাতে কোন সন্দেহ নেই। গগনচুম্বী এ জনপ্রিয়তা এর লেখককে অর্থসুবিধা দিলেও সাহিত্য সমালোচককে যে কী অসুবিধায় ফেলেছে তা অননুমেয়। হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার বড় সমস্যা হল তাঁর রচনার দীর্ঘ তালিকা। সমস্যাটি তীব্রতর হয় যেহেতু আমার অভিজ্ঞতা বলছে তাঁর ভক্তদের কাছে তাঁর রচিত কোন উপন্যাসই সামান্য কমও ভাললাগার নয়। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা যাঁরা কাগজে কলমে করেন তাঁদের মধ্যে দু’একজনের বেশি সমালোচককে পাওয়া যাবে না যিনি ‘নন্দিত নরকে’ এবং ‘শঙ্খনীল কারাগার’-এর পরের জনপ্রিয় হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য কমবেশি পড়েছেন বা স্মরণে রেখেছেন। শ’দেড়েক হুমায়ূন তালিকা থেকে দশ পরেনটি বেছে নিয়ে বর্তমানের অসম্পূর্ণ আলোচনাটি দাঁড় করানো হয়েছে। হয়তো নির্বাচনটি যথাযথ নয়, কিন্তু একজন লেখকের বই-এর সংখ্যা হিসেবেও দশ/পনেরটি নিশ্চয়ই হেলাফেলারও নয়।
খেয়াল করা যেতে পারে যে শুরু থেকেই সাহিত্যিক জীবনে হুমায়ূন আহমেদ পাঠককে আকর্ষণে সক্ষম। প্রথম দুটি উপন্যাস ‘নন্দিত নরকে’ (১৯৭২) ও ‘শঙ্খনীল কারাগার’ (১৯৭৩) 1 (যদিও দ্বিতীয় উপন্যাসটিই প্রকৃতপক্ষে হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস) সাহিত্যিকভাবে নন্দিত হলেও, এর কিছু পর বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার কারণে দীর্ঘ বিরতি ঘটে তাঁর কথাসাহিত্য রচনায়। দেশে ফেলার পর তাঁর সাহিত্য যে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল তাঁর মাত্রা এত বিপুল যে হুমায়ূন খুব দ্রুতই তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যসেবীদের ঈর্ষার কারণে বিরূপ সমালোচনার শিকার হয়ে পড়লেন। শ’দেড়েক গ্রন্থের জনক জনপ্রিয় হুমায়ূন আহমেদের এই কালিমা পরবর্তী বিশ বছরে সামান্যতম হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে।
এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘দূরে কোথায়’ (১৯৮৭) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কথাসাহিত্যিক ওসমান সাহেবের কিছু কিছু অনুষঙ্গকে আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ উপন্যাসের ‘ভূমিকা’-শব্দবিবর্জিত ভূমিকাতে হুমায়ূন আহমেদ উপন্যাসটি ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হবার ইতিহাস টেনে একসময় বলেছেন: ‘লক্ষ্য করলাম এই উপন্যাসে আমি নিজের কথাই বলতে শুরু করেছি। সব লেখাতেই লেখক খানিকটা ধরা দেন কিন্তু এ রকম নির্লজ্জভাবে দেন না।’ 2 এ উপন্যাসেরই আরেক সাহিত্যিক চরিত্র নবী যখন তাঁর প্রেমিকা মনিকাকে ওসমান সাহেবের লেখা সম্পর্কে বলে ‘পাঠযোগ্য লেখা মানেই ভাল লেখা না’ 3 বা ওসমানের প্রশ্নে ‘আপনি কি আমার কোন লেখা পড়েছেন?’ নবীর উত্তর হলে: ‘সেন্টিমেন্টাল লেখা আমি পড়ি না। আপনার একটা লেখা পড়তে চেষ্টা করেছিলাম, মেয়েলী জিনিসে এমন ঠাসা যে গা ঘিন ঘিন করে। মেয়েদের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়।’ 4 অর্থাৎ যারা পড়ে না তারাই ওসমানের উপন্যাসের সমালোচনা করে এমন ভাবনা হুমায়ূন আহমেদের নিজেরও বটে। ‘আপনি বোধহয় আগের চেয়ে বেশি সমালোচনা সহ্য করতে পারেন’ – বাংলাবাজার পত্রিকার পক্ষে ব্রাত্য রাইসুর এ প্রশ্নের জবাবে হুমায়ূন এক সময় বলেছিলেন: ‘একজন লোক কোনকিছু পড়েও নি আমার, অথচ তিনি সমালোচনা করতে বসলেন আমার, এটা তো হতে পারে না।’ 5 একজন তরুণ কবি বা গল্পকার দূরে কোথায় উপন্যাসে ওসমানকে প্রশ্ন করে ‘ইদানিংকার লেখাগুলি মনে হয় পপুলার ডিমান্ডে লেখা। তেমন ডেপথ নেই’ এবং ওসমানের কয়েকটি প্রশ্নের পর যখন স্পষ্ট হয় ছেলেটি ওসমানের সাম্প্রতিক বই পড়ে নি তখন ওসমানের বক্তব্য ‘না পড়ে মন্তব্য করা ঠিক না’ 6। সমালোচনা সহ্য করতে না পারার হুমায়ূনের এ ব্যাপারটি বহুজন বিদিত। ‘ভোরের কাগজ’ সাময়িকীতে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম একবার লিখেছিলেন ‘হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখি নিয়ে কোন মন্তব্য করা একটু বিপদ্দজনক এজন্য যে, আমার মনে হয়েছে, তিনি সমালোচনা পছন্দ করেন না।’ ঐ একই দিনের পত্রিকায় সাজ্জাদ শরিফ ও উনাদিত্য রায়কে হুমায়ূন যখন বলেন: ‘যে পড়ে সমালোচনা করে তার সমালোচনা, কষ্ট লাগলেও, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি।’ 7
সমালোচনার ব্যাপারে অসহিষ্ণু হুমায়ূন আহমেদের এ সকল কথার অবতারণা এজন্য যে দিন দশেকে একটি সমালোচনা লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর গোটা পনের উপন্যামস পাঠপর আমার ভাবনাগুলোকে কেমনভাবে গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে আমার নিজের মধ্যেও সংশয় রয়েছে।
যে সকল সমালোচক হুমায়ূন আহমেদের প্রথম দুটি উপন্যাসকে গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট দিয়ে বাকিগুলোকে ‘ট্রাস’ বলে অভিহিত করতে চান তাঁদের অভিমতকে যুক্তিতর্কহীনভাবে মেনে নেয়া কষ্টকর। এ সকল অভিমতের পেছনে ‘নন্দিত নরকে’-র প্রথম প্রকাশকাল ড. আহমদ শরীফের ভূমিকাটির 8
একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। তাছাড়া এমন একটি সাধারণ সমীকরণে হয়তো পৌঁছানো অসম্ভব নয় যে ঐ সকল সমালোচকেরা নিজেরাও তখন কৈশোর উত্তীর্ণ ঢাকার শহুরে যুবক যাদের কথা হুমায়ূন বলেছেন, এবং প্রথমবারের মত হুমায়ূনই বললেন এবং একটি বিশেষ ভঙ্গিতে বললেন যেখানে জীবনের কথাকেই সাবলীল এবং প্রীতিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদি বাংলাদেশের পাঠক সমাজের ইতিহাস এবং বিবর্তনের ব্যাপারটি আমাদের বিবেচনায় রাখি তাহলে দেখব হুমায়ূন এখনও ঢাকার সাতে সম্পর্কহীন অজগ্রামের পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেন নি – না, সেখানকার টিনএজারদেরকেও খুব বেশি নয়। কেননা তাদের যে চতুর্পাশ বা জীবনবোধ তা হুমায়ূনের উপন্যাসে অনুপস্থিত। ‘নন্দিত নরকে’ বা ‘শঙ্খনীল কারাগার’ তো ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তের জীবনকথা – তাদের দুঃখ-বেদনা, পাওয়া না পাওয়ার কথা। আর সেজন্যই স্বাধীনতাত্তোর পর্যায়ে ঢাকার যে নাগরিক জীবন সে জীবনকে রূপায়ণের কারণেই হুমায়ূন শহুরে অনেক পাঠকেরই মন জয় করতে সক্ষম হলেন। জাতির ইতিহাসে ঘটনাক্রমটিও এমন যে আশির দশকের শুরু থেকেই ঢাকা শহরের আয়তন ও জনসংখ্যার ঘটলো ব্যাপক বৃদ্ধি। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল উন্নতির কারণে দেশের বিরাট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সাথে এ নগরের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকলো – ঢাকা শহুরে বাস না করলেও এর জীবনধারায় আগ্রহী ও পরিচিত জনগোষ্ঠীর ঘটলো ব্যাপক প্রসার। হুমায়ূনের জনপ্রিয়তারও কিন্তু প্রসার ঘটতে থাকলো উত্তরোত্তর। হয়তো পরবর্তীকালে টেলিভিশন সিরিয়ালগুলো তাঁর অগ্রসরণে ভূমিকা রেখেছে কিন্তু তাঁর লেখার ঢঙটি বলতে গেলে একই রকম হয়ে গেছে। নগর সমাজে বর্ধিত টিনএজারদের চারপাশে গ্রাম নেই, গ্রামীণ প্রতিবেশ নেই – তারা শুধুমাত্র হুমায়ূনকে চিনলেও গ্রাম-স্পর্শিত টিনএজার পাঠক তাঁর ভাললাগার তালিকায় সাধারণভাবে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বা মশাররফ হোসেনকে তাজ্য করে নি।
‘নন্দিত নরকে’ এবং ‘শঙ্খনীল কারাগার’ নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার পূর্বে হুমায়ূন সাহত্য বিষয়ক আসাদুজ্জামান নূরের একটি লেখা প্রসঙ্গ টানবো। ‘নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো মানুষ’ (‘ভোরের কাগজ’, ৪ মার্চ ১৯৯৪) শিরোনামের সে-প্রবন্ধে নূর সহজভাবে খুব সূক্ষ্ম কিছু কথা বলেছিলেন হুমায়ূনের সাহিত্য নিয়ে যেগুলো যৌক্তিকতা ও মৌলিকতার কারণে আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি হুমায়ূনের উপন্যাসে যে সব বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছিলেন সেগুলো সংক্ষেপে এমন:
১. হুমায়ূনের বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সুবিধা তা হচ্ছে, পড়ার মধ্যে একটা আনন্দ পাওয়া যায়;
২. ওর লেখার সহজ ভঙ্গি পাঠকরা পছন্দ করে;
৩. হুমায়ূনের লেখার মধ্যে এক ধরনের পাগলামো আছে… অনুভূতিপ্রবন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই পাগলামো দেখা যায়;
৪. অধিকাংশ মানুষের জীবনেই চারিত্রিক অসামজ্ঞ্যতা দেখা যায়।… আসলে একটা বিষয় সত্য যে একজন মানুষ একটি পর্যায়ে নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো একা হয়ে যেতে চায়।…
হুমায়ূনের প্রায় লেখাতেই এই নিঃসঙ্গ, একা বিচিত্র মানুষটির সন্ধান পাওয়া যায়। যে কোন হুমায়ূন পাঠক উপলব্ধি করবেন নূরের বক্তব্যগুলোকে আমার মত করে যে চারটি বিন্দুতে আমি সাজিয়েছি সেগুলোই তাঁর সকল সাহিত্যের মূল সূর হিসেবে এখনও বর্তমান। এবং সূক্ষ্মদর্শী পাঠক লক্ষ করবেন ‘নন্দিত নরকে’ থেকেই হুমায়ূনের এমন যাত্রা। ২০০০-সালে প্রকাশিত ‘শুভ্র’ পর্যন্ত সে যাত্রায় প্রসারণ ঘটেছে, ঘটেছে ব্যাপ্তি, কিন্তু যাত্রাপথটি কমবেশি অপরিবর্তিত এমন কি তাঁর মিসির আলী বা হিমু সিরিজের বইগুলো এর অন্যথা নয়; এ ধারার বাইরে যেগুলোতে ভিন্নতা রয়েছে সেগুলো তাঁর পাঠক তেমন আদরে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় না। তিরিশ বছর ধরে কথাসাহিত্য রচনায় নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনচিত্রণের এ আয়োজনে তাই প্রেক্ষাপট ও গল্পকাঠামো বারবার বদলালেও সেগুলোর বিপুল সংখ্যকই পৌনঃপুনিকতায় দুষ্ট হয়েছে – চরিত্র চিত্রণ, পরিপার্শ্ব নির্মাণ, সংলাপ এবং মনোভাবনা সৃষ্টি ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই এ ত্রুটি লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে শক্তিমান ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস সমালোচক দেবেশ রায়ের একটি বক্তব্যকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়: ‘যদি কোন লেখক কেনা একবার মেলায় গিয়ে এমন একটা লিখে থাকেন যা পাঠক ক্রেতার ভালো লেগেছিল, তখন তার কাছ থেকে ঐ মেলার লেখাই চাওয়া হতে থাকবে।… লেখককে শুধু একবার মৌলিক হবার সুযোগ দেয়া হবে। শুধু একবার। সেই মৌলিকতায় যদি সে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, তা হলে তাকে তার ঐ মৌলিকতাতেই – শেষ দিন পর্যন্ত লিখে যেতে হবে, …’ (‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৩)। হুমায়ূনের দুর্ভাগ্যটি (?) বোধহয় এ সূত্রেই গ্রথিত। দীর্ঘ গ্রন্থ তালিকায় তাঁর ক’টি মহৎ বা অন্তত উঁচুমানের এমন প্রশ্নের যথাযথ জবাব তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় বলেই ধারণা। প্রতিটি উপন্যাসকে পৃথক পৃথকভাবে বিনির্মাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়ে গেছে তাঁর উপলব্ধির বাইরে। অথচ শক্তির বহিঃপ্রকাশ তো প্রথম উপন্যাসেই ঘটিয়েছিলেন (সেটি ‘নন্দিত নরকে’ বা ‘শঙ্খনীল কারাগার’ যেটিই হোক না কেন), বিচ্ছিন্ন কোন কোন প্রয়াসেও নিশ্চয়ই এমন প্রকাশ আছে। এমন উদাহরণ ‘১৯৭১’ যা আমার গোটা পনেরর তালিকাতেই পড়ছে।
‘নন্দিত নরকে’-র গল্পটি ঢাকা শহরের সাধারণ মধ্যবিত্ত একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রথম পুরুষের বক্তা খোকার (প্রকৃত নাম হুমায়ূন) দৃষ্টিকোণ থেকেই উপন্যাসটির মানুষগুলো নির্মিত ও নির্ণিত। পাগল যুবতী বোন রাবেয়ার এক বছরের ছোট খোকা। পরিবারে মা-বাবা ছাড়াও আরো যারা আছে তারা হলো ভাই মন্টু ও তেরো বছরেরা ছোট বোন রুনু। ছোট বাসার এ সংসারটির কথা প্রথম থেকেই পাঠককে আকৃষ্ট করতে থাকে রাবেয়ার অপ্রকৃতিস্থ ভাবনা ও তার অপ্রকাশিত অশ্লীল কথাবার্তা। অশ্লীল কথাগুলো কিন্তু হুমায়ূন তাঁর প্রকাশিত প্রথম এ উপন্যাসটিতে প্রকাশ করেন নি যেমনটি তিনি আরও পরের উপন্যাসগুলোতে করেছেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা চলে, ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত ‘কবি’-র প্রধান চরিত্র আতাহর মনে মনে কিছু অশ্লীল চিন্তা করেছিল যা হুমায়ূন প্রকাশ করেছেন: ‘আতাহার মনে মনে বলল – ‘ফের বলি তোর পশ্চাদ্দেশ দিয়ে ঢুকিয়ে দেব শালা চালবাজ’ (পৃ. ৩৫-৩৬)। ‘নন্দিত নরকে’-র দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই খোকার বাবা-মার রাত্রিকালীন কথাবার্তা ও আচরণের ইঙ্গিতও বাংলাদেশী উপন্যাস পাঠকের জন্য খানিকটা ভিন্নতা বৈকি। মধ্যবিত্ত এ পরিবারটির মানুষগুলোর দৈনিককার ভালোলাগা মন্দলাগা ভালোবাসাবাসির সবকিছু ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বা কখনও কখনও সামান্য বর্ণনা নিয়ে যখন উপস্থিত হতে থাকে তথন সাধারণ পাঠকের ভাল লাগে কেননা ঐ রকম একটি প্রতিশোধের অংশীদার তো পাঠক নিজেও। গল্পটির আকর্ষণ বাড়তে থাকে যখন জানা যায় অবিবাহিত মস্তিষ্ক বিকৃত রাবেয়া গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। রাবেয়ার পাগলপ্রায় বাবা হাতুরে চিকিৎসায় রাবেয়াকে গর্ভমুক্ত করতে যেয়ে প্রবল রক্তপাতের পর তার ঘটে মৃত্যু। পরিবারের আর একজন অনাত্মীয় কিন্তু আত্মীয়েরও বেশি মাস্টার কাকা (শরীফ আকন্দ) শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রাবেয়ার মৃত্যু ঘটে যায়। শরীফ আকন্দ ফিরতেই বটি দিয়ে তাকে খুন করে মন্টু। মন্টুর এ কাজটি যেন একটি রহস্যের মত পাঠকের কাছে। রহস্য আরও বৃদ্ধি পায় যখন জানা যায় মন্টু আসলে খোকাদের সৎ ভাই। ওদের বড়মা অর্থাৎ মন্টুর মার ছেলে মেয়ে না হওয়াতেই খোকাদের বাবা খোকাদের মাকে (শানু) বিয়ে করেন। যদিও পরবর্তীতে মন্টুর জন্ম হয় এবং মন্টুর এগারো বছর বয়সে তিনি মারা যান। সৎ ভাই হয়েও মন্টু যে কাজটি করে তা যেন অধিক মমতা মিশ্রিত সমর্থন লাভ করে পাঠকের, কেননা শরীফ আকন্দই রাবেয়ার গর্ভের কারণ।
হুমায়ূন আহমেদের প্রথম লেখা উপন্যাস ‘শঙ্খনীল কারাগার’-এর চরিত্ররাও কিন্তু নামে এবং প্রতিবেশে খুব কাছাকাছি, যদিও সেখানে গল্পটি ভিন্ন, বয়স ভিন্ন। হুমায়ূন ‘শঙ্খনীল কারাগার’ এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছিলেন, ‘নন্দিত নরকের সঙ্গে এই গল্পের কোন মিল নেই। দু’টি গল্প উত্তম পুরুষে এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের গল্প এই মিলটুকু ছাড়া। নামধাম দু’টি বইতেই প্রায় একই রেখেছি। প্রধানত নতুন নাম খুঁজে পাইনি বলে, দ্বিতীয়ত এই নামগুলোর প্রতি ভয়ানক দর্বল বলে।’ 9 চরিত্র নামের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটি হুমায়ূনের অন্যান্য উপন্যাসেও পরবর্তীতে লক্ষ করা যায়। ‘শঙ্খনীল’-র চরিত্রগুলো আরও একটু বেশি বয়সী; রাবেয়ার এখানে একত্রিশ, খোকার ছ’বছরের বড়। তবে হুমায়ূনের সহস্যময়তা তো এটি থেকেই শুরু। রাবেয়াকে কেন্দ্র করেই সেটি আবর্তিত। ‘নন্দিত নরকে’-তে মন্টুর যেমন গভীর ভালোবাসা তার সৎ ভাই-বোনদের প্রতি ‘শঙ্খনীল কারাগা ‘-এ রাবেয়ারও তাই। অথচ রাবেয়া যে ওদের সৎ বোন এ রহস্য তো প্রচারিত ও উন্মোচিত হতে হতে উপন্যাস শেষ। সাধারণ একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এ রহস্যময়তা পাঠকের মামনে অভিনবত্ব নিয়েই উপস্থাপিত হয়েছিল। যে আবিদ হোসেন ছোটবেলায় রাবেয়াকে স্কুলে দেখতে যেত, গাড়িতে করে রাবেয়া ও তার বন্ধুকে বেড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো সে যে রাবেয়ার বাবা অর্থাৎ খোকাদের মা’র প্রথম স্বামী সেটা উপন্যাসের শেষে এসে ময়মনসিংহে স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে চলে যাওয়ার পর খোকাকে লেখা রাবেয়ার চিঠিতে জানা যায়। ডিটেকটিভ উপন্যাস না হয়েও, পরিবার ও সমাজকেন্দ্রিক উপন্যাস হয়েও রহস্যময়তা সৃষ্টির এ প্রচেষ্টায় হুমায়ূন সফল হয়েছিলেন বলেই পাঠক তাকে ‘নন্দিত নরকে’ ও ‘শঙ্খনীল কারাগার’-এর উপন্যাসিক হিসেবে চিনে ফেলল সহজেই। এমন প্রচেষ্টা কি বাংলা উপন্যাসে আগে ছিল না? ছিল, রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ (১৯১০)ই তো এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। গোরা যে পালিত সন্তান সে রহস্যের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন উপন্যাসের শেষে যেয়ে। পরবর্তীকালে এ ধারায় খুব বেশি আর উপন্যাস লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না, কেননা ততদিনে রহস্য উপন্যাসের ধারাটিই তো শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। রহস্যময়তা সৃষ্টির এ ধাঁচ কিন্তু হুমায়ূন সাহিত্যে প্রতুল – বিজ্ঞান বিষয়ক রহস্য সৃষ্টিতে; ভৌতিক অতিবাস্তব উপন্যাস নির্মাণে তো বটেই। সামাজিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি এমন ধরনকে আশ্রয় করেছেন। ২০০০ সালে প্রকাশিত ‘শুভ্র’-এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বড়লোকের পুত্র নিজেই যে একজন পতিতার গর্ভজাত -জাহানারা শুভ্রর মা নয় এ সত্য প্রকাশ পায় একদম শেষে এসে (পৃ. ২৩৭)।
১৯৮৪ সালের ‘বিচিত্রা’ ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘একা একা’ উপন্যাসটিও মধ্যবিত্ত সামাজিক বলয়ের কাহিনী। তবে সময়ের হিসেবে এটিতে রাত এগারোটা পঁচিশ থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্তকে ধরা হয়েছে। এ উপন্যাসের উত্তম পুরুষের বক্তা টগর – যার দাদাজান মৃত্যুসজ্জায়। দাদাজানের এ আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাড়ির এবং বাড়ির সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত লোকজনগুলো কেমন আচরণ করছে তার ভেতর দিয়ে একটি রাতের কাহিনী ‘একা একা’। হুমায়ূন আহমেদের কৌতুকপ্রবণতার দৃষ্টান্ত তাঁর প্রথম উপন্যাসে থেকে স্পষ্ট হলেও এ উপন্যাসটিতে সেটি আরও প্রকট: বলা যায় ‘একা একা’ উপন্যাসে সেটি মাত্রাতিরিক্ত; কেননা বাড়িতে মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের বিদায় ঘন্টার মধ্যেও এ সকল কৌতুককর উপাদানগুলো উপস্থিত। এমন রাতে টগরের বড় চাচা, মগবাজারের ফুফু বা ছোট ফুফার আচরণগুলোর সবই কৌতুক সৃষ্টি করে। বাকি চরিত্রগুলোও মাঝে মাঝেই এমন কথাবার্তা বলে ও আচরণ করে যা হাস্য সৃষ্টিতে বাধ্য করে। ‘দাদার অবস্থা কি বেশি খারাপ?’- নীলুর এ প্রশ্নের জবাবে টগরের উত্তরে: ‘রাতের মধ্যেই কাম সাফ হবার সম্ভাবনা’ (যদিও টগর দাদাজানকে এমন কিছু অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না); বড় চাচার হাঁটা সম্পর্কে টগরের মন্তব্য: ‘তিনি কেমন যেন লাফিয়ে চলেন বলে মনে হয়। থপ থপ করে বানর হাঁটার মত শব্দ হয়’ – এমনই কিছু উদাহরণ। কৌতুক সৃষ্টির এ প্রচেষ্টাটি হুমায়ূনের উপন্যাসে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে অনাবশ্যকতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এমনটি বললেও অন্যায় হবে না। চরিত্রের উদ্ভট ভাবনা ও আচরণের ব্যাপারটি যেমন ব্যাপকতা লাভ করে হিমু সিরিজ-এর জন্ম ঘটিয়েছেন তেমনি সাধারণ সিরিয়াস বিষয়ের উপন্যাসও তাঁর হাতে হয়ে পড়েছে কৌতকতার উৎস। ‘পোকা’ (১৯৯৩) উপন্যাসের উদ্ভট চরিত্রটি যেমন উপন্যাসের পুরোটা জুড়ে ব্যাপৃতি ছড়িয়েছে তেমনি ‘জয়জয়ন্তী’-র (১৯৯৪) সিরিয়াস প্রসঙ্গটিতেও কৌতুকের ছোঁয়া যথেষ্ট। প্রাসঙ্গিকভাবে হিউমার সৃষ্টি তো জীবনের পূর্ণ রূপায়ণেরই প্রত্যাশায়। কিন্তু ‘কবি’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আতাহারের বাবার মৃত্যুর পর ওর মা যখন ওর বাবাকে হ্যালুসিনেসানে দেখে তখন আতাহার তার মাকে যে কথা বলে তাকে প্রয়োজনহীনভাবে সুড়সুড়ি দেয়া ছাড়া আর কিছু কি বলা যায়? আতাহার বলেছিল: ‘মা শোন, তোমার ভাবভঙ্গি ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে তুমি-পাগল হবার চেষ্টা করছ। ছেলেরা পাগল হলে মানায়, মেয়েরা পাগল হলে মানায় না।’ (পৃ. ১৮১)
ইতোমধ্যে হুমায়ূনের উপন্যাসে আর যে একটি প্রবণতা লক্ষণীয় হতে শুরু করে তা হলো চরিত্র-বিষয়-বক্তব্য-ভাবনায় পৌনঃপুনিকতা। নতুন গল্প কাঠামোয় তাঁর চরিত্রগুলো স্থাপিত হলেও তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডটি সে তুলনায় নতুনভাবে পরিপুষ্ট না হওয়ায় মধ্যবিত্ত মানুষ নিয়ে তাঁর উপন্যাস একঘেয়ে লাগতে শুরু করে পাঠকের। ‘একা একা’র টগর, বাবু ভাই এবং ‘কবি’-র আতাহরের ভেতর সাজুয্য খোঁজা যেমন কঠিন কিছু নয়, তেমনি ‘দ্বৈরথ’ (১৯৮৯)-এর বিজু ‘জয়জয়ন্তী’-র বাবলুও যথেষ্ট কাছাকাছি। ‘দ্বৈরথ’ ও ‘জয়জয়ন্তী’র অধ্যাপক আশরাফ হোসেন ও তার স্ত্রী অরূণা এবং নাজমূল সাহেব ও তার স্ত্রী পান্নার মধ্যে মিলও বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত। ‘কবি’-র আতাহারের বাবা রশূদ আলী সাহেব বা দূরে কোথায়-এর ওসমানের বোন মিলির চরিত্রের ছায়াও হুমায়ূনের অন্য উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। ‘শুভ্র’-র মীরা বা মৃন্ময়ী-র (২০০১) নাম চরিত্রটির মত তরুণী চরিত্র হুমায়ূনের সমসাময়িক উপন্যাসগুলোতে ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে আজকাল। নিচু শ্রেণীর প্রাণীদের বিশেষ বোধশক্তি, খাটের শোয়ার দিকের প্রসঙ্গ, পাখির কথা বলা ইত্যাদি তো তাঁর প্রিয় কিছু অনুসঙ্গ যেগুলোর উপস্থিতি বারংবার লক্ষ করা যায়। পুনরাবৃত্ত একটি বাক্যের উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাবো। ‘একা একা’-তে টগর বিলু সম্পর্কে বলেছিল ‘মেয়েরা সাধারণত রসিকতা করা দূরে থাকুক রসিকতা বুঝতে পর্যন্ত পারে না। কিন্তু বিলু রসিক’ যার তুলনীয় ‘দ্বৈরথ’-এর বাক্যগুলো হলো: ‘মেয়েরা সাধারণত রসিকতা করতে পারে না। কিন্তু ও (সোমার বোন ঊর্মী) দেখলাম সুন্দর রসিকতা করে’।
হুমায়ূন আহমেদ যে নিজেকে এমন একটি ঢং থেকে বের করে এনে বিষয়ের অভিনবত্ব এবং উপস্থাপনার নতুন কৌশল সৃষ্টি করতে পারেন তার প্রমাণ অপ্রতুল নয়। ১৯৮৫ সালের ‘সাপ্তাহিক বিচিত্রা’-র ঈদ সংখ্যায় এবং পরের বছর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এ উপন্যাসটির নাম ‘১৯৭১’। ছোট কলেবরে এবং সীমিত প্রেক্ষাপটে হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এটি। দরিদ্র শ্রীহীন প্রত্যন্ত এক গ্রাম নীলগঞ্জের পটভূমিতে ঔপন্যাসিক হুমায়ূন তাঁর এ উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। গ্রামের পেছনেই জঙ্গলা মাঠ – যে মাঠে আশ্রয় নিয়ে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু জোয়ান ও অফিসার লুকিয়ে আছে এবং তারা দু’জন পাকিস্তানীকে ধরে নিয়ে গেছে এমন সংবাদের ভিত্তিকে পাক মিলিটারীর একটি দল নীলগঞ্জ গ্রামে অবস্থান নেয়। পাকসৈন্যরা রাজাকারদের সাথে নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করছে এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্য কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে এই বিষয়গুলো উপন্যাসটির উপাত্ত। পাকদলটির প্রধান মেজর এজাজ আহমেদের সামনে উপস্থিত করা হয় ক্রমে ক্রমে নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব, প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার আজিজ মাস্টার এবং পরবর্তীতে গ্রামের সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি জয়নাল মিয়াকে। কবিতা চর্চা বাতিকগ্রস্ত আজিজ মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে মেজর আজিজের কবিতায় উদ্দিষ্ট মেয়েটির বয়স তের চৌদ্দ জানলে বলে ‘তের চৌদ্দ বছরের মেয়েই তো ভাল। যত কম বয়ত তত মজা।’ 10 ‘মেয়েটির বুক কেমন আমাকে বল। আমি শুনেছি বাঙালি মেয়েদের বুক খুব সুন্দর। কথাটা কি ঠিক?’ – ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে পাক মিলিটারীর মানসিকতা উন্মোচিত হয়। মেয়েদের গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া উচিত হবে কি না বিষয়ে জয়নাল মিয়ার সাথে আলাপের জন্য সদরউল্লাহ যখন গেছে সে সময়েই এল ঝড়। মিলিটারীর একজন সুবেদার ও তিনজন রাজাকারের একটি দল ছুটতে ছুটতে সদরউল্লাহর চালাঘরে এসে উঠল। এরপর সদরউল্লাহর পরিবারে যে নির্যাতন নেমে এল হুমায়ূনের বর্ণনায় তা হলো:
ওরা সদরউল্লাহর ঘরে ঢুকেই টর্চ টিপলো। সেই টর্চের আলো পড়লো জড়সড় হয়ে বসে থাকা সদরউল্লাহর স্ত্রী ও তার ছোটবোনের মুখে। ছোট বোনটির বয়স বার; সে বোনের সঙ্গে থাকে। মিলিটারী সুবাদার মুগ্ধ কণ্ঠে বললো – এরকম সুন্দর মেয়ে সে শুধু কাশ্মিরেই দেখেছে। বাঙালিদের মধ্যে এরকম দেখেনি। সে খুবই সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বার বছরের মেয়েটির বুকে হাত রাখলো। ঝড়ের জন্যে এই দু’বোনের চিৎকার কেউ শুনতে পেলো না। (পৃ. ৮৭)
এসবই ঘটেছে ফজরের আজানের সময় থেকে দিন পার হয়ে রাতের মধ্যে। হুমায়ূন কাজটি করতে যেয়ে বারে বারে গ্রামের বিভিন্ন অংশে চোখ ফিরিয়েছেন। আর এভাবেই নীলগঞ্জ গ্রামের ১৯৭১-এর পহেলা মে দিনটির একটি বাস্তব বর্ণনা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়। ‘১৯৭১’ মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ নয় কিন্তু এটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের মর্মস্পর্শী চিত্রণ।
তবে রহস্য সৃষ্টিতে হুমায়ূনের যে প্রবণতা তা এ উপন্যাসেও লক্ষিত হয়। পাক মেজরের সহযোগী নীল শার্ট পরা বাঙালি রফিক একটি বড় রহস্য। সে বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং অন্যান্য অনেক কাজে মেজর তথা পাক সেনাদলকে সাহায্য করছে কিন্তু তার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় একটি দ্বৈত সত্তা। মেজরের নির্দেশে আজিজ মাস্টার যখন কাপড় খুলে উলঙ্গ হয় তখন মেজরের বক্তব্য ‘বাঙ্গালিদের মান অপমান বলে কিছু নেই। একটা কুকুরেরও আত্মসম্মান থাকে। এদের তাও নেই। আমি যদি ওকে (আজিজকে) বলি যাও, ঐ ইমামের পশ্চাৎদেশ চেটে আস। ও তাই করবে।’ সাথে সাথে রফিকই কথা প্রসঙ্গে বলেছে ‘মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এরকম করবে’ বা ‘মৃত্যু একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কে কি করবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব না বা আপনার মত সাহসী মানুষও দেখা যাবে কাপুরুষের মত কাণ্ডকারখানা করছে।’ এবং শেষে জয়নালের সাথে মেজরের আলাপ থেকে বেড়িয়ে আসে স্বাধীনকামী সৈন্যদের খবর এবং মেজরের ধারণা হয়, রফিক নিজেও এসব জানতো। নিজাম পাগলও একটি রহস্যময় ভূমিকা রেখেছে উপন্যাসটিতে। রফিকের ভেতর দিয়ে হুমায়ূন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির একটি ছোট্ট অথচ তীক্ষ্ম ছবি দিয়েছেন। কালীমন্দিরের কালী দেখে মেজর যখন বলে যে চারটি হাতে মহিলাকে মাকড়শার মত লাগছে তখন রফিকের কথা ‘আমরা ছোটবেলা থেকেই মূর্তিগুলোকে এরকম দেখে আসছি। আমার কাছে এটাকে স্বাভাবিক মনে হয়।’
হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের আর একটি বিশেষত্ব হলো মাঝে মাঝে আকর্ষণীয় ও অবিশ্বাস্য তথ্য উপস্থাপন। এটি যেমন গল্প বা চরিত্রের উদ্ভটত্বের ক্ষেত্রে ঘটে তেমনি এর সরাসরি ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। ‘১৯৭১’-এ ‘অত্যাচারী রাজারা ইতিহাসে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মানিত হন। আলেকজান্ডারের নৃশংসতার কথা কেউ কি জানে? সবাই জানে আলেকজান্ডার দি গ্রেট’ 11 (বক্তা: মেজর) বা ‘জর্জ বার্নাডশ’ মিলিটারী অফিসার সম্পর্কে বলেছেন দশজন মিলিটারী অফিসারের মধ্যে ন’জনই হয় বোকা। বাকি একজন রামবোকা’ 12 (বক্তা: মেজর) ইত্যাদির মত বহু বহু উদাহরণের কয়েকটি এমন:
জর্জ ম্যারণ নামের এক আমেরিকান কবি বছরের একটি মাস নগর ছেড়ে অরণ্যে ঢুকে পড়তেন। কিছুই থাকত না তাঁর সঙ্গে। কাপড় পর্যন্ত নয়। খাদ্য সংগ্রহ করতেন বন থেকে।
তাতে অবশ্যি সাহিত্যের তেমন কোন লাভ হয়নি। জর্জ ম্যারণ নিম্নমানের কবিতাই লিখেছেন। বনবাসের ফল হিসেবে কোন মুক্ত মানুষের কবিতা লেখা হয়নি। 13
শিকাগোতে এক লোক আট বছর বয়সী একটা মেয়েকে খুন করে তার জরায়ু বের করে খেয়ে ফেলেছে। এতে না-কি যৌবন অক্ষয় হয়। 14
যখন কোন বিশেষ জায়গায় আণবিক বোমার টেস্টিং হয় তখন যে জায়গায় এই টেস্টিং করা হয় তার এক মাইলের ভেতর কোন পোকা মাকড় বিশেষ করে তেলাপোকা থাকে না। এরা মনে হয় কোন এক অদ্ভুতভাবে খবর পেয়ে যায় যে এখানে নিউক্লিয়ার বোমা টেস্টিং হবে। খবর পেয়ে সরে পড়ে। 15
পঙ্গপালের আক্রমণ ঠেকানোর কোন বুদ্ধি কি মানুষের আছে? মেশিনগান দিয়ে ঠেকাবে। পৃথিবীতে বিউবোনিক প্লেগ ছড়িয়েছিল ইঁদুর। ১৩৪৭ থেকে ১৩৫১-এই পাঁচ বছরে প্লেগে সারা পৃথিবীতে মানুষ মারা গেছে ৭৫ মিলিয়ন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বিউবোনিক প্লেগ হল – মানুষ মারা গেল ২০ মিলিয়ন। 16
পরিপূর্ণভাবে নিজেকে যে মানুষ জেনে ফেলে জীনব তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। সে তখন জীবন থেকে মুক্তি কামনা করে। কবি মায়াকোভস্কি নিজেকে জেনে ফেলেছিলেন – কাজেই জীবন তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেই সেই জীবনের ইতি করেছিলিন। 17
হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রের মত। যখন গতি জানা যায় তখন অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দু’টি অনিশ্চয়তার গুণফল সমান ‘h’ প্লাংক কনসটেন্ট। 18
মাকে খুশি করার জন্যে বিদ্যাসাগর এই কাজ [সাঁতরে দামোদর নদী পার] করেন নি। 19
If you meet a blind man, kick him, Why should you be kinder than God? 20
আলতাফুর রহমান স্যার… হঠাৎ বললেন তোমরা কেউ কি বলতে পারবে মানুষ তার সমগ্র জীবনে সবচে’ বেশি কোন শব্দটা বলে? কেউ উত্তর দিল না। স্যার চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় করে লিখলেন – ‘না’। 21
শুভ্রর ইজিচেয়ারটা জানালার কাছে। সে গভীর আগ্রহে একটা বই পড়ছে। উদ্ভট বই- নাম The 4th Eye লেখকের নাম R. Lampa তিন বইটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন মানুষ চারটা চোখ নিয়ে জন্মায়। দুটি চোখ দৃশ্যমান। দুটি অদৃশ্য। একটি অদৃশ্য চোখ থাকে মাথার পেছনের দিকে। আরেকটি অদৃশ্য চোখ থাকে নাভির ঠিক দু’আঙ্গুল নিচে। R. Lampa সাহেবের মত যে-কোন লোক এই দুটি চোখে অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে। তাকে ধৈর্য্য ধরে কয়েকদিন একটা পরীক্ষা করতে হবে। একজন কেউ ফুলস্কেপ কাগজে বড় বড় করে কোনো একটা সংখ্যা লিখে মাথার পেছন দিকে ধরবে। সেই সংখ্যাটি পড়ার চেষ্টা করতে হবে মাথার পেছনের চোখ দিয়ে। অনেকটা জেনার টেস্টের মত টেস্ট।
একই পরীক্ষা নাভির চোখ নিয়েও করা যায়। লেখক ভদ্রলোক দাবি করছেন যে, একটু চেষ্টা করলেই যে কেউ এটা পারবে। 22
মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত হুমায়ূনের অন্য আর একটি উপন্যাসের নাম হলো ‘শ্যামল ছায়া’। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত এ উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণ চিত্র না থাকলেও মেথিকান্দা নামক একটি স্থানের পাকিস্তানী সৈন্যদের ক্যাম্পের মুক্তি বাহিনীর একটি দলের আক্রমণের প্রস্তুতির চিত্র আছেÑ আক্রমণে অংশগ্রহণকারী সকলের নয় তাদের একটি ক্ষুদ্র দলের সদস্যদের অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা সদস্যরা হল আবু জাফর শাসসুদ্দিন, হুমায়ূন আহমেদ, হাসান আলি, আবদুল মজিদ, আনিস সাবেত। সবশেষে চার পৃষ্ঠায়, লেখক এ দলটির চূড়ান্ত আক্রমণের শুরুর ইঙ্গিতটিকে স্পষ্ট করেছেন। এদের স্বকথনের ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিককার কিছু পারিবারিক ও মানসিক চিত্র ফুটে ওঠে। সন্দেহ নেই শ্যামল ছায়া একটি গল্পেরই বর্ধিতরূপ: কায়া বিচারে ‘নন্দিত নরকে’ ও ‘শঙ্খনীল কারাগার’ যেভাবে ক্ষুদ্র হওয়ার পরও ব্যাপৃত একটি জীবনবোধকে প্রকাশ করে, ‘শ্যামল ছায়া’ তা করেনি। কিন্তু বহু চরিত্রের আত্মকথনের ভেতর দিয়ে উপন্যাসটি একটি অভিনবত্ব অর্জন করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের কথকের এ বিভিন্নতা বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু হলেও হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রে তা নতুন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে রাখা দরকার, বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে হুমায়ূন যখনই তাঁর নিজের বহু ব্যবহৃত ঢং থেকে বেড়িয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন তখন তা তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়েছে। ‘শ্যামল ছায়া’ বা ‘১৯৭১’ নিশ্চয়ই সাধারণ হুমায়ূনীয় উপন্যাস পদ্ধতিতে রচিত নয়; কিন্তু সে দু’টি যে জনপ্রিয় হয় নি তা হুমায়ূন সাহিত্যের জনপ্রিয়তার ইতিহাস না ঘেটেও বলে দেয়া যায়।
আমাদের আলোচনার পরবর্তী উপন্যাস ‘দূরে কোথায়’। লেখক ওসমানের স্ত্রী রানু স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় ছেলে টগরকে নিয়ে আলাদা একটি বাসাতে উঠেছে। রানুর সাথে একই বাসায় থাকছে অপলা – রানুর দূর সম্পর্কের বোন। ছেলেকে দেখার জন্য ওসমান প্রতি বুধবার রানুর বাসায় যায় আর এভাবেই অপলার সাতে তার তৈরি হয় একটি সহজ সম্পর্ক। স্বামীর সাথে রানুর সম্পর্ক না থাকলেও অপলার সাথে স্বামীর সাধারণ এ সম্পর্কটিকে সহজভাবে নিতে পারে না রানু। মানবিক সম্পর্কের এই জটিলতা উপন্যাসটিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। লেখালেখির প্রতি ওসমানের বিশেষ প্রীতির কারণেই রানুর ধারণা ওসমান তাকে বুঝতে পারে না। কিন্তু পাঠক উপন্যাসের শেষে যেয়ে বুঝতে পারেন ওসমানের ‘লিখতে না পারা’র ব্যাপারটির পেছনে রানুর অনুপস্থিতি দায়ী ছিল। গ্রামের বাড়িতে ওসমান কিছুদিনের জন্য নির্বাসন গ্রহণ করলে একসময় সেখানে টগরকে নিয় হাজির হয় অপলা এবং সবশেষে রানু সেখানে উপস্থিত হলে ওসমানের লেখার গতি ফেরে। উপন্যাস যখন শেষ হচ্ছে – তখন রানু রেলিং ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর ঘরে ওসমান সাহেব মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছেন। বাঙালি স্বামী-স্ত্রীর যে পারস্পারিক বোধ ও টান তা যেন বিচ্ছিন্ন হবার নয়। ‘দ্বৈরথ’-এর কামালের জন্য সোমার আকর্ষণকেও এমনই একটি স্তরের তুলনায় বিবেচনা করা যেতে পারে। কামালের বাজে ও অনৈতিক বিভিন্ন অভ্যাসের কারণে সোমা তাকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেও উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সে ফিরে এসেছে কামালের বাসাতেই।
আমার পাঠের পরবর্তী উপন্যাস ‘বৃহন্নলা’ (১৯৮৯) গ্রন্থটির প্রকাশকের লেখা ভূমিকার নাম ‘মিসির আলির আরেকটি উপাখ্যান’। এ দিয়ে বোঝা যায় মিসির আলি নিয়ে হুমায়ূন ইতোমধ্যে আরও একটি উপাখ্যান লিখেছেন। ‘অমিমাংসিত কুহেলিকা কিংবা রহস্যের মোড়কে আবৃত ঘটনার’ কার্যকারণ অনুসন্ধানে পাগলাটে চরিত্রের মিসির আলি ক্রমে ক্রমে হুমায়ূনের একটি সিরিজ গ্রন্থের প্রধান হয়ে উঠেছে। এ সকল উপন্যাসে হুমায়ূন এমন একটি আধিভৌতিক জাল বোনেন যা রোম উদ্দীপক এবং জাগতিকভাবে অসম্ভব। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে সে সকল গল্পের উপস্থাপনা ভঙ্গিতে হুমায়ূনের পারদর্শিতা এমন যে তা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। ‘বৃহন্নলা’-র কাহিনীও সে সকল বিচারে কম আকর্ষণীয় নয়।
অতিবাস্তব মূল গল্পটির প্রধান সুধাকান্ত ভৌমিক। বেঁটেখাটো, মৃদুভাষী, সাদা চুল ও ঋষি ঋষি ভাবের ষাটের মতো বয়েসী সে মানুষটার সাথে যোগাযোগ ঘটল গল্পের বক্তার যে কিনা মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে মফস্বলে গিয়ে রাতে শোয়ার জন্য সুধাকান্ত বাবুর আশ্রিত হয়েছে। সে রাতেই সুধাকান্ত তার নিজের জীবনের রোমহর্ষক ভৌতিক কাহিনীটি বলে। পরবর্তীকালে মুখ থেকে মুখে সে গল্প যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যবনরমাল সাইকোলজির পার্টটাইম শিক্ষক মিসির আলির কাছে। মিসির আলি যোগাযোগ করে উপন্যাসের বক্তা ‘আমি’র সাথে। তারপর সুধাকান্ত বাবুর সাথেও যোগযোগ ঘটায়। সেখানেই মিসির আলি প্রমাণ করে সুধাকান্ত বাবু নিজেই ভৌতিক সে গল্পটির নির্মাতা যা ব্যক্তিজীবনের নারীঘটিত কঠিন এক অপরাধকে লুকানোর জন্যে সে বানিয়েছিল। ব্যক্তি আচরণ ও চতুর্পার্শ্ব আপাতভাবে জটিল এমন সব রহস্যকে যুক্তিবুদ্ধির মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করাই মিসির আলির কাজ। আর এভাবেই হুমায়ূনের আরও অনেক উপন্যাসের জটিল রহস্যের সমাধানকারী মিসির আলি পাঠকের নিকট খুব জনপ্রিয়।
মিসির আলি প্রসঙ্গে হুমায়ূনের উপন্যাসে আরও যে একটি চরিত্র প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় সে হলো হিমু। মিসির আলির মত হিমুও হুমায়ূনের অনেক উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি। আর সে কারণেই যেমন আছে ‘মিসির আলি অমনিবাস’, তেমনি ‘হিমু সমগ্র’ও প্রকাশিত হয়েছে। এবং অমনিবাস ও সমগ্র প্রকাশের পরও মিসির আলি ও হিমু কাহিনী যে থেমে নেই, তা সহজেই অনুমান করা যায়। নতুন নতুন কাহিনী কাঠামোতে এরা বার বারই উপস্থিত হয়ে চলেছে।
‘বৃহন্নলা’ আর ‘দ্বৈরথ’ কিন্তু একই বছরে প্রকাশিত এবং এসব থেকে যে সমাধানটি আমরা পাই তা হলো হুমায়ূন নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তের ঘরোয়া কাহিনী নির্মাণ নিয়ে তাঁর উপন্যাসিক জীবনকে শুরু করেছিলেন যে ধারণাটি প্রয়োজনমত অদল-বদলের ভেতর দিয়ে এখনও বহমান। পাশাপাশি তাঁর কলম সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী যেগুলো সাধারণ পাঠকের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন হিমু-কাহিনী এবং অধিভৌতিক কল্পকাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতা অনস্বীকার্য। ‘বৃহন্নলা’র ভৌতিক কাহিনী ও এর রহস্য উন্মোচক হুমায়ূন ‘দ্বৈরথ’-ও রচনা করেন – এটি একটি কৃত্য বৈকি?
‘দ্বৈরথ’ উপন্যাসের পারিবারিক প্রেক্ষাপটের সাথে ‘নন্দিত নরকে’ এবং ‘শঙ্খনীল কারাগার’ এর প্রেক্ষাপটের সাযুজ্য পাঠকের চোখ এড়ায় না। একটি পরিবারের মধ্যে অনেকগুলো ভাই-বোনের যে অবস্থান তাদের পরিবারিক সংযোগ এটি হুমায়ূনের একটি প্রিয় বিষয় তা মনে করতে কোন অসুবিধা নেই। ১৯৯৪-এ প্রকাশিত ‘জয়জয়ন্তী’-তেও এমন প্রসঙ্গ বর্তমান। ‘দ্বৈরথ’-এ সোমা স্বামী কামালকে ছেড়ে বাপের বাড়িতো ফিরে এলেও শেষ পর্যন্ত কামালের কাছে ফিরে গেছে আবার; অন্যদিকে ‘জয়জয়ন্তী’-র রাত্রির স্বামী মামুন, যে চরিত্রগতভাবে কামালের চেয়ে উন্নত নয় তাকে ছেড়ে চলে গেলে সন্তান টুকুন তার বড় পিছুটান হয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে টুকুন হাসপাতালে মৃত্যুসজ্জায়; গেছে রাত্রি আর তার ভাই বাবুলও। অনেক আশঙ্কার পর টুকুন স্বাভাবিক হলে রাত্রি যখন ফিরছে তখন তার অভিব্যক্তি ভাই-বোনের পারস্পারিক নির্ভরতা ও আশ্রয়ের চূড়ান্ত প্রকাশ। হুমায়ূনের বর্ণনায় রাত্রির দৃষ্টিতে তা এমন:
বাইরে এসে দেখি বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে বাবুল কাঁদছে। আমি বললাম- কাঁদিস না। ও ভাল আছে। চল, বাবাকে খবরটা দিয়ে আসি।
আমরা দুই ভাইবোন হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। মামুন তার স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। তার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনরাও আছে। তারা সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।
আমি মনে মনে বললাম, হে পৃথিবীর সুখী মানুষরা, তোমরা এই দুঃখী ভাইবোনের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থেকো না। তোমরা আমাদেরকে আমাদের মত থাকতে দাও। 23
‘দ্বৈরথ’-এ সোমা কামালকে বিয়ে করল উপায়অন্তহীনভাবে। সোমাদের বাড়ির তিন বাড়ির পর নতুন যে ভাড়াটিয়া অধ্যাপক এলেন তার অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে যেয়েই যোগাযোগের সূত্র। অধ্যাপকের বিরাট লাইব্রেরী থেকে বই নেয়া শুরু করল। অধ্যাপকের প্রতি সোমার ভাল লাগাও তৈরি হচ্ছিল অজান্তে। ঠিক এমনি সময়ে এক বৃষ্টির দিন সোমা অধ্যাপকের কথার মাঝখানে তীব্র ও তীক্ষ্ম গলায় চিৎকার ভেসে আসলো: ‘তোমরা ঐ ঘরে কি করছ? তোমরা ঐ ঘরে কি করছ? তোমরা দু’জনে ঐ ঘরে কি করছ?’ 24 প্যারালাইসিসের রুগীর এ চিৎকারে সোমার জীবনের সব বদলে গেল। ‘আমি দেখেছি। আমি দেখেছি। আমি জানি তোমরা কি করছ। আমি জানি। আমি জানি’ – চিৎকার সারা পাড়াকে জড়ো করলো ঐ দুই বাড়িতে। পুলিশ এলো। সেই রাতেই টাঙ্গাইলের খালার বাড়ির দুর্গে আশ্রয় হলো সোমার। দু’দিন পর চিন্তাক্লিষ্ট সোমা ঢাকায় ফিললো শুনলো প্রকাশ আলোচনা। ‘পেট নামিয়ে এসেছে, দেখলেই বোঝা যায়। কোন আনাড়িকে দিয়ে কাজ করিয়েছে কে জানে – দেখেন না মেয়ে কি অবস্থা? প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিল।’ 25 এমন অবস্থাতেই টাঙ্গাইলে সোমার বিয়ে। বিয়ের রাত পার না হতেই কামালের অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণে সোমা ক্লান্ত হতে শুরু করল। পেশাগতভাবেও কামাল দালাল, ঠকবাজ। শেষ পর্যন্ত কামালের সাথে যখন সোমা না থাকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখনই উপন্যাসের শুরু। পরবর্তীতে অধ্যাপক সাহেব সোমার বাবাকে প্রস্তাব দিলেও এক সময় তার বুঝতে বাকি থাকে না সোমা কামালকে খুব পছন্দ করে। তাই কামালকে বদলাবার নতুন প্রত্যয় নিয়ে সোমাকে কামালের কাছে ফিরে যেতে বলে অধ্যাপক, ‘ঐ মানুষটার জন্যে তোমার তীব্য ভালবাসা আছে, কিন্তু তুমি সেটা বুঝতে পারছ না?’ 26 – ইত্যাদি সব কথাই সোমাকে কামালের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।
উপন্যাসটিতে কামালের কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন হুমায়ূন। সোমার জন্য কামাল ভালবাসার কিছু ইঙ্গিতও রেখেছেন। একজন মানুষ যে পূর্ণতাই একজন খারপ মানুষ নয় হুমায়ূনের অনেক উপাখ্যানেই এমন উপলদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ রহস্যময় – তাঁর পূর্ণ অনুসন্ধান কখনোই সম্ভব নয়। ভালো-মন্দের প্রশ্নেও মানুষের কোন চূড়ান্ত পরিচয় নেই। কামালকে কি পূর্ণতই একজন খারাপ মানুষ এমন অভিধা দেয়া চলে? ‘দ্বৈরথ’-এর সোমার ভাই বিজু, ‘জয়জয়ন্তী’-র মামুন, ‘কবি’র পত্রিকা সম্পাদক আবদুল গনি এদের সকলেই এমন সব চরিত্র।
‘জয়জয়ন্তী’-র রাত্রি মামুনের সাথে বাস করতে অপারগ হয়ে বাপের বাড়ি ফিরলেও মামুনের কিছু ভালো দিকের পরিচয়ও আমরা পাই। বড়লোক ব্যবসায়ী মামুনের অন্য নারীতে যৌন সংসর্গের কারণেই রাত্রি সিন্ধান্ত নিয়েছিল মামুনের সাথে না থাকার ব্যাপারে। ব্যবসার প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে ছ’সাত দিনের জন্য গেলে মামুনের সাথে তার অফিসের পুরষালী বেঁটে খাটো, কালো বয়স্কা মহিলাকে। সাইট সিইং-এ টাইপিস্টের প্রয়োজন জানতে চাইলে মামুনের সরাসরি উত্তর:
আমি যখন বাইরে যাই তখন সাইট সিইং-এর জন্যে যাই না। এটা কোন আনন্দের ভ্রমণ না, কাজের ভ্রমণ। সে সময় আমাকে কি পরিমাণ খাটুনি করতে হয় তা তোমাকে একবার নিয়ে দেখিয়ে আনব। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম-পৃথিবীর সকল পুরুষ-মানুষদের মতো আমারও কিছু শারীরিক চাহিদা আছে। আমি তো আর দেশের বাইরে গিয়ে প্রস্টিটিউট খুঁজে বেড়াতে পারি না। আমার সময়ও নেই, আগ্রহও নেই। ফরিদাকে এই কারণেই আমাকে নিয়ে যেতে হয়। 27
আর এসবের পরিণতিই রাত্রি-মামুনের বিচ্ছেদ। টুকুন অর্থাৎ ওদের ছেলের জন্য শেষ পর্যন্ত সে বিচ্ছেদ চূড়ান্ত কোন পরিণতির দিকে যায় নি। টুকুন দেশে ফিরেছে এবং পরদিন ওকে রাত্রির কাছে পাঠানো হবে মামুনের এই চিঠি তো রাত্রিকে বিপুলভাবে আন্দোলিত করে। ওর মনে হয়:
এটা কি স্বপ্ন? আমি কি স্বপ্ন দেখছি। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে- অপ্রত্যাশিত যে আনন্দ আমি এই মুহূর্তে পেলাম সেই আনন্দের জন্যে আমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিকে পারি।
টুকুন আসছে! টুকুন!
কত বড় হয়েছে টুকুন? তিন বছরে একটা শিশু কত বড় হয়? ও আমকে দেখে প্রথমে বাক্যটা কি বলবে? ও কি আমাকে লজ্জা পাবে? ওষুধপত্রের কথা বলছে কেন? ওর কি অসুখ? আমার বাবুর অসুখ হবে কেন?
আমি সারারাত বারান্দায় বসে রইলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর জ্বলছে। সেই যন্ত্রণাতেই তীব্র আনন্দ।
ঢাকা শহরের সব মানুষ ঘুমুচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে যাই। ওদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলি- আপনারা ঘুমুচ্ছেন কেন? টুকুন আসছে। টুকুন। আপনারা কেউ ঘুমুতে পারবেন না। আপনাদের সবাইকে জেগে থাকতে হবে। 28
‘জয়জয়ন্তী’-র নাজমুল সাহেব ও পান্না ভাবী উপকাহিনী উপন্যাসটির মধ্যে অবিনবত্ব ও রহস্য সৃষ্টির মাধ্যমে একটি ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে। নাজমুল-পান্না দম্পতির আচরণের কোনটি যে প্রকৃত এবং কোনটি বানানো সে রহস্য যেন পুরোপুরিভাবে উপন্যাসের শেষেও উন্মোচিত হয় না। তবে একথা সত্য মূল কাহিনী রাত্রি ও মামুনের প্রসঙ্গে ঐ উপকাহিনীটির উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে; দ্বৈরথ’-এর অধ্যাপক-অরুণা দম্পতি যেভাবে উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র সোমার জীবনের প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল পান্নাভাবীর ব্যাপারটি তেমনভাবে আসে নি।
‘দ্বৈরথ’ এবং ‘জয়জয়ন্তী’-র মধ্যবর্তীকালে রচিত হয়েছে ‘পোকা’(১৯৯৩)। অন্যান্য উপন্যাসের মত এটির শুরুতেও হুমায়ূন নিজের স্বভাব ভঙ্গিতে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন – আলবার্ট আইনস্টাইনের এ উদ্ধৃতি হলো: “মানবজাতিকে যে জিনিস বার বার অভিভূত করে তার নাম রহস্যময়তা। এই রহস্যময়তা থেকেই এসেছে সুকুমার কলা এবং কঠিন বিজ্ঞান”। এবং রহস্যময়তার চূড়ান্ত একটি প্রকাশ ঘটেছে ‘পোকা’র গল্পে। উপন্যাস হিসেবে এটির সার্থকতা নিয়ে সংশয় থাকলেও আকর্ষণের প্রশ্নে এটিতে কোন ঘাটতি নেই।
‘পোকা’র মূল চরিত্র আলতাফ হোসেন যে কিনা পোকাদের কথা শুনতে পায় এবং পোকারা যর কথা শোনে। আলতাফ পোকাদের সংঘবদ্ধ কার্যক্রমও বুঝতে পারে। আলতাফকে দুর্বল মেধার ও বোকা-সোকা প্রকৃতির লোক মনে হলেও সে আসলে যথেষ্ট সংবেদনশীল, বরং সেই তুলনায় আলতাফের মামা বজলুর রহমান, যার আশ্রয়ে আলতাফ শৈশব থেকে বড় হয়েছে তিনি অনেক বেশি পাগলাটে। আলতাফের বোকামীর পরিচয় শেষ হলে পর যে ঘোষণাটি আমরা শুনতে পাই তাহলো বজলুর রহমানের মেয়ে দুলারীর-সে তার মাকে শাসিয়েছে আলতাফ ছাড়া সে আর কাউকে বিয়ে করবে না। বিয়ে হয়েও গেল। এভাবেই উপন্যাসের শুরু। এরপরই প্রকাশিত আলতাফের শৈশব। সে সময়কাল ঘটনাক্রম আমাদের একটু যেন ঘোর লাগা পরিবেশে নিয়ে যায়। বজলুর রহমানের ছোট বোন মিনুর স্বামী মোবারক আলতাফকে কোলে নিয়ে একদিন জানাতে এল যে মিনু মারা গেছে। আরও জানালো অর্থাভাবে সে তখনও লাশের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা না করতে পেরে অর্থ খোঁজে তার কাছে এসেছে। রাগের মাথায় মোবারককে তাড়িয়ে দিলেও পরদিন খোঁজ নিতে যেয়ে বজলুর রহমান যা জানলেন তা হলো তার কাছে অর্থ না পেয়ে মোবারক বাড়িতে ফিরে লাশের পাশে খাটে আলতাফকে বসিয়ে রেখে টাকার খোঁজে গিয়েছিল এবং ফিরে দেখে ঘর ভর্তি লক্ষ লক্ষ তেলাপোকা যেগুলো লাশটি খেয়ে ফেলেছে। এভাবেই আলতাফের পোকা বিষয়ক ভাবনাগুলো একটি বিশ্বাসযোগ্যতায় স্থাপন করার প্রয়াস পান হুমায়ূন। আর পরবর্তী চাকরি ক্ষেত্রে এই পোকা জটিলতা যখন আলতাফকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি করছে তখন যোগাযোগ ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. ওসমানের যিনি কিনা প্রাণীদের অনেক রহস্যময়তার ব্যাপারে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেন। আর এভাবেই বিশ্বাসযোগ্যতার একটি ধূম্রজাল সৃষ্টি হতে হতে ‘পোকা’ উপন্যাসটি শেষ হয়। চূড়ান্ত অবাস্তবতার (?) এমন একটি কাহিনীতেও হুমায়ূনের কৃতিত্ব হলো পাঠককে ধরে রাখা-যা তাঁর জনপ্রিয়তার একটি প্রধানত কারণ।
‘জয়জয়ন্তী’-র পরবর্তী যে উপন্যাস আমার পড়ার তালিকায় পড়েছে সেটি হল ‘কবি’। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এ উপন্যাসটি হুমায়ূনের উপন্যাস তালিকায় কলেবর প্রশ্নে হলেও গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় তিনশ’ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যের আর যে সকল উপন্যাসের নাম করা চলে তার মধ্যে ‘শুভ্র’ (২০০০) একটি যেটি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। ‘কবি’ আতাহারের কাহিনী। শুধুমাত্র আতাহারই নয় কবি উপন্যাসে আরও যাঁরা আছে তাদের মধ্যে আতাহারের বন্ধু সাজ্জাদ অন্যতম। আতাহারের গল্পের সাথে এ উপন্যাসে সাজ্জাদের গল্পও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তৃতীয় আরও একজন যে কবির নাম প্রথমদিকে মাঝে মাঝে শুনলেও জলজ্যন্তভাবে পেয়েছি ২৩২ পৃষ্ঠার দিকে সে হলো মজিদ – বর্তমানে মফস্বল কলেঝের ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক। মাত্র ১২/১৩ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়ে মজিদের কাহিনী শেষ হলেও সো কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।
প্রথম অধ্যায় থেকেই উপন্যাসটিতে আতাহার ও সাজ্জাদের পরিবারের লোকজন সম্পৃক্ত হয়েছে কাহিনীতে। আতাহারের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার বাবা রশিদ আলি সাহেব, ছোপ বোন মিলি, সাজ্জাদের বাবা হোসেন সাহেব, বোন নীতু প্রমুখ তো যথেষ্ট পরিমাণে উপন্যাসটিতে জায়গা দখল করেছে। তুলনায় নিম্নবিত্তের আতাহারের সাথে উচ্চবিত্ত পরিবারের সাজ্জাদের যোগাযোগের কারণে উপন্যাসটিতে সামগ্রিক একটি পারিবারিক সামাজিক চিত্র স্থাপন করাপ বেশি সম্ভব হয়েছে। আতাহার যে কবি তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমেরিকা প্রবাসী বোন মনিকার ফ্লাট চেক করতে যেয়ে আতাহারের নোট বইতে কবিতা লেখার ভেতর দিয়ে। 29 মজিদ আতাহারকে ঠাট্টা করে কখনও উপুড় কবি এবং নিজেকে চিৎ কবি বলে থাকলেও একটি দীর্ঘ কবিতা আতাহার লিখে ফেলে। আর আতাহারের মা সালমা বেগম যখন ওকে বটু নামে ডাকলে আতাহার আপত্তি করে এবং বলে ‘কবি ডাকলেই পার। ছোট দুই অক্ষরের ইকারান্ত নাম। মাত্র দুই মাত্রা।’ 30 আতাহারের কৌতুকপূর্ণ আরও কথা হলো: ‘বাংলাদেশে এ পর্যন্ত শুধু জীবনানন্দ ছাড়া আমার চেয়ে ক্ষমতাবান কোন কবি জন্মায়নি।’ আতাহারের কোন কবিতা ‘সাপ্তাহিক সুবর্ণ’-র সম্পাদক আবদুল গনি সাহেব প্রথমদিকে না ছাপলেও পরবর্তীকালে তার কবিতা ছাপার সংবাদ পাওয়া যায়।
গনি সাহেবের সম্পৃক্ততাও উপন্যাসটিতে কম নয়; যেমনভাবে নাট-বল্টু-স্ক্রুর বিশাল দোকানের পা-হীন আবদুল্লাহ সাহেবও উপন্যাসটিতে ভূমিকা রেখেছেন। যেমনভাবে উপন্যাসটিতে সাজ্জাদের সূত্রে এসেছে শিল্পী মোসাদ্দেক সাহেবের প্রসঙ্গ, মোসাদ্দেক সাহেবের মডেল কন্যা প্রসঙ্গ, সাজ্জাদের অফিসের রিসেপসনিস্ট লীলার কথা, নীতুর সাথে কামালের বিয়ের প্রসঙ্গ। আতাহারদের পরিবারের প্রসঙ্গ আসতে আসতে যেমন সুড়সুড় করে আমেরিকা প্রবাসী মেয়ে মনিকার কথা, শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে মনিকার স্বামীর ভাবনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ‘কবি’-তে ঢুকে পড়ে। অন্য উপকাহিনীগুলোর মধ্যে আতাহারের বিশ্ববিদ্যালয়কালীন বন্ধু (নাকি প্রেমিকা) সাথী, আতাহারের ভাই ফরহাদের কথা, কর্ণার ফার্মেসীর ওষুধ চোর স্বামী ইত্যাদি বহু কিছু এসে উপন্যাসটি এত দীর্ঘ কলেবর দিতে সাহায্য করেছে। মূল কাহিনী কাঠামোর এ উপকাহিনীগুলোর সবক’টির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না যা হুমায়ূনের উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য। সাজ্জাদের হেরোইন আসক্তির ব্যাপারটিতে রীতিমত আরোপিত মনে হয়, যেমনভাবে মজিদের বাসায় যেয়ে নদীর পারে নেশা করে তিনজনের উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করার ব্যাপারটি খুব বেশি প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে বলে মনে হয় না।
তবে যে কোন পাঠকের কাছেই কবি পাগলাটে চরিত্রের সমাহার বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আতাহার ও সাজ্জাদ – উপন্যাসের এ দুটি প্রধান চরিত্র তো তাদের ভাবনা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে পাগলামীতে ভরা; যেগুলোর অনেকগুলোই সাধারণ যৌক্তিকতার হিসেবে মেলে না। আতাহারের বাবার আচরণের মধ্যেও পাগলামী ব্যাপারটি রীতিমত প্রকট যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ছেলে ফরহাদকে বেশি পড়ার কারণে উত্তেজিতভাবে প্রহার করার দিনে। পাগলাটে এ চরিত্রগুলোর পাশে মিলি, ফরহাদ, নীতু, কনা, লীলাবতি, আবদুল গনি, মজিদের ছাত্রী এবং প্রেমিকা জাহেদা খাতুনকে অনেক স্বাভাবিক মনে হয় যারা নিজেরাই বড় চরিত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে।
‘কবি’ পড়তে গিয়ে বরাবরই মনে হয়েছে এটি অতিকথনে ভরে উঠেছে। প্রয়োজনহীনভাবে চরিত্রগুলো পরস্পরের মধ্যে এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলে চলে যাকে অতিকথন আখ্যা দেয়া ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না। পূর্বেকার উপন্যাসগুলো এ ত্রুটি থেকে তুলনামূলক বেশি মুক্ত থাকায় সেগুলোতে গল্পের যে আঁটুনি সম্ভব হয়েছিল তা ‘কবি’-তে রক্ষিত হয়নি। কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজনের কারণেই এমনটি ঘটেছে ভাবলে দোষ দেয়া যাবে না কেননা বড় কলেবরের ‘শুভ্র’ও একই সমস্যায় জর্জরিত। কবি শেষ করে বর্তমান আলোচকের মনে হয়েছে যেন হুমায়ূন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উপন্যাসটিতে তিনি আর বর্ধন করবেন না। প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করতে চাই ‘নন্দিত নরকে’ এবং ‘শঙ্খনীল কারাগার’ উপন্যাসগুলো কলেবরের দিক দিয়ে মাত্র ৪০/৫০ পৃষ্ঠার হলেও সেগুলোতে একধরনের জীবনবীক্ষার পরিচয় এবং পরিণতি ঘটেছে 31
যা ‘কবি’-তে উপহার দিতে হুমায়ূন সফল হন নি।
অবাস্তবতার এই যে কুহক তা কিন্তু ‘হিমুর দ্বিতীয় প্রহর’ (১৯৯৭)-তেও বিশ্বাসযোগ্যতায় স্থাপিত নয়। বক্তা হিমু পূর্ণিমার সে রাতে শহর ঘোরার আনন্দে এ রাস্তা ও রাস্তা করে শেষে এসে পৌঁছল এক গলিতে যেখানে হুমায়ূন সৃষ্টি করেছেন ভৌতিক একা সময়। সে সময় হিমু যার দেখা পেল তার বর্ণনা এমন:
আমি দেখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখ, নাক, মুখ, কান কিছুই নেই। ঘাড়ের উপর যা আছে তা একদলা হলুদ মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু না। সেই মাংসপিণ্ডটা চোখ ছাড়াও আমাকে দেখতে পেল সে, লাঠিটা আমার দিকে উঁচু করল। আমি দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা লক্ষ করলাম তা হচ্ছে চাঁদের আলোয় লাঠিটার ছায়া পড়েছে, কিন্তু ‘মানুষটা’র কোন ছায়া পড়েনি। 32
মিসির আলিকে দিয়ে হিমুর এ দৃশ্য অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যাও আছে উপন্যাসটিতে। ভূমিকায় হুমায়ূন জানিয়েছেন এ উপন্যাসেই প্রথম হিমু আর মিসির আলির সাক্ষাৎ তিনি ঘটাচ্ছেন। উপন্যাসে হুমায়ূন হিমুর দেখা দৃশ্যের ব্যাখ্যার জন্য হিমুকে নিয়ে গেছেন মিসির আলির কাছে। আর সে ঘটনার ফাঁকে হিমুর নিজের একটি কাহিনী প্রকট হয়ে গেছে ‘হিমুর দ্বিতীয় প্রহর’-এ।
হিমু হুমায়ূন আহমেদের হিমুকে নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলোর প্রধান চরিত্র। হিমু হুমায়ূনের পাগলাটে চরিত্রগুলোর অন্যতম – তাঁর হলুদ পাঞ্জাবীতে আবার প্রকট থাকে না; খালি পায়ে সে ঘুরে বেড়ায়, কথাবার্তা বলে উদ্ভট। হিমুর নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে উপন্যাসটিতে তেমনি শহর ভরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যাদের সাতে দেখা হচ্ছে তাদের প্রসঙ্গও গুরুত্ব পেয়েছে। আত্মীয়দের মধ্যে বাদল, বাদলের বাবা হিমু মেজো ফুফা, ফুফু প্রমুখের সাথে সাথে হাসপাতালের ডাক্তার ফারজানা, চায়ের দোকানদার কাওছার মিয়া, দুই ছিনতাইকারী মোজাম্মেল ও জহিরুল, আশরাফুজ্জামান- যার মানি ব্যাগ হিমু রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিতে জিগাতলার বাসায় গিয়েছিল, আশরাফুজ্জামান সাহেবের মেয়ে মীরা, ফুটপাতে শুয়ে থাকা সুলায়মান, সুলায়মানের বাবা (বস্তা ভাই), যার শরীরে গু মাখিয়ে বসে থাকা ময়রা বাবা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। উপন্যাসটিতে বাদলের বিয়ের ব্যাপরটি যেমন মনোযোগ দাবি করতে পারে, তেমনি আশরাফুজ্জামান ও তার কন্যা মীরার কাহিনী হৃদয় স্পর্শ করে। মা-মরা মীরা বিয়ে হয়ে গেলে আশরাফুজ্জামান কী নিয়ে বাঁচবেন এ চিন্তাতেই গোপনে গোপনে সবসময় মীরা সম্পর্কে কুৎসিত কথা লিখে বেনামা চিঠি পাঠাতেন পাত্র পক্ষকে এবং বিয়ে ভেঙে যেত। তাই মীরার আত্মীয়রা যখন ওর বিয়ে দিল, তারা সেটা করল মীরার বাবাকে না জানিয়েই; বিয়ে সমাপ্ত হলেই মীরার বাবাকে জানানো হয়। হুমায়ূন আহমেদের একটি প্রধান কৃতিত্ব হলো তিনি পাঠকের কোমল অনুভূতিকে স্পর্শ করতে পারেন। সমাজের খারাপ মানুষগুলোর ভেতরেও তিনি এমন সত্যের সন্ধান পান যার আবিষ্কারক হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দাবিদার হতে পারেন। ‘দ্বৈরথ’-র কামালের মত একজন খারাপ মানুষের ভেতরেও হুমায়ূন সন্ধান করেছেন সোমার জন্য ভালবাসা। ‘জয়জয়ন্তী’-র মামুন যখন রাত্রিকে জানিয়েছিল ওদের ছেলে টুটুনের হার্টে সমস্যা হয়েছে এবং তার চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়া প্রয়োজন বলেই রাত্রির সাথে মামুন টুটুনকে দেখা করতে দেয় না; তখন যেন মামুনের চরিত্রের এটি স্বর্গীয় দিক পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয়। ‘রূপার পালঙ্ক’-র (১৯৯৯) মোবারক যখন ওর দাদীর শরীরে চুরি করা শালটা জড়িয়ে দিলে ওর দাদীর বেগে দিয়ে পানি পড়তে থাকে তখন মোবারকের সকল অপরাধ ক্ষমা করার জন্য পাঠক প্রস্তুত হতে থাকেন। শুরু থেকেই তো দেখা গেল বড়লোকের কাছে কিডনি বিক্রি করে অর্থ উপায়ের প্রচেষ্টায় আছে সে। উপন্যাসের শেষে অসৎ সঙ্গের বন্ধু মৃত্যপথযাত্রী জহিরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ‘দোস্ত ঝুলে থাক। খবরদার মরবি না। খবরদার না। কোনো চিন্তা নেই। আমি সব ব্যবস্থা করছি। দেখবি এই টাকা দিয়ে আমি আমাদের ভাগ্য বদলে ফেলব…।’ 33
দীর্ঘ কলেবরের ‘শুভ্র’-র নাম চরিত্রটি কিন্তু ‘কবি’-র প্রধান চরিত্র আতাহার বা হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য উপন্যাসের পাগলাটে ভাবসম্পন্ন চরিত্রগুলোর মত নয়। বরং ওর মা (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শুভ্র’র গর্ভধারিণী নয়) জাহানারা বেগম হুমায়ূনের পাগলাটে চরিত্রের প্রতিনিধি এ উপন্যাসে। বিনুকে জড়িয়ে শুভ্রকে নিয়ে জাহানারা বেগমের যে আশঙ্কা তা তো শুভ্রকে হারিয়ে ফেলাপর ভয় থেকেই উৎসারিত। আর যেহেতু জাহানারা বেগম জানে, শুভ্র তার গর্ভজাত নয়, শুভ্রকে হারানোর আশঙ্কায় অযৌক্তিক আচরণ করাও হয়তো তার জন্য স্বাভাবিক। তেইশ বছরের ‘লতানো গাছের মত’ শুভ্রকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব যখন জাহানারা বেগম তার স্বামী মোতাহার সাহেবের কাছে করছে তার কিছুদিন পরই মোতাহার সাহেবের দূর সম্পর্কের ভাগ্নি বিনু ইউনির্ভাসিটিতে ভর্তির জন্য ঢাকায় এসে ওদের বাসায় উঠল। তারপর মোতাহার সাহেবের মৃত্যু হলে শুভ্র ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে পড়ছে পতিতালয়ের সাথে সেভাবেই সে আবিষ্কার করে একটি ভিন্ন সত্তার – যে আবিষ্কারে তার জন্মরহস্যও জড়িত। ‘ভয়ঙ্কর বাড়িগুলিতে আমি যাই। চুপচাপ বসে থাকি। কী অদ্ভুত যে আমার লাগে। এইখানে আমার জন্ম! কী আশ্চর্য’ 34– শুভ্রর এই বোধ তাকে একটি ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছে। তাই ‘শুদ্ধতম মানুষ’ হতে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে বিনুর হাতে।
বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ধারাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। জাতির জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য সে-জাতির সকল পাঠকের সন্বিষ্ট মনযোগ প্রত্যশা করবে তেমনটিই স্বাভাবিক। স্বাধীন বাংলাদেশের পথ চলা শুরুর পরপরই এ ধারাটি সাহিত্যের সকল মাধ্যমেই স্থান পেতে শুরু করে এবং ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হতে থাকে। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কবিতা বা নাটকে যে সফলতা দ্রুত লাভ সম্ভব হয়েছিল, উপন্যাসে তেমনটি এত সহজে ঘটতে পারে নি। আর তাই মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি বিশাল ও মহৎ উপন্যাসের আকাঙ্ক্ষা বাংলাভাষী সকল পাঠকেরই দীর্ঘদিনের। সমরূপ বিষয়কে আশ্রয় করে রচিত প্রায় সকল উপন্যাস প্রচেষ্টাই সমালোচকের দৃষ্টিতে ‘খণ্ডিত’, ‘আংশিক’ ইত্যাদি অভিধাদুষ্ট। ছাপান্নো হাজার বর্গমাইলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে যুদ্ধ, যে যুদ্ধের ভেতর দিয়েই একটি জাতি পৌঁছুতে পেরেছিল তার জাতিসত্তার অভীষ্ট লক্ষ্যে, জাতির প্রতিটি মানুষ যে ঘটনায় কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ইতিহাস-সৃষ্টিকারী সে ঘটনাটির সামগ্রিক একটি উপন্যাস রূপ উপস্থিত না হওয়া সত্যি সত্যি এক দুর্মর যন্ত্রণার কারণ ছিল। সে দুরবস্থা থেকে প্রথম যে প্রচেষ্টা আমাদেরকে তুলে আনতে ভূমিকা রাখে তার নাম ‘বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ’। সৈয়দ শামসুল হক রচিত এ উপন্যাসটি বেশ কয়েকটি সংস্করণের পর পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ পায় ১৯৯৮ সালে। একই রকম বিশাল কলেবর নিয়ে অন্য আরও যে একটি মহৎ উপন্যাস আমরা পেয়েছি সেটি হলো শামসদ্দীন আবুল কালামের ‘কাঞ্চনগ্রাম’ (১৯৯৮)। শক্তিমান ও সাহিত্যিক এ দুটি প্রচেষ্টারই বৈশিষ্ট্য হলো দুটিতেই জাতির দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক একটি কাহিনী স্থাপন করা হয়েছে। যদিও জাতিগত ইতিহাসের প্রসঙ্গটি গভীরতাকে স্পর্শ করলেও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গটি এর ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে ঐ যুদ্ধকালে শহীদ শহীদুল্লা কায়সারের ‘কবে পোহাবে বিভাবরী’-র নাম উল্লেখ করা চলে। আলাদা গ্রন্থ হিসাবে অপ্রকাশিত এ উপন্যাসটির পত্রিকায় প্রথম আংশিক প্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালে এবং পরবর্তীতে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ‘শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী-৪’ তে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া এক কাহিনীতে জন ও ঘটনা প্রাবল্যের কারণে এমন একটি মাত্রা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে যার ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিশালতাকে অনুভব করা যায়। লেখকের অকালমৃত্যুর কারণেই উপন্যাসটির কাহিনী চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছায় নি। হুমায়ূন আহমেদ রচিত ‘জোছনা ও জননী’র গল্প শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পূর্বেকার সময়ে এবং সমাপ্তি লাভ করেছে ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিজয় লাভের ভেতর দিয়েই।
‘জোছনা ও জননীর গল্প’ মুক্তিযুদ্ধিভিত্তিক উপন্যাস রচনায় হুমায়ূন আহমেদের প্রথম প্রচেষ্টা নয়। বহু আগেই তিনি লিখেছিলেন ‘শ্যামল ছায়া’ (১৯৭৩) এবং ‘১৯৭১’ (১৯৮৬)-এর মতো সুখপাঠ্য কিন্তু কৃশকায় কাহিনী। সময় ও সমাজের সামগ্রিক রূপায়ণের যে ব্যর্থতায় আমাদের আরও বহু উপন্যাস দুষ্ট হয়েছিল উপর্যুক্ত দুটিও সে বলয়ের বাইরে নয়। তাছাড়া সে উপন্যাস দুটির রচনাকালে নিশ্চয়ই হুমায়ূন জনপ্রিয়তার এমন উত্তুঙ্গ অবস্থায় পৌঁছান নি। লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে সৃষ্ট সবচেয়ে বিতর্কিত প্রকৃতপক্ষে অবহেলিত সময়ে তিনি, অর্থাৎ তাঁর মতো বিশাল জনপ্রিয়তার অধিকারী একজন লেখক, বিশাল প্রেক্ষাপটে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন। এমনটি অনুমান করা বাতুলতা হবে না যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে রচিত অন্য সকল উপন্যাস আমাদের তরুন প্রজন্মের যত পাঠক পড়েছেন তার চেয়ে অধিক পাঠক ‘জোছনা ও জননীর গল্প’ পড়বেন এবং জাতির জীবনের এই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁরা পড়তে ও জানতে আগ্রহী হবেন।
হুমায়ূন তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতই সাধারণ একটি কাহিনী দিয়েই বর্তমান গুরুগম্ভীর উপন্যাসটিরও উন্মোচন ঘটিয়েছেন। শুরু হয়েছে নীলগঞ্জ হাই স্কুলের আরবির শিক্ষক মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরীকে দিয়ে। মাওলানা সাহেব ঢাকা এসেছেন তার ভাই শাহেদের বাসার উদ্দেশ্যে। তিনি সাথে এনেছেন অনেক কিছুর সাথে একটি রাজহাঁস -শাহেদের মেয়েটি এই হাঁস দেখে খুশি হবে এমনটিই তার প্রত্যাশা। যদিও এই হাঁস অনেক কৌতুকের সৃষ্টি করে চলেছে প্রথম থেকেই। বিরক্তি সৃষ্টি হয়ে চলেছে যেহেতু রাত গভীর হয়ে চললেও শাহেদের বাসাটি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। আর এসবের ভেতরেই ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হতে থাকে কিছু কিছু ঘটনা-কনিকা যা সে সময়টাকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। আমরা বুঝতে পারি শহরটি তখন মিছিলক্ষুব্ধ। আরও বুঝি ইতোমধ্যে জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেছে যাবে পূর্ব পাকিস্তানের যাতে ১৬৯টা আসনের মধ্যে ১৬৭টা পেয়েছে আওয়ামী লীগ। সে সব মিছিলেরই স্লোগান ‘জয় বাংলা’। কিন্তু সেসব কণিকার ভেতরে বড় হয়ে উপস্থাপিত হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন যার চিত্রটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলেছে শাহেদ, তার স্ত্রী আসমানী এবং মেয়ে রুনিকে কেন্দ্র করে। এই পরিবারের কাহিনীটি কিন্তু যুদ্ধ সংক্ষুব্ধ এ উপন্যাসটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাসের একবারে শেষ পর্যায়ে এসে (পৃ. ৪৮৫) আমরা দেখি শাহেদ তার বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা নাইমুলের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে কোলকাতার বারাসাতের একটি বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে যেখানে অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগের পর আশ্রয় হয়েছে আসমানী ও রুনির। আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ যখন জানালেন আসমানী পুকুরঘাটে” ।
শাহেদ বিড়বিড় করে বলল, পুকুরঘাট কোন দিকে?
বৃদ্ধ ঘাট দেখিয়ে দিলেন। শাহেদ এলোমেলো পা ফেলে এগুচ্ছে। সে নিশ্চিত ঘাট পর্যন্ত যেতে পারবে না। তার আগেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। এখন সে নিঃশ্বাসও নিতে পারছে না। তার স্বাসকষ্ট হচ্ছে।
তারো কিছুক্ষণ পরে রুনি মায়ের খোঁজে পুকুরঘাটে এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। মা অচেনা অজানা দাড়ি গোঁফওয়ালা এক লোককে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর লজ্জার ব্যাপার। রুনি তীক্ষ্ম গলায় বলল, এসব কী হচ্ছে মা? কী হচ্ছে এসব?
বড় মধুর সে দৃশ্য। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংস আঘাতে যে জাতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ আসতে আসতে তারাই ক্রমাগত মিলিত হতে শুরু করে আবার। দীর্ঘ দশ মাসের কল্পনাতীত দুর্যোগকে মোকাবেলা করে তারা সফলকাম হয়। যদিও সে কাহিনীতে বেদনাতুর উপাদারে সংখ্যাও কম নয়।
নাইমুলই বোধ হয় এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে আলোচিত হবার অধিকারী। নাইমুল শাহেদের বন্ধু। আসাধারণ মেধাবী, যদিও পারিবারিক প্রশ্নে অনাথই বলা যায় তাকে। এই নাইমুলের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রারম্ভিককালে বিয়ে হয়েছিল মরিয়মের। মরিয়ম পুলিশ অফিসার মোবারক হোসেনের মেয়ে। বিয়ের পরপরই ২৫ মার্চের ঘটনা। নির্বিকার ওনিবিরোধ নাইমুল কার্ফুর সময়ে ঢাকা শহর ঘুরে ফিরে এলো নতুন মানুস হয়ে যার বক্তব্য: ‘আমি কিন্তু যুদ্ধে যাবো।’ স্ত্রীর ‘তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে’ প্রশ্নে তার নির্বিকার উত্তর ‘হ্যাঁ তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে – স্বাধীন বাংলাদেশে নাইমুল কি তার স্ত্রীর কাছে ফিরে এসেছিল? হ্যাঁ, কাহিনীতে তাই দেখানো হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর দাঁড়ি-গোঁফ ভর্তি এক যুবক এসেছে মরিয়মের বাড়িতে যাকে দেখে মরিয়ম চিৎকার করে চলচে: ‘মা দেখ, কে এসেছে! মাগো দেখ কে এসেছে!’ যদিও সে বিবরণের সামান্য পরেই এপিলোগের মত আমরা একটা অনুচ্ছেদ পেয়েছি যেখানে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন:
বাস্তবের সমাপ্তি এরকম ছিল না। নাইমুল কথা রাখে নি। সে ফিরে আসতে পারে নি তার স্ত্রীর কাছে। বাংলার বিশাল প্রান্তরে কোথাও তার কবর হয়েছে। কেউ জানি না কোথায়। এই দেশের ঠিকানাবিহীন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার কবরের মধ্যে তারটাও আছে। তাতে কিছু যায় আসে না। বাংলার মাটি পরম আদরে তার বীর সন্তানকে ধারণ করেছে। জোছনার রাতে সে তার বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করে। গভীর বেদনায় বলে, আহারে! আহারে!
এভাবেই ব্যক্তিগত আখ্যানের ভেতর ঢুকে পড়েছে জাতির মহাকাব্যগাধা। অথবা এমনটিও বলা যায় ব্যক্তিগত আখ্যানগুলো একত্রিত হয়ে নির্মাণ করেছে করেছে সেই মহাকাব্যটি। ব্যক্তিগত আখ্যানগুলোতে সহজাতভাবে লেখক স্থান দিয়েছেন দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জি-ঝগড়া-বিবাদ, তুচ্ছ কাজকাম ভাবনা, প্রত্যাশা ও দ্বন্দ্বকে।
একটি প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে মূল্যবান, তা হলো মূল্যহীন সে সকল বিবরণ সাহিত্যের জন্য কতখানি জরুরি ছিল। তবে সেগুলো যে ‘মূল্যহীন’ নয় পুরোপুরি তেমনটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কেননা লেখক তো সে সবের ভেতর থেকেই তাঁর চরিত্রগুলো তুলে আনেনএবং একটি পর্যায়ে এই চরিত্রগুলোই সামগ্রিক পটভূমিকা এবং কাহিনী নির্মাণে ভূমিকা রাখে। সেই যে গৌরাঙ্গকে আমরা পেলাম শাহেদের অফিসে তাকে নিয়ে লেখক কত কৌতুক করেন। অথচ মার্চের সেই দিনগুলোর পর তাকে শাহেদ আবিষ্কার করে নিজের বাসাতে। রাগ করে আসমানী চলে গিয়েছিল বাসা ছেড়ে সেই যেদিন শাহেদের বড় ভাই ঢাকায় আসেন। তারপর থেকে হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে শেষে শাহেদ আবার তার বাসায় এলো এবং দেখল খোঁচা খোঁচা দাড়ি হলুদ চোখের গৌরাঙ্গ। কিন্তু তখন আসলে গৌরাঙ্গ পাগল হবার পর্যায়ে। তাই প্রথমে শাহেদের প্রশ্নে তার স্ত্রী ও মেয়ে ভালো আছে বললেও খানিক পরেই আমরা জানি ওর মেয়েটাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে আর বৌকে তুলে নিয়ে গেছে। মেষে গৌরাঙ্গ কিন্তু পুরোপুরি পাগল। মিলিটারিরা ওকে বেঁধে রেখে মজা করে কেননা ও যে হিন্দু প্যান্ট খুলে সাথে সাথে প্রমাণ করে ও, ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে উত্তরও ইংরেজিতে দেয়।
এমন সাধারণ চরিত্রগুলোই কেমন যেন সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে আসে উপন্যাসে। মাওলানা ইরতাজউদ্দিন যাদের অন্যতম। উপন্যাসে শুরুতে মিছিলে- ‘জয় বাংলা’ বাক্যটা তাঁর ভালো লাগছে না। ‘জয় বাংলা’ এসেছে ‘জয় হিন্দ’ থেকে। এটা ঠিক না। তাছাড়া লাঠি সোটা বল্লাম দিয়ে কিছু হয় না। একশ’ বছর আগেও বাঁশের কেল্লা দিয়ে তিতুমীর কিছু করতে পারে নি। শুধু শুধুই পরিশ্রম। এটা একটা আফসোস যে বাঙালি জাতি কাজে পরিশ্রম করতে পারে না, অকাজে পারে।
সেই মাওলানার দোয়া শুনে ওসি ছদরুল আমিনের স্ত্রীর ভেতরে জাগে গভীর শ্রদ্ধাবোধ। একদিন কদমবুচির জন্য নিচু হলে ওসি সাহেবের স্ত্রীকে তিনি বললেন ‘মাগো, মাথা নিচু করে সালাম করা ঠিক নয়। মানুষ একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া আর কারো কাছেই মাথা নিচু করবে না।’ তারপর পাক বাহিনী ছদরুল সাহেব হত্যা করলে ঐ মহিলাকে সদ্যজাত বাচ্চাসত তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। কিন্তু ডাকাত হারুন অকারণে ছদরুল সাহেবকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে দুজন মিলিটারি সদস্যকে হত্যা করলে মিরিটারি নীলগঞ্জ গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ জ্বালিয়ে দেয়, হত্যা করে মোট আটত্রিশ জনকে (পৃ. ৩৩০)। এসবেরই প্রতিবাদে ইরতাজউদ্দিন মাওলানা জুম্মার নামাজ পড়াতে অস্বীকৃতি জানান। মিলিটারির হুমকিও তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে সরাতে পারে নি। শাস্তি হিসাবে ইরতাজউদ্দিন সাহেবকে উলংগ করে নীলগঞ্জ বাজারে প্রদক্ষিণ করানো হয়। সবশেষে সোহাগী নদীর পাড়ে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
গুলি খেয়ে নিহত হয়েছে এমন আরো অনেকের মধ্যে রয়েছে পুলিশ অফিসার মোবারক হোসেন নিজে। রাষ্ট্রীয় নির্দেশেই এই মানুষটাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারী করার জন্য। সপ্তাহান্তে সে বিষয়ক রিপোর্টও তাকে প্রদান করতে হতো। যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিকেই তিনি নিহত হন। আসমানী যে দারোগা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই বাড়ির প্রধানতম ব্যক্তিটিও একই রকমভাবে মারা যান। সরফরাজ খান নামের পাগল কিসিমের সেই মানুষটি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে একপাও নড়তে রাজি হন নি। অথচ মিলিটারি দলের অল্প বয়স্ক ক্যাপ্টেনটি তার সাথে আদবোচিত ব্যবহার করলো না। বরং জিজ্ঞেস করলো: ‘তোমকো দাড়ি কাহা’। নিখুঁত উর্দুতে সরফরাজ সাহেবও উত্তর করলেন: ‘তুমি তো মুসলমান, তোমার দাড়ি কোথায়? যার নিজের দাড়ি নেই সে অন্যের দাড়ির খোঁজ কেন নেবে?’ ফল যা হবার তাই হলো। জুটলো বুটের লাতি। ভোরবেলায় রক্তবমি হয়ে মারা গেলেন তিনি।
এমন যে যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ সময় তাতে কিন্তু কম নির্যাতিত হয় নি শিশুরাও। আসমানির মেয়ে রুনি তো মূল গল্প-কাঠামোর সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কী দুর্দশাগ্রস্ত ভিখারী জীবন-যাপন করতে হয়েছে তাকে! দুর্দশাতে কংকনও কম যায় না। পঁচিশে মার্চের রাতে বিজয় নগরের যে বাসাতে শাহেদ আটকে পড়ে কংকন সেই বাড়ির মালিক ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিবাগের অধ্যাপক সানাউল্লাহ সাহেবের মেয়ে। জরুরি সে অবস্থায় বাসায় নেই অধ্যাপক। রয়েছেন তার বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী এবং ঐ ছোট্ট মেয়ে। কী ভাব হয়ে গেল একদিনেই। তারপর আবার নিজেদের গতিতে পথচলা। অথচ যেদিন শাহেদ কুমিল্লার পথে, ফেরিত ওর গায়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ভিখারী ধরনের এক মেয়ে – কংকন। মা আর দাদুর কাছ থেকে ছিটকে পড়েছে সে। আর কংকন কাঁধে করে আগরতলায় শরণার্থী শিবিরে শাহেদ প্রথম বারেই পেয়ে গেল ওর মা আর দাদুকে। আর হুমায়ূন আহমেদের বৈশিষ্ট্য যেমনটি – কংকনের কাহিনী প্রকৃতপক্ষে একটি সত্য ঘটনা। যেমনভাবে মাওলানা ইরতাজউদ্দিনের ঘটনার সাথে রয়ে গেছে সত্য ঘটনার সত্য ঘটনা। যেমনভাবে মাওলানা ইরতাজউদ্দিনের ঘটনার সাথে রয়ে গেছে সত্য ঘটনার গভীর সংযোগ। মাওলানা সাহেবকে উলংগ করে যখন নীলগঞ্জ বাজারে ঘোরানো হচ্ছিল তখন একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটে। দরজির দোকানের এক দরজি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দিনকে জড়িয়ে ধরে থাকে। মৃত্যুর আগে ইরতাজউদ্দিন পরম নির্ভরতায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন: ‘যে মানুষটা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল তুমি তার প্রতি দয়া করো।’ সত্য এ ঘটনাটির অংশীদারী সেই দর্জি গুলি খাওয়ার পরও প্রাণে বেঁচে যায় (পৃ. ৩৮৪)। তবে সত্য ঘটনার প্রধান যে অন্তবর্য়ন ঘটেছে এ উপন্যাসের কাহিনীতে সেটি বোধহয় হুমায়ূন আহমেদের নিজের। ২৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হলে পিরোজপুর মহকুমার সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার যিনি দেশের দুই জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ ও মুহম্মদ জাফর ইকবালের বাবা, পুলিশের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে দুইশ রাইফেল স্থানীয় জনগণকে দিয়ে দেন। পাকিস্তানী মিলিটারি তাকে ৫ মে হত্যা করে (পৃ. ১৮৩)। এভাবেই প্রামাণ্য সত্যকে কল্পনার মিশেলে হুমায়ূন নির্মাণ করেছেন ‘জোছনা ও জননীর গল্প’।
মুক্তিযুদ্ধকে আশ্রয় করে রচিত উপাখ্যান অবশ্যই ইতিহাস-সন্নিকটস্থ হতে হবে। কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতাকে সুউচ্চ রাখতে যেমন সেটি প্রয়োজন তেমনি সুপরিচিত সে কাহিনী ক্রমধারাটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত। ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ সচেতনভাবে বহুল পাঠ ও ভাবনা দিয়ে সে কাজটিকে মজবুত করে রেখেছেন। জেনারেল ইয়াহিয়াকে লেখা আইয়ুব খানের চিঠিটি (২৪ মার্চ ১৯৬৯-পৃ. ৫৫) এতদপ্রসঙ্গে প্রথম নজির। তারপর এসছে ১৯৭১-এ ৭ মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ (পৃ. ১০৪-৫)। এসেছে সাংবাদিক সিমন ড্রিঙের রিপোর্ট (পৃ. ৪১)সহ আরও অনেক কিছু। তবে সন্দেহ নেই পঁচিশে মার্চের ঘটনার যে বিবরণ ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র’ থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়েছে তা খানিকটা ক্লান্তিকর (পৃ. ১৪৯-১৫৪)। অনুরূপ আরও কিছু সংযোজন ঘটেছে পৃষ্ঠা ৩৩৩ থেকে ৩৩৯ পর্যন্ত। সে-সব বিবরণের মর্মস্পর্শিতা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, তবে শেষে ‘পরিশিষ্ট’ অংশে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাটি সংযোজনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। ‘জোছনা ও জননীর গল্প’ উপন্যাসটির পাঠক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আগ্রহী ও অনুভূতিশীল হওয়ার পরও এই তালিকাটি অনুপুঙ্ক্ষ পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সকল মানুষকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেও এমন প্রশ্ন তোলা আশা করি অন্যায় হবে না। এভাবে ১৮টি অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজনের পরও লেখক যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের তালিকাটি (দ্রষ্টব্য পূর্বকথা) সংযোজন করে কলেবরকে আরও একশ পৃষ্ঠা বৃদ্ধি ঘটান নি সেটি শুভবুদ্ধির লক্ষণ বলেই মনে করা যায়। কেননা উপন্যাসের পাঠকের উপলব্ধিকে শাণিত করার জন্য দেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মানুষের মোট সংখ্যা, বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা, বা নিহত ভারতীয় সৈন্যদের মোট সংখ্যাটিই যথেষ্ট বলে অনুমান হয়।
‘জোছনা ও জননীর গল্প’-তে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক রাজনৈতিক ও পাকিস্তানী সামরিক ব্যক্তিত্বকে সশরীরে চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জেনারেল নিয়াজী, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এদের মধ্যে অন্যতম। সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে শামসুর রহমানের দীর্ঘ উপস্থিতিও অনেক ঔৎসুক্যের উদ্দীপক। সন্দেহ নেই সমাজ-রাজনীতির এই মানুষগুলো কল্পনা ও সত্যির কাহিনীতে উপস্থাপনে লেখকের কুশলতা প্রশংসার যোগ্য।
একথা সত্য বর্তমান প্রবন্ধে হুমায়ুন আহমেদের সকল উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয় নি কিন্তু অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না যে উপন্যাস রচনার জন্য প্রধান যে প্রয়োজন অর্থাৎ গল্প নির্মাণ তাতে হুমায়ূনের পারঙ্গমতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তারপরও আমাদের অভিজ্ঞতা এমন সে তাঁর উপন্যাস শুধুমাত্র কম বয়েসী তরুণ-তরুণীদেরই তৃপ্ত করতে পারে – যা তাঁর জন্য কোন কৃতিত্ব বয়ে আনে নি। তাঁর বিপুল লেখার পরিমাণই কি তাঁর এই ব্যর্থতার কারণ? নাসির আলী মামুনকে একবার হুমায়ূন বলেছিলেন মৌলিক কাজের ক্ষেত্রেও মানুষ একই সাতে অনেক কাজ করতে পারে। 35
তাঁর সে বক্তব্যের যথার্থতা স্বীকার করে নিয়ে বলতে চাই- তাঁর প্রচলনের বাইরে গিয়ে, বিষয় ও শৈলীর অভিনবত্বের অনুসন্ধানের মাধ্যমে হুমায়ূন কি একটি মহৎ উপন্যাসও পাঠককে উপহার দিতে পারেন না যা হবে কথাসাহিত্যিক হুমায়ূনের প্রথম পরিচয়। ‘The writer can only be fertile if he renews himself, and he can only renew himself if his soul is constantly enriched by fresh experience 36 বিশ্ববিখ্যাত এ ঔপন্যাসিক-সমালোচকের অভিজ্ঞতার আলোটি যদি হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে বাংলা সাহিত্য তাঁর কলম থেকে অনেক উপকৃত হবে এ প্রত্যাশা এখনও বাতুল নয়।
টীকা:
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘নিজের কিছু কথা’, ‘উপন্যাস সমগ্র’ প্রথম খণ্ড, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭ ↩
- ‘দূরে কোথায়’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৩ (১৯৮৭) ↩
- ঐ, পৃ. ৪২ ↩
- ঐ পৃ. ৪৩ ↩
- আমার মেজর ত্রুটি হলো আমার অসহিষ্ণুতা ‘হুমায়ূন আহমেদ: সাক্ষাৎকার, ‘বাংলাবাজার পত্রিকা’, ঢাকা, ১৯ মে ১৯৯৪ ↩
- ‘দূরে কোথায়’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩ ↩
- ‘নিজের লেখা সম্পর্কে আমার অহঙ্কার অনেক বেশি’ সাক্ষাৎকার, ‘ভোরের কাগজ’, ঢাকা, ৪ মার্চ ১৯৯৪ ↩
- ভূমিকাটির কিয়দংশ এমন:
মাসিক ‘মুখপত্রে’র প্রথম তৃতীয় সংখ্যায় গল্পের নাম ‘নন্দিত নরকে’ দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেননা ঐ নামের মধ্যেই যেন একটি নতুন জীবন দৃষ্টি, একটি অভিনব রুচি, চেতনার একটি নতুন আকাশ উঁকি দিচ্ছিল। লেখক তো বটেই, তাঁর নামটিও ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু পড়তে শুরু করলাম ঐ নামের মোহেই।
পড়ে আমি অভিভূত হলাম। গল্পে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি একজন সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর; একজন কুশলীদ স্রষ্টারদ পাকা হাত। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক সুনিপুণ শিল্পীর, এক দক্ষরূপকারের, এক প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টার জন্মলগ্ন যেন অনুভব করলাম।
জীবনের প্রাত্যহিকতার ও তুচ্ছতার মধ্যেই যে ভিন্নমুখী প্রকৃতি ও প্রবুত্তির জটাজটিল জীবনকাব্য তার মাধুর্য, তার ঐশ্বর্য, তার মহিমা, তার গ্লানি, তার দুর্বলতা,দ তার বঞ্চনা ও বিড়ম্বনা, তার শূন্যতার যন্ত্রণা ও আনন্দিত স্বপ্ন নিয়ে কলেবরে ও বৈচিত্র্যে স্ফীত হতে থাকে, এত অল্প বয়সেও লেখক তাঁর চিন্তা-চেতনায় থা ধারণ করতে পেরেছেন দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত।
‘উপন্যাস সমগ্র’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ‘শঙ্খনীল কারাগার’, ‘উপন্যাস সমগ্র’, প্রাগুক্ত পৃ. ৫০ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ১৯৭১, ‘বিচিত্রা’ ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৫ ↩
- ঐ পৃ. ৮৪ ↩
- ঐ পৃ. ৮৬ ↩
- ‘দূরে কোথায়’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘পোকা’, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩১ ↩
- ঐ পৃ. ৯০ ↩
- ঐ পৃ. ৯১ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘কবি’, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৯ ↩
- ঐ পৃ. ২০৫ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘শুভ্র’, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩ ↩
- ঐ পৃ. ৫৩ ↩
- ঐ পৃ. ৮৭ ↩
- ঐ পৃ. ১৫১ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘জয়জয়ন্তী’, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১০১ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘দ্বৈরথ’, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৫১ ↩
- ঐ পৃ. ৫২ ↩
- ঐ পৃ. ৯০ ↩
- ‘জয়জয়ন্তী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪ ↩
- ঐ পৃ. ৮৯-৯০ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘কবি’, প্রাগুক্ত পৃ. ২০ আতাহারের কবিতাগুলো যদিও আতাহারের নয়, হুমায়ূন আহমেদ সে কথা ভূমিকাতে জানিয়েছেন ↩
- ‘কবি’, ঐ পৃ. ৩২ ↩
- যদিও কোন কোন সমালোচক ‘নন্দিত নরকে’ এবং ‘শঙ্খনীল কারাগার’ উপন্যাস দুটোকে বড়গল্প আখ্যা দিতে পছন্দ করনে। দ্রষ্টব্য বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রবন্ধ ‘বাংলাদেশের উপন্যাস’, সাহিত্য পত্রিকা, অষ্টাবিংশ বর্ষ; প্রথম সংখ্যা, আষাঢ়-আশ্বিন ১৩৯১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৮১ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘হিমুর দ্বিতীয় প্রহর’, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১২-১৩ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘রূপার পালঙ্ক’, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৮ ↩
- হুমায়ূন আহমেদ, ‘শুভ্র’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮ ↩
- দ্রঃ নাসির আলী মামুন, ‘হুমায়ূন আহমেদের সুবর্ণ জন্মজয়ন্তী’, ‘প্রথম আলো’ শুক্রবারের সাময়িকী, ঢাকা, ১৩ নভেম্বর ১৯৯৮। সে লেখায় হুমায়ূনের যে বক্তব্য নাসির উৎকলন করেছিলেন তা হলো:
মানুষের মস্তিষ্ক যেটি আছে ‘ব্রেন’ যেটি নিয়ে মানুষ বাস করছে, এটির ক্ষমতা অসাধারণ। একটা লেখা শুরু করলাম, ব্রেন একটা ফাইল খুললো, কম্পিউটারের মতো। সেই ফাইলে লেখাগুলো ব্রেন স্টোর হচ্ছে। অন্য একটা লেখা শুরু করলাম, আগের ফাইলটা ব্রেন বন্ধ করে দিলো। নতুন ফাইল খুলে গেলো আরেকটা। আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা এতোই বেশি যে, কোনো লেখক যদি এক সঙ্গে একশখানা উপন্যাস লেখা শুরু করেন সে একশখানা উপন্যাস ব্রেনের বিভিন্ন কোষে স্টোর বা জমা রাখা সম্ভব। কেউ চেষ্টা করেন না। কাজেই পারেন না। পাশ্চাত্যে অনেকেই তা করেন আমি জানি। ↩
- W. Somerset Maugham, The Summing Up (1938), 1963, P. 65 ↩