
শুরুটা করা যাক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা’ প্রবন্ধের শুরুর লাইন দিয়ে – “কথাসাহিত্যচর্চার সূত্রপাত্র মানুষ যখন ব্যক্তি হয়ে উঠেছে এবং আর দশজনের মধ্যে বসবাস করেও ব্যক্তি যখন নিজেকে ‘একজন’ বলে চিনতে পারছে তখন থেকে।” এটি মধ্যবিত্ত সমাজের এক কথাকারের কথা। চলমান বা প্রচলিত যে মধ্যবিত্ত সামাজিক অবস্থা সমাজে বিদ্যমান তার বয়ানকারী এই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। মধ্যবিত্তের অনুপুঙ্খ জীবন ও তার ঈপ্সিত স্বপ্নবাস্তবতার সাথে মূল্যবোধের আছে তুমুল দ্বন্দ্ব। কেননা তাদের এ দ্বান্দ্বিক জীবন বড়োই নিরালম্ব। সেখান থেকে জৈবিক বিন্যাস কিংবা সঠিক তাৎপর্য অনুধ্যান করা কষ্টকর। তাই মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক বলয় যে পরস্পর-বিরোধী হবে তা নিশ্চয় বলার অবকাশ রাখে না। সামন্তবাদের সাথে গ্রামীণ মূল্যবোধ মিলেমিশে বুর্জোয়া জীবন-প্রণালির যে ভিত্তিহীন সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে আজ, অনেকের কাছে তা ‘অচ্ছুৎ সংস্কৃতি’ হিসেবে গণ্য হতেই পারে। ইলিয়াস এই সংস্কৃতিরই এ অনন্য কথাশিল্পী। তাঁর ভাষায় – “অসুস্থ লোককে রোগী বলে ঠাহর করাই সমীচীন, তার রুগ্ন ও পাণ্ডুর গালে চুমু খাওয়ার মানে হয় না। দেখতে দেখতে মানুষকে চেনা হয়, লিখতে লিখতেও তার সঙ্গে পরিচয়টা গাঢ় হতে থাকে। রোগ নিয়েই তো আর মানুষ জন্ম নেয় না, এর বীজাণুর ডিপোটা কোথায় তারও খোঁজ নেওয়াটা লেখকের কাজ। লেখক সমাধান দিতে পারে না, কিন্তু রুগ্ন মানুষের সুস্থ হওয়ার কাঙাল সাধটা দেখতে পারলেও তার বাঁচবার সম্ভাবনা লেখকের চোখে পড়বে।” [আমার প্রথম বই; ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-৩’; সম্পাদনা : খলিকুজ্জামান ইলিয়াস; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা]।
এমন স্পষ্টীকরণ বিবৃতি না হয় ছেড়েই দিলাম, ইলিয়াসের যেকোনো লেখার মধ্য দিয়েই মনোযোগী পাঠকমাত্রই এমনটা দেখতে পায় অকপটে। মধ্যবিত্তের রুচিবোধ, তথাকথিত বাঙালি ভদ্রলোকের সংস্কৃতিক চর্চা ইত্যাদি ইত্যাদি শাব্দিক মারপ্যাঁচ থেকে পাঠককে মুক্তি দিয়েছেন তিনি। আর অনেকটা নির্মোহ হয়ে তুলে ধরেছেন সে সমাজের মধ্যকার অন্তঃসারশূন্যতাকে। যদিও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম (ভিন্নমতে একমাত্র) ধারক ও বাহক এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তবুও এ শ্রেণিসমাজের ভেতরকার নানা সংগতি-অসংগতি, আচার-কপটাচারগুলোকে নগ্ন করে উপস্থাপন করেছেন ইলিয়াস। নিজে এ সমাজের একজন প্রতিনিধি হয়েও এ সমাজকে সুতীব্র ও যৌক্তিক ভাষায় গাল দিতেও ছাড়েনি তিনি। তাই বুঝি নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরিটিতে লিখেছিলেন – “এ রকম ইতর মধ্যবিত্ত বোধহয় দুনিয়ার আর কোনো দেশে নেই, এখানে রাজনীতি মানে প্রতারণা আর হারামিপনা, ন্যূনতম মর্যাদাবোধ থাকলে এখানে রাজনীতি করা অসম্ভব। দেশের মানুষ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ঘেউ ঘেউ করা হলো এখানকার বুদ্ধিজীবীদের সার্বক্ষণিক তৎপরতা। বিজ্ঞানে ডিগ্রি পাওয়া মানুষ এখানে ব্যবসা করে ধর্ম নিয়ে। টাকার লোভে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার লোভে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পারে না হেন কম্ম নেই।” [সূত্র : এই শ্রদ্ধাঞ্জলি বরং প্রতিবাদ বলেই গণ্য হোক, ফারুক ওয়াসিফ, ‘প্রথম আলো’, ৫ জানুয়ারি ২০১০ সংখ্যা]
ইলিয়াসের মতে, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের উন্নাসিকতার ফলেই নিম্নবিত্ত শ্রেণির সাথে মধ্যবিত্তের ক্রমাগত বেড়েছে সাংস্কৃতিক দূরত্ব। আর এ কারণে শিকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মধ্যবিত্তরা, আছে ত্রিশঙ্কু অবস্থায়। তবে এ কথাও বলতে ভুলেন না যে, শ্রমজীবী মানুষের সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ হলেও তার সৃষ্টি-ক্ষমতা মূলত শিক্ষিত শ্রেণির হাতেই। লেখকের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই শ্রম-মানুষের সংস্কৃতি ওঠে আসে, প্রাণ পায় সাহিত্যে, পরিণত হয় শিল্পে। তাই তিনি মনে করতেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের সাথে নি¤œবিত্ত শ্রমজীবীদের দূরত্ব যত কমবে, ততই প্রাণসঞ্চারক ও সার্থক হয়ে উঠবে সাহিত্যের নানা দিক। এক্ষেত্রে ইলিয়াসের ছোট ভাই অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াসের সম্পাদিত প্রগুক্ত গ্রন্থটির ভূমিকার কিছু অংশ প্রসঙ্গিক বলে তুলে ধরছি – “আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে সাধারণভাবে একজন সার্থবাদী লেখক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি অবশ্য কখনো কোনো মতবাদের কট্টর অনুসারী ছিলেন নাÑ না ব্যক্তিগত জীবনে, না সৃজনশীল ও মননশীল লেখায়। তবে আদর্শগতভাবে তিনি এমন এক সমাজবাদে বিশ্বাস করতেন যা শ্রেণীবৈষম্যের অবসান চায় এবং যা প্রত্যেক মানুষের সহজাত সম্ভাবনার পূর্ণ স্ফূরণে আস্থাশীল। এ ধরনের বিশ্বাস শিল্পীকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে এবং শ্রেণীসম্পর্ক, শ্রেণীশোষণের আপাত ও সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াকে কাহিনী ও চরিত্রের অগ্রগতির মাধ্যমে আবিষ্কার করতে শেখায়। ফলে পাঠকও ওইসব দৃশ্যমান ও অদৃশ্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকিত হন। সার্থবাদকে ইলিয়াস রোগ নির্ণয় ও রোগের নিরাময় উভয়েরই উপায় হিসেবে মনে করতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে এই তত্ত্ব মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে তখনই যখন তা সংস্কৃতির অংশ হবে। আদর্শ বা মতবাদকে জীবনযাপনের অপরিহার্য অংশ না করে কেবল ওপর থেকে চাপিয়ে কখনোই মানুষের সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটানো সম্ভব নয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।”
কেবল বাংলাদেশের সাহিত্য বিচারে নয়, বরং সামগ্রিক বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায় এক অম্লান ও শক্তিশালী সাহিত্যস্রষ্টার নাম আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। নিতান্ত সংখ্যার আলোকে নিজের সাহিত্যকে বাঁধতে চাননি বলেই তাঁর লেখার সংখ্যানুপাত এতো নিতান্ত। সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম বলতে পাঁচটি গল্পগ্রন্থ : ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ (১৯৭৬), ‘খোঁয়ারি’ (১৯৮২), ‘দুধেভাতে উৎপাত’ (১৯৮৫), ‘দোজখের ওম’ (১৯৮৯), ‘জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল’ (১৯৯৭); দুটি উপন্যাস : ‘চিলেকোঠার সেপাই’ (১৯৮৬), ‘খোয়াবনামা’ (১৯৯৬) এবং একমাত্র প্রবন্ধ সংকলন ‘সংস্কৃতির ভাঙা সেতু’ (১৯৯৭) – এই তো। আর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে ইলিয়াসের তেমন একটা আগ্রহ ছিল বলেও মনে হয় না। কেননা বাজারি বা ফরমায়েশি লেখার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। বরং আঙ্গিক ভিন্নতা ও বাচনিক প্রকরণের প্রতি অধিক মনোযোগ লক্ষ করা গেছে তাঁর প্রতিটি লেখায়। ফলে ‘রাশি রাশি ভারা ভারা’ লেখার স্তূপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছেন তিনি। তাই বুঝি অনেকটা আক্ষেপ করে ফরহাদ মজহার উচ্চারণ করেন – “খুবই কম লিখেছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আমাদের জন্য এটা ভাল নাকি মন্দ বলা মুশকিল। তবে তাঁর খুব লোকশান হয়েছে কি? এত কম লিখে বাংলাসাহিত্যে নিজের জন্যে একটি জায়গা করে নিতে পারা দারুণ একটা ব্যাপার। ঈর্ষা করার মত। তবুও আমাদের সেই দোনামোনা থাকে না থাকে না যে, আখতার সবাইকে একটু চীট করেছেন। প্রতারণা। বোধ হয় তিনি আরো লিখতে পারতেন, লিখেন নি। তিনি আর লিখবেন না এটা মস্ত বড় লোকশান। আমরা ঠকেছি।” [ইলিয়াসের গল্প, মেডিকেল তত্ত্ব ও টেকনোলজি সংক্রান্ত ভাষ্য, ফরহাদ মজহার, ‘দৈনিক বাংলাবাজার’, ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৭]
এ কথা অস্বীকার করার জো নেই, যতখানি ইলিয়াস লিখেছেন, ঠিক ততখানিই হয়ে উঠেছে শিল্প-বিচারে বিশ্বমানের। সসীম জীবনের অসীম ও গাঢ়তর মর্মার্থকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে দ্বিধাহীন প্রকাশের ক্ষমতা ছিল তাঁর অনবদ্য। তুমুল কৌতূহলে শিল্পকে প্রকাশ করার যে ভঙ্গি তাঁর আত্মগত ছিল তা একান্তই স্বতন্ত্র। এমনকি বানানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিরীক্ষা। যেমন : ‘দুটো’র বদলে ‘২টো’, ‘একবার’-এর বদলে ‘১বার’ ইত্যাদি বানানরূপ লিখতে দেখা যায় তাঁর রচনাগুলোতে। তবে দ্ব্যর্থহীন প্রকৃতি তাঁকে খুব বেশি সময় দেয়নি এ জগৎটাকে উপলব্ধি করার। এ জন্যই হয়ত স্বল্পায়ু নিয়েই শানিত দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন জানা কিংবা অজানা পরিবেশকে। যাপিত জীবন ছাড়াও যে দেখার কিংবা বোঝার বিষয়বস্তু আছে তা নিষ্ঠাবান পাঠকের ইলিয়াস পাঠ করলেই উপলব্ধ হয়। তাঁর লেখায় পাওয়া যায় গাঢ় জীবন-চেতনা ও সূক্ষ্ম হাস্যকৌতুকের সম্মিলন। নিম্নবর্গের মানুষের কথ্য ভাষাও মর্যাদা পায় তাঁর রচনায়। নিছক গপ্পের ফাঁদে পাঠককে বন্দি করতে চাননি তিনি। তাঁর লেখায় পাঠক জাগ্রত হয় অথবা নাড়া খেয়ে জেগে ওঠে। ইলিয়াসের স্বগতোক্তি – “আমি যেভাবে মানুষকে দেখি, মাস্টারমশাইরা যাবে বলে পর্যবেক্ষণ, আমার তোত্লা কলমে তাই লিখতে চেষ্টা করেছি। সমাজের ভেতরে থেকে এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলি বজায় রেখেও মানুষ কেবলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার এলাকা ঢুকে পড়ে একটি বাড়ির ভেতর, বাড়ি গুটিশুটি মেরে ঠাঁই নেয় ঘরে, ঘর পরিণত হয় কামরাতে এবং ঐ কামরাও শেষ পর্যন্ত সংকুচিত হতে হতে রূপ নেয় কোঁচকানো শরীরে। সবাই এবং আর সবাই তার কাছে অপরিচিত এবং অস্বস্তিকর। তার দিকে কেউ হাত বাড়ায় না। তার চেয়েও বড়ো কথা কারো হাতে তার আস্থা নেই। …যে কোনো স্তরের এবং যে কোনো শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতার সংকট দেখা যায়। এতে লেখকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে না। কিন্তু তখন এটাই আমার চোখে পড়েছে এবং এটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। বিচ্ছিন্নতাকে নিঃসঙ্গতার বেদনা বলে গৌরব দেওয়া একটি অসহ্য প্যানপ্যানানি প্রবণতা।”
ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস ‘চিলেকোঠার সেপাই’। মহান সেই অভ্যুত্থানের প্রধান শক্তি যে শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষ, তাদেরকে পরবর্তী সময়ে কীভাবে বঞ্চিত, প্রতারিত বা অবহেলিত করা হয়েছে তারই এক চমৎকার আখ্যান চিলেকোঠার সেপাই। অনেক সাহিত্যবোদ্ধার কাছে এটিই ইলিয়াসের শ্রেষ্ঠ কৃতি। গত শতকের আশির দশকের শুরুতে উপন্যাসটি সাপ্তাহিত ‘রোববার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৮৬ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। উপন্যাসটির প্রধান চার চরিত্র – ওসমান গনি ওরফে রঞ্জু, তার বন্ধু বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী আনোয়ার, ডানপন্থী রাজনীতিক আলতাফ এবং শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিনিধি বিপ্লবী খিজির ওরফে হাড্ডি খিজির। উপন্যাসের শুরুতে মেলে ওসমানের দেখা – শেষেও তাই। পুরো আখ্যানের সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করে আছে এই ওসমান গনি। অথচ উপন্যাসটির মূল ঘটনাবলির সাথে তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। সে কেবল অবলোকন করে যায়। কোনো কিছুই পর্যবেক্ষণ করে না। কেননা এই পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িয়ে আছে পর্যালোচনা, যা উপন্যাসে কোথাও তাকে করতে দেখা যায়নি। গণ-আন্দোলন থেকে গণ-অভ্যুত্থান কিছুতেই যেন সম্পৃক্ত নয় ওসমান। কিন্তু উত্তাল সেই ঘটনার অভ্যন্তরেই থাকতে হয় তাকে। পুরান ঢাকার মহাজন রহমতউল্লা যে কিনা আইয়ুব খানপ্রেমী, তার বিল্ডিংয়ের চিলেকোঠার একমাত্র ঘরে ওসমানের বসবাস। সেখানে বসেই সে রাস্তা দেখে। রাস্তার ওপর রিকশা, বেবিট্যাক্সি, নারায়ণগঞ্জগামী বাসের পাশাপাশি হেঁটে চলা মানুষের ভিড় ও মিছিল দেখে। চাকরি করে ইপিআরসি’তে। অফিস যেতে পথে দেখে বাহাদুর শাহ পার্কের বা পল্টনের জনসভা। খাবারের দোকানে বসে রাজনীতিতে সক্রিয় বন্ধুদের কাছে শোনে আন্দোলন-সংগ্রামের কথা। কিন্তু এগুলোর কোনো কিছুই তাকে তেমনভাবে জড়িত করতে পারে না। তার চিন্তার জগৎ জগতে আছে ফেলে আসা বাবার চিন্তা, বিল্ডিংয়ের দোতলার ভাড়াটে মকবুল হোসেনের একমাত্র মেয়ে অর্থাৎ নিজের নামের সাথে মিল পাওয়া রঞ্জুর বড়ো বোন রানুর কিংবা অন্য বন্ধুদের চিন্তা। তবে এমনটা নয় যে সে দেশব্যাপী চলমান ঘটনা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। চিন্তা করে, অনেক চিন্তা ঘুরপাক খায়। না খেয়েও তো কোনো উপায় নেই। কেননা, সেসময় ঢাকা তো বটেই পূর্ব পাকিস্তানের সকল চেতনাবান মানুষকেই নাড়া দিয়েছে এ গণ-আন্দোলন। এর আগে ঢাকার নীলক্ষেত পাওয়ার স্টেশনের কেরানি ওসমানদের বিল্ডিংয়ের সেই রানুর ভাই আবু তালেব পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হয়। এ ঘটনার রেশ ধরেই গণ-অভ্যুত্থানে শরিক হওয়া শ্রমজীবী মানুষগুলোর সাথে একে একে পরিচয় হতে থাকে পাঠকের। দিনরাত চলে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা। আর তার কারণে এমনকি শত বছরের আগে বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য নবাব আবদুল গনিকে দিয়ে পোঁতানো পামগাছ অথবা সেই সব পামগাছের বাচ্চারা ভালোভাবে ঘুমাতে পারে না মানুষের সমবেত স্লোগানে – “শহীদের রক্ত – বৃথা যেতে দেবো না” “আইয়ুব শাহী জুলুম শাহী”। ফলে ওসমানেরও কমে যায় ঘুম। আর সেসময় সে দিবাস্বপ্ন দেখে। বেশির ভাগ সময়ই সেইসব স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। তবে নানামুখী অসংগতির কারণে কোনোভাবেই নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না ওসমান। তাই তার ভেতর জন্ম নেয় প্রচণ্ড ক্ষোভের। সবকিছুর সাথে জড়িত থেকেও কোনো কিছুরই প্রতিকার করতে পারে না সে। এ ব্যর্থতা তার ব্যক্তিত্বকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক স্খলন ও সমাজের পচনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, পরিণত হয় সিজোফ্রেনিয়া রোগীতে। তবে কারো কারো মনে প্রশ্ন দানা বাঁধে – এ আন্দোলনের শেষ কোথায়? এছাড়া আইয়ুব খান তথা পাকিস্তানিদের প্রতি মানুষের এমনই ঘৃণা যে হোটেলের দেয়ালে কোথাও কোনোখানে আইয়ুব খানের ছবি দেখলেই আন্দোলনকারীরা এসে সেটি গুঁড়িয়ে দেয় – “আইয়ুবের দালালি – চলবে না, চলবে না
। ভাঙো হালা চুতমারানির ছবি ভাইঙা ফালাও। কুত্তার বাচ্চারে লাথি মাইরা ভাঙ!” কিন্তু তাতে করে কী বয়ে আনবে, এমন প্রশ্নও দেখা যায়। এর ফলে কি অপসারণ হবে আইয়ুব খানের, কিংবা স্বায়ত্তশান বা ছয়দফা বা স্বাধীনতা লাভ? কিন্তু মানুষের আকাক্সক্ষার পরিমাণ তো তার চেয়েও বেশি। আনোয়ারের একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে উঠে আসে এ আকাক্সক্ষার কথা – “ভাষা, কালচার, চাকরি-বাকরিতে সমান অধিকার, আর্মিতে মেজর জেনারেলের পদ পাওয়া – এসব ভদ্রলোকের প্রবলেম। এই ইস্যুতে ভোটের রাইট পাওয়ার জন্যে মানুষের এত বড়ো আপসার্জ হতে পারে?” তাই ওসমানের এ কলেজ শিক্ষক বন্ধুটি একসময় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে সর্বহারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনে। বাম রাজনীতি চেতনায় দিক্ষিত এ মানুষটি একপর্যায়ে তাই গ্রামে ফিরে যায় চাষা-ভুষা মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। এদিকে সাধারণ মানুষ রাজনীতির জটিল প্রশ্নের উত্তরের তোয়াক্কা না করে শারিক হয়েছে গণ-আন্দোলনে। আর সেই আন্দোলনকারীদের অন্যতম প্রতিনিধি হাড্ডি খিজির। তার প্রথম ক্ষোভ প্রকাশ পায় নিজের মুনিব রহমতউল্লার ওপর, যে নাকি তার মা ও বোন দুজনকেই ভোগের পণ্য বানিয়েছে। খিজিররা শহরে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তেমনই গ্রামে-গঞ্জে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার লড়াকু চেংটু, করমালি, আলিবক্সরা। যমুনা পাড়ের এ মানুষগুলোর কাজ আরো একটু এগিয়ে। তারা যেমন হাজার মাইল দূরের আইয়ুব খান বা পাকিস্তানি বাহিনীর শোষণ দেখতে পায়, তেমনি চোখের সামনে দেখতে পায় খয়বার গাজী, আফসার গাজীদের কার্যক্রম। তারা জানতে পারে এইসব খয়বার গাজীরাই হচ্ছে আইয়ুব খানের পদলেহনকারী। আইয়ুব খানরা যদি প্রকা-দেহী জোঁক হয়, তবে সেই জোঁকের মুখ হচ্ছে খয়বার গাজীরা। আর তাই জোঁকের মুখে লবণ দেওয়ার কাজটা করতে চায় তারা। কিন্তু তাতে করে সমর্থন মেলে না আইয়ুব-বিরোধী ছয় দফা দাবিদার নেতার কাছ থেকে। এর কারণ, সেই সব নেতারাও যে খয়বার গাজীদের শ্রেণির উত্তরসূরি। এদিকে খয়বার গাজীরা অযথা মানুষের নামে মামলার প্যাঁচে ফেলে, জমিজমা দখল করে। আর এর প্রতিবাদ করলেই তার লাশ মেলে মাঠে-নদীতে। এমনকি হাজারো মানুষের চোখের সামনেই নিজের অবাধ্য কৃষককে খুঁটির সাথে বেঁধে পুড়িয়ে মারতেও দ্বিধা করে না খয়বার গাজীরা। মামলায় খয়বার গাজীদের আদালত কখনো শাস্তি দেয় না। কারণ সরকারি আদালত তো এক অর্থে তাদেরই আদালত। তাই চেংটু, করমালি, আলিবক্সরা বসাতে চায় গণ-আদালত। সেখানে তারা বিচার করতে চায় খয়বার গাজীদের। বিচার করতে চায়, কারণ এত দিন পর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে। মানুষ জেগে উঠেছে। যমুনা নদীতে শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার ডাক। সেই ফকির মজনু শাহের সময় থেকে দিয়ে আসছে এ ডাক। “বড় ধরনের বালা-মুসিবত, সংকট, বিপদ-আপদ, দুর্যোগ, বিপর্যয় সামনে থাকলে যমুনার মধ্যে দেড় শ দুই শ ঘোড়া সংকেত দেয়।” তবে এবারের বালা-মুসিবত খয়বার গাজীদের। এদিকে ডাকাত-মারা চরের বাথান লুট হয় খয়বারের। বিক্ষুব্ধ মানুষের হাতে নিহত হয় তার প্রধান অনুচর হোসেন আলী। গণ-আদালতে বিচার হবে খয়বার গাজীর। আদালতে সকলের সম্মতিক্রমে তার রায় দেওয়া হয় মৃত্যুদ-। আদালত বসে বৃহস্পতিবারে। কিন্তু মৃত্যুর আগে সে তার শেষ ইচ্ছের কথা বলে সবাইকে। আগামীকাল শুক্রবার সে তার জীবনের শেষ জুমার নামাজটি আদায় করতে চায়। এর পর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক – আপত্তি নেই। মুহূর্তেই গলে যায় উপস্থিত সকলের মন। আহা! তার জীবনের শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করতে দেওয়া হোক। তবে আনোয়ার বুঝতে পারে খয়বার সময় চেয়ে নিচ্ছে, সুযোগ পেলেই কেটে পড়বে। আলিবক্স ব্যাপারটি ধরতে গিয়ে ধরতে পারে না। এদিকে মানুষ খয়বার গাজীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে যেমন একমত, তেমনি তাকে শেষবারের মতো জুমার নামাজ আদায় করতে দেওয়াতেও একমত। এর পরিণতি – খয়বার গাজী পালিয়ে যায়, নিজের লোকদের গুছিয়ে নেয়, প্রশাসনের সাহায্যে আলিবক্সকে এলাক
াছাড়া করে এবং চেংটু মারা পড়ে। এর পর পরই মানুষ ফের ফিরে আসে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে। বিরোধী পক্ষের নেতা হয় খয়বার গাজীর লম্পট-মদ্যপ ভাতিজা আফসার গাজী। ক্ষমতার বদল ঘটে পূর্বাকার শ্রেণিদের মধ্যেই।
উপন্যাসটি প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক জাকির তালুকদারের একটি লেখা মনে পড়ে যাচ্ছে। চমৎকার সেই লেখার কিছু অংশ তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। “ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের ওপর যেসব ইতিহাসগ্রন্থ লিখিত হয়েছে, সেগুলোতে হয়তো নির্ভুল তথ্য রয়েছে, কিন্তু সেগুলো পাঠ করে কেউ সেই দিনগুলোর উত্তাল মুহূর্তগুলোকে অনুভব করতে পারবেন না। কারণ লিখিত বিবরণ কোনো দিনই রক্তের দানায় দানায় ছড়িয়ে থাকা উত্তেজনা, উত্তাপ, আকাক্সক্ষা, ক্ষোভ, গ্লানি এবং আনন্দকে তুলে আনতে পারে না। বিশেষ করে প্রবন্ধ বা দলিল। তাই বলে দলিলের কোনো উপযোগিতা নেই, এমন কথা মূর্খ ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আমরা ইতিহাসগ্রন্থ আকারে যেসব দলিল হাতে পেয়েছি, সেগুলোতে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ইলিয়াসকথিত মানুষের ‘আরো অনেক কিছু’ চাওয়ার বিষয়টি। এ ব্যাপারটিকে ধরতে পেরেছিলেন ইলিয়াস, এই শূন্যতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন – খুঁজছিলেন এমন একটি গ্রন্থ, যেখানে ঊনসত্তরে মানুষের আত্মদানের এবং আকাঙ্ক্ষার সঠিক মাত্রাগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। পাননি। পাননি বলে নিজেকেই লিখতে হলো তাঁর। আর ঔপন্যাসিকের কলমে এবং উপন্যাসের আঙ্গিকে বেরিয়ে এল বাঙালির ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্দোলনের হৃদস্পন্দন – চিলেকোঠার সেপাই। … বাংলা ভাষার গুটিকয় সফল উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম একটি উপন্যাস ‘চিলেকোঠার সেপাই’। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাসের জন্য আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় সেই ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর। কারণ? ওই যে অ্যাঙ্গেলস বলেছিলেন, ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের মধ্যে ওই সময়ের চালচিত্র যত নিখুঁতভাবে পাওয়া যায়, সব ইংরেজ ইতিহাসবিদের সব পুস্তক একত্র করলেও সেটা পাওয়া যাবে না। এখানেই তো সত্যিকারের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব।” [সূত্র : চিলেকোঠার সেপাই-ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, জাকির তালুকদার]
‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের প্রথম দুটি লাইনের দিকে পাঠককে ফের দৃষ্টি দিতে বলব। দীর্ঘ বাক্য দুটিতে কী আছে তা খুঁজতে বলব আবার – “পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলার রগ টানটান করে যতোটা পারে উঁচুতে তাকিয়ে গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে তমিজের বাপ কালো কুচকুচে হাত দুটো নাড়ছিলো, ঐ জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করা দরকার। অনেকদিন আগে, তখন তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, তার বাপেরও জন্ম হয় নি, তার দাদা বাঘাড় মাঝিরই তখনো দুনিয়ায় আসতে ঢের দেরি, বাঘাড় মাঝির দাদার বাপ না-কি দাদারই জন্ম হয়েছে কি হয় নি, হলেও বন-কেটে বসত-করা বাড়ির নতুন মাটি ফেলা ভিটায় কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, ঐসব দিনের এক বিকালবেলা মজনু শাহের বেশুমার ফকিরের সঙ্গে মহাস্থান কেল্লায় যাবার জন্যে করতোয়ার দিকে ছোটার সময় মুনসি বয়তুল্লা শাহ গোরা সেপাইদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে গিয়েছিলো ঘোড়া থেকে।” প্রিয় পাঠক, পড়ার পর মনে হয় না যেন এক অদৃশ্য শক্তি দিয়ে মুহূর্তেই জালবন্ধে আটকে ফেলেছে আষ্টেপৃষ্ঠে? এ যেন অবিচ্ছিন্ন বাঁধন। ইলিয়াসের এ জাদুটা রপ্ত ছিল বেশ ভালো রকম। আজকের ভাষায় যাকে বলে ম্যাজিক রিয়েলিজম, বাংলায় তার প্রয়োগের পূর্ব রূপ ছিল এমনটা। ঘোর লাগা ঘূর্ণিপাক। স্থান-কাল-পাত্র একাকার হয়ে পড়ে। কাৎলাহার বিল, যার পাশে বসে পোড়াদহের মেলা। যেখানে একসময় আখড়া গেড়েছিল ফকির মজনু শাহ আর ভবানী পাঠকের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বেশুমার ঘোড়সওয়ারেরা। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত শ্লোক আর গাথায় সমৃদ্ধ যমুনা তীরে জেলে-মাঝি-কৃষকের জীবনকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছে এ উপন্যাস। খোয়াবনামা একদিকে যেমন তেভাগা আন্দোলন, অন্যদিকে তেমন পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যকার সময়ে গ্রামীণ জীবনের কাক্সিক্ষত-অনাকক্সিক্ষত চিহ্নগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছে বিস্তৃত ক্যানভাসে। অন্যভাবে পর্যলোচনা করলে দেখা যায়, স্বপ্নের পাকিস্তান যে অচিরেই কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যায় বাঙালি মুসলমান কৃষকের চোখের সামনে, তারই এক অনন্য আখ্যান এটি। তমিজ-ফুলজান তারই নগণ্য প্রতিনিধি মাত্র। প্রাবন্ধিক-গবেষক শান্তনু কায়সার তাঁর এক লেখায় ইলিয়াসের বন্ধু মির্জা হারুন-অর রশিদের চিঠির বরাত দিয়ে জানান – “প্রাথমিক অধিদপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর থাকার সময় (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস) গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থা ও বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত বিষয় নিয়ে যেমন সরেজমিন অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, বরেন্দ্রভূমিতে গিয়ে তেমনি সেখানকার সৌন্দর্য, নৃতত্ত্ব ও স্থাপত্য বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। পরিশ্রুত হলেও মূল এই ভিত্তিই তাকে (ইলিয়াস) খোয়াবনামা রচনায় অনুপ্রাণিত করে।” [সূত্র : নির্মাণ-বিনির্মাণের ইলিয়াস, শান্তনু কায়সার]
‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিপুণভাবে ওঠে এসেছে। এ উপন্যাসের পটভূমি হলো গত শতকের চল্লিশের দশক। চারিদিকে তখন চলছে দুর্ভিক্ষ। এরই ভেতর আধিয়ার বিদ্রোহ পেরিয়ে জোট বাঁধছে বাংলার কৃষক। যুদ্ধের বাজারে সীমিত হয়ে পড়েছে কাজ, কমে গেছে শ্রমের মজুরি। ফসলি বীজ কেনার পয়সা নেই কৃষকের। এদিকে আধপেটা খেয়ে কোনো রকম দিন পার করছে গ্রামের দরিদ্র-অসহায় মানুষ। তারপরও স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় – ‘নিজ খেলানে ধান তোলো’, ‘জোতদার মজুতদার হুঁশিয়ার’। এদিকে পাকিস্তানের দাবি, ছেচল্লিশের ভোটাভুটি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গায় পাল্টে যেতে থাকে ইতিহাসের পট, ভাগ হচ্ছে দেশ। এর মধ্যেই কোনো এক গাঁয়ের ‘তমিজের বাপ’ বিলের ধারের কাদায় পা গেঁথে সেখানকার পাকুড় গাছের ডালে দেড়শো বছর আগের গোরা-ঠ্যাঙানো ভবানী সন্ন্যাসীর পাঠান সেনাপতি ‘মুনসি’কে এক পলক দেখার আশায় দিনের পর দিন আকাশে জমা ছাই রঙের মেঘ তাড়িয়ে বেড়ায়। উপন্যাসে তমিজের বাপ এক বিচিত্র চরিত্র। তার জন্ম বা মৃত্যুর হদিশ নেই, এমনকি নাম পর্যন্ত জানা যায় না কোথাও। মুখে মুখে শ্লোক আউড়ে গ্রামের লোকের ব্যাখ্যাতীত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বেড়ায় সে। এ যেন এক অলৌকিক মানুষ লৌকিক মানুষের আশেপাশে বসবাস করে। লৌকিকতা বলতে তমিজের বাপের আছে ফকিরি, ভিক্ষাবৃত্তি, অকারণে বেগার খাটা আর কঙ্কারসার শরীরে সীমাহীন ক্ষুধা। এই তমিজের বাপের কাছেই আছে ইলিয়াসে সেই গোপন খোয়াবনামা। কারণ চেরাগ আলি ফকিরের কাটাকুটি করা খাতায় সন্ধান মেলে সকল স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা এ তমিজের বাপে জানে। একদিকে ভাবলে তমিজের বাপ এ উপন্যাসের অতীত ও ভবিষ্যতের অতীন্দ্রিয় যোগসূত্র। এই আখ্যানে আছে স্মৃতিবাস্তবতা, ইতিহাসের পাশাপাশি কিংবদন্তী, প্রান্তিক মানুষ ও তাদের পূর্ব-প্রজন্মের সহবস্থান। এ যেন ইতিহাস না হয়েও এক খণ্ড ইতিহাস।
‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসটি ১৯৯৪ সালে ‘দৈনিক জনকণ্ঠ’ পত্রিকার সাহিত্য পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। কিন্তু পুরো উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার আগেই রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে ‘জনকণ্ঠ’ কর্তৃপক্ষ এর ছাপা বন্ধ করে দেয়। এদিকে ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে মাকে হারান ইলিয়াস। মায়ের মৃত্যুর পর পরই নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পায়ের তীব্র ব্যথা উপেক্ষা করে সেসময় দিনরাত লিখতে থাকেন ‘খোয়াবনামা’র এক একটি অধ্যায়। ডাক্তাররা তখন মরণব্যাধি ক্যান্সারকে বাত ভেবে কেবলই ভুল চিকিৎসা করে যাচ্ছিলেন। তারই মধ্য দিয়ে ৩১ ডিসেম্বর শেষ করেন এ উপন্যাস। ১৯৯৬ সালের ১৩ জানুয়ারি ইলিয়াসের পায়ে ধরা পড়ে ক্যান্সার। তখন অনেকটাই পার হয়ে গেছে সময়। ২০ মার্চ তাঁর ডান পা সম্পূর্ণ কেটে ফেলে দিতে হয় ক্যান্সারের কারণে। এর আগে সে বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয় ইলিয়াসের শ্রেষ্ঠ রচনা মহাকাব্যোচিত উপন্যাস ‘খোয়াবনামা’।
কোথায় যেন পড়েছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী একবার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কে বলেছিলেন – “কি পশ্চিম বাংলা কি বাংলাদেশ, সবটা মেলালে তিনি (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস) শ্রেষ্ঠ লেখক। ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম।”
অঞ্জন আচার্য: কবি ও সাংবাদিক

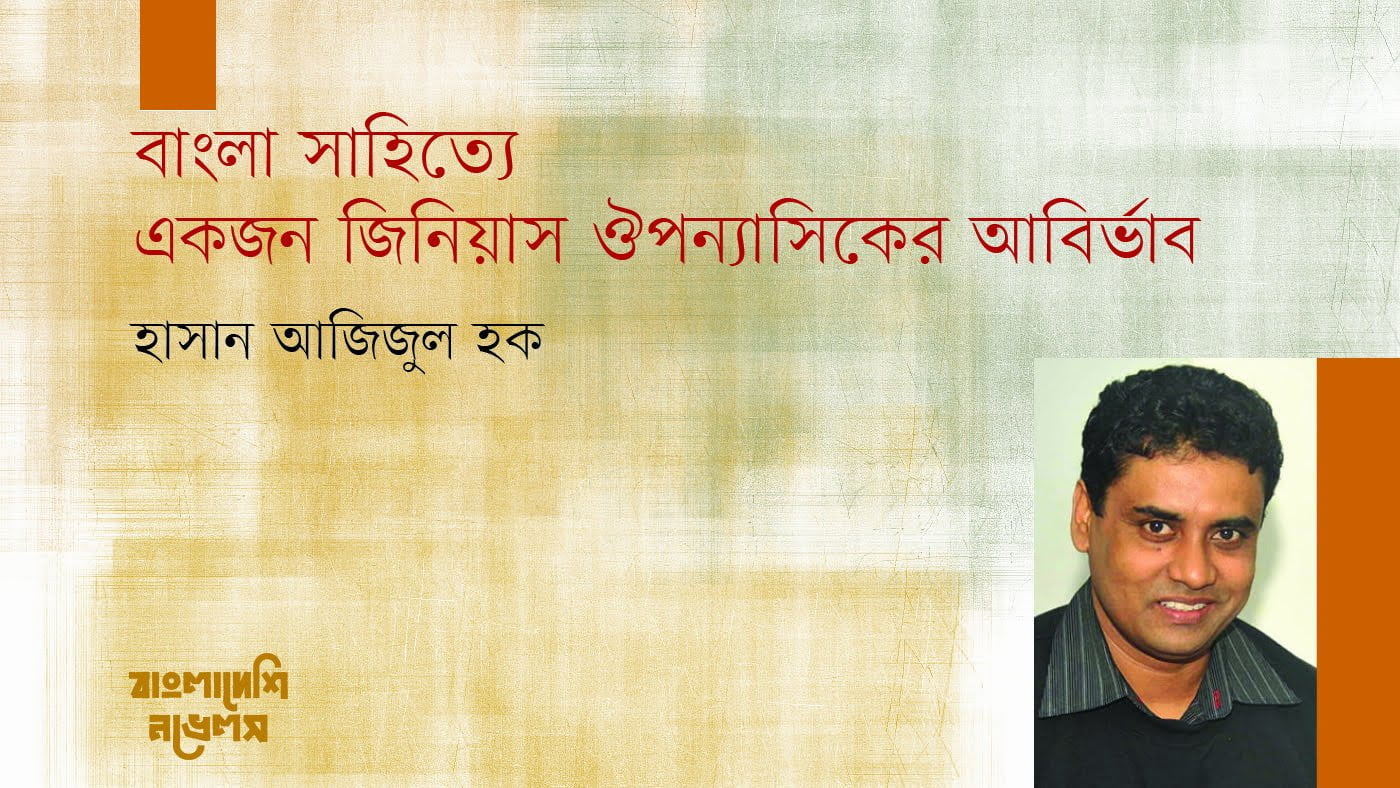

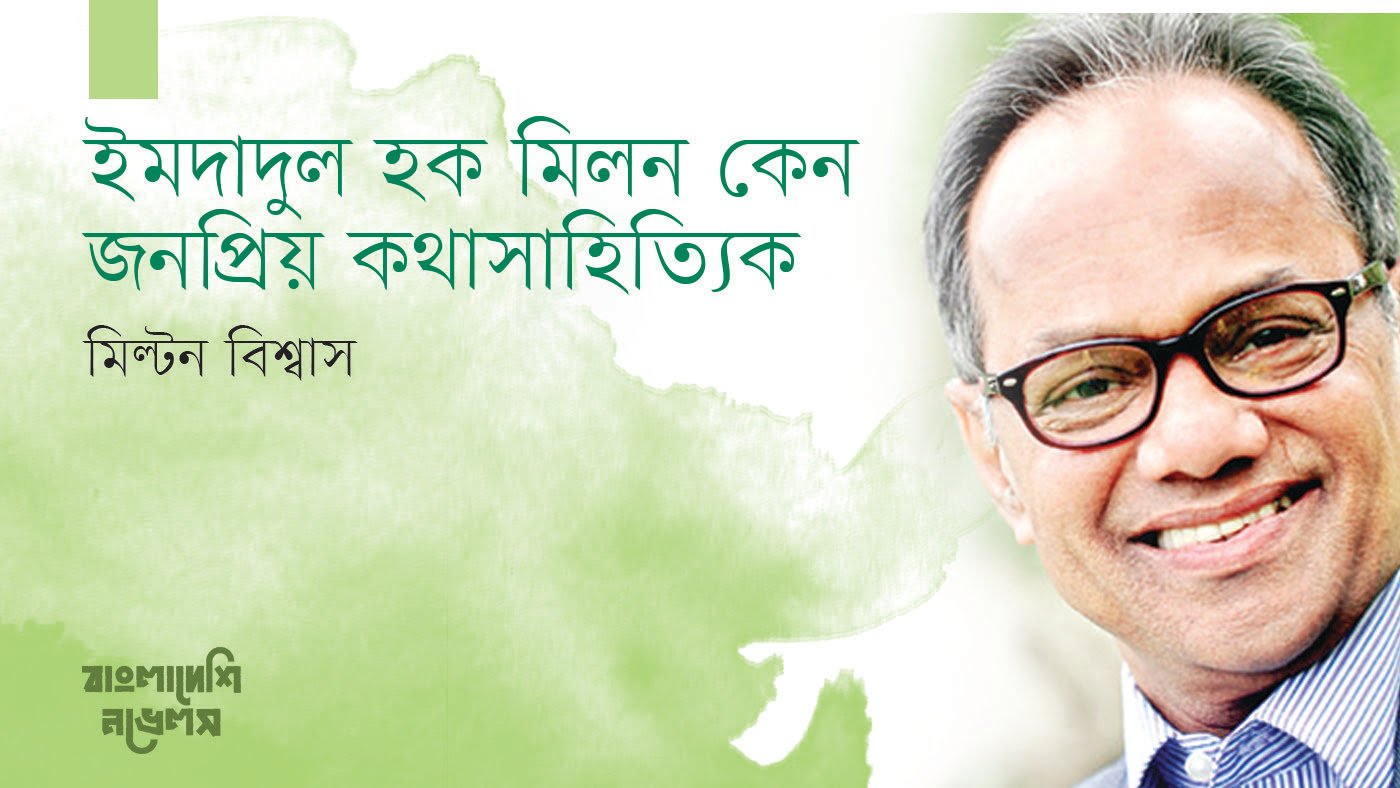





One Comment
sulaiman suman
প্রিয় লেখককে নিয়ে লেখার জন্য ধন্যবাদ।