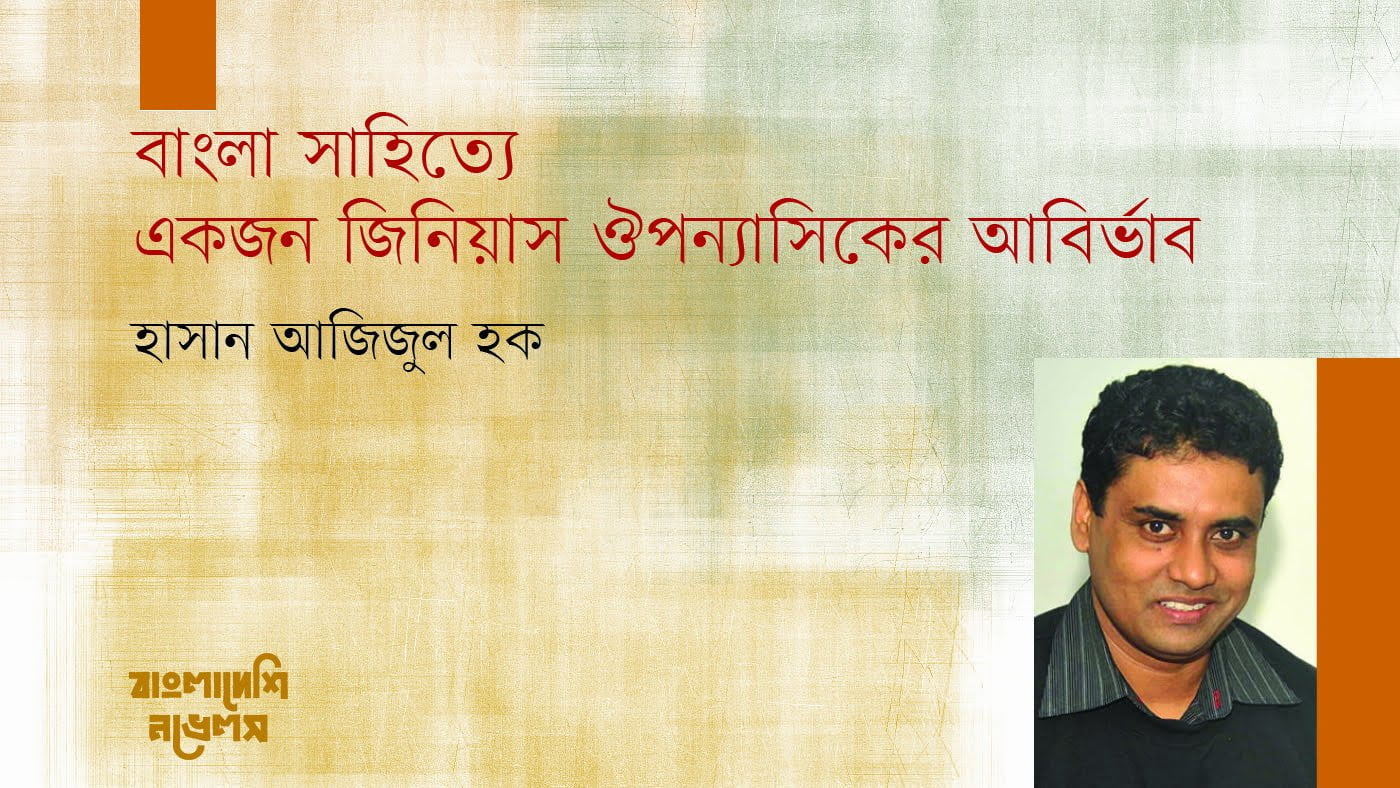মধ্যযুগে বাংলায় যখন পদ্য-সাহিত্য নির্মাণ শুরু হয়েছিল তখন সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদ্য-সাহিত্যের ছন্দ ও ভাবের ভেতর বাংলা অঞ্চলের লোকভাষার ভাব ও ছন্দের সামঞ্জস্য রক্ষা করে সান্ধ্য ভাষায় একটা নতুন নির্মাণের সুযোগ এসেছিল, বাংলা ভাষার ভ্রুণের সঞ্চার হয়েছিল, ভাষাটার আদিরূপ দানা বাধতে শুরু করেছিল। কিন্তু ঊনিশ শতকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শুরুর সময়ে সে-সুযোগটা ছিল না। সংস্কৃত তখন মৃত ভাষা, রামায়ণ মহাভারতের মতো আখ্যান কাব্যগুলোকে ধর্মগ্রন্থ করে তোলা হয়েছে। জাতকের গল্পগুলোও ধর্মাধিকারীদের হাতে পবিত্র পঠন হয়ে উঠেছে। ঈসপের গল্পের মতো ওগুলো আর সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি।
বাংলা ভাষাটা অবশ্য দাঁড়িয়ে গেছে ততদিনে। শিল্প হিসেবে উপন্যাস অনেকটা অচেনা ছিল তখন। উপনিবেশে থাকার ফসল হিসেবে ওটা নিতে হয়েছিল ইউরোপ থেকে। এরও আগে, মাঝখানের কয়েকশো বছরের পরাধীনতার কালে পশ্চিম এশিয়া থেকে আসা শাসকদের হাতে বাংলা সাহিত্যে গ্রহণ-বর্জনের কোনো বিষয় ছিল না। যদিও সুলতান ইলিয়াস শাহ চৌদ্দ শতকে বাংলা ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া শুরু করেছিলেন। বিশ্বখ্যাত ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসি প্রমুখ মনিষীদের সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষায় এসেছে পশ্চিম এশিয়ার শাসকবর্গের উত্তরসুরীদের পরাজয়ের পর। বাংলাকে শুধু শাসন ও শোষণই করেছে ঐসব আগ্রাসী শাসকগোষ্ঠি ও তাদের দেশীয় উত্তরপুরুষেরা। বলা যেতে পারে বাংলার শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কিছুই করেনি ওরা। একটা জাতির বৌদ্ধিক মনোবৃত্তি গড়ে উঠার কোনো সুযোগ আসেনি সুদীর্ঘ ঐ সময়টায়। সেন-বর্মন রাজাদের আমলে যে তিমিরে ঢুকে পড়েছিল বাংলার জনগোষ্ঠি তা থেকে আরো গভীর তিমিরে তলিয়ে যায় পশ্চিম এশিয়ার ঐসব শাসকদের যাঁতাকলের নিচে এসে। বাংলা নামের এই অন্ধকূপের বাইরের জগতটা দেখার কোনো সুযোগ ছিল না এদেশের মানুষের। ইউরোপের উপনিবেশ-কালে কিছুটা সুযোগ আসে বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সামান্য জানার ও কিছুটা চাক্ষুষ করার।
ইউরোপ, বা আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে, ইংরেজি সাহিত্য থেকে উপন্যাসের আঙ্গিকটা এসেছে বাংলা সাহিত্যে। গল্প বলার একটা ঐতিহ্য আগে থেকেই ছিল এখানে। ফলে উপন্যাস রচনা করা সে-সময়ের সাহিত্যিকদের জন্য খুব কঠিন হয়নি। বঙ্কিম, রবিঠাকুর, তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেক শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের মাধ্যমে উপন্যাস শিল্পের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠে বাংলা সাহিত্যে। ফুলে ফসলে এত দ্রুত উপচে উঠে ওটা যে বাংলা উপন্যাস শিল্পকে এখন মনেই হয় না যে এটার দুশতকও পেরোয়নি, যেখানে বাংলা পদ্য-সাহিত্যের রয়েছে হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য।
ইউরোপের উপন্যাস শিল্পের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় ব্যপকভাবে ওটার শুরু সতেরো শতকের শুরুতে, সারভেন্তেসের ‘ডন কুইক্সোট’-এর পর। বাংলা সাহিত্য তখন পরাধীনতার চাপে প্রায় পুরোপুরি বিলীন। ইউরোপের উপন্যাস শিল্প শুরুর প্রায় দুশো বছর পর বাংলা সাহিত্যে এটার শুরু আবার অন্য এক পরাধীন পর্বে। বাংলার পদ্য-সাহিত্যের উন্মেষকালে স্বাধীনতা বা পরাধীনতা শব্দটাই হয়তো কোনো বিশেষ অর্থ বহন করতো না। কিন্তু গদ্য-সাহিত্যের যাত্রাটা পরাধীনতার সময়ে, এবং অনেক পড়ে শুরু হলেও এর মান পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উপন্যাস শিল্পকে অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে কম করে হলেও দশ বিশ জন ঔপন্যাসিক রয়েছেন যাদের নির্মাণ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অনেক ঔপন্যাসিকের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে বাংলা ঔপন্যাসিকদের পরিচিতি না আসার একটা কারণ হতে পারে এঁদের প্রায় সবার আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বমনস্কতা কারো ছিল না, বলা যায় ঐ ভাবনাটাই তৈরি হয়নি তাঁদের ভেতর। বিশ্বমনস্কতা গড়ে উঠার কোনো কারণও ছিল না। বিশ্ব-সাহিত্যের বিষয়-আশয় সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের কোনো সুযোগ ছিল না। তাছাড়া ঘরের ভেতরটাও ছিল শূন্য। ফলে ভাষা, আঙ্গিক, বিষয়, ভাব প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই ছিল আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি, ও ক্ষেত্র-বিশেষে কিছুটা পাশ্চাত্য প্রভাব। ফলে ওরকম কোনো স্বকীয়তা গড়ে উঠেনি তাঁদের রচনাকর্মে যা বিশ্ব সাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য যে অনুবাদক, আলোচক ও উপস্থাপক চক্রটা গড়ে উঠা প্রয়োজন তা এখনো হয়ে উঠেনি। প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে আসা এখনো সম্ভব হয়নি বাংলা সাহিত্যের।
ব্যতিক্রম ছিলেন রবিঠাকুর। কিন্তু কবিতা, গান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেকে যতটা উজাড় করে দিতে পেরেছিলেন তিনি, উপন্যাসে ততটা না। এরপর বুদ্ধদেব বসুতে এসে দেখা যায় বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এবং তখনই, শুধু বাংলা অঞ্চলটাই না, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নেমে আসে দেশভাগের নির্মম কুঠার। এটার প্রভাব আরো কয়েকশো বছরেও শেষ হবে কিনা তা বুঝতে পারা সত্যিই কঠিন। বাংলা বিভাজনের ফলে একটা জাতির গড়ে উঠার সময়ে বৌদ্ধিক দিকটার যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা বোঝা যায় তার শিল্প ও সংস্কৃতি চেতনার পরিবর্তন থেকে। বিভাজনের ফলে এপার বাংলার মানুষেরা আরো দুই যুগ সংগ্রাম করে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব তৈরি করেছে। কিন্তু এটা ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে এসে পুরোপুরি বিকশিত হতে পারছে না। ঊনিশশো একাত্তরের স্বাধীনতা অর্জনের ঊষাকালে এদেশের পাকি দোসররা পুরো জাতিটাকে প্রায় মেধাশূন্য করে ফেলেছিল। বাকি মেধাটুকু নিঃশেষ করা হয়েছে পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর। এর পর থেকে মেধার বহির্মুখী স্রোত যে গতিতে বয়ে যেতে শুরু করেছে তা স্তিমিত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। ফলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রায় সব ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক শূন্যতা দেখা দিয়েছে। সাহিত্যে এর প্রভাব এত স্পষ্ট যে উল্লেখ করার মতো উঁচুমানের সাহিত্য সৃষ্টি একেবারে হাতে-গোনা। বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ, এমনকি পঞ্চাশ-ষাট দশকের তুলনায়ও তা একেবারে অনুল্লেখ্য। ওদিকটায় তাকালে দেখা যায়, ওপার বাংলার মানুষগুলো একটা বিশাল দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠি হয়েই রয়ে গেছে। জাতি(এথনিক) হিসেবে ওদের নিজস্বতা আর বেশি দিন থাকবে কিনা সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এটার পেছনে বাস্তবতা হিসেবে বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষ কখনোই একটা দেশ বা জাতিসত্ত্বা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইউরোপ যেমন একটা দেশ নয়, বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠা একটা আঞ্চলিক পরিচয়, ভারতবর্ষও তেমনি, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, বাঙালি প্রভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্টির সমন্বয়ে গড়ে উঠা একটা আঞ্চলিক পরিচয়। এদের ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি কোনোটাই এক না। ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলো স্বকীয়তা বুঝতে পেরে নিজেদের পৃথক করে নিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতিগুলোর ভেতর ঐ চেতনা গড়ে উঠেনি, বা ওটার সুযোগই আসেনি। ফলে অপেক্ষাকৃত শক্তিধর অংশগুলো দ্বারা পর্যায়ক্রমে শৃঙ্খলিত রয়েছে দুর্বলতর অংশগুলো। এপার বাংলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল ওপার বাংলার রাজধানী নগর। ওটা হারিয়ে, এবং বৌদ্ধিক চেতনায় অগ্রসর অংশটা ওপার বাংলায় পাড়ি দেয়ায় বড় রকমের একটা শূন্যতা দেখা দেয়। ওটা পূরণ করে ওঠা এখনো সম্ভব হয়নি। বাংলার এই বৌদ্ধিক স্তরটা আবহমান কাল থেকেই ধরে রাখা আছে উচ্চ বর্ণের মানুষদের ভেতর। ওপার বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, উঁচু অবস্থানের আমলা প্রভৃতি প্রত্যেকটা স্তরই প্রায় শতভাগের কাছাকাছি এই উচ্চ বর্ণের মানুষদের আয়ত্বে। এপার বাংলা হতে এদের অভিবাসনের ফলে যে শূন্যতা গড়ে উঠেছিল তার পরিপূরণ ঘটে এখানের সমাজে কিছুটা উপরের দিকে থাকা মানুষদের দিয়ে, যারা সামন্ত বা প্রায়-সামন্ত ধরনের একটা জীবন যাপন করে আসছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ থেকে শুরু করে হালের মামুন হুসাইন পর্যন্ত সবাই সুবিধেপ্রাপ্ত শ্রেণি থেকে আসা। ফলে এখানের উপন্যাস শিল্পে প্রান্তিক মানুষদের উপস্থাপন ভেতর থেকে আসেনি। অদ্বৈত বা হরিশংকরদের সংখ্যা এত কম যে এদের রচনা বাংলার বিশাল উপন্যাস সাহিত্যে প্রায় আনুবীক্ষণিক। যদিও প্রায় সব ঔপন্যাসিক প্রান্তিক সমাজটাকে নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু তাদের রচনাগুলো সব গবেষণা নির্ভর। গভীর পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজটাকে দেখেছেন এরা, হলাহল মন্থন করে এর নির্যাসটা তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। এই
ধারারই একজন ঔপন্যাসিক হাসান আজিজুল হক। একজন অভিবাসী হিসেবে তাঁর যে দুটো উপন্যাস এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তার দুটোই ওপার বাংলার প্রেক্ষাপটে রচিত। অভিবাসী হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলোয়। তাঁর গল্পের ভেতর যে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি, গভীর ব্যঞ্জনা ও ভাবনা উদ্রেককারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অনেক উপন্যাসকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আগুনপাখি’ একটা অনেক বড় গল্পের বিশেষত ছাড়িয়ে খুব বেশি দূরে নিয়ে যায় না পাঠককে। দ্বিতীয় উপন্যাস ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’ সে তুলনায় আরো ক্লিশে। হাসান আজিজুল হকের মতো উচ্চাঙ্গের সাহিত্যশিল্পীর কাছে পাঠকের প্রত্যাশা আরো অনেক বেশি। তাঁর সাহিত্যকর্ম বিষয়ে লেখা আমার জন্য ধৃষ্ঠতা পর্যায়ের। তাঁর কাছ থেকে গল্প লেখাটা শেখার চেষ্টা শুরু থেকেই করে এসেছি।
একটা উপন্যাসের যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় সে-সবের ভেতর শুরুতেই আসে প্লট, যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক এটাকে, আসলে কাহিনীই, এটা তাঁর উপন্যাসে অবশ্যই আছে। চমৎকার একটা কাহিনীর রূপায়ন করেছেন তিনি ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসে। একটা সময় ও সমাজকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, ভেতর থেকে ও বাইরে থেকে, তা অনবদ্য নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশ ভূখণ্ড হতে এটাই হয়তো ভারতবর্ষ বিভাজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা শেষ উপন্যাস। সোয়া দুশো পৃষ্ঠার কলেবরের জন্য এটা একটা উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে, নয়তো ঠাঁস-বুনোটে লেখা একটা বড় গল্প। প্রায় পুরোটাই কাহিনী। দুই বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের মধ্যে বিকশিত একটা মুসলমান যৌথ-পরিবারের গড়ে উঠা ও ভেঙ্গে পড়ার সচল ইতিহাস। ডালপালা হিসেবে ছিটেফোটা দুএকটা অনুষঙ্গ এসেছে নেহায়েতই একহাড়া কাণ্ডটাকে একটা গাছের মর্যাদা দিতে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মানুষের চিন্তা-ভাবনা বদলে যাওয়ার ফলে বিষয়গুলো দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায়। মুক্তিযুদ্ধকে আমাদের প্রজন্ম যেভাবে দেখেছে পরবর্তী প্রজন্ম তা কোনোভাবে বুঝে উঠতে পারবে না। যেমন আমরা বুঝে উঠতে পারি না দেশ-ভাগের যন্ত্রণা, নিষ্ঠুরতা ও করুণ অবস্থাটা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য। হাসান আজিজুল হক এই দেশ বিভাজনের বিষয়টি যতোটা বিশ্বাসযোগ্য করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, বর্তমান প্রজন্মের কারো পক্ষে তা খুব কঠিন হবে, সন্দেহ নেই।
‘আগুনপাখি’র জন্য হাসান আজিজুল হক নতুন কোনো শৈলী ব্যবহার করেননি। তাঁর ছোটগল্পের কাহিনী-বয়ানের প্রচলিত ভঙ্গিটাই ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের মূলে থাকে যে গল্পটা তা নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন। কোথায় হোঁচট খেতে কিংবা ঝিমিয়ে পড়তে দেননি তাঁর পাঠককে। সময়-ভাবনানির্ভর জীবন এঁকেছেন তিনি, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা গড়িয়ে চলা দিনানুগ দিনের ছবি, শনি-রবি-সোম, এভাবে বয়ে চলা সময়ের গতানুগতিক সরল-রৈখিক জীবন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। জটিল কোনো বিষয়ের অবতারণা নয়, একটা সময় ও সমাজের নিখুঁত চিত্র, ও নির্মোহ উপস্থাপনা সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন পাঠকের সামনে।
একজন গদ্যশিল্পীর অননুসরণীয় বৈশিষ্ট্যতাসূচক ভিন্নতা তাঁর রয়েছে। এটা তিনি সৃষ্টি করেছেন রাঢ়-বাংলার প্রচলিত ভাষা ও প্রমিত ভাষার মিশ্রণে। এ ভাষাটা তাঁর একান্ত নিজস্ব, পৃথকভাবে চেনা যায়। সাধারণীকরণ করেননি তাঁর পূর্বসুরী বুদ্ধদেব বসুদের মতো। বাংলাদেশের গদ্যশিল্পীদের এই পৃথক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর সাহিত্য নির্মাণের সময় হতে। ভিন্ন স্রোত সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা যেমন তিনি গ্রহণ করেছেন, তেমনি সৈয়দ শামসুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, মাহমুদুল হক, কায়েস আহমেদ, কিছুটা সাম্প্রতিক শহীদুল জহির, মামুন হুসাইন এঁদের প্রত্যেকের গদ্যভাষায় দেখা যায় সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য, এবং অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য। বিষয়ের ভিন্নতার সঙ্গে ভাষাভঙ্গিটাও ভিন্ন করার প্রয়াস রয়েছে এঁদের।
কাহিনীর জটিলতা বর্তমান সময়ের উপন্যাসের একটা নির্ধারক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু আগুনপাখির প্লটে কোনো জটিলতা নেই। রয়েছে সাদামাটাভাবে বয়ে চলা সাবলীল গতি ও তাঁর আশ্চর্য মসৃণ ভাষা। একটা উচ্চাঙ্গের উপন্যাস পাঠককে শুধু নতুন অভিজ্ঞতাই দেয় না, ক্ষেত্র-বিশেষে তাকে শিক্ষিতও করে তোলে, তার মূল্যবোধে অনেক সদর্থক অনুষঙ্গ যোগ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলা সাহিত্যের খুব কম উপন্যাসই বিষয়ের উর্ধে উঠে একটা সর্বজনীন মূল্যবোধ তৈরি করতে সমর্থ হয়। ফলে এসব উপন্যাস অনূদিত হলেও বৈশ্বিক পাঠক পায় না। হাসান আজিজুল হকের উপন্যাস দুটো বাংলাভাষী সাহিত্যের পাঠক, অথবা বড়জোর উপমহাদেশের পাঠকের কাছে আদৃত হওয়ার মতো যথেষ্ট উপাদানে সম্বৃদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বৈশ্বিক পাঠকের জন্য সম্ভবত বিশেষ কিছু নেই সেখানে। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শিল্প এই প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে না।
এর পর আসে, উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ। এখানে হাসান আজিজুল হক তাঁর অসাধারণ সব গল্প লেখার সূত্রে এক অসাধারণ কারিগর। আজীবন দমিত থেকে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অধিবক্তা চরিত্রটা যে দার্ঢ্য প্রকাশ করে তা পুরো উপন্যাসটিতে এক অসাধারণত্ব আরোপ করেছে। মানুষের অপরাজেয় যে রূপটি কোথাও না কোথাও ফুটে উঠে, দেশ বিভাগের অর্থহীনতা, আবিমৃষ্যকারিতা ও ফাঁকিটার বিরুদ্ধে এককভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠার মধ্যে তা প্রকাশ করে ঐ চরিত্রটি। ওপার বাংলার বাঙালি মুসলমানের যে চিত্র নির্মাণ করেছেন তিনি তা এপার বাংলার অনেকের কাছে ছিল অপরিচিত। সময় ও সমাজের রূপ ফুটিয়ে তোলার যে বিষয় গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে একটা উপন্যাসের ভেতর তা প্রায় সর্বাংশে সফলভাবে উপস্থাপন করেছেন হাসান আজিজুল হক। উপন্যাসের সফলতার পেছনে যে বিষয় মুখ্য হয়ে দেখা দেয় তার অনেকটা গদ্য-শৈলী। নতুনভাবে হাসান আজিজুল হকের বিশেষ কিছু করতে হয়নি এখানে। পাঁচ দশকের গল্প লেখার মুনশিয়ানায় নিজস্ব একটা গদ্য-শৈলী প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। ওটা থেকে সরে আসার তেমন কোনো প্রচেষ্টা ‘আগুনপাখি’তে দেখা যায় না।
‘সাবিত্রী উপাখ্যানের’ কাহিনী ঐ অর্থে নির্মাণ করেননি হাসান আজিজুল হক। উপন্যাস জুড়ে দেয়া তথ্যসূত্র ধরে পাঠক জেনে যায় ওটা। সাবিত্রীর করুণ ও হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর ভেতর সে-সময়ের সমাজচিত্রের কিছুটা আভাস রয়েছে। সাংস্কৃতিকভাবে বিভাজিত একটা সমাজে আলোড়ণ তোলা ঘটনা পরম্পরার ভেতর একটা অসহায়ত্বও রয়েছে। ঐসব তথ্যসূত্রগুলো ভিত্তি করে তিনি যা নির্মাণ করেছেন, তা তাঁর আকর্ষণীয় গদ্য-ভঙ্গিমার চমক, এবং পাঠক ধরে রেখে কাহিনীকে শেষ পর্যন্ত টেনে নেয়ার কৌশল, যাতে সিদ্ধহস্ত তিনি। উপন্যাসের শেষে পাঠকের প্রাপ্তি লেখকের ঐ উপস্থাপন কৌশলটার বাইরে তেমন আর কিছু নেই। আগুনপাখিতে সে-সময়ের একটা সমাজ, একটা পরিবারের গড়ে উঠা ও ভেঙ্গে পড়ার কাহিনী, রাষ্ট্রের সুবিধেভোগীদের অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম, দেশ-ভাগের অর্থহীনতা ও সর্বোপরি সমাজের সব চেয়ে নিরীহ মানুষটাও যে কোনো একটা অবস্থানে যেয়ে চরম দৃঢ়তা প্রকাশ করতে পারে, তার সুনিপুণ প্রকাশ রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক একটা বিশ্লেষণের কিছুটা সুযোগ রয়েছে উপন্যাসের চরিত্রগুলোয়। ঐ সব বিবেচনায় ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’ একেবারে পানসে।
‘সাবিত্রী উপাখ্যান’-এর শুরুটা তো অসাধারণ। চমৎকার একটা উপন্যাস পাঠের তৃষ্ণা বেশ ভালোভাবেই জেগে উঠে পাঠকের ভেতর। কিছুদূর এগোনোর পর, বিস্ময়করভাবে শুরু হয় একটা কাহিনীকে গতানুগতিকভাবে শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা। হাসান আজিজুল হকের গল্প বলার অসাধারণ দক্ষতাগুণে শেষ পর্যন্ত বিষয়টা উতরে যায়। কিন্তু মননশীল পাঠকের জন্য তা যথেষ্ট নয়। একটা ভালো উপন্যাস পড়ার পর যে ঘোর থেকে যায় পাঠকের ভেতর, তা তৈরিই হয় না ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’-এর শেষে। পাশাপাশি যদি মার্কেসের বড় গল্প ‘বেচারি এরেনদিরা ও তার নির্দয় ঠাকুরমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী’র বিষয় মনে করি, এরেনদিরার শরীর যাপন অথবা নির্যাতনের শুরুটাও ধর্ষণের মধ্য দিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত তার মালকিনের হাত থেকে অনন্তের পথে পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত ধর্ষণের শিকার হয়েছে সে। এটার পরিশোধ অবশ্য নিয়েছে সে প্রেমিকের হাতে মালকিনকে হত্যা করানোর মধ্য দিয়ে। কলেবরের দিক থেকে যদি দেখি সাবিত্রী উপাখ্যান এরেনদিরার কাহিনীর কম করে হলেও চারগুণ বড়। অথচ এরেনদিরার ঐ কাহিনীর ভেতর মার্কেস বুনে দিয়েছেন কত বিচিত্র বিষয়! বড় একটা গল্পের ভেতর যে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়া যায়, মার্কেস তা নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন। অথচ হাসান আজিজুল হকের সাবিত্রী উপাখ্যান একেবারে সরল-রৈখিক উপস্থাপন। যে শক্তিমত্তা হাসানের লেখনিতে রয়েছে, তাঁর ভাষার অসামান্য যাদু, গল্প বলার কৌশল, প্রাজ্ঞ জীবন-অভিজ্ঞতা, গভীর দার্শনিক উপলব্ধি, কাহিনী বয়ানের অসাধারণ পারঙ্গমতা, সে-সবের খুব কমই তিনি ব্যবহার করেছেন উপন্যাসটিতে। ফলে পাঠকের অতৃপ্তি রয়ে গেছে। উপন্যাস রচনার যে আশ্চর্য সূচনা করেছিলেন আগুনপাখিতে তা ম্লান করে দিয়েছেন ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’-এ এসে। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের নিতান্তই দুর্ভাগ্য এটা। সার্বিক বিবেচনায় এটা হয়তো একটা ভালো উপন্যাস, কিন্তু তাঁর মাপের নয়।
আধুনিক উপন্যাসের একটা বিশেষত এর জটিল মনোবিশ্লেষণ। হাসান আজিজুল হকের দুটো উপন্যাসের কোনোটাতেই ঐ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। ধরে নেয়া যায়, ভালোভাবেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গল্প লেখাটাই তাঁর মূল পারদর্শিতার জায়গা, তাঁর শিল্প-কুশলতার আসল দিকটা গল্প লেখায়, হয়তো এজন্য সুদীর্ঘ পাঁচ দশকে উপন্যাস লেখায় হাত দেননি। তাঁর উপন্যাস দুটোও এর যথার্থতা প্রমাণ করে। গল্পের ভূবনে যে আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতায় তাঁর অবস্থান, উপন্যাসকে সেখানে নিয়ে যেতে এখনো সক্ষম হননি তিনি।
উপন্যাসের কলেবর নিয়ে যদিও ভিন্নমত রয়েছে, পনেরো বিশ হাজার শব্দেও অনেক ভালো উপন্যাস রচিত হয়েছে, কিন্তু সাধারণভাবে স্বীকৃত যে কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার শব্দের প্রয়োজন একটা উপন্যাসের কাহিনীকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য। হাসান আজিজুল হকের দুটো উপন্যাসই কলেবরের দিক থেকে ঐ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।
তাঁর ছোট গল্পগুলোয় যে সব চরিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন, সে-সব বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। ভবিষ্যতে এ ধরনের নির্মাণ আর আশা করা যায় না। জমিরুদ্দির শারিরীক কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সহনশীল আচরণ বর্তমান সময়ে অকল্পনীয়। জমিরুদ্দির গ্রাম সুবাদে চাচা, আধ-বুড়ো মানুষটার মানবিক অনুভূতি অকৃত্রিম। এসব চরিত্র আর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এজন্য যে আমাদের সামাজিক অবস্থাটাই পুরোপুরি বদলে গেছে। মানবিক দিকগুলো পরিবর্তিত হয়েছে পাশবিক উল্লাসে। মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক শুভকামনা প্রভৃতি আর নেই। বরং রয়েছে পৈশাচিক নির্মমতা।
তাঁর গল্পের ভূবনে যদি ফিরে তাকাই, সেখানেও নিজেই খুঁত নির্মাণ করেন তিনি, হয়তো তাঁর ইচ্ছাকৃত, কিংবা আমার দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটি। আত্মজা ও একটি করবীগাছ গল্পটা শেষ হয়ে গেছে ‘… ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ – প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো-’ ওখানেই। গল্পের শেষে ‘এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ?’ এভাবে বারবার উচ্চারিত বাক্যগুলো গল্পটার গভীরতা নষ্ট করে হালকা আবেগ নিয়ে আসে। বিলি ব্যবস্থা গল্পের শেষেও দেখা যায় একই রকম অর্থহীনতা। ‘চোখের আঁসুতে সোনার দাড়ি ভিজাইয়া আমার পয়গম্বর নবীজী কাঁদে। জারে জার হইয়া কাঁদে।’ এরকম একটা বিচারে বা বিলি ব্যবস্থায় দ্বীনের নবী কাঁদবে কোন দুঃখে? স্ববিরোধী এমন বক্তব্য হাসান আজিজুল হকের গল্পে আশা করা যায় না। মা মেয়ের সংসার গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটা একেবারে অপ্রয়োজনীয়। ফেরা গল্পের এক বাক্যের শেষ অনুচ্ছেদটাও গল্পের ভেতর ভিন্ন কোনো মাত্রা এনে দেয় না। তাঁর অনেক গল্পের ক্ষেত্রে এরকম উদাহরণ দেয়া যায়। গল্পের শেষে পাঠকের ভাবনার জায়গাটা আর রাখেন না তিনি। জানি না এটা তাঁর কৌশল, না দুর্বলতা।
হাসান আজিজুল হকের সৃষ্টিশীল সাহিত্য নির্মাণের সময়টাকে স্পষ্টতই দুভাগে ভাগ করা যায়। পাতালে হাসপাতালে গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ১৯৮১ পর্যন্ত সময়কাল, যা তাঁর গল্পের ভূবনটাকে নির্মাণ করেছে। এর পর ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ষোল বছরের একটা ছেদ। দ্বিতীয় পর্বে এসে যে গল্পগুলো পাওয়া যায় সে-সবের অধিকাংশ আগের পর্বের তুলনায় নিতান্তই ক্লিশে। আগের গল্পগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, উত্তরণ তো নেইই, বরং মনে হয় তিনি ফুরিয়ে যাওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর উপন্যাস দুটো পড়ে মনে হয় খুব বিচক্ষণতার সঙ্গেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে গল্পটাই তাঁর আসল জায়গা। একটা ভালো উপন্যাস লেখার জন্য যে গবেষণা, অধ্যবসায়, চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এবং সর্বোপরি একটা উপন্যাসের খসড়া তৈরি হওয়ার পর যে কঠিন শ্রম ও সময় দিতে হয় তা সম্ভবত তাঁর নেই। ‘পাতালে হাসপাতালে’, ‘আত্মজা ও একটি করবীগাছ’, ‘ফেরা’, ‘খাঁচা’, ‘নামহীন গোত্রহীন’ প্রভৃতি গল্পে একটা সময় ও সমাজের নির্মমতা ও অসহায়ত্বের বিভিন্ন চিত্র যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রতিফলন দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলোর ভেতর খুব একটা নেই। গল্পকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে পৌঁছা যে-কোনো গল্পলেখকের জন্য সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শের অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয় হতে পারে। একজন গল্পকার পাতালে হাসপাতালের মতো গল্প এক জীবনে খুব বেশি লিখতে সক্ষম হন না। স্ব-সৃষ্ট ঐ উচ্চতায় হাসান আজিজুল হক যদি নিজেই আর না পৌঁছাতে পারেন, সেটা তাঁর দায় বা ব্যর্থতা নয়। এভারেস্ট শৃঙ্গে দুবার উঠতে পারা হয়তো কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব না, বা আকাঙ্খিতও না।
অভিবাসী হিসেবে হাসান আজিজুল হকের যে তুলনামূলক সুবিধেগুলো রয়েছে, সে-সবের ব্যবহার খুব একটা করেননি তিনি। দুটো সমান্তরাল সমাজকে ভেতর ও বাইরে থেকে দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে, এ দুটো সমাজের সদস্যদের ভেতরে সংঘটিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহিত্য-রূপ দেয়ায় উদ্যোগী হননি। ‘আগুনপাখি’ ও ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’ দুটোই রাঢ় বাংলার অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, এবং অতীতাশ্রয়ী। দেশ-ভাগ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও অভিক্ষেপ থেকে এখনো দূরে রয়েছেন তিনি। অভিবাসিত নতুন একটা দেশকে কীভাবে পেলেন, স্থানান্তরিত বিশাল একটা মানবগোষ্ঠি অন্য এক ভূগোলে কেমন করে নিজেদের প্রোথিত করলো, জীবন ও জীবিকার সন্ধানে এসে যে-সব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলো, অথবা যে-সব আনুকূল্য আশা করে দেশান্তরী হয়েছিল তা কতটুকু বাস্তবানুগ ছিল, এসবের তেমন কোনো প্রতিফলন নেই হাসান আজিজুল হকের গল্প বা উপন্যাসে। এসবের কিছুটা প্রতিফলন রয়েছে তাঁর প্রবন্ধ/নিবন্ধগুলোয়।