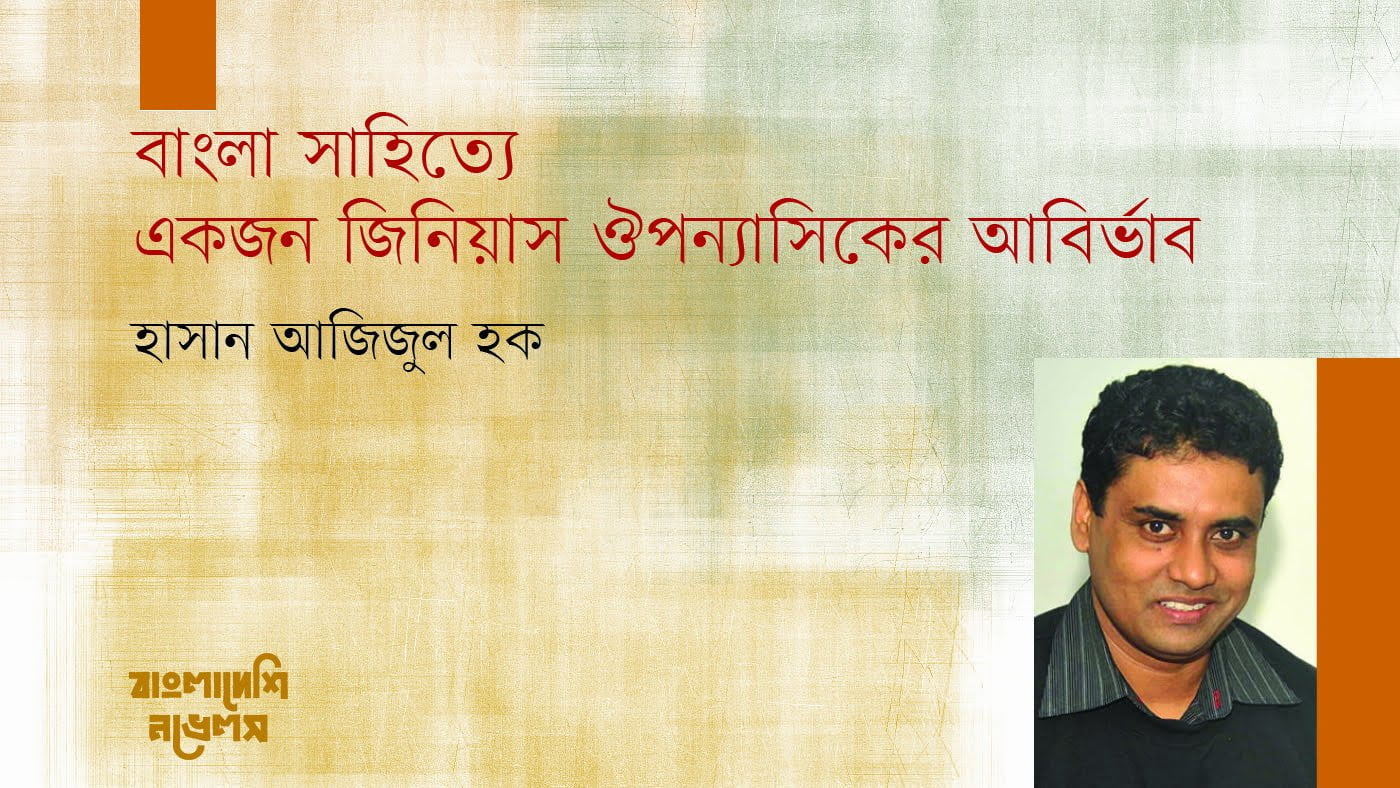আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) বাংলাদেশের উপন্যাসের অগ্রগণ্য পুরুষ। সমগ্র বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতেও তাঁর উপন্যাস যে আলোচনার দাবি রাখে সে ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানে রচিত কর্ম যে সাহিত্য পদবাচ্য নয় তেমন সব ভাবনা থেকেই ‘বাংলাদেশের’ অভিধায় একটি আলাদা ধারা আমরা নিজেরাই তৈরি করে ফেলেছি যেখানে সবকিছুকেই শীর্ণ এ ধারাটির আলোকেই আমরা বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। অথচ সে গণ্ডীর বাইরেও যাওয়া সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ রায় রচিত ‘বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা’ (দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১) গ্রন্থ বাংলাদেশের যে সকল উপন্যাসিককে সূচিবিদ্ধ করা হয়েছে তাঁরা হলেন আবু ইসহাক, শহীদুল্লা কায়সার, সত্যেন সেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। পঞ্চাশ বছর পর হলেও এমন একটি অনুশীলন ইতিবাচকতার ইঙ্গিত দেয়। যদিও প্রশ্ন উঠতেই পারে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সে তালিকায় সারম্বরে ঘোষিত হলে আবুজাফর শামসুদ্দিন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম বা সৈয়দ শামসুল হকের প্রসঙ্গ অনালোচিত কেন! তাছাড়া শুধুমাত্র আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে ভুক্ত করেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব প্রচারের মেকী একটি মানসিকতা কয়েক বছর ধরে পশ্চিম বাংলাতে সুস্পষ্ট। অন্যদিকে ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ‘পরিকথা’-র বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ক সংখ্যাটি অনেকের দৃষ্টি কেড়েছে। ‘লালসালু’ (১৯৪৮) থেকে ‘জন্ম জন্মান্তর’ (২০০০) পর্যন্ত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য উনিশটি উপন্যাসের অধিকাংশই দীর্ঘ কলেবরে পশ্চিম বাংলার সমালোচক কর্তৃক আদৃত হওয়ায় নতুন ভাবনার সুযোগ এসেছে প্রতিতুল বিচারের। ১৯৫৫ সালে আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও উপন্যাসটি যে জনপ্রিয়তা সেখানে পেয়েছিল তার ইতিহাস আমরা ভুলে গেছি। অন্যদিকে জনপ্রিয়তার কারণেই হয়তো সমালোচক কর্তৃক কটু বাক্যও আবু ইসহাকের ললাট লিখন হয়ে দাঁড়ায়। সে সব কারণেই কি ১৯৮৬ সালে তৃতীয় উপন্যাস (প্রকাশকারে বিচারে দ্বিতীয়) ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ সমাদর থেকে বঞ্চিত? এত গভীরভাবে বাংলার জীবনকে নিয়ে সুপরিকল্পনার ছকে গল্পকে আটকে রেখেও ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এ আবু ইসহাক জনগণমন পান নি। যদিও এমন প্রশ্ন হয়তো বিশেষ বাতুল হবে না যে ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এর মত একই তলের আর কটি উপন্যাস বাঙলা ভাষায় সমকালে রচিত হয়েছে!
‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ ১৯৪৮ সালে রচিত। প্রকাশকের অভাবে সাত বছর বাদে প্রকাশ পেলে বেশ নড়াচড়া হয়েছিল উপন্যাসটি নিয়ে। যদি সেকালের বাংলাদেশের উপন্যাস বলতে যে ধারাটিকে আমরা বুঝে থাকি সেদিকে চোখ ফেরাই দেখা যাবে প্রথম আসছে মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১) এর নাম যাঁর ‘মফিজন’ (১৯৪৮) আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের শুরুর সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য, শক্তিমান এবং অনালোচিত নাম। এর পরই সফল যে নামটি আজ জনে জনে উচ্চারিত তা হলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র (১৯২২-১৯৭১) ‘লালসালু’ (১৯৪৮)। যদিও পাঠকপ্রিয়তা পেতে ‘লালসালু’-কে এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬০) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এ সময়ের আরও যে একজন ঔপন্যাসিক ‘জননী’ ১৯৪৮ সালের আগে রচিত হলেও এবং ১৯৪৪-৪৫ সলে আংশিকভাবে ‘সওগাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গ্রন্থরূপ পায় ১৯৫৮ সালের। ১৯৪৭ সালে রচিত আমাদের উপন্যাস শিল্পের অন্য গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনটি হল শাসসুদদীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) ‘কাশবনের কন্যা’, যেটিও প্রকাশক না পাওয়ায় ছাপা হয় লিখিত হওয়ার ৬/৭ বছর পর। ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’-র রচনা ও প্রকাশকাল নিয়ে এসব তথ্য জরুরি এ জন্যে যে বাংলাদেশের সমাজ নিয়ে বিশেষ করে মুসলমান জীবনগোষ্ঠীর কথকতা নিয়ে তখন থেকেই সফল সাহিত্য প্রয়াস শুরু। আর সে কারণেই যুগটার শুরুতে কেমন সাহিত্য নিয়ে যাত্রা হয়েছিল তা আমাদের ধারণায় থাকা প্রয়োজন।
‘লালসালু’, ‘জননী’ এবং ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ তিনটি উপন্যাসেরই একটি সাজুয্য সহজেই চোখে পড়ে: ধর্মীয় কুসংস্কারের উন্মোচন এবং তার বিরুদ্ধে উচ্চারণ। ব্যাপারটির মধ্যে প্রগতিবোধ থাকুক না-থাকুক, পরিবর্তনশীল সমাজের দাবির কাছে সামাজিক এ কূপমণ্ডুকতার চিত্র সাহিত্যে ভীষণভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তা সন্দেহাতীত। আর সে কারণেই উপর্যুক্ত তিনটি উপন্যাসই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ‘শুভারম্বের’ দিনগুলোতেই প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তাদের রচনাকাল পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বেই। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় বাংলাদেশের তিনজন প্রথম ও প্রধান সারির ঔপন্যাসিকের প্রথম সে প্রচেষ্টার পূর্বে বাঙালি মুসলমান সমাজের চিত্র প্রত্যাশিতভাবে কথাসাহিত্যে আসেন নি। তাই সে উপন্যাস রচনার চল্লিশ বছর পর যদি কোন ঔপন্যাসিক-সমালোচক চলেন ‘পীর-ফকির হলেওই ভণ্ড হতে হবে কেন?’ 1 তাহলে তা অগ্রজ সাহিত্যিককে অসম্মান প্রদর্শনই হয়। মনে হয় যেনন সূর্য-দীঘল বাড়ি-এ ধাঁচে লেখা অগুনতি উপন্যাসের ভীড়ে আবু ইসহাক আরও একটি যোগ করেছিলেন।
সমসাময়িককালে রচিত এ চারটি উপন্যাসকে যদি জনপ্রিয়তার নিরিখে বিচার করা যায় তাহলে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ শীর্ষে স্থান পাবে ; যদিও লালসালু-ও তার থেকে খুব বেশি কম নয়। তবে কাশবনের কন্যা বোধহয় চতুর্থ স্থানে থাকবে এজন্যে যে এতে দুটি সমান্তরাল কাহিনীকে লেখক অনেকখানি অগ্রসর করিয়েছিলেন যার যৌক্তিকতা সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার বাইরে। ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ যে এমন জনপ্রিয় হলো তা কি শুধু সিনেমার দৌলতে। নাকি মহৎ কিন্তু দরিদ্র নায়িকা 2 চরিত্রের জন্য! জয়গুণ যে সমাদর পেয়েছিল তা কিন্তু বাংলা উপন্যাসের কোন ধারাবাহিকতায় নয়। আবু ইসহাকের কৃতি এই জয়গুণের মতো সহজলভ্য বাঙালি নারীকে তিনি দৃষ্টিহীন পাঠকের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন। আর সেটা করতে যেয়ে তিনি যে ভাষাটাকে আশওয় করেছিলেন তা ছিল মেকিত্বশূন্য। যে কারণগুলো আবু ইসহাককে সফল ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় বসিয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই সে সবের উর্ধ্বে উঠে চেষ্টা করেছেন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির: যার ফসল পদ্মার পলিদ্বীপ – জনপ্রিয়তার সামান্যটুকুও উপন্যাসটির ভাগে জোটে নি। কাঠামো শৈলী প্রশ্নে সূর্য-দীঘল বাড়ি-র ছোটখাট ত্র“টিগুলোর জন্যই হয়তো সাহিত্যিক বিচারে লালসালু-তে কিন্তু ভাষা মোটেই সরল নয়, বরং তা’ বিদগ্ধ, জটিল অথচ দুতিময়।’ 3 যদিও লালসালু ও এর ভাষা বিষয়ে রশীদ করীমের মন্তব্য : ‘তাঁর ভাষা আরো আধুনিক ও আরো ভালো হওয়া সম্ভব ছিল।’ 4 তবে সামগ্রিক বিচারে কাশবনের কন্যা-কে অনেক কারণেই অভিনব আখ্যা দেওয়া চলে। বর্ণনায় এর লেখক সাধু ক্রিয়ারীতিকে ব্যবহার করলেও কথোপকথনে তিনি নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করেছেন চূড়ান্ত আঞ্চলিক। উপন্যাস শুরুর কিছু নাই। হরিঙ’ এর গোস্ত তো খাও নাই, এই জাগাডু হরিঙ’ এর গোস্তের নাহান মজা’ – কথাসাহিত্যে ভাষা ব্যবহারে ১৯৪৭-এর প্রেক্ষাপটে রীতিমত বৈচিত্র্যময়, যার বিপরীতে সাধু ক্রিয়ারীতি।
‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’-র তৃতীয় বাক্যটি হলো ‘ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল’ – পঞ্চাশের মন্বন্তর-পরবর্তী বাংলার সমাজে এর চেয়ে নির্মম সত্য আর কিছু নেই। পরবর্তী দশকগুলোতেও এ বাক্য অমোঘ হয়েছে যেহেতু সাহিত্যের গড়পড়তা পাঠক তো ঐ মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত যাদের অনেক লড়াইয়ের অন্যতমটি হলো ভাতের জন্য লড়াই। যদিও এ বাক্যটির পরের পুরো অনুচ্ছেদটিই প্রাণহীন কথায় ভরপুর, সেখানে রয়েছে সামাজিক সত্যের পূর্ণ উপস্থিতি। সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারী লেখকের এমন উপক্রমণিকা কিন্তু ‘লালসালু’-তে রয়েছে। ‘কাশবনের কন্যা’-য় উপন্যাস শুরুর পূর্বেই একটি আলাদা পরিচ্ছেদ সংযুক্ত, যদিও ‘জননী’-র কথামুখ অংশটি পরবর্তী ঘটনার সাথে অনেকখানিই পারস্পর্যবিহীন।
পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কালে স্থাপিত এ উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ যে তীক্ষ্ম সত্যের সামনাসামনি তা উপন্যাসটিতে অত্যুজ্জ্বল; গ্রামীণ ধর্মান্ধ সংস্কৃতির প্রতিচিত্র এখানে অনুপম ইত্যাদি মন্তব্য যথার্থ হলেও উপন্যাসটির একটি আবশ্যিক প্রসঙ্গ অনালোচিত: কেন জয়গুণকে সূর্যের উদয়াস্তের একটি ঘর যা কিনা সূর্য-দীঘল বাড়ি নামে পরিচিত সেখানে বাস করতে হবে! এবং ঔপন্যাসিক কেনই বা ঐ ঘরের নামেই উপন্যাসটির নামকরণ করলেন। অনুমান হয় ঔপন্যাসিকের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাসের ঐ কালটিই ছিল অভিশপ্ত যখন দেশটি যেন সূর্য-দীঘল বাড়ির মতই-কিছুতেই সে দেশটির উপর থেকে অভিশাপের চাপা বিলুপ্ত হবার নয়।
জয়গুণ কেন আকর্ষণ করলো বাঙালি পাঠককে। কারণ হিসেবে তিনটি বিষয়কে উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমত জয়গুণের দুঃখবোধ – দুর্ভিক্ষের দুঃখের ভেতরে দ্বিতীয় স্বামী করিমবক্শ তাকে তালাক দিয়েছিল বিনা দোষে; তালাকের সময় করিমবক্শ ছেলে রেখে দিয়ে মেয়ে দুটোকে চাপিয়ে দিল জয়গুণের ঘাড়ে; ছোট মেয়েটি দুর্ভিক্ষের কালেই মারা যায়; ওদিকে রয়েছে প্রথম স্বামীর সন্তান হাসু। অর্থাৎ স্বামী-সন্তান সবকিছু নিয়েই যেমন ওর অর্থনৈতিক দৈন্য তেমনি দৈন্য ভালবাসার। জয়গুণের এই দুঃখবোধের সাথে ইসহাক-পূর্বকালে আমরা যে সাহিত্য পেয়েছি তার ফারাক বিস্তর। জীবন ক্লিষ্টতার এমন মুখোমুখি হয়তো আগে কোন চরিত্রকে আমরা পাই নি: নারী চরিত্রের তো কোন প্রশ্নই নেই। আবু ইসহাকের বিশিষ্টতা এই যে তিনি এমন চরিত্রকে নির্মাণ করছেন জীবনঘনিষ্ঠভাবে। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি জয়গুণকে পাঠকপ্রিয় করে তা হলো জীবনের প্রয়োজন, সন্তানের অস্তিত্বের প্রয়োজন তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পায় যার ফরে সকল বাধা পার হতে সে সচেষ্ট। ছেলে হাসু তার বাইরে যাওয়া বিষয়ে প্রশ্ন তুললে জয়গুণের ধমক : ‘বাইরে যাইমু না? ঘরে আইন্যা কে মোখের উপুর তুইল্যা দিব?’ 5 গায়ের লোকের কথা শুনলে তাকে না খেয়ে মরতে হবে: ‘খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইরাও খাই না, খ’রাত নিয়াও খাইনা। কউক না, যার মনে যা।’ জয়গুণের জন্য পাঠকের সহানুভূতির কারণ অনুসন্ধান করলে তৃতীয় যে কারণ পরিস্ফুটিত তা দ্বিতীয় কারণ দ্রোহের সাথেই সম্পর্কিত। তৃতীয় কারণটি হলো জয়গুণের দ্রোহ – এমনকি ধর্মের বিরুদ্ধেও। মানবিকতার ব্যাপারটি প্রথম হয়ে উপস্থিত হয়েছে; ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী নয়। যদিও তৃতীয় অধ্যায়েই স্পষ্ট হয়ে যায় যে জয়গুণ আসলেই ধর্মভীরু। সে করণেই বেহেশত-দোজখের বিশ্বাস এবং প্রাসঙ্গিক ভয় থেকে সে কিছুতেই মুক্ত করতে পারে না। ‘তার বিশ্বা, হাশরের দিন জব্বর মুনসী কিছুতেই তাকে তার বেপর্দার জন্য নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না।’[ঐ, পৃ. ১৯[/ref] কিন্তু ধর্মভীরু সাধারণ শ্রমজীবী গ্রামীণ এই রমণী ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে ধর্মের অনুশাসন ভুলে যায় সহজেই; কেননা সে তো ঘর-পোড়া গরু। যখন কোলের মেয়েটি মারা যায়:
তখন দুর্ভিক্ষ সবে দেখা দিয়েছে। দুর্নামের ভয়ে স্বামী-পরিত্যক্ষা জয়গুণ তখনও ঘরের বার হয় নি। খেতে না পাওয়ায় তার বুকে দুধ ছিল না। দুধের শিশু দুধ না খেয়ে শুকনো পাটখড়ির মত হয়েছিল। শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন মারা গেল। তাকে কবর দিতে কাফনের কাপড় জোটেনি।’ 6
প্রথম বিয়ের বোম্বাই শাড়িটা ছিঁড়ে কবর দেয়া হয়েছিল কোলের মেয়েটিকে। শাড়ির প্রতীকী ব্যঞ্জনাও অনেকখানি। শাড়ির অবশিষ্ট অংশ হাসুরা নেয় স্বাধীনতা দিবসে পতাকা বানানোর জন্য। যা হোক, রূঢ় বাস্তবই এভাবে জয়গুণকে সাহসী করে; জীবনের সাথে মোকাবিলা করতে উদ্যোগী করে। মায়মুনের বিয়ের সময় মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে তওবা করার প্রশ্ন আসলে প্রথম পর্যায়ে জয়গুণ গররাজী হলে জহিরুদ্দিন বলেছিল : ‘খোদায় খাওয়াইব। মোখ দিছে যে, আহার দিব সে’ যা শুনে জয়গুণ শ্লেষের হাসি হেসেছিল কেননা এমন বাক্যের অর্থশূন্যতা তার মত করে কতজন আর বুঝেছে! গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মত ধর্মবিশ্বাসে সেও আপ্লুত বলেই একদিনের জন্য তওবাকে গ্রহণ করেনি সে। সেই তওবাই তাকে নিষ্কর্মা করেছে। অন্নাভাবে সন্তানদের মৃত্যু যখন জয়গুণের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন উপায়হীন সে আবার ত্যাগ করে নিজ গ্রাম যেখানে উপন্যাসের শুরুতে তারা ফিরে এসেছিল শহরকে ত্যাগ করে।
‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’-তে আবু ইসহাক ক্লিষ্ট জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তেমনটি পূর্বসূরি জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) উপন্যাসেই পাওয়া যেতে পারে। কৃষিজীবনী মুসলমান সমাজের আধাঁরে তেমন চিত্রণ আবু ইসহাকই প্রথম করেন। তবে ‘জীবনকে সর্বআয়তনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন ও রূপায়ণে তিনি সর্বাংশে সক্ষম হননি,’ বা ‘জীবনের বহির্চিত্র অঙ্কনের আন্তরিকতায় তাঁর ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ পাঠক চৈতন্যে গভীর জীবনবোধ সঞ্চারে ব্যর্থ হয়’ 7 এমন মন্তব্য যথাযথ নয় কেননা জীবনের নতুন একটি পাঠ ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’-তে যে আমরা পেয়েছি তা অনস্বীকার্য হয়তো কাহিনী উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকের প্রথম প্রয়াস হিসেবে কিছু ত্র“টি বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছি। যদিও সে প্রসঙ্গে শিরীন আখতারের বক্তব্যকে যথার্থ ভাবতে কষ্ট হয়। এই সমালোচক লিখেছেন:
উপন্যাসে দু’একটি ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। শফীর মা’র মুখে নানা গল্পকথা উপন্যাসের জন্য অপরিহার্য ছিল না। রমেশ ডাক্তারকে কেন্দ্র করে যে উপকাহিনী গড়ে উঠেছে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বলা যায়, তা অপ্রয়োজনীয়ভাবে কিছুটা দীর্ঘ ও শিথিল-বিন্যস্ত হয়েছে। 8
যদিও সব সমালোচক এ বক্তব্যের সাথে হয়তো একমত হবেন না। যেমনভাবে দ্বিমত পোষণ করবেন অন্য আর এক সমালোচক মন্তব্যে যেখানে তিনি বলেছেন উপন্যাসটি স্কেচধর্মী এবং শিল্পোত্তীর্ণ নয়। 9
‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ বাংলাদেশের একটি কর্কট কালকে ধারণ করেছে এর কাহিনীতে: ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ছুঁয়ে সে কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে পাকিস্তানের স্বাধীনতা এবং বিপুলসংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর এ দেশ ত্যাগের ভেতর দিয়ে। যে মন্বন্তরের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৫ থেকে ৪০ লাখ তার সামগ্রিক চিত্রণের জন্য একজন ঔপন্যাসিকের অভাব আমরা এতদিনেও পূর্ণ করতে পারি নি একথা সত্য কিন্তু বাঙালি দুর্ভিক্ষপীড়িত বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি প্রতীকী পারিবারিক চিত্র কি জয়গুণ-হাসু-মায়মুনের ভেতর যথেষ্ট শক্তিশালীভাবে প্রকাশিত নয়? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) ‘অশনি সংকেত’ (১৯৪৪), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭০) ‘মন্বন্তর’ (১৯৪৪), গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) ত্রয়ী উপন্যাস ‘পঞ্চাশের পথ’ (১৯৪৪), ‘উনপঞ্চাশী’ (১৯৪৬) ‘তেরশ পঞ্চাশ’ (১৯৪৫), সরোজকুমার রায় চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৭২) ‘কালোঘোড়া’ (১৩৫৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) ‘চিন্তামনি’ (১৯৪৬), অমলেন্দু ঘোষের (জন্ম ১৯৩৪) ‘আকালের সন্ধান’-এর (১৯৮২) পাশে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তা সহজেই বলা চলে। তবে সমসাময়িক যে দুটি অনুযঙ্গ উপন্যাসটিতে অস্পর্শিত রয়ে গেছে তা হলো তেভাগা আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। ত্রিশ বছর পর প্রকাশিত ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এর কাহিনীও কিন্তু একই সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্মিত।
সন্দেহ নেই ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ আবু ইসহাকের প্রথম উপন্যাস ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ থেকে বহুগুণে সংত। দক্ষিণ বাংলার চরাঞ্চলের মানুষের পরিবর্তনশীল সামগ্রিক জীবনাচার নিয়ে এমন উপন্যাস বাংলা ভাষায় নিশ্চয়ই নগণ্যসংখ্যক। মহাকাব্যিক পরিসরে রচনার পরিকল্পনা করলেও 10 শেষ পর্যন্ত জীবদ্দশায় শুধুমাত্র প্রথম খণ্ডটিই তিনি প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন। পূর্ণ রূপ না পাওয়ায় ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এর প্লট-সফলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট সুযোগ থেকে যায়। তবে যে জীবনকে তিনি উপন্যাসের ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তা দর্শনে কোন ফাঁক আবু ইসহাকের ছিল না। ছিল না সেই জীবনের ভাষা-ভাবনার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা। ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’-র ভাবালুতা এতে অনুপস্থিত, যেমনভাবে প্রতিটি চরিত্র-ঘটানাংশ-বর্ণনা যুক্তিযুক্ততার নিরিখে স্থাপিত। চরাঞ্চলের পরিপূর্ণ একটি জীবনধারার সাথে এ উপন্যাস সমসাময়িক যে সকল প্রসঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বাঙলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম সমাজ পর্যন্ত কেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
চাকরি সূত্রে নারায়ণগঞ্জে অবস্থানকালে ট্রেনে দুঃস্থ যে রমণীদেরকে আবু ইসহাক দেখেছিলেন ১৯৪৪ সালের দিকে তারাই চিত্রিত হয়েছে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’-তে যেমন শরীয়তপুর অঞ্চলের তাঁর আশৈশব দেখা জীবন উপস্থাপিত হয়েছে ‘পদ্মা পলিদ্বীপ’-এ। পদ্মার পলিদ্বীপ একইসাথে পদ্মার প্রকৃতি এবং সে প্রকৃতিতে বাসিন্দাদের জীবন যাপন পূর্ণ বিবরণে বিবৃত। ঔপন্যাসিকের মৌলিকত্ব এই যে পদ্মাকে তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও আলোকিত করেছেন। এই বদ্বীপ-ভূখণ্ডে নদী যে সময়ের সাথে সাথে ভৌগলিকভাবেও কত বদলায় তার ইঙ্গিত পদ্মার প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসে পাওয়া সম্ভব। তবে চূড়ান্তভাবে উপন্যাসটি মানুষের কথাই বলে – তাদের আশা-আকাক্সক্ষা-চেতনারই রূপায়ণ করে।
‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ শুরু হয়েছে ফজলকে দিয়ে। ফজল উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্রও বটে। সে সায়োকচিত ব্যক্তিত্বও; কেননা সে যুবক, বুকভরা তার ভালবাসা, বাহুতে তার শক্তিও কম নয়, সাহসী পৌরষ তার কর্মকাণ্ডে দীপ্যমান। ফজল সুপরিকল্পনাকারী, যোগ্য নেতৃত্বদানকারী। ফজলকে কি আবু ইসহাক মহাকাব্যের বীর নায়কের অনুরূপে গড়তে চেয়েছিলেন! প্রাচীনকালে যে মহাকাব্যিক নায়কদের আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছি তার ছাপ ফজলের চরিত্র নির্মাণে স্পষ্ট। আর মহাকাব্য অর্থই তো যুদ্ধ-প্রসঙ্গ, বীরোচিত যুদ্ধে নায়কের চয়লাভ বিজয়ের অংশীদারী বিপুল দেশবাসী ইত্যাদি। যুদ্ধ তো দেশ দখল নিয়েই; যেমন ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এর দখলদারীর কাণ্ডকারখানা চলেছে খুনের চর নামে দশ বছর আগের লটাবনিয়া চরের পুনরায় জেগে ওঠাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই চর জাগার সংবাদ পায় পাঠক। সংবাদটির পরিবেশক ফজল নিজেই। পদ্মায় নৌকা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ‘বানবীর জোড়া তালগাছ’ বরাবর নদীর মাঝে বক হাঁটতে দেখেই রুদ্ধশ্বাস ফজল। বাড়ি ফিরে খবর দিতেই জ্বরে এবং বার্ধক্যে ন্যুব্জ বাবা এরফান মাতব্বরের শরীরটা সোজা হয়ে ওঠে, শিথিল হাত অজান্তে মুষ্টিবদ্ধ হয়। কণ্ঠে ধ্বনিত যুদ্ধের দামাবার ধ্বনি:
ফজু, শিগরির মানুষজন খবর দে। দ্যাখ, জমিরদ্দি, লালুর বাপ, রুস্তম, আহাদালী, মেহের মুনসী কে কোন খানে আছে। মান্ত্রায় আর শিলপারনে কারুরে পাড়াইয়ে দে। কদম শিকারী, ধলাইসরদার, জাবেদ লস্কর আর রমিজ মিরধারে খবর দে। …ঢোলে বাড়ি দিসনা কিন্তু। চর জাগনের কথা কানে কানে কইয়া আহিস। দুফরের মইদ্যে বেবাক মানুষ আজির অওয়ন চাই। যার যার আতিয়ার যেন লগে লইয়া আহে। 11
রীতিমত যুদ্ধ পরিস্থিতি। আর সেই তুঙ্গ অবস্থার অতীত পাওয়া যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। জানা যায় ঘটনা শুরুর দশ বছর আগেই জেগেছিল এই চর যার নাম তখন ছিল লটাবনিয়া। দখল নিয়েছিল এরফান মাতব্বরের দল। এক হাটবারে ষোলটা নৌকা বোঝাই লোক নিয়ে চেরাগ আলী সরদারের লোকজন দখন নিতে আসে। বাঁধে মারামারি যাতে খুন হয় এরফান মাতব্বরের বড় ছেলে বাইশ বছরের জোয়ান রশীদসহ মোট পাঁচজন। ছেলে খুন আর চর হারিয়েছিল এরফান মাতব্বর। যদিও তিন বছর পার না হতেই সে চর নিজেই হারিয়ে যায় পদ্মার জঠরে। এভাবেই বর্তমান খুনের চরের সাথে জড়িয়ে আছে এরফান মাতব্বরদের অতীত, শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস এবং পরাজয়ের গ্লানি ও সন্তান হারানোর বেদনা। আর তাই চর জাগান সংবাদে এরফান মাতব্বরের ঘোলাটে চোখ যেমন বড় বড় হয়ে ওঠে, পালিয়ে যায় শীত আর কাঁপুনি তেমনি তার স্ত্রী বরুবিবির বুকের ভেতর শুরু হয় ঢেঁকির পাড়: ‘ও আমার রশুরে, বা’জান। ক-ত বছর না যে পার অইয়া গেল, রশু-রে-আ-মা-র। তোরে না-যে ভোলতে না-যে পা-রি, মানিকরে- আ-মা-র। 12 আর এভাবেই বিনির্মিত হয় ভবিষ্যৎ একটি বীরগাঁথার পটভূমি।
চতুর্থ অনুচ্ছেদে উপন্যাসের প্রতিনায়ক জঙ্গুরুল্লার অনুপ্রবেশ। যদিও কাহিনী কাঠামোর ভেতর দিয়ে তার প্রকাশ ঘটলে অনেক বেশি সহজতা লাভ করতো এমনটি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এই এন্টি-হিরোকে নিয়ে আবু ইসহাক কি একটি এন্টি-প্লট নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন? জঙ্গুরুল্লার কাহিনীতে কিন্তু ফজলের কাহিনীর চেয়ে খুব বেশি হেরফের ঘটেনি গুরুত্ব প্রশ্নে। পঁয়তাল্লিশ বছরের জঙ্গুরুল্লার চল্লিশটি বছর কিন্তু দুর্দশায় কেটেশে। সে দুর্দশা কাটা শুরু হয়েছে অতি সম্প্রতি: নতুন নতুন চর উঠছে যার দখলদার সে – কোলশরীকদের কাছ থেকে পাওয়া খাজনার টাকা, বর্গাচাষীদের ধান বেচা টাকা আরও আছে ঘাস বেচা টাকা। আর টাকার পাহাড় দিয়ে পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা এখন চৌধুরী। শক্তিতে যেমন শয়তানীতেও কম যায় না জঙ্গুরুল্লা। আর দ্বিতীয়টি দিয়ে খুব সহজেই সে দখল করে নেয় খুনের চর। বোঝা যায় তার জাল অনেক বিস্তৃত। থানায় যোগাযোগ তার, এমনটি ফুলপরী পীরবাবারও আশীর্বাদপুষ্ট সে। ফজলের স্ত্রী পিতৃঘর নিবাসী রূপজালকে মিথ্যে তালাক দিয়ে হলেও ফুলপরী পীরবাবার সাথে বিয়ে দিতে চায় জঙ্গুরুল্লা। কেননা, পীরবাবাকে এ অঞ্চলে ধরে রাখতে হলে সুন্দরী এক যুবতীকে দিয়েই সেটি করা সম্ভব। শুধু কি তাই? পীরবাবা মারা গেলে তার কবরের নিশ্চয়তাও এ মাটিতে করতে চায় জঙ্গুরুল্লা। জঙ্গুরুল্লার এ সব পরিকল্পনার জালে আটকা পরে ফজল, জেলও খাটে, বাড়ি ছাড়া হয় রূপজানের বাবা আয়শেদ মোল্লা ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও জঙ্গুরুল্লার এসব কুট-পরিকল্পনাকে পরাজিত করেই এগিয়ে চলে ফজল। রূপজানকে উদ্ধার করে এবং খুনের চর পুনর্দখল করে।
এবার আসা যাক ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এর প্রেমপ্রসঙ্গে যার পুরুষ প্রবরটি ফজল নিজে এবং নারী আসলে একজন নয় দু’জন। বর্তমান বা দ্বিতীয় স্ত্রী রূপজান গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রথম স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা জরিনাও উপন্যাসটিতে উজ্জ্বল। ছদ্মবেশে ফজলে ও তার লোকজন রূপজানকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসরেও জরিনার প্রসঙ্গে বিশেষ কোন পরিণতি পরিলক্ষিত হয় না কেননা খুব সামান্য ইঙ্গিতে 13 আমরা জেনেছি জরিনা আসলে ফজলের সন্তানের মা হতে চলেছে। তাছাড়া ঘটনার প্রাথমিক পর্যায়ে রূপজানের জন্য ফজলের বিশেষ প্রীতির প্রকাশ লক্ষিত হয়। রূপজানের বাপের বাড়িতে রাতের বেলায় জরিনার সাথে ফজলের শারীরিক যে নৈকট্য ঘটে সেটি অনভিপ্রেত হলেও পরবর্তীতে বিপদের দিনে জরিনার সহযোগিতা ফজলকে তার নিকটবর্তী হতে বাধ্য করে।
সন্দেহ নেই ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ বাংলা ভাষার উপন্যাসের একটি মূল্যবান সম্পদ। ভাষার সাবলীলতা এবং কাহিনী সারল্যের কারণে সূর্য-দীঘল বাড়ি যেভাবে সাধারণ পাঠকমনকে জয় করতে পেরেছিল ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এ সে বিজয় দুরাশা মাত্র। তবে বিস্তৃত পটভূমিকে জীবনালেখ্য রচনায় ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ বাংলা উপন্যাসে অদ্বিতীয় তেমন বোধের কাছাকাছি পৌঁছাতেও কোন কোন সমালোচক ব্যর্থ হতে পারেন। তেমন একটি দৃষ্টান্ত হলো:
এ উপন্যাসে আবু ইসহাকের জীবন বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শৈশব-কৈশোর দেখা পদ্মাচরঅঞ্চলের জীবনধারার স্মৃতিই তাঁকে বৃত্তাবাদ্ধ করে রেখেছে অথবা বৃটিশ শাসনের শেষ ভাগের দিগন্তেই তাঁর চেতনা বাধা হয়ে আছে। আবু ইসহাকের মধ্যে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, যে প্রত্যাশার উন্মেষ ঘটিয়েছিল তাঁর ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ তা পরিপূর্ণতা পেল না বা পুরণ হতে পারল না ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ মাধ্যমে। 14
আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে নদীতীরবর্তী অঞ্চলে চার নিয়ে মানুষে মানুষে যে লড়াই তা ‘চরদখল’ হলেও চরের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইও বটে। একটি নির্দিষ্ট চরের উপর একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে তাদের আহার-বিহার তথা সমগ্র জীবনই নির্ভরশীল। চর ও মানুষের এই নৈকট্য আবু ইসহাক দেখেছিলেন খুব কাছ থেকেই। আর সে কারণেই চর-মানুষের সম্পর্ককে তিনি এমন হৃদয়গ্রাহীভাবে উপহার দিতে পেরেছেন পাঠককে। তাঁর লেখক সত্তার পরিপক্বতার কারণেই তিনি জানা গল্পটিকে ভাবালুতার আশ্রয়ে উপস্থাপন করেন নি। শিল্প হওয়ার শর্তকে পূরণ করতে গিয়েছেন বলেই বোধ করি উপন্যাসটি কম পাঠকের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সারা বাংলা উপন্যাসের জগতে চর নিয়ে এমন গভীর উপলব্ধির কাহিনী হিসেবে সম্ভবত আর যে একটি উপন্যাসের নাম আমাদের মনে আসে সেটি হলো শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) রচিত ‘সমুদ্র বাসর’ (১৯৮৬)। প্রাথমিকভাবে ১৯৪৭-৪৮ সালে রচিত এ উপন্যাসটিতে বরং একটি বিষয়ে অগ্রসরণ পরিলক্ষিত হয়: উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি সুজাত আলী ও তার লোকজন সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ এবং দীর্ঘ পরিশ্রমে যে চরকে বাসোপযোগী করেছিল সেটি বন্যার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে।
‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এর পটভূমি পদ্মা তীরবর্তী দক্ষিণ বঙ্গের শরিয়তপুর অঞ্চল হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছাপ যে এমন এলাকাতেও পড়েছিল তা বোধ করি এ উপন্যাস পাঠের আগে অনেকেরই অভিজ্ঞতায় ছিল না। তেরো পরিচ্ছেদে প্রথম আমরা জানতে পারি খুনের চরের উত্তর দিক দিয়ে পূর্বগামী একটি জাহাজে চলেছৈ দেশি-বিদেশি সৈন্য; দশম পরিচ্ছেদে মাথার উপর দিয়ে উড়োজাহাজ উড়ে গেলেও তা স্পষ্ট হয় নি। আরো পরে ষোল পরিচ্ছেদে জানা যায় ফজলদের এলাকার শতশত নৌকা পুলিশ আর মিলিটারীতে আটক করছে। স্পষ্ট হয় প্রয়োজনে সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধের সরঞ্জাম আনা-নেওয়ার জন্য সরকারের এ ব্যবস্থা। জাপানিরা এগিয়ে এলে বেগতিক অবস্থায় যাতে নৌকাগুলো ধ্বংস করে পালানো যায়। ইংরেজ সরকারের সৈন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম ভরে গিয়েছিল তেমন তথ্য আমাদের উপন্যাসগুলো অপ্রতুল না হলেও নৌযান বিষয়ক এমন তথ্য সম্ভবত আবু ইসহাকই প্রথম দিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে বাঙালি জীবনের আর একটি সম্পৃক্তির প্রসঙ্গ হলো নারী নির্যাতন। এ মুহূর্তে অন্ততপক্ষে সুলেখা স্যানালের (১৯২৮-১৯৬২) ‘নবাঙ্কুর’ (১৯৫৬) উপন্যাসটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে যেখানে প্রধান চরিত্র নারীবাদী নায়িকা ছবি চট্টগ্রামে থাকাকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু এবং চট্টগ্রামে ভরে গেল মিত্র বাহিনীর সৈন্যে-যাদের ভয়ে শহরের মেয়েরা পুত্রের বউ সবুরলণ ভোরে নদীতে গোসল করতে গেলে উধাও হয়ে যায়। কোন হদিস না পোয়ে গ্রামবাসী সিদ্ধান্তে পৌঁছায় নিশ্চয়ই কুমিরে খেয়েছে বউটিকে। কয়েকদিন বাদে ভোরবেলা একই স্থানে মেয়েটিকে যখন খুশবু মাখান অবস্থায় পাওয়া যায় তখন সবাই নিশ্চিত হয় ওকে জিনে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির ফেরার দৃশ্য দেখেছিল শুধু ফজল। সেদিন ভোর হতেই ফজল লুকিয়েছিল নদীর ধারে ঝোপের ভেতর, কেননা ও তকন জেলভাঙ্গা ফেরারী আসামী। টহলরত গোরা সৈন্যদের লঞ্চটা পাড়ের কাছাকাছি এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে স্রোতের টানে এগিয়ে আসে। তারপর:
আবছা আলোয় দেখা যায় দুজন গোরা সৈন্য বৈঠার খোঁচ মেরে লঞ্চটা পারের দিকে ঠেলছে। তাদের একজন লঞ্চের ডানপাশে এসে বৈঠা দিয়ে পানির গভীরতা মেপে চলে যায় কেবিনের ভেতর। অল্পক্ষণ পরেই একটা মেয়েলোককে পাঁজাকোলা করে এসে সে নামিয়ে দেয় কোমর পানিতে। মেয়েলোকটি হুমড়ি খেয়ে পানির উপর পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পানি ভেঙে কোন মতে পা টেনে তীরে উঠে সে বসে পড়ে মাটিতে। 15
এছাড়া আটাশ পরিচ্ছেদের শেষ দিকে এরফান মাতব্বরের বড় ভাই এমরান মাতব্বরের ছেলে জাহিদের প্রসঙ্গ এসেছে যে কিনা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েও ফিরে এসেছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বঙ্গীয় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কালো থাবার কথা ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’তে যেমন উপস্থিত, ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এ তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দারিদ্রক্লিষ্ট জরিনা তার চূড়ান্ত প্রকাশ। অন্যদিকে প্রথম উপন্যাসে ধর্মভীরু মুসলমানদের বিশ্বাসকে পুঁজি করে ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ আবু ইসহাক যেভাবে খুলেছেন, ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’-এর পীরবাবার কাহিনী তারই ভিন্ন উপস্থাপন মাত্র।
কথাকার আবু ইসহাক বিষয়ে রচিত এ প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তাঁর ‘জাল’ উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা এতে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে প্রথম উপন্যাস রচনা শেষ করার পরবর্তী চার বছরেও যখন তিনি উপন্যাসটির জন্য একজন প্রকাশক খুঁজে পান নি, সে সময়ই তার ভাবনায় আসে ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখলে হয়তো তার প্রকাশক পাওয়া যাবে। ১৯৫৪ সালে ‘জাল’ উপন্যাসটি লিখে যখন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছিলেন তখনই ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’-র প্রকাশক জোটে এবং উপন্যাসটি প্রকাশপর সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে তিনি ‘জাল’-এর মত একটি ডিটেকটিভ উপন্যাসকে প্রকাশ করা অসমীচীন মনে করেন। ১৯৮৬ সালে পদ্মার পলিদ্বীপ প্রকাশের পর জাল-এর পাণ্ডুলিপিটি তিনি আবার পড়েন এবং তাঁর মনে হয়:
‘জাল’ আমার সুনাম মোটেই ক্ষুণ্ণ করবে না – কারণ এটি একটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। গতানুগতিক ডিটেকটিভ উপন্যাস নয়। তা’ ছাড়া এর ভেতরে আছে অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে আমার উদ্ভাবিত কিছু মৌলিক পদ্ধতি। 16
ব্যক্তিজীবনে পুলিশের ডিটেকটিভ আবু ইসহাকের অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে ছিল পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা। ১৯৫০ সালে জাল নোটের কয়েকটা মামলা তদন্তের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল সে আলোকেই উপন্যাসটি রচিত।
উপন্যাসটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে বাজারে জাল নোটের যোগানদানকারী একটি গ্রুপকে চিহ্নিত করা এবং ধরার ভেতর। সামগ্রিকভাবে প্লটটি কৌতুহল উদ্দীপক সন্দেহ নেই, তবে লক্ষ করা যায় ঔপন্যাসিক অসম্ভব কোন সম্ভাবনাকে অতর্কিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চমক সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি। কাহিনীতে প্রেমের প্রসঙ্গ যেটি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ইলিয়াস এবং সরল সোজা বুদ্ধিমতি মেয়ে রোকসানার মধ্যে ঘটেছে তার ভেতরেও দেখা যায় যৌক্তিকতার আবরণ। তবে যে বিষয়টি বেশি জটিল হওয়ায় পাঠকের আনন্দ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে তা হলো সন্দেহজনক চিঠির সংকেতলিপি। এমন একটি সাঙ্কেতিক লিপির মর্মোদ্ধার লেখক করে দেয়ার পরও কোন পাঠক সেটি থেকে আনন্দ পেয়েছেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। উপন্যাসটিকে বুদ্ধিবৃত্তিক করার প্রয়াস থেকেই আবু ইসহাক এমনটি করেছেন তা ধারণা করা চলে।
রচনাকাল: ২০০৪
টীকা:
- রশীদ করীম, একটি বিখ্যাত উপন্যাস, ‘আর এক দৃষ্টিকোণ’, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৮০ ↩
- ঐ. পৃ. ৭০ ↩
- আলী আনোয়ার, বাংলাদেশের উপন্যাস: থীম ও ফর্ম, ‘সমকালীন বাংলা সাহিত্য’ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ১২৮ ↩
- রশীদ করীম, সমসাময়িকের চোখে: লালসালূ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬ ↩
- আবু ইসহাক, ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’, নওরোজ কিতাবিস্তান, পাকিস্তানী চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৮, পৃ. ১৮ ↩
- ঐ. পৃ. ৩৮ ↩
- রফিকউল্লাহ খান, ‘বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ’ (১৯৪৭-১৯৮৭), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৭০ ↩
- শিরীন আখতার, ‘বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক’, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৮৬ ↩
- মূল উদ্ধৃতিটি এমন: আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ (১৯৫৫) উপন্যাস-এর গঠন কৌশল ও চরিত্রচিত্রণে প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুসরণ করা হয়নি। উপন্যাসটি স্কেচধর্মী। একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য এতে উপস্থাপিত। কিন্তু শিল্পোত্তীর্ণ বলা যায় না। (শাহিদা আখতার, ‘পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৭১)’, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ১৮৯) ↩
- সৈয়দ আজিজুল হকের সম্পাদনায় দৈনিক ‘প্রথম আলো’-তে আবদুল হকের ‘স্মৃতি সঞ্চয়’ শিরোনামের যে ডায়েরি প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় ২৩ জুন ১৯৮৬-তে আবুদুল হক আবু ইসহাকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লিখেছেন: ‘কথায় কথায় জানালের পদ্মা পলিদ্বীপ একটি এপিক (epic) উপন্যাসের প্রথম খণ্ড, যদিও উপন্যাসে সেকথা লেখা হয়নি (‘প্রথম আলো’, শুক্রবারের সাময়িকী, ১২ ডিসেম্বর ২০০৩)। ↩
- আবু ইসহাক, ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’, মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃ. ২১ ↩
- ঐ পৃ. ২২ ↩
- ঐ পৃ. ২৯৩ তে আমরা দেখি জরিনা বাসায় ফিরে দেখতে পায় তার শাশুড়ি নাজুবিবি ছোট কাঁথা সেলাই করছে। সে ভাবে: ‘একটা বংশধরের জন্যে শাশুড়ির কত যে আকুতি। তার বিয়ের পর থেকেই নাজুবিবি অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। তার বহু দিনের আশা পূর্ণ হবে এবার। কিন্তু সে যদি জানতো তার আশার বাসায় কোন পাখির ডিম।’ ↩
- মুহম্মদ ইদরিস আলী এমন মন্তব্য করেছেন সমালোচনা করতে গিয়ে (‘সুন্দরম’, সম্পা. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, শরৎ সংখ্যা ১৩৯৪, পৃ. ৯৪)। ↩
- আবু ইসহাক, ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’, পূর্বোক্ত পৃ. ২০০ ↩
- আবু ইসহাক, ‘লেখকের ভূমিকা’ জাল, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৮৯ ↩