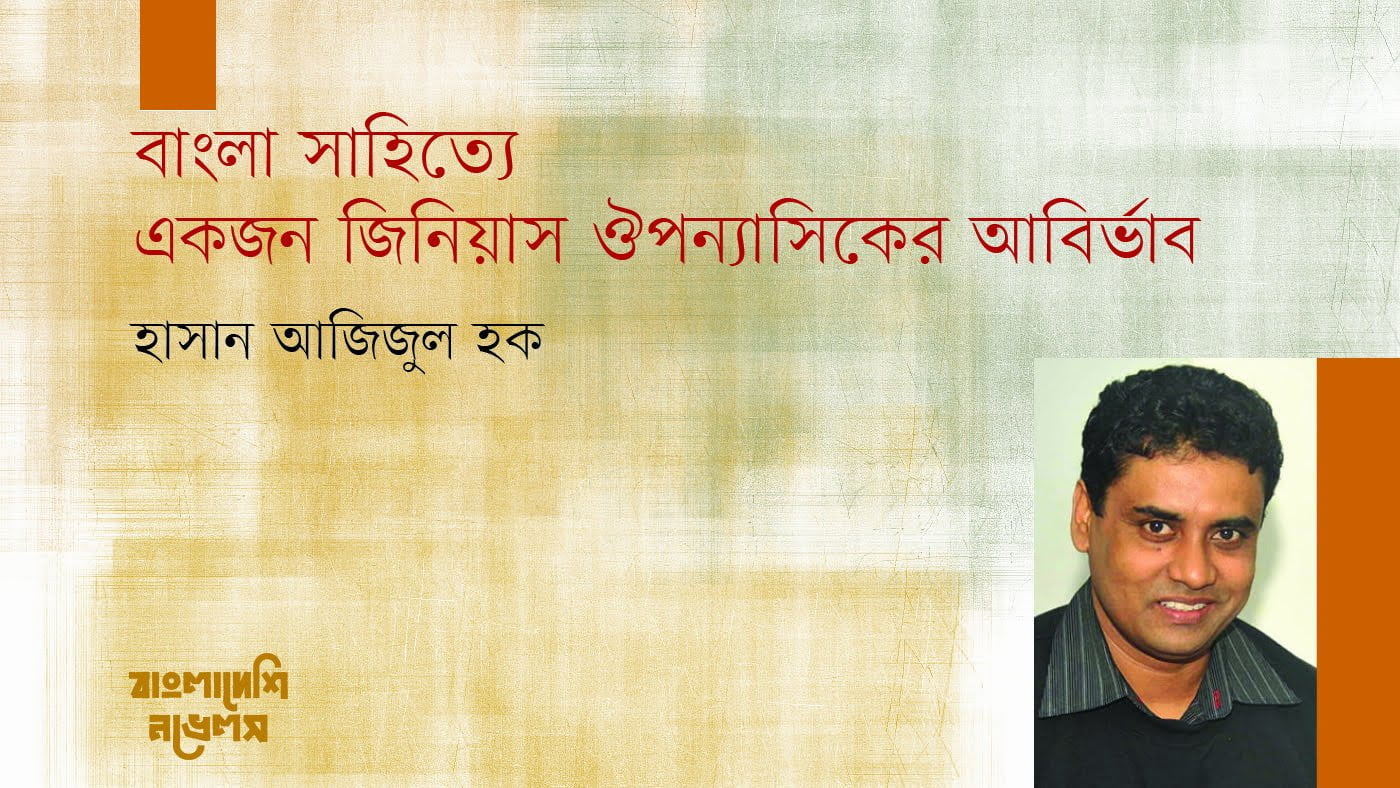বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে যে নাগরিক জীবন ও তার নানাবিধ আন্তর অসঙ্গতির চিত্র ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঁচড়ে উন্মোচিত হয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের “রজনী’’ থেকে রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি’’ ও শরৎচন্দ্রের “গৃহদাহের’’ পল অতিক্রম করে বহুবর্ণিল বর্ণনা বিন্যাসে এক ভাস্কর্যসুলভ সৌধ নির্মাণের পর দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের উপন্যাসে ক্রমপ্রসার লাভ করেছিল অনিবার্য গতি সূত্রে।
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নগরায়ণ এবং নাগরিক জীবনর ক্রমবর্ধমান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন প্রণালী ও রুচির পরিবর্তন হতে থাকে। জীবনের নানাবিধ অনুষঙ্গ যেমন প্রেম-ভালোবাসা, নর-নারীর জটিল মানসিক ও দৈকি সম্পর্ক এবং অন্যান্য মূল্যবোধের পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে ঔপন্যাসিক তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিক সমাজে ব্যক্তির প্রথাগত পথের বিপরীতমুখীন হবার প্রবণতা ও তা থেকে পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব সংঘাতের উন্মেষ এবং সর্বোপরি ব্যক্তি চৈতন্যের অতল গহ্বরে টানাপোড়েনের পলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তারই কুশলী উপস্থাপন হতে থাকল এ সময়ে।
সেলিনা হোসেন স্বাধীনতা উত্তরকালে সাহিত্য জগতে প্রবেশের পরে নাগরিক জীবনের চিন্তা ও আবেগকে অন্তরে লালন করে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি মানুষকে অবলোকন করতে চেয়েছেন তাঁর “পদশব্দ’’ (১৩৯০/১৯৮৩) “মগ্নচৈতন্যে শিস’’ (১৯৭৯) “খুন ও ভালোবাসা’’ (১৯৯০) এবং “ক্ষরণ’’ (১৯৮৮) উপন্যাসে। আলোচ্য উপন্যাসে তিনি নাগরিক জীবনে ব্যক্তি মানুষের অতল গহীনে ডুব দিয়ে তাঁর যন্ত্রণা, কষ্ট, ভয়, হতাশা, সংশয়, সাহসিকতাকে পরিস্ফুট করেছেন অসামান্য আলোকসম্পাতে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো একডিকে যেমন নাগরিক রুচি এবং আবেগকে লালন করে তেমনি অন্যদিকে নাগরিক সভ্যতার যে ঋণাত্মক অবদান-সংশয়, বিচ্ছিন্নতাবোধ, কপটদাম্ভিকতা, নিঃসঙ্গতা, আত্মানুসন্ধানের আত্মদহন প্রভৃতি মনোজগতের অতল গহ্বরের অন্ধকারের পুঞ্জীভূত উপাদানসমূহ চরিত্রের মনের মধ্যে থেকে লেখক আবিষ্কার করেছেন বিশ্লেমুখী প্রক্রিয়ায়। নাগরিক পুঁজিতন্ত্রের অভিঘাতে যেহানে ব্যক্তির সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো অগ্রাহ্য হয়েছে, অনিকেত সঞ্চারী করে তুলেছে তার দৈনন্দিন জীবন, সেখানে যন্ত্রণাদগ্ধ সেই ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের বিবরণ ও বিশে¬ষণ হয়ে উযেছে প্রধান। নাগরিক সভ্যতাও যে ধর্মীয় আবেষ্টন থেকে ব্যক্তির যন্ত্রণা ও অবচেতনার কামনাকে অগ্রাহ্য করতে চায় এবং এরই ফলে ব্যক্তি মানুষ কিভাবে প্রতিবাদী সত্তায় জাগরিত হয় তারই শিল্পরূপ এ-পর্যায়ের উপন্যাসের গতিচঞ্চল প্রান্ত।
সেলিনা হোসেনের “পদশব্দ’’ আট পরিচ্ছেদে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রী সালমার নাগরিক জীবনে দর্শনের অধ্যাপক পিতা এবং মা ও ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে একই গৃহে অবস্থান করা সত্ত্বেও নিরন্তর শূন্য থেকে শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে শেষে সকল প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধাচারণের মাধ্যমে দীর্ঘদহন ও যন্ত্রণার মাঝসমুদ্র পেরিয়ে আত্মঅনুসন্ধানের উপকূলে উপনীত হবার কাহিনী।
উপন্যাসের পাঠ উন্মোচনেই আমরা সালমার সাক্ষাৎ পাই সে আবছেশ “পাপ আবার কি? মানুষ যতক্ষণ নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী নয় ততক্ষণ কোন পাপ নেই।’’ জিজ্ঞাসায় জর্জরিত সে “তবু কেন তোমার জ্ঞানের তলায় এত অন্ধকার দেখি বাবা?’’ এবং বিরক্তি প্রকাশ “মা একবার ডেকে গেছে। সালমা ওঠেনি। আবার ডাকছে। সালমা চুপচাপ বসে থাকে। সাড়া দেয় না। মাঝে মাঝে ঐ কণ্ঠ ভীষণ কর্কশ লাগে। দয়ামায়হীন নিষ্ঠুর জল¬াদের মত’’ অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছি সালমা যে পরিবারে ছোট ভাই সাকিব ও পিতা-মাতার সঙ্গে থাকে সে পরিবারের ওপর তীব্র ক্রোধ লালন করে। কিন্তু নিঃসঙ্গ সালমার এমন কোন সঙ্গী নেই যে সে সেই যন্ত্রণা লাঘবের জন্য সঙ্গ দেয়। এজন্য সে দোতলার নাসিমা আপা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে, যার- “মুখটা মুছে দিয়ে বড় একটা গোলাপ ফুলে ভেসে ওঠে’’। সেই নাসিমা আপা সম্পর্কে তার মার : “মা নাসিমাকে দেখতে পারে না। কেননা নাসিমা প্রচলিত সংস্কারের বেড়ি ভেঙ্গেছে। তাই মা’র যত রাগ’’ (পৃ. ১২)।
সালমা সাকিবের উল্টো মেরুর মানুষ। সালমা “ক্লান্ত হলেও গণ্ডীতে ফেরে না নতুন ছাউনী খুজে।’’ আর সাকিব “হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হলে ছাউনীতে ফেরে।’’ সালমা দর্শনের ছাত্রী, সাকিব সাইকোলজির, যা নাসিমা পড়ান। কিন্তু এ দুই ভাইবোন যেন একে অপরকে আশ্রয় করতে চায়। নিজেদের ভেতরের শূন্যতা পূরণের জন্য তারা নিদেনপক্ষে কলা বলতে চায়। উপন্যাসে উলে¬খ না থাকলেও এদের শূন্যতাবোধ দীর্ঘকালীন এটা বোঝা যায়। একদিকে সাকিব স্প্যানিশ গিটারের সুর মূর্ছনায় শূন্যতার ভেতর নিমজ্জিত হয়। আর তার শূন্যতা এমনই অনিকেত সঙ্কেত নির্দেশকে যে সে বাগানের মালি জলিলের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে ভাবে- “ষাট বছরের ওপরে আর কাউকে বাঁচতে দেয়া উচিত না। এর মধ্যে কারো যদি স্বাভাবিক মৃত্যু না হয় তবে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা দরকার’’ (পৃ. ১৬)। কিন্তু তারপরও সে অশিক্ষিত মূর্খ জলিল মিয়ার ভালোবাসার গল্প শোনে। স্বাভাবিক জীবন বিকাশের জন্য নাসিমা আপার সঙ্গে সাব্বির ভাইয়ের নিঃসঙ্কোচ মিলন দৃশ্য দেখে সালমাও সহপাঠী বন্ধু রকিবের সঙ্গে জীবনের স্বাভাবিক প্রান্তকে স্পর্শ করতে চেয়েছে:
“রকিব তুই আমাকে নিয়ে যাবি সেই দ্বীপে? আমি যাব। স্লো মোশন ছবির মত যাব। নিঃশব্দে। ভেসে আসে। আঃ কি আনন্দ। সুখ পেতে হলে সুখের মত করে পেতে হবে। একটু সুখে তৃপ্তি নেই। স্থল হয়ে যায়। তুই আর আমি আলাদা জগৎ পড়ব। নিয়ম ভাঙ্গবো সুখের রঙ্গ দেখব। পাখির ডাক বদলাব। গাছের পাতা বানাব। আমরা বিধাতার মত হবো। সৃষ্টির আনন্দে মাতবো। আরো কত কি করব। আরো কত কি’’ (পৃ. ৩৫)।
সালমার বহির্বাস্তবতার সঙ্গে অন্তর্বাস্তবতার দ্বন্দ্ব রূপায়ণে লেখক হয়েছেন আছেরা গতিশীল। এ জন্য সম্পর্কের সূত্র ও অধিকার থেকে পিতা-মাতা যে শাসন ও কর্তৃত্ব আরোপ করতে চায় তার ওপর সে সম্পর্কে তার সতর্ক, যুক্তিশীল মানসিকতা–
“উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের কাছ থেকে পাওয়া সংস্কারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে এমন শর্ততো কেউ দেয়নি।’’ এজন্য–
“প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অতিক্রম করে চলতে’’ চায় সালমা। সালমা এও জানে যে পিতা জাহিদ চৌধুরীর আদরের আতিশয্যের কারণ একদা গণকের বাণী নির্ভর–
“এ মেয়ে আপনার জন্যে ভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে। এ যদিন ঘর ছাড়বে আরপরই আপনার একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে’’ (পৃ. ২২)।
ভাগ্যে বিশ্বাসী অস্তিত্বের বিপন্নতায় ভীত পিতার অপত্য øেহে যে সালমা বাল্যকালে সংকট-পীড়া থেকে পিতার মধুর স্মৃতি নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছিল, একদিন সে পরিণত মানসিকতা অর্জনের পরে ভাবছে–
“তুমি অধ্যাপক জাহিদ চৌধুরী থাক। আমার বাবা হতে এস না’’ (পৃ. ৪৭)।
সালমা বিস্ময় জীবনের বিষণ্ণ মানসিকতা উন্মোচনের জন্য নির্ভাবনাময়ী রুবা ভাবীর সংসার চিত্রের উপকাহিনীটি লেখক বিষয়ের অনিবার্যতায় সংগ্রথিত করেছেন।
স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবন দৃষ্টির আলিঙ্গনে সালমা পিতামাতাকে সমালোচনা করেছে নির্মোহ-নিরাসক্তভাবে। তাঁদের চারিত্রিক ক্রটিসমূহ বিশ্লেষণে উন্মুক্ত সালমার সহনশীল ও মননশীল প্রবৃত্তিসমূহকে উন্মোচন ঔপন্যাসিকের অন্যতম কৃতিত্ব। তার ছোট ভাই সাকিবের সঙ্গে মিতালীর সম্পর্ক, বাগানে পোষা একজোড়া সুখ-দ্রঃখ নামে খরগোশ এবং জলিল মিয়ার বাল্যপ্রেমের গল্প ও টেলিফোনে অজ্ঞাত কণ্ঠস্বরে আলাপী জনৈক ব্যক্তির বেদনার্তস্বর প্রভৃতি অনুষঙ্গে ঔপন্যাসিক সালমার অন্তর্জগতের প্রচণ্ড ক্ষরণকে নাগরিক জটিলতার আশে¬ষে বিবৃত করেছেন।
প্রচলিত জীবনাগ্রহে অস¤মত সালমা জহিরের সঙ্গে মা’র দেয়া বিবাহ প্রস্তাব প্রতাাখ্যান করে বন্ধু রকিবের সঙ্গে নির্জন লোকালয়ের ডাকবাংলায় মিলিত হয়েছে।
নিজের আত্মমর্যাদায় সর্বদা সজীব ও স্বতন্ত্র সালমা পিতার প্রেসিডেন্ট পুরস্কার এবং রুবা ভাবীর পুনঃ পুনঃ সন্তান গ্রহণ প্রভৃতি অনুষঙ্গকে স্থুলভাবে পর্যবেক্ষণ করে। পিতার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা থেকে সালমার মনোজগৎ বিশ্লেষিত ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে-
“সালমার ক্ষেত্রে বাবার ভালোবাসার অর্থ ওর নীতিজ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা।’’ এ জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে সালমার বমন উদগীরণ সঙ্কেতাবহ সৃষ্টি করে। এরপরই পিতার সাফল্যে বাসায় পার্টির আয়োজন হলে তা প্রত্যাখ্যান করে উপরতলায় নাসিমা আপার সঙ্গে মাদকদ্রব্যে রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতে চায় সে। এ প্রসঙ্গে নাসিমা চরিত্রের বিকাশও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রচলিত সমাজের বিপক্ষ স্রোতে তিনি ইউনিভার্সিটির যোগ্য শিক্ষক হয়েও নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেন, অন্যদিকে নিজের পিতামাতার জন্য দুঃখবোধ জাগ্রত হলেও তাকে সাময়িক বলে উড়িয়ে দিয়ে নেশায় লুপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। আর দাদুর মনোভঙ্গ পছন্দ না হলে সমাজের উপর কটাক্ষপাত করে নিজের আত্মস্বরূপ অন্বেষণে হন ব্রতী। এ জন্য তীক্ষ্ণ অনুভাবনার জাগরণ তার জাগরকেন্দ্রে :
“মাঝে মাঝে লাগে। তবে সেটা সাময়িক। খুব এটা বেদনাদায়ক নয়। আমার এক দাদু আছেন। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমি চলে আসার পর আমি তার অসুখের কারণ হই। ভাবতে মজা লাগে যে নাসিমা একটি অসুখের নাম’’ (পৃ. ৯৬)।
এভাবে সালমা বাস্তবের সংঘাতে নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রকিবের ভালবাসাকে সে বলে :
“দূর, ভালবাসা আবার কি ?’’ মিলনের পরও তার শূন্যতা আবিষ্কার হয়ে ওঠে অনিবার্য :
“মিছে ডাকছিস রকিব। তোর ঐ আবাল খেলার স্বাদ তো তুই আমাকে দিয়েছিস। সত্যি বড় চমৎকার। কিন্তু এত ক্ষণিকের যে আমি ভুলে যাই সে স্মৃতি। কেন আমার সোনার কৌটায় মানিক হয়ে জ্বলে না রকিব ? কেন জোনাকীর মত জ্বলে নিভে যায় ?’’ (পৃ. ১১৭)।
নিঃসঙ্গ সালমা, ব্যক্তিমানসে জাগরুক নেই রকিব। পার্থিব চাওয়া-পাওয়া যেন তার শেষ হবার পথে। মনোজগতের অসীম সংকটের শিল্পরূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক সময়-পরিবেশ-পরিস্থিতির সংমিশ্রণে কাব্যময় ভাষার সুষম বিন্যাস করেন :
সালসমার চোখের কোণায় জলের রেখা দ্রুত গড়ায়। চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে ও। অন্তরে কোন রকিব নেই। বাইরে সন্ধ্যা গাঢ় হয়। জলিল মিয়া বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। সালমার ঘরে মিটমিটে আলো। সালমার চোখে জল। ঠোঁটে রকিবের স্পর্শ। গালে রকিবের স্পর্শ। বুকের ওপর রকিবের স্পর্শ। কিন্তু অন্তরে কোন রকিব নেই’’ (পৃ. ১২১)।
ছকবাঁধা জীবনের বাইরে এসে যেমন নাসিমা-সাব্বির যে জীবনকে অবগাহন করেছে, সেই জীবনের চিত্রগুলো খুব নিকট থেকে দেখে দেখে সালমার ভেতর জেগে ওঠে নিঃসব্দের বিদ্রোহ চেতনা। এ জন্য রকিবের “তুই ভালোবাসা চাস না সালমা’’ প্রশ্নের জবাবে সে বলেছে :
“কখনো কখনো চাই। সব সময় না। তাছাড়া ভালবাসার অধিকার আমার আর সহ্য হয় না। অধিকার যখন জোর করে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তখন আমার মরতে ইচ্ছে করে’’ (পৃ. ১৩০)।
রকিবের প্রেমসংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে চেয়ে পত্রের প্রত্যুত্তর না দেয়া, তাকে বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যান করে তাড়িয়ে দেয়া, পিতার ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে আমেরিকা যাত্রাকালে কোন রকম আগ্রহ আতিশয্যের প্রকাশ না করা এবং এরই পাশাপাশি রুবা আবীর সিলেটে চলে যাবার সিদ্ধান্তে বিচলিত হওয়া সবকিছুই সালমার চেতনায় আলো ফেলে।
অন্যদিকে নাসিমা-সাব্বির যারা বুকবাঁধা জীবনের অভিলাষী নন, দু’জন তরুণ-তরুণী অনাড়ম্বরভাবে ঘরোয়া বিবাহে স¤মত হয়েছেন কারণ:
“আমি মা হতে চাই সালমা। ঐ ছেলের জন্যে আমার একটা পরিণতি দরকার।’’
অর্থাৎ পুরাতনের মধ্যে নতুনের অভ্যূদ্বয়কে স্বাগত জানানো প্রগতিশীল চরিত্রের অন্বিষ্ট। একারণে সন্তান লাভেরর জন্য প্রলাগত বিবাহের স্পর্শ সালমার দৃষ্টিকোণ লেকে উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে:
“বীজ বোনার জন্যেই তো ওদের জীবনে রংয়ের আবির্ভাব। ওদের চোখে এখন ফসলের স্বপ্ন। ফসলের সোনালী ঐশ্বর্য।’’
পিতার বিবাহ আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বলে:
“জাহিদ চৌধুরী তুমি অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়াও। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দাও। বই লিখে নাম কর। ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে বিদেশ যাও। ছাত্র পিটিয়ে মানুষ করার গৌরবে অহংকারবোধ কর। কৃতীছাত্রকে নিয়ে জোর গলায় কথা বলে আরাম পাও। কিন্তু সত্যি করে বলতো জাহিদ চৌধুরী তুমি নিজের সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছ কি না ? আজ তুমি আরেকজনের ওপর সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ। অথচ সেই ক্ষমতাই যে তোমার নেই তুমি তা একবারও তলিয়ে দেখছ না। আমি একটা সামান্য মেয়ে। তোমার ভাষায় এক রত্তি মেয়ে। আমি নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তোমার মত বেঁকেচুরে যাই না। তোমার মত ভুল পথে গিয়ে দীনতার গ¬ানিতে হাবুডুবু খাই না। আমি সালমা অনায়াসে সাগর সাঁতরাতে পারি।’’
অনায়াসে সাঁতার কাটার ক্ষমতা নিয়ে সালমা ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে নাসিমা সাব্বিরের নতুন বাসায় গমনও যেন সালমার পরিণতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কারণ সালমাদের দোতালায় তারা থাকলে সালমা-রকিবের বিবাহোত্তর আশ্রয় পাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠত। দুর্বিনীত ভালোবসার কাছে আত্মসমর্পণ করেও সালমার ভেতর “মুক্তির আনন্দ’’ আর “ভালবাসার স্বাদ’’ একীভূত না হয়ে বিচ্ছিন্নতা বোধের জন্ম হয়। এ জন্য তার অনুভাবনাময় চেতনালোক:
“আমি চেয়েছিলাম একজন শক্তিমান পিতা, একজন মহৎ পিতা। — যার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি নিজের অস্তিত্বকে মহান বলে অনুভব করতে পারতাম। … ভালোবাসা নয়। তোমায় নিয়ে আমি দূরে সরে যেতে চাই। আমি যা করেছি তার জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইব না। কেননা আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পার না। তোমার ব্যর্থতাকে আমি নিজে অতিক্রম করব বলে পথে নেমেছি। তোমার কানে কোনদিন পৌছবে না আমার পদশব্দ’’ (পৃ. ১৭৯)।
এভাবে সালমা জন্মদাতা পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন দিগন্তের সংস্পর্শে এসেছে এবং বাস্তব জীবনে সে নির্বাচন করে নিয়েছে নব জীবনের অঙ্গীকার।
সরলপ¬টে সংগ্রথিত কাহিনী সর্বজ্ঞলেখকের দৃষ্টিকোণ লেকে রূপায়িত হয়েছে। তবে চরিত্রের মনোজগত উন্মোচন ও অপর পার্শ্বচরিত্রের বিকাশে সালমার দৃষ্টিকোণ বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া প্রতিপার্শ্ব নির্মাণ ও চরিত্রের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব উন্মোচনে ঔপন্যাসিক সেলিনা
হোসেন দৃশ্যময়, চিত্রময় পরিচর্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সময়প্রবাহকে জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সংশি¬ষ্ট করে ভাষায় গতিবেগ এনেছেন সযতœ প্রয়াসে। চেতনাপ্রবাহ রীতির সরল আবর্তে সালমার মনোকথন হয়েছে উপন্যাসের মূল কৌশল।
বর্ণনামূলক “পদশব্দের’’র শব্দ ও ভাষা প্রয়োগে সেলিনা হোসেনের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান:
ক. রিণরিণে যন্ত্রণার কাঁপুনি (পৃ. ১৬৯)।
খ. মাড়াল পথেই আমার সুখ বেশি (পৃ. ১৭৭)।
গ. কয়েক হাজার স্পিলিনটারের মত তা গেঁথে গেল মনে (পৃ. ১৭১)।
জীবন ও সময়প্রবাহের সঙ্গে ব্যক্তির যন্ত্রণাকে একাত্ম করে তাকে রুপায়িত করা হয়। সালমার মনোজগতে নাসিমা আপার কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা থেক যন্ত্রণার সূত্রপাত এবং নির্ঘুম মধ্যহ্নে তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তকে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নরূপে:
“বাগানে রোদের লুটোপুটি। কলাবতী ঝোপ লেকে টুনটুনি উড়ে গেছে। হলুদ প্রজাপতিও নেই। আনুর মা রান্নাঘরের বারান্দায় আঁচল পেতে শুয়ে আছে। জলিল মিয়া কামিনীগাছের নিচে বসে বিড়ি টানেন। দুপুরে ঘুম আসে না ওর। করতোয়াপাড়ের ছেলে সহজে অলস হয় না। কাঠের বাক্সের ভেতরে সালমার সুখ-দুঃখ একে অপরের গায়ে মুখ ঘষে। জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। বাটি থেকে দুধ খায়। অথবা তারের ওপর মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আম, নিম, আমড়ার পাতা ফসফস করে জ্বলে ওঠা দিয়াশলাইর কাঠির মত টুপ করে ঝরে যায়। বেদনাহীন ঝরায় কোন আলোড়ন নেই’’ (পৃ. ৩৬)।
মূলত নারীর অধিকার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে আত্মস্বরূপ বিকাশে প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে উজ্জীবিত হয়ে ইতিবাচক জীবনদর্শন নির্বাচন করাই সেলিনা হোসেনের “পদশব্দের মূল বিষয়।’’ ‘সালমা’ যে পদশব্দ শুনেছে নাসিমা আপার কাছ থেকে সেই পদশব্দের শ্র“তি তাকে পৌঁছে দিয়েছে গন্তব্যের দিকে সিদ্ধান্তের সন্নিকটে। এজন্য সালমা সমাজের কাছে পদশব্দ শুনিয়েছে কারণ সমাজের গতানুগতিক পথের বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয় সুনির্দিষ্ট জীবনপরিক্রমায়।
“মগ্ন চৈতন্যে শিস’’ (১৯৭৯) সেলিনা হোসেনের নাগরিক মধ্যবিত্তের মানসিক জটিলতার শিল্পভাষ্য। চেতনার গহীন স্তর থেকে নৈঃসঙ্গ পীড়িত মানুষের আর্তনাদ চূর্ণবিচূর্ণ স্মৃতিচারণে প্রবল আবেগের অনুরণনে শব্দরূপ পেয়েছে। উপন্যাস বিধৃত চরিত্রপুঞ্জের ভেতর জামেরী ও মিতুলের অন্তর্যন্ত্রণা এবং অন্তর্মুখি চেতনাপ্রবাহ গীতলতায় পর্যবসিত হয়েছে পরিণতিতে।
জামেরী ও মিতুলের অন্তঃসংলাপ, স্বীকারোক্তি, আত্মঅনুসন্ধানের আত্মদহন, বোধ ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হওয়ার কাহিনী “মগ্ন চৈতন্যে শিস।’’ ‘ইনার রিয়ালিটি’ ধর্মী এই ধরনের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সেলিনা হোসেনের বক্তব্য স্মরণীয় ঃ
“এ ধরনের উপন্যাস মাত্রই রঙিন জলবায়ুর অধিকারী। জলবায়ু দেহের এবং মনের। দেহ যেমন আঙ্গিকের বিষুবরেখার বিচিত্রিত হয় মন তেমন সাইকেডেলিক কালারে নিঃশেষ পরিক্রমণ ভালোবাসে। বিদেশি উপকরণে অরুচি নেই, কিন্তু আমরা চাই দেশীয় চেতনায় তার আত্মস্থ রূপ। নইলে রচনার বর্ণাভ উজ্জ্বলতা ফিকে হতে বাধ্য’’ (স্বদেশে পরবাসী, পৃ. ২০)।
এই সাইকেডেলিক কালারের বিচিত্র মাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে। পিতৃমাতৃহীন শহুরে বাড়ির মালিক মধ্যবিত্ত লেখক জামেরী তার ভাড়াটিয়ার মেয়ে মিতুলের প্রণয়নের ভেতর দিয়ে যে অর্থময় জীবন প্রত্যাশা করেছে, তা মিতুলের পারিবারিক ক্ষেত্রে বাবার সঙ্গে মার বিচ্ছিন্নতা এবং এর ফলে মিতুলের মাতৃ অনুসন্ধান ও নিরন্তর পিতৃপৃহ বিষদগ্ধ হবার ফলে মানসিক অসুস্থতায় চেতনা লুপ্তিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং অতলান্তিক শূন্যতা ও যন্ত্রণার অসীম হাহাকারে বেদনার্থ হয়েছে জামেরী।
মোট সাতটি পরিচ্ছেদে জামেরীর আত্মকথনে মিতুলের বিষণ্ণ জীবনের পরিচয় আভাসিত এবং বন্ধু রায়হানের ধ্বংসজনক ভালোবাসার পট নির্মিত হয়েছে।
জামেরী পিতার বহু কষ্টে নির্মিত বাড়িতে অবস্থান করে নির্দিষ্ট আয় নিয়ে। অর্থ আসে সংবাদপত্রে অফিসে কাজ করে এবং বাড়ি ভাড়া থেকে। সে স্বপ্ন দেখে প্রমিথিউসের জায়গায় নিজেকে, একটি ঈগল পাখি হৃৎপিণ্ড খাবলে খাচ্ছে। তার শ্রাবণের বৃষ্টিমুখর আকাশ ভাল লাগে। স্বপ্ন ভালো লাগে না। নিঃসঙ্গ পীড়াদায়ক হয়ে উঠলে মিতুলকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কারণ, সে জানে মিতুল তাকে যতটুকু ভালবাসে তার চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। এ জন্য সে মিতুলের কষ্টের সঙ্গী হয়। কারণ, মিতুলের দু’বছর বয়সে মা, আর একজনের সঙ্গে চলে যায় ফলে পিতা অন্য একজনকে বিবাহ করে। বর্তমান মা তার কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেও পারিপার্শ্বিকতা তাকে বিষণ্ণ করে তোলে। কারণ তার পিতাকে সহ্য করতে পারে না সে। জামেরীর আত্মকথনে:
“আমি জানি মা কেন চলে গেছে ? আমি ভেবে ভেবে খুঁজে বের করেছি। বাবার এই মেয়েলীপনার জন্যই মা বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে। বল আমি ঠিক বলেছি কিনা জামী ? ওর এসব কলা শুনলে আমার শরীরে একটা শিরশিরে অনুভূতি হয়। বুকটা খালি হয়ে যায়। মনে হয় মিতুল আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে’’ (পৃ. ১৪)।
জামেরী একজন ঔপন্যাসিক। শিল্পের নির্মম জগত নিয়ে সে নিরন্তর দগ্ধ হয় স্বজনহীন এই শহরের বুকে সে শিল্পের গোলকধাঁধায় অনন্তকালের যাত্রার আয়োজন করেছে। স্বপ্নের শেষে সে উপন্যাসের প¬ট পেয়ে যায়।
জামেরী সংবাদপত্র অফিসে কাজ করে। রাতে ফিরে জানালা দিয়ে ইউক্যালিপটাসের সৌন্দর্য দেখে, বালজাক পড়ে আর যে মিতুলের প্রত্যাশা করে সে ভোরে এসে জানায়:
“চল আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে খুঁজে দেখি কোথায় মাকে পাওয়া যাবে। মা কিসের তাড়নায় বাবার কাছ থেকে দূরে চলে গেলো। আচ্ছা জামী, মা যখন চলে যায়, আমার কথা তার কি একবারও মনে হয়নি’’ (পৃ. ২১)।
এই মিতুল যেন ‘খুন ও ভালোবাসা’র কাহারী। যে কাহারী বেজন্মা শব্দটি শোনার পর অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছে। এই মিতুলও মা’র ত্যাগ করে চলে যাওয়া মেনে নিতে না পেরে
বিষণœতা লেকে রহস্য উন্মোচনে পথে নেমেছে। মিতুলের এই আত্মক্ষরণ জামেরীর কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। জামেরী নিঃসঙ্গতায় আশ্রয় খোঁজে, হাসপাতালে যায় ডাক্তার বন্ধু রেজার কাছে রুগীর মাঝে ভিন্নতর অর্থ অন্বেষণ করতে। বন্ধু রায়হান, যে তার বন্ধু জামিলকে মত পার্থক্যের জন্যে খুন করেছে সে তার ঘরে এলে তার মাঝে উপন্যাসের উপাদান অন্বেষণ করে।
জামেরীর বন্ধু রায়হান সিদ্ধান্ত নিয়েছে “ছন্দা যে লোককে তুমি বিয়ে করবে তাকে আমি খুন করব।’’ জামেরী যায়হানকে দেখে, মিতুলকে দেখে। তার উপন্যাসের ছক মাথার ভিতর তৈরি হতে থাকে। রাতে ত্রিশ পৃষ্ঠা লেখার পর তার মনে হয় কিছুই হচ্ছেনা। তার বন্ধু শরাফীর কথা মনে হয়, যে কয়েক ঘন্টায় একটি গল্প দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু জামেরী সমাজের কাছে কমিটেড। এজন্য জীবনকে পরিপূর্ণ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সাহিত্য গড়ে তুলতে চায়।
কিন্তু যখন তার উপন্যাসের চরিত্র রায়হান বর্তমানের আণবিক যুগে ‘আণবিক ভালোবাসা’ চায়, তখন তার ব্যর্থতাবোধ জেগে ওঠে কিছু না করতে পারার জন্য। রায়হান মিতুলের মা’র সংবাদ জামেরীকে দেয়। মিতুলও জামেরীর মতো প্রমিথিউসের অনুরূপ শাস্তির স্বপ্ন দেখে। তবে কি জামেরী মিতুল একই পরিণতির দিকে যাচ্ছে ? হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে যন্ত্রণার বহ্নি শিখা কি জ্বালিয়ে দিবে তারা এ উপন্যাস ?
মিতুলের মা’র বাসা খুঁজতে বের হওয়া, জামেরী মিতুলকে সঙ্গে নিয়ে নাটক দেখতে গিয়ে মিতুলের অসুস্থ হওয়া, ছন্দার বিবাহ সম্পন্ন হওয়া, রায়হানের খুনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, মিন্টুর জামেরীকে উপেক্ষা করা এবং মিতুলের মা’র সঙ্গে জামেরীর সাক্ষাৎ ও মিতুলের মা’র মিতুলকে সাক্ষাৎ দানে অপারগতা প্রকাশ–বহুমাত্রিক দ্বান্দ্বিক শব্দরূপ পরিগ্রহ করে। তবে মধ্যবিন্দুর মধ্যে জামেরীর নিঃসঙ্গত ও মর্মপীড়া তীব্রভাব প্রকাশ পেয়েছে একই সঙ্গে মিতুলেরও:
“এক মহিলা তার পঁচিশ বছর আগের ইতিহাস ঢেকে রেহেছে সঙ্গোপনে। সে জবিনের প্রতি তার কোন আকাক্সক্ষা আছে কি-না, আমি জানি না। আর একটি মেয়ে সে ইতিহাসের তৃষ্ণায় ব্যাকুল। শুধু ব্যাকুল নয়, সে তৃষ্ণা তার জীবন-মরণ সমস্যা’ (পৃ. ৬৭)।
অন্যদিকে রায়হানের ছন্দার স্বামীকে হত্যা এবং জামেরীর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ, জামেরীর তৃতীয় উপন্যাসের প্রকাশ, শরাফীর ও অন্যান্যদের সৃজনশীল শিল্প সম্পর্কে আলোকপাত, রায়হানের সিজোফ্রেনিয়া রুমীতে পরিণত হওয়া, এবং রেজার কাছে নিয়ে যাওয়া, মিতুলের মা’র সঙ্গে সাক্ষাৎ, মিতুলকে জামেরীর বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মিতুলের মা’র মিতুলের সঙ্গে নিস্পৃহ ব্যবহার বিস্তৃত পটে শিল্পরূপ পেয়েছে। রায়হানের খুন পরবর্তী অপরাধবোধ তীব্র ভাষারূপ পেয়েছে এবং জামেরী যেন তার যন্ত্রণা এবং মিতুলের যন্ত্রণা ও ছন্দার যন্ত্রণার মহাকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে।
“আমি পাগলের মতো আমার ভালবাসা হাতড়ে বেড়াই। কোথাও কিছু নেই। সব ফাঁকা কামালপুরে বাংকারে বসে সমগ্র দেশটাকে যেমন বুকের মধ্যে পুরে রাখতাম, তেমন করে আর কিছুই পারছি না। এতক্ষণে নিজেকে একটা পুরোপুরি খুনী মনে হচ্ছে। শুধু ছন্দার নয়, এখন আমার বুকের বাংকারেও পড়ে আছে একটা লাশ। উঃ জামেরী, তোকে আমি বোঝাতে পারবো না এ যন্ত্রণার কথা’’ (পৃ. ১০৬)।
উপন্যাসে এম্বুলেন্সের তীব্র শব্দ গ্যালিলিওর আকাশে শাণিত রোদ্দুর, পীচ গলে যাবার ঘটনা জামেরীর অন্তর্বেদনাকে উন্মোচিত করার জন্যে ব্যবহৃত। জামেরী মিতুলকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার মার সব সংবাদ জানালে মিতুল অন্যরকম হয়ে যায় যেন দূরে সরে যায়। তখন জামেরী দেখে নীলাভ ধোঁয়ায় রেজা, রায়হান, শরাফী, সাইকি, মিতুল সবাই ঢাকা পড়েছে। কাউকে সে খুঁজে পাচ্ছে না। জামেরীর আর্তনাদ:
“বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো। সে জনস্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলাম, আমার চারপাশে কেউ নেই। আমার নিজস্ব কেউ নেই। যার ওপর আমার সব আবদার, সব অভিমান, সব অত্যাচার খাটবে। মিতুল ছিলো সেও এখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। দৌড়ে গিয়ে কোলে মুখ গুজে শুয়ে থাকতে পারবো না। বলতে পারবো না, মিতুল, আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে। আমি এহন কোলায় যাবো ?’’ (পৃ. ১৪০)।
এই আশ্রয়চ্যুত, মানসিক জটিলতায় বিধ্বস্ত, জামেরী যেন শাহরিয়ারের অন্যরূপ। যার রাত কাটে প্রায় ঘুমহীন। দিন কাটে মিতুল রায়হানকে নিয়ে। এরই মাঝে মিতুল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ্যাম্বুলেন্সির বিচিত্র শব্দ তখন জামেরীর কাছে অনন্তকালের পথে যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে জানে মিতুলের সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার “মগ্ন চৈতন্যে সমস্ত প্রাণ শিস’’ বাজাতো সেই মিতুল এখন অচেতন। তার চেতনায় কোন ভালোবাসার জল পড়ে না (পৃ. ১৪৪)।
যে মিতুলকে নিয়ে জামেরীর স্বপ্ন-কল্পনা ভালোবাসার জন্ম হয়েছিল তা যেন অসহ্য বেদনার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়। তার ডাক্তার বন্ধু রেজা তাকে সান্ত্বনা দেয়। অনেক শখ করে কেনা তার বিবাহের উপকরর এখন বেদনার উপকরর শুধু। আর রায়হানকে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তখন:
“রায়হান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে থাকতে চেয়েছিলো। আমি রাখতে পারিনি। রায়হানকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার ছিলো না। মিতুল ? মিতুলও তো আমার কাছেই থাকতে চেয়েছিলো। কৈ রাখতে তো পারলাম না। কাউকে ধরে রাখার আমার কোন ক্ষমতা নেই। দু’হাতে মাথাটা চেপে ধরলাম। কপালের শিরা দপদপ করছে। মনে হচ্ছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বিরাণ জনপদ। খাঁ খাঁ জনমানবহীন আমি একা একা পথ হাতড়ে চলি’’ (পৃ. ১৫৭)।
এই বিরাণ জনপদে একাকী দাঁড়িয়ে জামেরী অচেতন মিতুলের জন্যে সংগ্রাম করে। তার উপন্যাস রচনা শেষ করে। ইতোমধ্যে সংবাদপত্রে চিঠিপত্র কলামে মিতুলের কৃতিম শ্বাস প্রত্যাহার নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়। জামেরী কলম মরে মিতুলের পক্ষে। মিতুলের পিতাকে
ইবলিশের মতো তার মনে হয়। শীতের কুয়াশার মতো চারিদিকের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের প্রতি তার বিতৃষ্ণা জন্মায়। ম্যাক্স প¬্যাঙ্কের জীবনী পড়ে অনমনীয় মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ পায় জামেরী। মিতুলের শ্বাস প্রত্যাহারের বিপক্ষে যেমন সে অনড় মন্তব্য প্রকাশ করে। তেমনি তার প্রকাশিত উপন্যাসের বক্তব্যের স্বপক্ষে সে অনড় অবস্থান নেয়। তার প্রকাশিত উপন্যাসের বক্তব্য নিয়ে মৌলবাদী গোষ্ঠী উত্তেজিত হলে সে নির্বিকার থাকে। এজন্য প্রকাশকের সাবধানে থাকার উপদেশে সে হেসে বলে:
সাবধান থাকার আগ্রহ আমার নেই। যা আমি লিখেছি তার মোকাবিলা আমি নিজই করবো। তাকে ছেড়ে পালাবো না। পালিয়ে যাওয়ার অর্থ নিজেকে প্রতারিত করা। আমার বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা যদি না হয়, তাহলে আমি লিখলাম কেন ? কার ভরসা করে শব্দগুলো আমার প্রেমে পড়েছিলো ? তাদের একলা ফেলে এখন আমার পালিয়ে যাওয়ারয কোন মানেই হয় না’’ (পৃ. ২০৩)।
জামেরীর কাম্য, সমাজের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্যক্তি, যে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে বেড় ওযে তাকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচিত হয়। এ জন্যে কল্পনার রঙ মিশিয়ে ব্যক্তিকে ঔপন্যাসিক করে তোলেন জীবন্ত। একারণে জামেরী তার উপন্যাসে খুনী রায়হানকে হত্যা করলেও বাস্তবে ছন্দা জামেরীর চেয়েও বেশি জীবনবাদী।
কিন্তু সাইকি হয়ত রায়হানের সঙ্গে আবার ভালবাসার সূত্রে মিলিত হতে পারে। আর জামেরী ? জামেরী নিস্তব্ধতার শূন্যে স্বপ্ন দেখে জীবন কাটাবে ? নাকি সৃষ্টির নতুন সংবেদনায় আবার সজীব হয়ে উঠবে ?:
“হাতের তালুতে চোখের জল মুছলাম। মনটা এমন। কিছুতেই বিষণœতা ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বাঁধ ভেঙে গলগলিয়ে ঢোকে। তছনছ করে যতেœর শস্যভূমি। আবার জল মুছলাম। হাতটা কেঁপে গেলো। থাক, মুছবো না। মনে হলো জলটাই উৎস। জলটাই সব। চারদিকে শান্ত গভীর সমুদ্র ? আমি প্রোটপ্লাজমের বিন্দু হয়ে অসছি। চোখের জল এখন ছলছল কলকল। আদিম চরাচরে বুঁদ হয়ে গন্ধ নেয়ার দিন শুরু। কেবল আমার বুকে সৃষ্টির বেদনার চৈ চৈ’’ (পৃ. ২০৮)।
এই কেন্দ্রীয় চরিত্রের আত্মকথনে “মগ্ন চৈতন্যে শিস’’ উপন্যাসের অবয়ব গঠিত। নায়ক জামেরী তার ব্যক্তিজীবন, মিতুলের জীবন ও রায়হানের জীবন সর্বজ্ঞ স্রষ্টা হয়ে উপন্যাসে সক্রিয়। অন্যান্য চরিত্রের জীবন-দর্শন ও আচার-আচরণ তার প্রেক্ষণে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে চরিত্রের জীবনরেন সংকট ও সমস্যাকে অতিক্রমণের যন্ত্রণা এবং আর্তনাদকে শব্দরূপ দেয়ার জন্যে ঔপন্যাসিক প্রমানত বিশে¬ষণমূলক, গীতময় ও ভবিষ্যৎ নির্দেশকে মনোকথনের স্বপ্নময় পরিচর্যা রীতিতে উপস্থাপন করেছেন। অতীত বর্তমানকে মেলবন্ধনরূপে ও স্মৃতিচারণে বিজ্ঞান, প্রাচীন সাহিত্য মিথ প্রভৃতি অনুষঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন:
(ক) শিল্প হোল সেই ক্রীট দ্বীপের ক্রুর হৃদয়হীন নিষ্ঠুর বাদশাহ মিনোস। শিল্পীকে সে গোলকধাঁধার ভেতর মিনোট—ওরের সামনে ঠেলে দেয়। শিংওয়ালা ষাঁড়ের মাথা আর মানুষের শরীর নিয়ে সে জন্তু খাবার জন্যে হাঁ করে থাকে। সে এক বিচিত্র জগৎ। সে ধাঁধায় ঢুকলে পথ খুঁজে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। শক্তিমানরা পারে মিনোটওরকে হত্যা করতে। আরি-আদনির মতো অনির্বাণ প্রজ্ঞা রেশমী সূতো হয়ে পথ দেখায়। কিন্তু দুর্বলেরা মরে। ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে পথ হাতড়ায় । কোনদিন সে পথ খুঁজে পায় না। তারপর মিনোটওরের খোরাক হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শিল্পের যে গোলকধাঁধায় আমি নেমেছি, তা আমি অতিক্রম করবই। অফুরাণ শক্তির খনি আমার গায়ের নিচে জমে আছে। মিনোটওরকে হত্যা করব। হৃদয়ের আলো আরি-আদনি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেশমী সুতো ধরে। আমি বেরিয়ে আসবই’’ (পৃ. ১৭)।
মিতুলের সৎ ভাই মিন্টু জামেরীকে নিয়ে অন্তরালে ঠাট্টা করলে, জামেরী তা শু-নে মানসিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। ফলে তার বিক্ষিপ্ত মানসিকতা রূপায়রের জন্যে আগুন জ্বলে ওঠা এবং গ্যালিলির প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় সত্যবাদীতার জন্যে নির্যাতনের কথা। এখানেও জামেরী তার উপন্যাসের জন্যে মিন্টুর কাছে যে উপেক্ষা পেয়েছে তাকেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে।
(খ) “মুকুটের মতো নীল বাতি মিতুলের নীল বেনারসী হয়ে আমার বুকে আটকে রইল।’’ নীল বাতি যেমন মুকুটের মতো সৌন্দর্য বিস্তার করে তেমনি জামেরীর কেনা মিতুলের জন্যে নীল বেনারসী হৃদয় জুড়ে থাকল।
বস্তুত সাবলীল গদ্যভঙ্গ ও ছোট ছোট বাক্যে সেলিনা হোসেন “মগ্ন চৈতন্যে শিস’’ উপন্যাসে যে শিল্পীর জীবন রূপায়ণ করেছেন তা বিংশ শতাব্দীর ঢাকা নগরের সংকীর্ণ, অব্যবস্থাপূর্ণ ও অসঙ্গতিময় জীবনেরই চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেখানে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন, সীমাহীন শূন্যতায় নিমজ্জমান এবং ব্যক্তির হৃদয় খুঁড়ে যে শিল্প প্রকাশ পায় তাও সমাজের গণ্ডিতে নিরর্থক হয়ে যায় অথচ এরই ভেতর শিল্পী পুনরায় নিজের ভেতর উৎসাহ বোধ করে। চেতনা পায়, আবার সৃষ্টির বেদনা নিয়ে জেগে ওঠে। ঔপন্যাসিকের আত্মদর্শনই যেন এভাবে প্রকাশ পায়, আমাদের আলোড়িত করে।
“খুন ও ভালোবাসা’’ (১৯৯০) নাগরিক চেতনায় লালিত জনৈক শাহরিয়ার প্রণয়িনী শামান্তাকে সন্দেহ বশত হত্যা করে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী হয়ে পলাতক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা শেষে বিবেক দংশনে পীড়িত হয়ে আইনের কাছে আত্মসমর্পণের কাহিনী। নাগরিক জীবনে সমকালের নানাবিধ অসঙ্গতি কিভাবে ব্যক্তি মানুষকে অসহায় বিপর্যস্ত করে তুলেছে চৈতন্যের গূঢ় প্রবহমানতায় সেলিনা হোসেন আলোচ্য উপন্যাসে তা বিধৃত করেছেন।
বন্ধু কায়সারের সংবাদে শাহরিয়ার ইমতিয়াজের সাথে শামান্তার অবৈধ সম্পর্ক কল্পনা করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে শামান্তাকে, প্রতারণার প্রতিশোধ হিসেবে। নগরসভ্যতা সবকিছু গ্রাস করেছে। এখানে ভালোবাসা স্নেহ মমতা নিক্তির পরিমাপে নির্ণিয় হয়। ব্যক্তিজীবনের
আকাক্ষ্ণাআশ্লেষে পূর্ণ হয়ে ওঠে সমাজের নানাবিধ ব্যধির কারণে। এ জন্যে নাগরিক মানুষ ভালোবাসার কাঙ্গাল হয়ে নির্ভর করে প্রেমিকার ওপর। কিন্তু প্রেমিকা যখন প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে তখন আশ্রয়চ্যুত মানুষ ভয়ানক হয়ে ওঠে। মানুষের এই মনস্তত্ত্বের পশ্চাতে তার জৈবিক এবং একক কর্তৃত্ব অর্জনের মানসিকতা প্রধান ভূমিকা পালন করে। মূলত প্রেম এবং নরনারী সম্পর্কের নানাবিধ জটিল উপল ক্ষণভঙ্গুর চেতনার অবলম্বন–সেলিনা হোসেনের নাগরিক জীবনসম্পৃক্ত উপন্যাসের মৌল বৈশিষ্ট্য।
উপন্যাসটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক প্রথমেই শাহরিয়ারকে উপন্যাসে অবতীর্ণ করে ১-৩২ পৃষ্ঠাব্যপী তার শামান্তা হত্যার কারণ, স্মৃতি তাড়না থেকে তার ভানুগাছের মনিপুরিদের মাঝে বন্ধু দীননাথের সহায়তায় আশ্রয় গ্রহণ ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন। ৩৩-৮৬ পৃষ্ঠার মধ্যে শ্রীমঙ্গলের জুরিন চা বাগানে কাহারির সাহচর্যে খাসিয়া পরিমণ্ডলে জীবনের অন্য প্রান্তের অভিজ্ঞতা অর্জন বিধৃত। এখানে কাহারি সোনাই একটি উপকাহিনী সংশি¬ষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে ৮৭-১৫৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমঙ্গল থেকে অজানার উদ্দেশে যাত্রা করে সাজেক ভ্যালির লুসাই সম্প্রদায়ের সঙ্গে শাহরিয়ার আত্মীয়তার সম্পর্কের পটভূমি সৃজিত। বৃহৎ পরিসরে শাহরিয়ারের লুসাই সমেয়ে রুহিনের সঙ্গে খ্রিষ্টান রবিনে পরিবর্তিত হয়ে বিবাহ বন্ধন এবং রুহিনের সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যু ও তাদের সম্প্রদায়ের জীবন-যাপন নিয়ে বড় ক্যানভাসে চিত্র অঙ্কনের কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও মেরীর থিওপিল এবং সর্দারের উপকাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। ১৫৮-১৭৪ পৃষ্ঠার মধ্যে ভবঘুরে খুনি শাহরিয়ারের গোমতী নদীর তীরে জেলে হারাধন বুড়োর আশ্রয়ের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। অবশেষে ১৭৪-১৮৪ পৃষ্ঠায় ৭ বছর পরে আত্মগ¬ানিতে উন্মুলিত শাহরিয়ারের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন এবং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের নাটকীয় ঘটনা পরিণতির সহজ মীমাংসায় পর্যবসিত।
বস্তুত এই ক্রম উল¬স্ফুন জীবনাচারের ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক শাহরিয়ারের আত্মগ্লানি থেকে প্রশান্তি এবং শেষে আবার অন্তর্লীন বেদনা যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হবার প্রক্রিয়াটি অঙ্কন করেছেন।
চিলোকোঠায় রক্ত তুলি ক্যানভাস এবং বইয়ের জগতে যার একদিন সময় কাটত নির্বিঘ্নে সে এখন পলাতক জীবন যাপন করছে। কিন্তু সে উপলব্ধি করে সচেতনভাবে সে খুন করেনি; হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়েছিলো, তার এই অনুতপ্ত হৃদয় আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে:
“মানুষের জীবনে এমন সর্বনাশ পরিবেশ আসেন কেন ? কেন নিজের ভবিষ্যৎ ন্ধকার করে তার বর্তমান? ও যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, যে কাজের সঙ্গে আমার মগজ ক্রিয়াশীল ছিলো না, তার জন্য কি আমার দায় আছে ? কিন্তু আমি তো একজনের জীবন নষ্ট করেছি, সে দায়িত্ব আমাকে বহন করতেই হবে। আমি কেমন করে এড়াবো ? একি এড়ানো যায় ? নাকি এড়ানো উচিত ? (পৃ. ২)।
মাধবপুরে দীননাথের আশ্রয়ে সে নতুন জন্ম প্রত্যাশা করেছে রাস উৎসবের শেষে স্থানীয় স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টারের চাকরি পাবার পরে ক্লাসের রেণুবালাকে নিয়ে শাহরিয়ার স্বপ্ন
দেখে, শামান্তার সঙ্গে মিলাতে চায়। কিন্তু মনিপুরিদের বিয়ের অনুষ্ঠান চমৎকার লাগলেও দীননাথের গ্রামে রাধাকান্তের মতো যুবকরা কৈফিয়ত চায়:
“তুমি সব সময় রেণুবালার দিকে তাকিয়ে থাকো কেনো ?’’
শাহরিয়ার তার ভালোলাগার কথা জানালে অনর্থ ঘটে। অবশেষে দীননাথের ব্যবস্থায় তাকে শ্রীমঙ্গলের জুরিন চা বাগানে আনারস পাহারার কাজে নিযুক্ত কাহারীর সাহচর্যে টিলার ওপর কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিতে হয়।
কাহারীর কাহিনীর সূত্রপাত নাটকীয়ভাবে। পাঁচদিনের কাহারীকে কোলে নিয়ে পাত্র খোলা চা বাগান থেকে যে সুভাষ একদা জুরিন চা বাগানে রমজান আলীর আনারস বাগান পাহারা দিতে চলে এসেছিলো সেই সুভাষ আসলে ওর প্রকৃত পিতা নয়। তাহলে তার বাবা মা কারা ? সুভাষের মৃত্যু তাকে আত্মসত্তার অনুসন্ধানের পথে বের হতে ভেতর থেকে ধাক্কা দেয়:
“আনারস বাগানের ওপর ছোট্ট কুঁড়েঘর সুভাষ ওকে দিয়ে গেছে, দিয়ে গেছে আনারস বাগান পাহারা দেবার চাকরি, আর দিয়েছে একটা শব্দ। জানিয়ে দিয়েছে যে, ও বেজন্মা’’ (পৃ. ৩৭)।
যে প্রকৃতির সৌন্দর্য, পাহাড়ী ঝরনা, আনারসসের ফুল একদা তাকে পাগল করে তুলতো তা এখন পরাবাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়:
“কাহারী আনারসের কচি ফুলের মালায় সৌন্দর্যের বদলে এখন ওর বাবার হৃৎপিণ্ড দেখতে পায়। সে হৃৎপিণ্ড খুবলে খাবার জন্যে ওর বুকে আকণ্ঠ পিপাসা।’’
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে কাহারী সোনাইর মাঝে আশ্রয় নেয় কিন্তু ভালোবাসার কথাও এক সময় বৃশ্চিক দংশন হয়ে ওঠে। তখন পাত্র খোলা চা বাগানে সুভাষ-ঝুমুরির সম্পর্কের কথা মনে পড়ে। সুভাষ গল্পচ্ছলে বিভিন্ন সময় ঝুমুরির সম্পর্কের কথা কাহারীর কাছে প্রকাশ করেছিলো। ঝুমুরি সুভাষের সঙ্গে প্রতারণা করে “একজনের প্রলোভনে পড়ে পেটে বাচ্চা’’ ধরেছিল। তারপর সেই সন্তান পদ্মপুকুর পাড়ে ফেলে দিয়েছিলো।
কাহারী বুঝে বিশাল প্রকৃতি ছাড়া তার কেউ নেই। তবু শাহরিয়ারকে ত্যাগ করতে চায় না ও। চুটিয়া ময়নার জীবন ধারণ নিরীক্ষণ করে ওর “মা অমন ব্যস্ত হয়ে বাসা বানানো ছাড়াই বাচ্চা ফুটিয়েছিলো’’ মা বাবা সুভাষ সোনাই সকলের ওপর ঘৃণা প্রবলতর হয়ে ওঠে। বিক্ষিপ্ত কাহারী শাহরিয়ারকে হাসিয়া পল্লীতে নোংগক্রেম নাচের উৎসবে নিয়ে যায়। পাহাড়ের পাদদেশে প্রকৃতির অপূর্বতায় মুগ্ধ হয়ে শাহরিয়ার গতজীবনের অনুশোচনা ভুলতে চায়:
“চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে সমতল। পাখি ডাকছে অবিরাম। কাছাকাছি কোথাও ঝরনার জল পড়েছে। সে শব্দ ওকে আনমনা করে দেয়। নিজের ওপর মমতা হয় ওর। শামান্তাকে খুন করার পর কতদিন ভেবেছিলো নিজেকে শেষ করে দেবো, এই গ¬ানির বোঝা রয়ে বেড়ানো কষ্ট। এখন ভাবছে, এ জীবনে এত কিছু দেখার আছে, কেন নিজেকে ধ্বংস করবে ? কেন সব দেখে, সব জেনে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলবে না’’ (পৃ. ৫৭)।
শাহরিয়ার আনারস কাটা কাজে নিযুক্ত হয়। অন্যদিকে সোনাই কাহারীকে অবলম্বন করে লাকতে চায়। কিন্তু কাহারীর অশান্ত অস্থির যন্ত্রণা তাকেও স্পর্শ করে, বিহবল করে তোলে:
“কাহারীর মতো আর কাউকে ভালো লাগে না, ওকে ওর সব কিছু উজাড় করে দিতে ইচ্ছ করে, ও না চাইলেও করে’’ (পৃ. ৬০)।
কাহীর কান্না তাকে সজল করে ফেলে ও কাহারীকে আশ্রয় দেয়। অথচ কাহারী ভাবে:
“সোনাই একটা কুত্তী হবে। বাচ্চা ফেলে চলে যাবে অনেক দূরে। সেখানে নতুন করে সংসার পাতবে। সেই সংসারে অনেক ছেলে মেয়ে হবে। তখন ও ভুলে যাবে পথের ধারে ফেলে দেখা প্রথম ছেলেটির কথা’’ (পৃ. ৬৩)।
এই বিশ্বাসহনিতা, সন্দেহ প্রবণতা যেন শাহরিয়ারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে যায়। সে সন্দোহবশত শামান্তাকে খুন করেছিলো অকপটে, তাই প্রকৃতির মাঝে নতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত হলেও শামান্তাকে ভুলতে পারে না। তার এই উন্মুলিত অবস্থা যেন কাহারীর বেজন্মা হবার সমান্তরাল ঘটনায় পরিণত হয়। এ জন্যে একসময় কাহারি সোনাইর স্নিগ্ধ সম্পর্ক ওকে ঈর্ষাপারায়ণ করে তোলে। সে কাহারীর ছবি শেষ করার উৎসাহ হারায়।
কাহারী-সোনাই কাহিনীতে কানাই চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করি। পাত্রখোলা লেকে জ্বরিনে এসে উন্মুলিত কানাই কাহারীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কানাই ঝুমুরীর নাম উচ্চারণ করলে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কের কথা প্রকাশ করলে কাহারী নাটকীয়ভাবে তার জন্ম রহস্যের অজ্ঞাত তথ্য পেয়ে যায়। তহন নির্বিত্ত, নিমূল কাহারী বিভ্রান্ত কিন্তু জাগ্রত চেতনা শাণিত হয়ে ওঠে:
“সুভাষ মেয়েমানুষ এনে ঘর থেকে বের করে দিলে আমি ঘুমানোর জায়গা চাইনি; ঘরে কোনো দিন খাবার না থাকলে আমি খাবার চাইনি; কাপড় না ছেড়ে পর্যন্ত কাপড় কিনিনি। হাতে পয়সা না থাকলে আমি কারো কাছে চেয়ে বিড়ি খাইনি। একটা জিনিসই চেয়েছিলাম, তা ভালোবাসা এবং একটা জিনিসই মাথায় গেঁথে রেখেছি তা খুন। আমি একটা খুন করতে চাই’’ (পূ. ৮৫)।
কানাইকে কাহারী নির্মমআবে খুন করে তার পরিদিনই শাহরিয়ার জুরিন ত্যাগ করে; কারণ তার মনে হয়:
“শামান্তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ও পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। এই জীবনে ওর আর কি-ই বা চাইবার আছে’’। (পৃ. ৮৭)।
শ্রীমঙ্গল ষ্টেশনে বিশ বাইশ বছরের চটপটে তুচেকের সঙ্গে পরিচয় হয় শাহরিয়ারের। লুসাই পাহাড়ের পাদদেশে সাজেক ভ্যালিতে এক শীতের বিকেলে পদার্পণ করে সে। খ্রিষ্টান লুসাইদের গ্রামের চীফের আশ্রয়ের সে অতিথিরূপে আশ্রয় পায় তাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলে। সাজেক ভ্যালি সেলিনা হোসেনের পরিচিত পরিমণ্ডল, এ জন্যে সেহানকার জীবনযাত্রা প্রাকৃতিক
পরিবেশের অপূর্ব চিত্রগুলো উপন্যাসে আবেগের ঝরনা ধারা প্রবাহিত করেছে। কারর তাঁর স্বীকারোক্তি:
“সাজেক ভ্যালির বিস্তৃত কমলালেবুর বাগান হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস পাঠের আনন্দ দিয়েছিলো। পাহাড়ের পাদদেশে ঘর বানিয়ে বাস করা মানুষগুলোর ঘর গেরাস্তি কত শিল্পিত তার নির্মাণ বুঝি আমাদের মতো শহুরে লোকের এক পুরুষে সম্ভব নয়’’ (স্বদেশে পরবাসী, পৃ. ১২)।
এই অপূর্ব পরিবেশে একজন শিল্পী নিজেকে খুঁজে পায়। অতীতের গ¬ানি মুছে যায় মানুষের সহজ সুন্দর হৃদ্যতায়। শাহরিয়ার যে নবজন্মের প্রত্যাশা করেছিলো তা যেনো এই সাজেক ভ্যালিতে এসে পূরণ হয়। তার শিল্পিসত্তার উন্মোচনও একই সঙ্গে উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কমলালেবুর বাগানে রুহিনাকে দেখে তার জীবন পিপাসা উদ্বেলিত হয়।
বাল্যে পিতৃমাতৃহীন নানীর হাতে মানুষ শাহরিয়ার যৌবনে শামান্তাকে খুন করেছে। শাহরিয়ারের গন্তব্যহীন জীবন যেনো নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সাজেক ভ্যালিতে রুহিনাকে বিয়ে করে স্থির হয়। অথচ রুহিনার মৃত্যু তাকে আবার পথে নামায়। এরই মধ্যে হারাধনের কাহিনী পর্বে নাসির ও শাহরিয়ার গোমতীতে মাছ ধরার সময় হারাধন বুড়োর গলিত লাশ দেখতে পায়। একই সঙ্গে নমিতারও। ঔপন্যাসিক এই অংশটি অতি সংক্ষেপে ইজিগতে বর্ণনা করেছেন। শাহরিয়ার যেে অপরাধবোধ লালন করে চিন্নমূল হয়ে ক্রমাগত পরিক্রমণ করেছিলো, তার যেনো সমাপ্তি এসে গেছে। মানুষের নিষ্ঠুরতা-সহৃদয়তা-হিংসা-ক্রোধ সবই সে দেখেছে। অপরাধী শাহরিয়ারের প্রেক্ষণে যেনো ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের সমগ্র অবস্থাকে ধরতে চেয়েছেন।
যে শাহরিয়ার নিজের অপরাধের কথা অন্তরালে রেখে রেণুবালার প্রণয় প্রত্যাশা করে ব্যর্থ হয়েছে, যে শাহরিয়ার রবিন হয়ে রুহিনাকে বিবাহ করেছে সেখানেও প্রতারণার জন্যেই যেনো এ রকম পরিণতি এসেছ। আর কাহারী ও হারাধন, দু’প্রান্তের দুই যন্ত্রণাকাতর মানুষ একজন উৎসমূল খুঁজতে দহনদগ্ধ, অন্যজন অস্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিরুচি বজায় রাখার জন্যে সচেষ্ট হয়ে শেষে ব্যর্থ হয়েছে সমাজের নিষ্ঠুর ক্ষতের কাছে।
শাহরিয়ার ক্লান্ত, ব্যর্থ, ক্লিষ্ট হয়ে সাত বছর পরে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেছে। যে ঢাকা শ্বাসরুদ্ধকর মৃত্যুদণ্ড নিয়ে অপেক্ষমান। সে কি ভালোবাসার জন্যে খুন করেছিলো, না খুন করে ভালোবাসা দেখতে চেয়েছিলো ? শামান্তাকে খুন করার সময় নিশ্চয় তার ভালোবাসা শূন্যের কোঠায় ছিলো নতুবা, সহনশীলতা যে ভালোবাসায় থাকা স্বাভাবিক ছিলো সেখানে কেনো অসহিষ্ণু হয়ে উযেছিলো ? একি ঈর্ষার জ্বলজ্যান্ত রূপ ! যে ঈর্ষা রাধাকান্তের মধ্যে শাহরিয়ার দেখেছিলো মনিপুরিদের সমাজে। কিন্তু শাহরিয়ার ঢাকায় ফিরে। কারণ, “পালাবে কোথায় মানুষকে ফিরে আসতে হয় নিজের বুকের খাঁচায় । প্রতিনিয়ত বন্দী এই জীবটি ক্ষমতার দম্ভে মাতে; আসলে প্রচণ্ড অসহায়, নিজের নীলকণ্ঠ বিবেকের কাছে সূতোয় বাধা
পুতুল। তাই নিজের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়াই সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে নির্মম এবং অসাধ্য’’ (পৃ. ১৭৫)।
কারণ শাহরিয়ার খুনি এবং কাহারীর খুনের দর্শক। কিন্তু ঢাকায় তমিজউদ্দীনের মতো ব্যক্তিরা খুন করে জেল থেকে মুক্ত হয় নেতাদের সহায়তায়। তবে তার কোনো বিবেক নেই কারণ সে মদ খায়, জুয়া খেলে, বেশ্যা বাড়ি যায়। শাহরিয়ার তো শিল্পী, একজন বিবেকবান মানুষ।
ভালোবাসার জন্যে ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে খুন করেছে শামান্তাকে। এ জন্য ফিরে আসতে চেয়েছে সেই বোধের কাছে যেখান থেকে জীবনের শুরু যে প্রবহমানতা মানুষের শুভ।
এই শুভ কামনায় মানবিকতার জন্যেই শাহরিয়ার আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কিন্তু আজন্মের মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে শাহরিয়ার মুক্ত মানুষ হতে পারেনি বলে সেলিনা হোসেন নায়কের পরিণতি জেলে প্রবেশের মধ্যে দিয়ে উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন। এ যেনো ঔপন্যাসিকের আজন্ম মূল্যবোধ থেকে উদ্ভব হয়েছে। ঔপন্যাসিক তাকে সমাজে প্রশ্রয় দেননি কারণ:
“এভাবে সবাই এড়াতে চাইলে তো যার যা খুশি করার অধিকার লাকতো। এমন নৈরাজ্য সমাজ সহ্য করবে কেন ?’’ (পৃ. ২)।
নিজের সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ঔপন্যাসিক। তবে মানবিকতা এই আত্মসমর্পণের পেছনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে শাহরিয়ারের সাত বছরের অভিজ্ঞতার বিবরণ ঘটনা ও অন্যান্য চরিত্রসমূহের সমবায়ে।
সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সেলিনা হোসেন শাহরিয়ারের নির্মূল জীবনের নানা দ্বন্দ্ব জটিল কাহিনীকে উন্মোচন করেছেন “খুন ও ভালোবাসা’’ উপন্যাসে। শাহরিয়ারের চেতনাপ্রবাহের সজেগ বিচিত্র স্থানিক ভূগোল ও প্রকৃতি গীতময়, কাব্যিক, চিত্রল পরিচর্যায় উপন্যাসের অবয়বে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন:
“সামনের খোলা মাঠ হা হা করে। দূরে অন্ধকার, কিছুই স্পষ্ট নয়। আশপাশ তারস্বরে শেয়াল ডাকে, ওর একটুও ভয় করে না। বিড়বিড়িয়ে বলে, আমি আর পালিয়ে থাকতে পারছি না; আমার আত্মসমর্পণ প্রয়োজন, বলতে চাই, আমি এসেছি, তোমরা আমাকে শাস্তি দাও’’ (পৃ. ১৭)।
এই অংশে শাহরিয়ারের শামান্তা হত্যার স্মৃতি স্মরণে এলে যে অপরাধবোধের যন্ত্রণা তাকে প্রকাশ করার জন্যে ‘হা হা মাঠ’ এবং ‘শেয়ালের তারস্বরে’ চিৎকার ব্যবহার পরিচর্যার একটি উলে¬খযোগ্য মাত্রা।
অন্যদিকে সর্দারের জন্যে সাংনুকে মরতে হয়েছিলো আর সেই ভীষণ কণ্ঠের কলা শাহরিয়ার শোনার পর তার ভেতরের কণ্ঠ লুসাই পাহাড় মুছে যাওয়া ও অন্যান্য চিত্রকল্পে প্রকাশিত হয়েছে।
মূলত সেলিনা হোসেন সৎ প্রবত্তির জয় এবং অসৎ প্রবৃত্তির পরাজয় রূপায়ণ করতে গিয়ে সচেতন শিল্প অভিপ্রায়ে শাহরিয়ারের জীবনের সংকট মুহূর্তের চিত্র এঁকেছেন। মানুষে যখন চেতনে এলোমেলো হয়ে ভয়ানক কিছু করে ফেলে তখন তাকে আইনের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। সুস্থ জীবন প্রত্যাশী শাহরিয়ার যেমন চেয়েছিল শামান্তাকে ঘিরে স্বপ্নময় গৃহ, তেমনি তার ঈর্ষা বহ্নি যা এই চরিত্রের অন্যতম দুর্বলতা তা তাকে ক্ষয়িত করেছে। পলে ওলেলোর মতো শাহরিয়ার প্রবৃত্তির কাছে হেরে গেছে কিন্তু মানবিকতায় সহানুভূহতি অর্জন করেছে তার সংবেদনশীল শিল্পিসত্তার জন্যে। চরিত্র রূপায়ণে “খুন ও ভালোবাসা’’ এখানেই সার্থক হয়ে উঠেছে।
নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনে যে অপ্রাপ্তি ও অপূর্ণতাজনিত বিচ্ছিন্নতাবোধ, যন্ত্রণা ও দগ্ধ জীবন লেকে উত্তীর্ণ হতে না পেরে যে পরিস্থিতিজাত শূন্যতা আক্রান্ত মানুষ তার অন্তরে রক্তক্ষরণ ও যন্ত্রণাবোধ থেকে আত্মহননের ও আত্মবিনষ্টির অনিবার্য সত্যে উপনীত হয়, তারই শিল্পরূপ সেলিনা হোসেনের “ক্ষরণ’’ (১৯৮৮)। এখানে “পদশব্দে’’র মতোই ব্যক্তির অন্তর্গত চেতনাস্রোতের রক্তাক্ত পথ পরিক্রমায় উপন্যাসের কাঠমো নির্মিত। ব্যক্তি সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতার সূত্রে যন্ত্রণা অনুভব করে না। নিতান্তই পারিবারিক আবেষ্টনে পারস্পরিক অসম-জোয়ালের ভিত্তি নাগরিক জীবনে যে সন্দেহ-সংশয় ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব তারই দিগন্তহীন কাতরতায় দগ্ধ হয় নিজের বিষাদময় জীবনের পরিবৃত্তে।
এ জন্য কেন্দ্রীয় চরিত্র ইশতিয়াক যার স্ত্রী আধুনিকা ডেজী ও সন্তান রোমেলকে নিয়ে নির্বিঘ্নে জীবননির্বাহের কলা সেখানে তাকে দগ্ধ হতে হয় অতীতের বেদনাময় স্মৃতি রোমস্থনে। বাল্যকালে পিতৃহীন (পিতার মৃত্যু দুর্ঘটনাক্রমে হলেও তার মা পিতার মৃত্যুর জন্য তাকে দায়ী করেছিল) মা’র নিরাসক্ত চোখের দৃষ্টিতে মানুষ ইশতিয়াক আজ নিজের সংসারে ক্রমে রোমেলের মা’র সঙ্গে নিজের মা’র সাদৃশ্য খুঁজে গ্লানি লাঘব করতে চায়। কিন্তু রোমেলের বন্ধু নিশুর মা’র সঙ্গে নিজের মা’র তুলনা করে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত বুভুক্ষ হৃদয়ে কাতরতা প্রকাশ করে:
“… নিশুর মা’কে আমি কোনদিন ভুলব না। তার মৃত্যুর তারিখে কবরে যাবো, মিলাদ পড়াবো। নিশুর মা’কে না দেখলে আমি জানতেই পারতাম না মা কেমন। ভাবতাম মায়েরা বুঝি আমার মায়ের মতো’’ (পৃ. ৯)।
রোমেলের মাতৃধাররায় ও বিশ্বাসে আঙ্গন মরেছে তার মা’র আচরণ থেকেই। এজন্য ইশতিয়াক রোমেলের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে চায়। আর এজন্য নিজের জীবনে তার মা’র স্মৃতি বড় উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে।
“আমি তেইশ বছরের ইশতিয়াক, আঠারো বছর বয়সে মা’র কাছে এক ভয়ানক গল্প শুনেছিলাম। তারপর থেকে জেনেছিলাম আমি মা’র শক্র’’। মা ইশতিয়াককে ক্ষমা করতে পারেনি, কিন্তু সন্তানের মঙ্গলাঙ্ক্ষা তাকে তাড়িত করেছে। দ্বিতীয় বিবাহে অস¤মত হয়েছেন এবং নির্বিকারচিত্তে সন্তান পালনের দায়িত্ব বহন করে গেছেন। কিন্তু ইশতিয়াককে হৃদয় খুঁড়ে বেদনার দীর্ঘশ্বাসকে জাগরুক রাখতে হলো। কারণ- “আমি আর মা’র মুখের দিকে
তাকাবার সাহস পাই না। বাবার মৃত্যুর সমস্ত দায়ভার এভাবে এভাবে কাঁধে নিতে হবে ভাবিনি। দৌড়ে নিজের ঘরে আসি। সারারাত আমার কান্নার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যায়। কেবলই মনে হয় মাথার ভেতর বিষ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। আমি চিৎকার করছি। কোনো কিছুতেই আমার চিৎকার লামছে না। সেদিন মুহূর্তের মধ্যে মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তারপর ভোজালির পেঁচের সঙ্গে সে বন্ধন শিথিল হয়ে যায় সেটা আর কোনো দিনই আন্তরিক হয় না’’ (পৃ. ২৩)।
গৃহে মা’র সংস্পর্শ বিষণ্ণতায় নিমগ্ন করলে সে বন্ধুদের সাহচর্যে উৎফুল¬ হতে চায়। এজন্য টিটুলের প্রেমিকা রুপু সম্পর্কে তার অভিব্যক্তি:
“কিন্তু রুপুকে আমার ভালো লাগে, ওর সঙ্গ পেলে বর্তে যাই। অবশ্য ভালোবাসি কি না বুঝতে পারি না।’’
কিন্তু রুপু’র তো ঘর আছে। তাকে সেখানে ফিরতে হয়। ইশতিয়াকের ঘর আছে অথচ “সাদা রঙের দু’কামরার বাড়িটা যে নিঃসঙ্গ’’ কিন্তু বাড়ি ফিরতে হয়। মা’র আদেশ অর্পিত হয় “বন্ধুদের সঙ্গে বেশি আড্ডা চলবে না।’’ শীতল অনুভূতি নিয়ে ইশতিয়াক তখন শিল্পী টিটুলের রঙতুলির বিশৃঙ্খল জীবনের প্রতি অনুরক্ত হতে চায়। তথচ সামাজিক বন্ধন অতি পোক্ত। মামা সেখানে বিবাহ প্রস্তাব পেশ করে। মা প্রত্যাখান করেন। ইশতিয়াকের মাকে ভীষণ স্বার্থপর, হিংসুটে এবং ভয়াবহ মনে হলো। “কিন্তু বাবা মারা যাবার পর তোমাকে নিয়ে আমার কষ্ট করতে হয়েছে’’ এ কথায় কান্না গলিয়ে ওঠে তাই বন্ধু টিটুলকে বলে: “আমার জীবনে একটা গল্প আছে টিটুল। সেই গ্লানি আমাকে প্রতি মুহূর্তে রক্তাক্ত করে।’’
ইশতিয়াকের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকাতর জীবনের বিপরিতে নিস্তরঙ্গ রুপু-টিটুলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও জীবন অন্বেষণ রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে লেখক দুই বিপরীত পরিস্থিতিতে ব্যক্তির জীবনাকাক্সক্ষাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।
ইশতিয়াক জীবন অনুসন্ধানে দেখতে পায় রুপুর কাছে প্রেমাকাঙ্ক্ষা কতটা শূন্যতার সামিল। কারণ, রুপুতো টিটুলের প্রতি সমর্পিত। বিশ্বাসের পাথরে ধস নেমেছে। এজন্য মা’র মুখোমুখি হয় ভয়শূন্য হয়ে। কারর, হয় তাকে মা’র গোয়ার্তুমি ক্ষমা করতে হবে নতুবা মাকে হত্যা করতে হবে। শেষে সে ক্ষমাশীল হতে চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে টিটুল স্কলারশিপ নিয়ে গ্রীসে চলে গেল। আর রুপু অন্য একজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো। ইশতিয়াকের মনোজগতে অনিকেত সংকেত প্রবাহিত হয়:
“আমি কোথা যাবো ? আমার সেই শীতার্ত গুহায় ? যে গুহা এক মহিলার জেদ আর প্রতিশোধের ভয়ানক আকোশে হিম’’ (পৃ. ৫৪)।
শূন্যতায় মুহ্যমান ইশতিয়াক কিন্তু আশাহত হয় না:
“এখনো আমার জন্য কেউ আছে, নিশ্চয় কেউ না কেউ আছে, তাকে আমি দেখিনি সেও আমাকে না, তবু আমার জন্য সে আছে। মুযি ভরা মহুয়া নিয়ে আমি পায়চারি করি। এখন আমার কিছুই খারাপ লাগছে না’’ (পৃ. ৫৫)।
ইশতিয়াক নিজের পথ অন্বেষণ করে নেয়। পরীক্ষায় পাস করে লাহোরে ট্রেনিং-এর সময় ডেজীর সঙ্গে পরিচয়সূত্রে ঘনিষ্ঠতা ও বিবাহ। কিন্তু তাতেও কি নাগরিক জীবনে সমস্ত প্রাপ্তির পূর্ণতা আসে ? প্রশ্নদীর্ণ হয়ে সে বলে:
“আমাদের ওড়া শেষ-আমরা মাটিতে নেমেছি। সে জন্য দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে, কেউ কারো কাছে পৌঁছুতে পারছি না। তাই আর একটি ভাজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের পুরোটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এখন ভাঙনে আর ভয় পাই না’’।
ভাঙন থেকে স্ত্রী-স্বামী সম্পর্কের যে সংকট তার মধ্যবিন্দু স্পর্শ করে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে একটি অনুকাহিনীর মধ্যদিয়ে। যা রোমেলের মানসিক বিন্যশের প্রান্ত স্পর্শ করার জন্য উপন্যাসে প্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে।
রোমেলের বন্মুনিশু খুন করেছে অলোককে। কারণ বন্মু অলোকের বোন পিংকিকে নিশু ভালোবাসত কিন্তু অলোক সে সম্পর্ক অস্বীকার করে খুলনায় চাচার বাড়ি পাযিয়ে পিংকিকে ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিবাহ দেবার দিন সাতেকের মধ্যে খুন হতে হয় তাকে। এরপর নিশু আত্মরক্ষার জন্য প্রথমে বড় আপার ননদ নীলার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করে “চারদিনে ক্লান্ত, বীতশ্রদ্ধ এবং বিধ্বস্ত’’ হয়ে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনাটি লেখক নিশুর একটি গল্প যা রোমেলকে পাঠিয়েছিল তার ভেতর দিয়ে উদঘাটন করেছেন। নিশুর সবুজ জীবনের প্রতি তৃষ্ণা এবং মা’র প্রতি আলোবাসা ইশতিয়াকের বাল্যযৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইশতিয়াক জেদি মা’র জন্য করুণাবোধ করেছে ভালোবাসতে পারেনি, কিন্তু নিশু বিধবা মা’র জন্য প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করেছে।
নিশুর জীবনের নৈরাশ্য রোমেলকে আত্মখননে অনুপ্রাণিত করে। মা-বাবার সম্পর্ক যেহানে গভীর শূন্যতাময়; যেখানে বাবা অসহায়, ছেলের প্রতি সচেতন কেউ নেই গৃহে, সেখানে রোমেল ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সুস্থ জীবন থেকে। অসুস্থ প্রবৃত্তি তাকে নিঃশেষ জীবনের পথে নিয়ে যায়।
স্ত্রী ডেজীর পারিবারিক সংশ্রম ত্যাগ ও ইশতিয়াকের বন্মু রহমানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং রোমেলের নেশাসক্ত পথে আত্মবিনাশ প্রচেষ্টা যুগপৎ ইশতিয়াককে দুর্দান্ত অসহায় ও অস্থির করে তোলে। জীবনের জটিল সমস্যার আস্তরণকে আরো মোটা দাগে নির্মাণের জন্য লেখক তাদের পাশের বাসায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমজেদ-মেহেরে সুখের জীবন প্রণালী উন্মোচন করে সমান্তরালভাবে বিশে¬ষণ করার চেষ্টা করেছেন আধুনিক মানুষের অপ্রাপ্তিজনিত হাহাকারের মর্মান্তিক রূপটিকে।
“ভালোবেসে বিয়ে করার পরও ডেজী ওর মনের মতো হয়নি।’’ অফিস কামায় করে ইশতিয়াক সংসারের অন্তহনি সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। রোমেলকে বন্ধু করার
জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু সে জানে : “এই সংসারে তিনজন মানুষ একদম একা, কারো সঙ্গে কারো কোনো যোগাযোগ নেই।’’ রোমেলকে নেশা করে ফিরতে দেখে ইশতিয়াক তার প্রতিবাদ করে কিন্তু রোমেলের কাছ থেকে “আমি এসবের মধ্যে বাঁচতে শিখেছি’’ শুনে বিস্ময়াভূত হয়ে যায়। –“ইশতিয়াকের মনে হয় বাবার ওপর ওর দীর্ঘদিনের রাগ। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রোমেল কতকাল ধরে হৃদয়ের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবোধে ভুগছে ? হায় ঈশ্বর এই ছোট ছাদের নীচে কত কি যে ঘটে যায়। ইশতিয়াক ছেলের রাগে নিজের মধ্যে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে। কিছুটা রূঢ়কণ্ঠে ছেলেকে শাসন করে’’ (পৃ. ৯৪)। কিন্তু রোমেলের কণ্ঠ “তুমি আমাকে কিছুতেই ফেরাতে পারবে না কিছুতেই না।’’ পিতৃত্বের পরাজয় ও পারস্পরিক সম্পর্কের নগ্নতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।
ক্লান্ত হতাশ জীবন টেনে যাওয়ার কোন সদর্থক দিক নেই। এজন্য মেহের-সমজেদের ক্লান্তিহীন সুখের জীবনের সঙ্গে নিজের সংসারের তুলনা করে ডেজীর স্বার্থপরতাকে দায়ী করেছে ইশতিয়াক। ইশতিয়াকের অতীত জীবনের চলনবিলে বালিহাঁস শিকারের ঘটনা নিঃসঙ্গ, শূন্যগৃহে স্মৃতিপটে এনে ভয়ানক পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করে।
“বউ ঘরে নেই, ছেলে পালিয়ে গেছে, মাসুদকে ডাকলে সাড়া দেবেনা; ওর হাতে দোনলা বন্দুক, ও শুধু ট্রিগার টেপার অপেক্ষায় আছে। সাঁই করে ছুটে আসবে বুলেট। রক্তাক্ত বালিহাঁস ও নিজে’’ (পৃ. ১০৯)।
বন্দুকের গুলি যে কাকে বিদ্ধ করবে তা লেখকের অগোচর। কারণ ইশতিয়াকের মানসিক পরিস্থিতি এখনও পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা রাখে। অন্যদিকে এখনও তাদের অনেক ঘটনাই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এ জন্য ঔপন্যাসিক রোমেলের লিখিত ডায়েরীর আঠারোটি অনুচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশগুলো পাঠক ইশতিয়াকের প্রতিক্রিয়াসহ তুলে ধরেছেন। ডায়েরী তার গ¬ানি বিষাদ এবং অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। অন্ধকার খুঁড়ে খুঁড়ে অগ্রসর কি আলোকিত ভোরের জন্যে নাকি বিনাশের গহ্বরে প্রবেশের জন্যে ? এজন্য হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়া এবং সামনের ফ্ল্যাটে বন্দুক তাক করা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে না।
ইশতিয়াক যন্ত্রণা লাঘব করার জন্যে প্রাচীন সুখের নীড় চূর্ণ করে। এখন থাকল নিজের অবস্থান। সেটাও এতদিনে ধে গেছে। অতএব জীবিত থাকা নিরর্থক। তাই আত্মহত্যা করতে হয় তাকে। কিন্তু রোমেল ? কি করবে তৃতীয় প্রজন্মের এই সন্তান দীন মোহা¤মদের দোকানে নেশা করতে গিয়েছে কারণ, সে তো জানে:
বাবা তবু আমাকে চড় মারে। সেটা আমার জন্য সান্ত্বনা। আমি দুঃখ পাই না। মা’র কাছ থেকে আমার কিছু পাওয়া নেই, আমার ঘর নেই, আমার শিক্ষা নেই, নিশ্চয়তা নেই।’’
অস্তিত্বের এই বিপন্ন অবস্থায় তার জীবনে কেউ থাকল না। তারও মৃত্যু হলো একপ্রকারে। এভাবে মৃত্যু ধ্বংসের ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক জীবন বিচ্যুতগ্রহের বাসিন্দাদের কাহিনী সমাপ্ত হয়।
আত্মকথন ও চেতনাপ্রবাহের প্রাধান্যে উপন্যাসের অবয়ব সংস্থান সংগঠিত হয়েছে সরল প¬টে। এ ক্ষেত্রে ঘটনার জটিলতা নয়, চরিত্রের অন্তর্জগতের সংকট সমস্যা উন্মোচনই মূল বিবেচ্য বিষয়। এজন্য সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ কখনও ইশতিয়াক, রোমেল এবং নিশুর দৃষ্টিকোণে পরিবৃত্ত হয়ে উঠেছে। ইশতিয়াকের মনস্তত্ত্ব বিশে¬ষণের জন্য যাবতীয় ঘটনার বিন্যাস এবং অন্যান্য চরিত্রের অন্তর্নিহিত সংকট উন্মোচনে লেখকের প্রচেষ্টা পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বর্ণনামূলক ও বিশে¬ষণধর্মী পরিচর্যা প্রাধান্য পেলেও কখনও কখনও চরিত্রের আত্মস্বরূপ উন্মোচনে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যময় পরিচর্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন নিম্নোক্ত অংশে চরিত্রের অবচেতনের বিক্ষোভ উদঘাটনের প্রতীকী পরিচর্যায় দৃশ্যময় ব্যঞ্জনা:
“চাঁদ হেলে গিয়ে মহুয়া গাছের আড়ালে পড়েছে, ঘরে আলো আঁধারী। আমি বিছানায় আছি। বিশাল একটা মাকড়সা দেয়াল জুড়ে পা ছড়িয়ে আছে। ভীষণ নির্জনতা আমার চারপাশে। সে মুহূর্তে আমার মনে হয় মা’র সঙ্গে এহন আমার ইঁদুর-বেড়াল খেলা। মা এক অতিকায় বেড়াল; আমি নেংটি ইঁদুর। মা’র ভয়ে প্রাণপরে দৌড়াচ্ছি; মা ইচ্ছে করলে খপ করে আমাকে ধরে ফেলতে পারেন। কিন্তু ধরছেন না এবং মারছেন না। কেবল আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।’’
মূলত সেলিনা হোসেন নাগরিক জীবনের নানাবিধ সংকটকে ব্যক্তির বহুমাত্রিক চেতনার সংস্পর্শে দৃশ্যমান করতে চেয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তি তো শুধু গণ্ডিবদ্ধ পরিবারের সংকটের চূড়ান্তসীমায় এভাবে ক্ষয়ে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সচেতন শিক্ষিত নাগরিক জীবনযন্ত্রণার মূলে থাকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাস্রোত। লেখক সযত্নে তা থেকে দূরে সরে নির্জলা মনস্তাত্তিকমূলক উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। তবে লেখক সংহত বিবরণ ও একঘেঁয়েমী কাহিনীসূত্র সংগ্রথিত না করে নাগরিক বৃত্তের জীবনদগ্ধ উপন্যাস উপহার দিতে পেরেছেন বলে আমার বিশ্বাস।
সহায়ক গ্রন্থ:
১ সেলিনা হোসেন, ‘পদশব্দ’, ১৩৯০, চট্টগ্রাম, বইঘর।
২ সেলিনা হোসেন, ‘মগ্নচৈতন্যে শিস’, ১৯৭৯, প্র. সমিক প্রকাশনী, ঢাকা।
৩ সেলিনা হোসেন, ‘ক্ষরণ’, ১৯৮৮, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা।
৪ সেলিনা হোসেন, ‘খুন ও ভালোবাসা’, ১৯৯০, সৃজন প্রকাশনী।