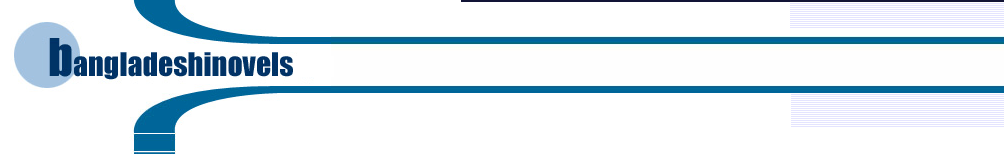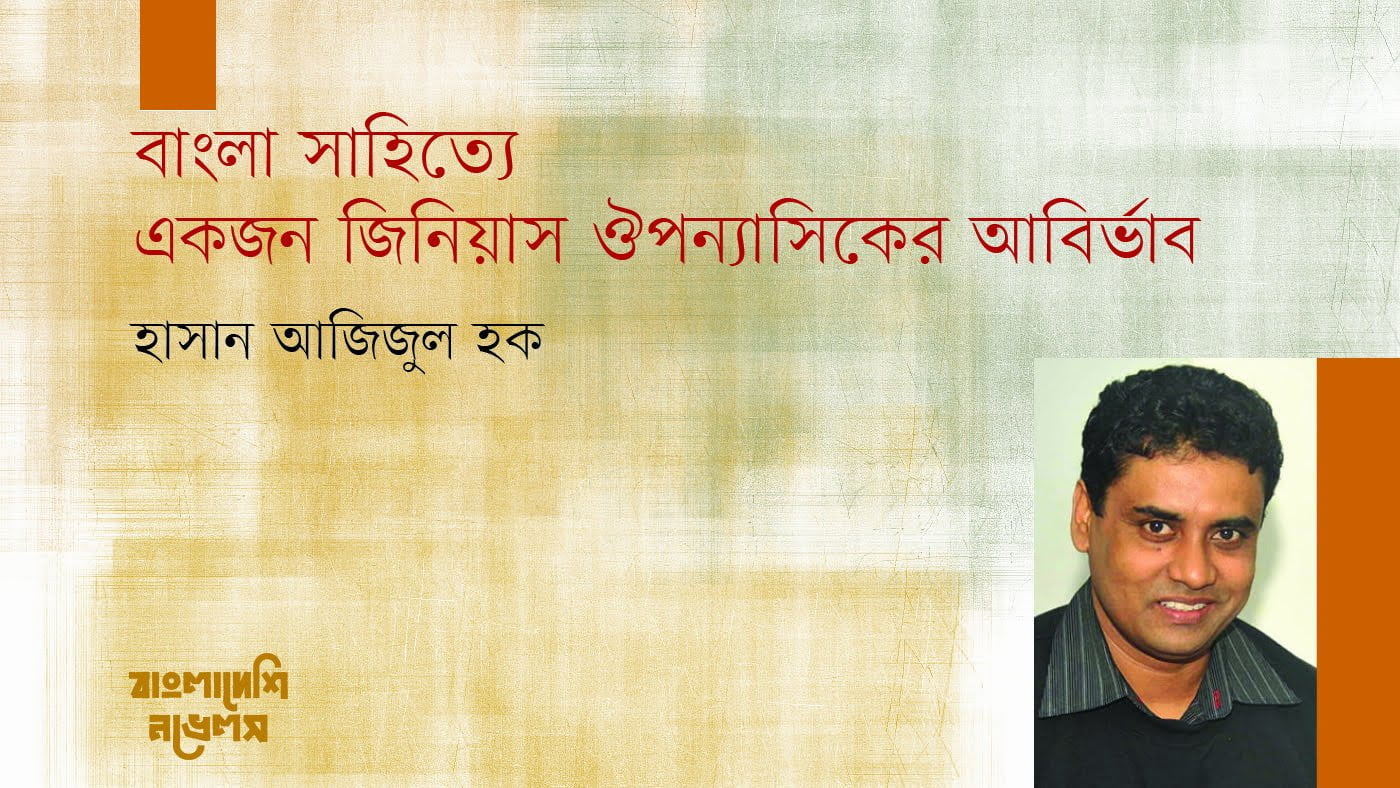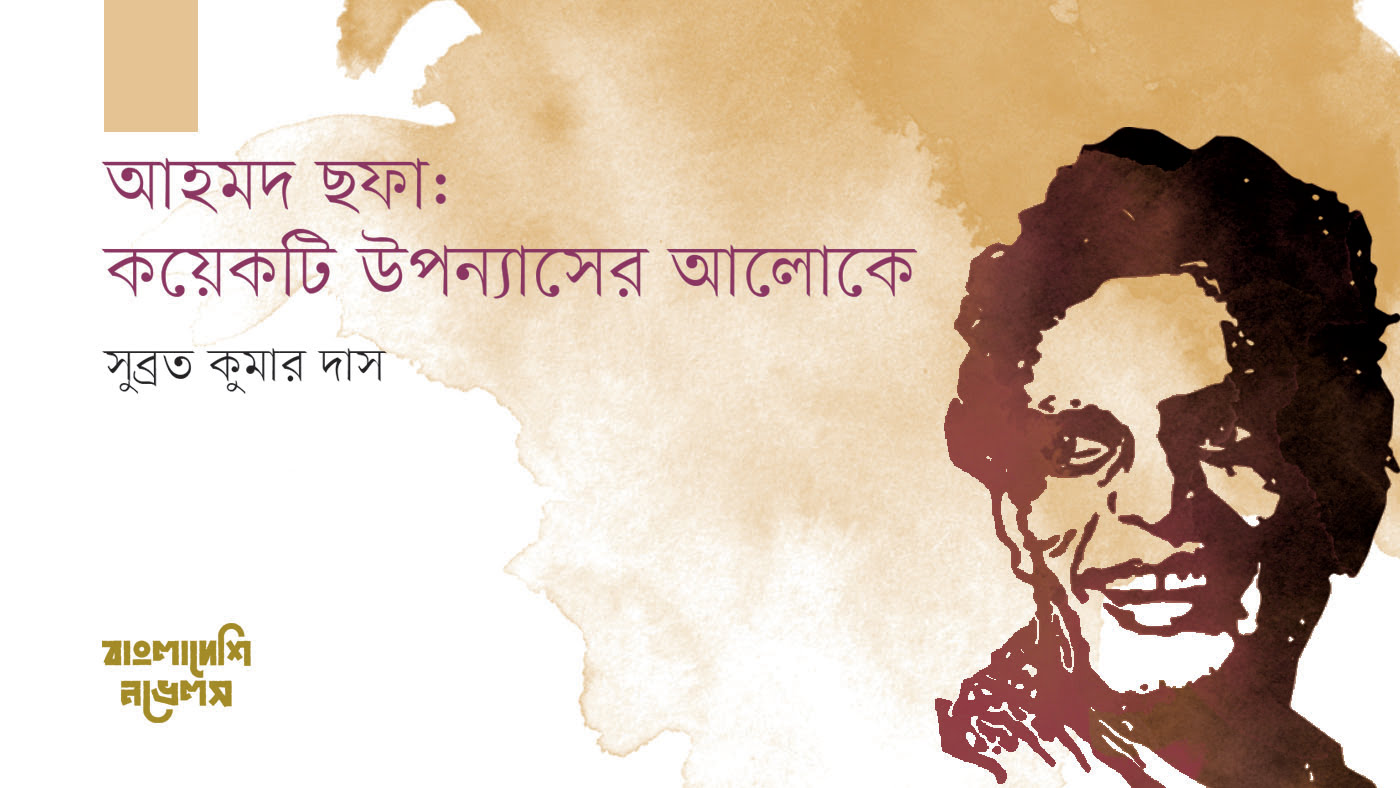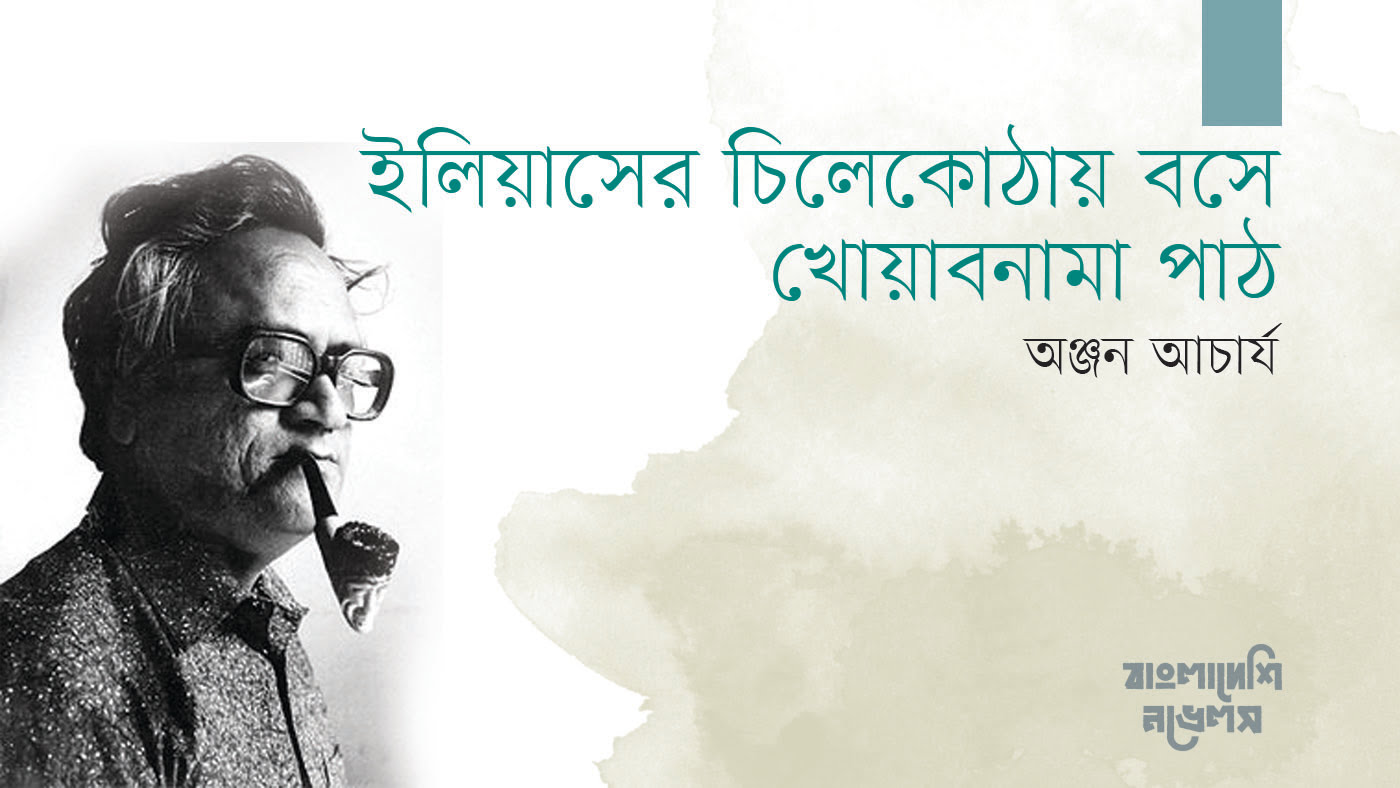বাংলা উপন্যাস রচনা শুরুর প্রায় এক শতক পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র(১৯২২-১৯৭১) ‘লালসালু’-র প্রকাশ; যদিও সামান্য পরিচিতিটুকুর জন্য এর লেখককে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬০) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর তাঁর উপন্যাসের মূল্যায়ন শুরু হয়েছে তিনি লোকান্তরিত হওয়ার পর যা এখনও প্রয়োজনীয় মাত্রায় পৌঁছায় নি। এ অনুযঙ্গে কবি জীবনান্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) সাথে ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ্-র একটি সাযুজ্য সহজেই চোখে পড়ে; আর তা হল তাঁরা দুজনেই মৃত্যু পরবর্তীকালেই যেন পাঠক-সমালোচক কর্তৃক বেশি করে পঠিত ও মূল্যায়িত। সময়ের অগ্রবর্তী লেখককে হয়তো এমন করেই অনাগত প্রজন্মেও পাঠকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। বাংলাদেশের উপন্যাসের পটভূমিকায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাসের মূল্যায়ন গত কয়েক দশক ধরে চললেও তা ক্রমশ সে বৃত্তের পরিধিকে অতিক্রম করে চলেছে এবং এমন ভাবনাও অনেক সমালোচক করে থাকে যে সামগ্রিক বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে ‘অন্যতম প্রধান’ অভিধাটি তাঁর মুকুটে সংযোজিত হতে খুব বেশি দেরি নেই। তাঁর উপন্যাস নিয়ে এমন সব উচ্চ ধারণার উৎস বোধ করি ঔপন্যাসিকের বর্ণনার কৌশল ও ইঙ্গিতদানের মধ্যে নিহিত। অভিনব এবং সপ্রযুক্ত সে পদ্ধতির কারণেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র উপন্যাস পুনঃপাঠের পরও পাঠ দাবি করে থাকে। এবং উল্লেখ্য যে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ (১৯৪৮) থেকেই তিনি পরিক্রমাটি শুরু করেছেন যা দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপন্যাস ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪) বা ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮)-তে নতুন বিন্যাসে উপস্থাপিত।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র সমসাময়িক যে সকল বাঙালি লেখক মুসলিম সমাজের ধর্মান্ধতা অথবা ধর্মব্যবসায়ী ও আচারসর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থাটিকে চিত্রায়ণে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের তালিকায় আরও রয়েছে শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) এবং আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) এবং ঘটনাচক্রটি এমন যে তাঁরা সবাই বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রথম পর্বের কথাকার। ‘লালসালু’-ও সমকালে রচিত এই দুই লেখকের উপন্যাস ‘জননী’ (১৯৬১) এবং ‘সূর্য-দীঘল বাড়ি’ (১৯৫৫)-তেও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মব্যবসায়ীদের কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র ভিন্নতা এই যে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস দুটিতেও এ অবস্থান থেকে সরেন নি। ‘লালুসালু’-তে মজিদ ও তার মিথ্যা আবিষ্কার মোদাচ্ছের পীরের মাজার এবং স্ব-উদ্ভাবিত ধর্মীয় বাণীর পর ‘চাঁদের অমাবস্যা’-তে কাদের এবং তার বড় ভাই দাদাসাহেবের চিন্তা ও কার্যেও ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক সে সফলতাতেই পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। আর ‘কাঁদো নদী কাঁদো’-ও ‘কুমুর ডাঙায় ধর্মের তৎপরতা নেই। তবে সেখানে মুহাম্মদ মুস্তফা আছে, যার মায়ের নাম আমেনা, বাগদত্তার নাম খোদেজা, পিতা যার খেদমতুল্লাহ। মুস্তফা এ যুগের প্রেরিত পুরুষ যেন, এ যুগে আবদ্ধ পূর্ববংগের মুহাম্মদ মুস্তফা বিদ্রোহ করে না, নতুন ধর্মমত প্রচার করে না, নীরবে আত্মহত্যা করে।’ 1 শুধু কি তাই। খোদেজার মৃত্যুর কারণে অন্তর্যাতনায় দগ্ধ মুহাম্মদ মুস্তফা যখন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তখনই কলিজাটির কথা অপ্রত্যাশিতভাবে তার মনে হয়েছিল। সে ‘বহুদিন আগে গ্রামের একটি মেয়েলোকের কাছে কলিজাটির কথা প্রথম শুনেছিলো। মেয়েলোকটি বলতো, খোদা কলিজার মত দেখতে, কলিজার মতই অবিরত থরথর করে কাঁপে’ (পৃ. ৩৪২)। সন্দেহ নেই প্রতীকীভাবে হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অনেকখানিক এগিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে তিন দশক পরও আমরা পৌঁছতে পারি নি।
ধর্মীয় সংস্কারের উন্মোচন তাঁর উপন্যাসের একটি মাত্রা যাতে তিনি ক্রমান্বয়ে অধিকতর শিল্পীত উপস্থাপনার আশ্রয় নিয়েছেন। বিষয়গত প্রশ্নে তাঁর উপন্যাস ত্রয়ের দ্বিতীয় অনুযঙ্গ হলো চরিত্রের অন্তর্গত প্রবহমান চিন্তাস্রোত। ‘লালসালু’-র মজিদের দ্বন্দ্বপূর্ণ গোপন সে ভাবনাস্রোতই উপন্যাসটিকে যেন পাঠকপ্রীতির স্তরে উন্নীত করে; যেমনিভাবে ‘চাঁদের অমাবস্যা’-র আরেফ আলী বা ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র মুহাম্মদ মুস্তফা। তবে অতি আবশ্যক উল্লেখ-প্রসঙ্গ হলো ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় এ ব্যাপারটিতেও ক্রমউত্তোরণশীল। সূক্ষাতিসূক্ষ্মতার অনুসন্ধান তিনি করেছেন যেমন ভাষা ও উপস্থাপনার কারুকাজে তেমনি মানব-মনের গহীনেও। আর সেসবের প্রতিস্থাপন ঘটেছে অব্যবহৃতপূর্ব নিরীক্ষাধর্মী কিন্তু শক্তিশালী এক শৈলীতে।
অনুসন্ধানটি ‘লালসালু’ থেকে শুরু করা উচিত। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মজিদ নামে ধর্মব্যবসায়ী কেন্দ্রীয় চরিত্রটির জন্মস্থানের বিবরণ দিয়ে। এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ‘বিবরণ’ অর্থ যে বর্ণনামাত্র নয় তা তীক্ষ্মধী পাঠকের অজানা নয়। প্রতিটি বাক্য, এমনকি শব্দও বটে, প্রযুক্ত হয় হিসেব নিকেসের পর যা পাঠককে নতুনতর বোধনে নিয়ে যায় পুনঃপুনঃ পাঠে। মজিদেও সেই জন্মস্থানের বিবরণ দিয়ে শুরু উপন্যাসটির প্রথম শব্দ বন্ধটি হলো ‘শস্যহীন জনবহুল’ যা প্রথম ছোট্ট পরিচ্ছেদটিতে পৌনঃপুনিকভাববে ব্যবহৃত। সে জনপদটির যে চিত্র এ পরিচ্ছেদটিতে উপস্থাপিত তা যে কোন পাঠককে ভাবায়, বোধন ঘটে পাঠকের রোমন্থনে; কেননা বাংলার চিরকালীন চিত্র তো এমনটিই। অথচ সে দারিদ্রের ভেতরও সাধারণ জনমানুষের যে ধর্মপ্রীতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র চোখে তা পরিহার্য নয়। বর্ণনাটিকে মনোজ্ঞ করার জন্যই সেখানে হাস্যরসের প্রাচুর্যও অনেক। যে অঞ্চলের মানুষ রুটিরুজির সন্ধানে অঞ্চল ছাড়ার জন্য অধীর ও উন্মুত্ত তাদেরকে বর্ণনায় লেখকের হাস্যরসাত্মক বাক্যরাশি এমন:
১. কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারো-বা আসল জিনিসটা অর্থাৎ বদনটা-যা না হলে বিদেশে এক পা চলে- কি করে আলগোছে হারিয়ে যায়।
২. অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত।
অথচ এমন সব হাস্য উদ্রেককারী বাক্যাবলির ভেতর দিয়ে বেড়িয়ে আসে সমাজ ও ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক শব্দ বা বাক্যরাশি, যেমন:
১. শস্যের চয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।
২. ভোর বেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে মনে হয় এটা খোদাতা’লার বিশেষ দেশ।
৩. কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যা লেখা তা কোন এক বিগত যুগের চড়ায় পড়ে আটকে গেছে।
অথচ সে দেশটাতে বিরান। সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদী গহ্বরেও জমি কম নেই। দেশে শস্য নেই। নিরন্তর টানাটানি। কেমন মরার দেশ। সেখানে খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মাত্র তিন পৃষ্ঠার ভূমিকা-পরিচ্ছেদে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কৃত এতসব সন্ন্যস্ত অনুযঙ্গ। আবার আর প্রায় এক পৃষ্ঠা রূপে রয়েছে সেই বুটপরা বিদেশি পোশাকের নব্যশিক্ষিত মুসলমান শিকারির কথা। তবে শিকারির নাম শুনে মৌলবীর চোখ যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার পেছনের কারণটি কি এই যে শিকারিও মৌলবীর স্ব-ধর্মের – এমন স্বচ্ছল একজন মুসলমানকে দেখেই কি মজিদের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল নতুন জীবনের, স্বপ্ন দেখেছিল সে – তা সে যে উপায়েই হোক। এভাবেই লালসালু-তে ইঙ্গিতময়তার অনুসন্ধান করা চলে যা উপন্যাসটির শিল্পভাতির মূল রহস্য।
‘কিন্তু তাঁর ভাষা আরো আধুনিক ও আরো ভালো হওয়া সম্ভব ছিলো।’ 2 – এমন মন্তব্য তাঁরই সমসাময়িকের। মন্তব্যকারীর প্রতি সম্মান রেখেই বলা যায় ভাষার আধুনিকত্ব বা ভালোত্ব কত বিপ্রতীপ একটি ব্যাপার। অনুপুঙ্খ পাঠে স্পষ্ট হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কাহিনী বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন শিষ্ট চলিত, মজিদের বুলিতে ব্যবহার করেছেন বৃত্তিক ভাষা ‘ মোল্লাবুলি’, অন্যদিকে অন্যান্য চরিত্রের সংলাপে প্রবিষ্ট হয়েছে আঞ্চলিক বা ঔপভাষিক ভাষা।’ 3 প্রথম উপন্যাস থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র যে কাহিনী-বয়ানের প্রচলের বাইরে থেকেছেন তা কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় না। আর সে কারণেই ইংরেজি সাহিত্যেও প্রাজ্ঞ অধ্যাপক, বাংলা কথাসাহিত্যেও অনুসন্ধানী সমালোচক আলী আনোয়ার বলেন, ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র লালাসালুতে কিন্তু ভাষা মোটেই সরল নয়, বরং তা’ বিদগ্ধ, জটিল অথচ দ্যুতিময়। পরতে পরতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র এক জটিল ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন।’ 4 ভিন্ন ভিন্ন তিন রকমের ভাষা ব্যবহার করে, নতুনতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির মাধ্যমে এভাবেই ‘লালসালু’-ও লেখকের অভিযাত্রা। প্রথম উপন্যাসে যেমন মুসলমান সমাজ চিত্রণ, ধর্ম-সংস্কারে আঘাত, মনুষ্য-মন বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়তেও তাই। পার্থক্য শুধু মাত্রাগত। বিশ বছরে মাত্র তিনটি বাংলা উপন্যাস – অন্তর্গত প্রস্তুতি যে যজ্ঞমত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।
তর্কাতীত যে, লালুসালু থেকে অন্য দুটি উপন্যাস প্লট-প্রশ্নে অসরল। ‘লালসালু’তে প্রথম পরিচ্ছেদেও কার্যকারণ অনুধাবনে পাঠকের মনে দ্বান্দ্বিক একটি অবস্থার তৈরি হলেও, পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে গল্পের অগ্রসরণে বিশেষ জটিলতার মুখোমুখি পাঠককে পড়তে হয় না; যদিও তার অর্থ এই নয় যে এটি তরল গল্প কাঠামোর একটি উপন্যাস। বরং বলা যেতে পারে যে, লালসালুতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে কোন গল্পই বলতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন গ্রামীণ বাংলার মুসলমান সমাজটিকে চিত্র দিতে, সে সমাজের রন্ধ্রে ধর্মীয় সংস্কারের চিত্রকে উন্মোচন করতে এবং সর্বোপরি সে সমাজের মানুষের মননকে ধারণ করতে। মজিদ-রহিমা-জমিলার যে গল্প তা আসলে সে লক্ষ্য অর্জনে সামান্য অবলম্বন বৈ কিছু নয়। যদিও পরবর্তী উপন্যাস চাঁদের অমাবস্যাতে আয়তনিক পরিণাহ বাড়লেও এতে গল্পটি হ্রস্ব হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। সরলরৈখিক গল্প কাঠামোর বাইরের উপন্যাস পাঠে অভ্যস্থ না হওয়াই এমন ভাবনার পেছনের কারণ। সে কারণেই শিবনারায়ণ রায় লিখেছিলেন: ‘কৌতুহলী হয়ে যাকেই প্রশ্ন করি তিনি বলেন ‘চাঁদের অমাবস্যা’ একটি দুর্বোধ্য উপন্যাস, এটির লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ প্রবাসী হওয়ার ফলে দেশের বাস্তব অবস্থা বিষয়ে অজ্ঞ এবং অনবহিত, তাঁর অনাশ্রয় কল্পনা তৎকালীন পশ্চিমী সাহিত্যের অনুচিকীর্ষু।’ 5
‘চাঁদের অমাবস্যা’ বুঝতে শিবনারায়ণ রায়ের নিজের ভুল না হলেও বয়স-বিচারে তাঁর সমসাময়িক পাঠকদের চাঁদের অমাবস্যা বিষয়ে যে মন্তব্য তা গুরুত্ববহ। ঘটনার ঘনঘটা দেখতে অভ্যস্ত বাঙালি পাঠক ‘চাঁদের অমাবস্যা’-র প্রথম পরিচ্ছেদে যেন কোন গল্পের সূত্রই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যদিও একথা এখন সবাই মানেন যে, তরুণ প্রজন্ম খুব সহজেই এই উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদেই একটি শক্তিশালী গল্প কাঠামোর উপস্থিতি টের পেয়ে যায় যা একই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনন্যসাধারণ কুশলতায় বিবর্ধিত। এমন পরিমিত গদ্যে এত বিপুল ভাবনারাশির উথালপাথাল বাংলা ভাষায় রচিত আর কোন গল্প-উপন্যাসে হয়েছে কি? মাঝি বৌ ও কাদের প্রসঙ্গটি ঔপন্যাসিক পৌনঃপুনিকভাবে যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর সামনে উপস্থাপন করেছেন যা একান্তই মানবোচিত। কেননা মানব মন তো জটিল সমস্যার ব্যবচ্ছেদই আগ্রহী। আর সে কারণেই লেখক পঞ্চম অধ্যায়ে সে ঘটনাটির বিশ্লেষণ করেছেন আরেফ আলীর দৃষ্টিকোণ থেকে। এই যে পুনরাবৃত্তি তা কিন্তু কোনক্রমেই হুবহু নয়। শৈল্পিক দক্ষতার আঁচড়ে ওয়ালীউল্লাহ্ পুনঃপুনঃ স্থাপিত সে বর্ণনায় অভিযোজন ঘটিয়েছেন নতুন ইঙ্গিতের যা সৃষ্টি করেছে অপূর্বপঠিত এক একটি টেক্সট।
ভণ্ড দরবেশ কাদের যে মাঝি বৌকে গলা টিতে হত্যা করলো তার প্রত্যক্ষদর্শী আরেফ আলী যে কিনা একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষক এবং ঐ কাদেরের বাড়িতে আশ্রিত হলেও সে সত্য প্রকাশে অদম্য। এবং ধর্মগৃধু বাঙালি সমাজে যেমন অমোঘ পরিণতি স্বাভাবিক তেমনটিই ঘটেছে গল্পে: ঐ হত্যার দায় এসে পড়েছে আরেফ আলীর উপর। এত বেশি সমাজ-ঘনিষ্ঠ একটি কাহিনী কীভাবে যে পাঠক কর্তৃক প্রকাশপর অনাদৃত হয়েছিল তা বুঝতে ঐ বুনন-কৌশলের কাছেই আমাদের আবার ফিরতে হয়। প্রথম অধ্যায় দুটি আলাদা অলাদা পরিচ্ছেদে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রিক দুটি বিবরণ পাঠ করেই বর্তমান পাঠক যেন বুঝে ফেলেন ঔপন্যাসিকের অভীপ্সা। এবং আরও কৌতূহলের যে দ্বিত্ব-বিবরণের সে উপস্থাপন যে যথাযথ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোনক্রমেই সে নিশ্চয়তাতে পৌঁছতে দিতে চান না। অনিশ্চয়তার এমন ঘনঘটা বোধকরি দ্বিতীয় কোন বাংলা উপন্যাসে মিলবে না। নয় পৃষ্ঠার প্রথম অধ্যায়ে
অনিশ্চয়তাজ্ঞাপক ‘যেন’, ‘হয়তো’ এবং ‘মনে হয়’ ব্যবহৃত হয়েছে তেত্রিশ বার। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে যেখানে দাদাসাহেব কাদেরের দরবেশ হওয়ার বিত্তান্ত বলে বাড়ির শিশুদেরকে সেখানে অনিশ্চয়তাজ্ঞাপক শব্দের কোন ব্যবহার নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর অনুপ্রবেশ ঘটলে তেমনি শব্দরাশির ব্যবহাপর আবার লক্ষ করা যায় যা প্রাবল্যে রূপ নেয় কাদের-মাঝি বৌ সম্পর্কিত ব্যাপারটির ভাবনায়। সারা উপন্যাসটিতে ‘যেন’ মোট একত্রিশ বার, ‘হয়তো’ মোট একুশ বার আবার ‘মনে হয়’ মোট এগারো বার ছাড়াও অস্পষ্টতারসূচক আরও অন্যান্য শব্দ প্রয়োগিত হয়েছে যেগুলোর সামগ্রিক ফলাফলে উপন্যাসটি ক্রমে ক্রমে একটি পাঠক-নির্ভর টেক্সটে পরিণত হয়। উপন্যাসের কাহিনী সন্নিবেশে পাঠককে এত বেশিমাত্রায় স্বাধীনতা বোধ করি অন্য কোন বাংলা উপন্যাসে দেয়া হয় নি। পাঠক লক্ষ করবেন কাঁদো নদী কাঁদো-তেও মেন অনির্দেশক শব্দের প্রাচুর্য: প্রথম পরিচ্ছেদেই রয়েছে পনেরটি এবং ক্ষুদ্র তিন পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এগারটি। আর সে কারণেই বাঁশঝাড়ের যুবতীটি যে কাদেরের হাতেই খুন হয়েছে এ নিশ্চয়তা পেতে অষ্টম অধ্যায় এসে পড়ে। এবং নবম অধ্যায়ে প্রথম খোলসা করে বলা হয়:
আজ সকালে কাদের স্বীকার করেছে, সে-ই যুবতী নারীর হত্যাকারী। তবে সেটি ঠিক হত্যা নয়, একটি দুর্ঘটনা। বাঁশঝাড়ের বাইরে যুবক শিক্ষকের পদধ্বনি এবং পরে তার গলার শব্দ শুনতে পেলে হঠাৎ ভয়ে দিশেহারা হয়ে সে যুবতী নারীর গলা টিপে ধরেছিলো। তহ্যার উদ্দেশ্যে নয়, তার মুখের আওয়াজ বন্ধ করার জন্য। মুখ না ঢেকে গলা টিপে ধরেছিল কেন সে তা বলতে পারে না। (পৃ. ১৫৩)
এবং এ পর্যায়ে নতুন বিশ্লেষণে ঘটনাটি বিবৃত হয়। আপাত চলৎশক্তিহীন এ ঘটনায় বার বার নতুন নতুন মাত্রাও যুক্ত হয়ে চলে। দশম পরিচ্ছেদে দুটি তেমন সংযোজন হলো:
কাদের-যুবতী নারীর সম্পর্কে প্রেম-অনুসন্ধান এবং দ্বিতীয়টি হলো যুবতী নারীর হত্যার জন্য আরেফ আলীর নিজেকেই দায়ী করা। এভাবেই লক্ষ করা যেতে পারে যে নতুন বিবরণ ক্রমশই পূর্ববর্তী বিবরণ থেকে এ অর্থে অগ্রগামী যে তাতে প্রথম রাতের ঘটনার সাথে পরবর্তী অংশও সংযোজিত। তবে একাদশ অধ্যায়ের শেষে এমেস এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ‘কাদেরের পক্ষে দরিদ্র মাঝি বউ-এর প্রতি কোন ভাবাবেগ বোধ করা সম্ভব নয়’ (পৃ. ১৬৮)।
দ্বাদশ অধ্যায়ে শুরুর ঘটনাটির পুনর্বিন্যাস ঘটেছে এবং তা অধিকাংশত করা হয়েছে কাদেরের দৃষ্টিকোণ থেকে। ভিন্ন কৌণিক এ বিশ্লেষণে পাঠকের সামনে উপস্থিত অভিনবতর মাত্রা। কাদেরের হাতে কীভাবে যুবতী নারীর মৃত্যু হলো তার ব্যাখ্যাসহ কেন সে মৃত নারীদেহটিতে নদীতে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয় সে বিবরণও সব্যাখ্যা উপস্থিত। আর এভাবেই উপন্যাস পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায। আরেফ আলীকে কেন্দ্র করে চাঁদের অমাবস্যা-র এই যে কাহিনী নির্মিত তাতে অন্তর্লোক যেমন বিবরিত, সমাজলোকও কম চিত্রিত নয়। তাই ওয়ালীউল্লাহ্র একাগ্র সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন:
আরেফ আলীর অন্তর্অভিযাত্রা এই উপন্যাসের [চাঁদের অমাবস্যা] বিষয়। তার এই অন্তর্অভিযাত্রা কি বিশ্বাস্যতার চৌকাঠ মাড়িয়ে যায়? আমার তো মনে হয় আরেফ আলী ও তার মনোলোককে আবিষ্কার করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। এই আবিষ্কার কিছুতেই অর্জিত নয়- দেশ-মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ্রিত, সমাজসত্তার সাথে সম্পূর্ণ সংলগ্ন। 6
কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণে ‘চাঁদের অমাবস্যা’ ব্যর্থ হয় কারণ:
বাংলা ভাষার আর কোন উপন্যাসের সঙ্গে এর ঘটনা ও ঘটনা সংস্থানের, বিষয় ও প্রকরণের মিল খুঁজে না পেয়েই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা থেকে বিরত থাকেন সমালোচকরা। 7
আরও যে একটি কারণ তা হলো:
সে সময়কার অর্ধশিক্ষিত পাঠকসমাজ ‘লালসালু’র প্রতিবাদী বক্তব্য যদি বা গ্রহণ করল ‘চাঁদের অমাবস্যা’র মূল চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের অতলশায়ী গাম্ভীর্যকে হজম করার জারক তারা খুঁজে পেল না। কারণ তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকে দ্বিতীয় উপন্যাসের দূরত্ব চৌদ্দ বছরের। এই দীর্ঘ বিলম্বের অবসরে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছেন আবু রুশদ, সরদার জয়েনউদ্দীন, রশীদ করিম, শওকত ওসমান, শামসুদদীন আবুল কালাম প্রমুখ লেখকেরা। এঁরা মূলত কাহিনী নির্ভর, সরল রৈখিকও প্রথাগত উপন্যাস নির্মাণে সিদ্ধহস্ত। 8
আর উপর্যুক্ত দুটি প্রধান কারণই পাঠককূলকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল দীর্ঘদিন। যদিও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র তিনটি উপন্যাসই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজকেই চিত্রিত করেছিল, তাঁর সবশেষ উপন্যাস ‘কাঁদো নদী কাঁদো’-ও সে ধারার বহির্ভূত কিছু নয়।
সর্বশেষ এই উপন্যাসটিতে লেখক নির্দিষ্টভাবে সংখ্যা দ্বারা অধ্যায়-বিভাজন করেন নি। প্রয়োজনমত সামান্য সামান্য ফাঁকা রেখে স্টিমারযাত্রার ভেতর দিয়ে মুহাম্মাদ মুস্তফার কাহিনীটি রূপ লাভ করে। লক্ষ করা যেতে পারে প্রথম উপন্যাসেও ওয়ালীউল্লাহ্ অধ্যায় বিভাজনে একইরূপ একটি শৈলীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি প্রথাগতভাবে ষোলটি অধ্যায় ভাগ করলেও তা নিয়ে যে তিনি সন্তুষ্ট নন সেটি স্পষ্ট হয় প্রথম অধ্যায়েই। প্রথম অধ্যায়টিতেই সামান্য ফাঁকা রেখে দুটি আলাদা পরিচ্ছেদমত তৈরি করেছে, যেমনটি আরও লক্ষ করা যায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়গুলো।
‘কাঁদো নদী কাঁদো’-র প্রথম পরিচ্ছেদটি থেকেই পাঠক ইঙ্গিত পেয়ে যান একটি গল্পসূত্রের যদিও নবম পৃষ্ঠাতে এসে মূল চরিত্র মুহামামদ মুস্তফার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয় যা আরও পর মূল কাহিনীর নতুন কেটি ধারা নির্মাণ করে যা থেকে স্পষ্ট হতে থাকে প্রথম পরিচ্ছেদের গল্পসূত্রটি প্রকৃতপক্ষে মূল গল্প নির্মাণের একটি পরিপ্রেক্ষিত। পূর্ববর্তী উপন্যাস ‘চাঁদের অমাবস্যা’-তেও প্রথম পরিচ্ছেদটি একটি গল্পের সন্ধান দিয়েছিল। এবং সে প্রসঙ্গে বলা চলে প্রথম উপন্যাসেই, অন্তত কথামুখ পর্যায়ে, ঔপন্যাসিক দুর্বোধ্য ছিলেন কেননা ‘লালসালু’-র প্রথম পরিচ্ছদটি কোন গল্পের সন্ধান দেয় না। এবং সে অর্থে ‘লালসালু’-র শুরুর অংশটি অপর দুটি উপন্যাসে উন্মোচন পর্বের তুলনায় জটিলতর। তবে কাহিনী অগ্রসরণে ‘লালসালু’ দ্বিতীয়
পরিচ্ছেদ থেকে যে সহজতাতে বিস্তারিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপন্যাসে তা ক্রমশ জটিলতার। কিন্তু ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ কেন অমনোযোগী পাঠকের বিরূপতা পায় তার উৎস হয়তো এর দ্বি-কথক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করা চলে। বার বার কথক পরিবর্তন এবং কাহিনীসূত্রের অতীত-বর্তমানের পুনর্বিন্যাসকরণের ফলেই পাঠক কখনও কখনও খেই হারিয়ে ফেলেন অনবধানবশত।
উপন্যাসটির কাহিনী বিবৃত হয়েছে দুজন কথকের বয়ানে। ‘আমি’ সর্বনামের কথককে প্রথমে স্বয়ং লেখক বলেই পাঠকের মনে হয়, যদিও আসলে সে মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাতো ভাই। এই ‘আমি’ মুস্তফার সব ব্যাপারে জ্ঞাত হলেও নিজে একটি চরিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় নি। পুরো কাহিনী ‘আমি’র বয়ানে উপস্থাপিত হলেও তার সাথে ওতপ্রোতভাবে আরও যে একটি বয়ান মিশ্রিত হয়েছে সেটি তবারক ভুইঞার যার সাথে মুস্তফার যোগাযোগ ঘটেছিল কুমুরডাঙ্গায় ছোট হাকিম পদে মুস্তফার যোগদানের পর। মুস্তফার শৈশব থেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটনাংশগুলো সম্পূর্ণতই বর্ণিত হয়েছে ‘আমি’র কথনে; অন্যদিকে সে ঘটনার সাথে সংস্থাপিত কুমুরডাঙ্গা এবং তৎসলগ্ন জনপদের দীর্ঘ ইতিহাস সন্নিবিষ্ট হয়েছে তবারকের বর্ণনাতে। তবারক একবারও মুস্তফার কথা না বললেও ‘আমি’ এবং তবারক দুজনই বারে বারে সর্বজ্ঞ লেখকের অবস্থানে চলে আসে। মুস্তফার অবচেতনের বিবরণ দিতে যেয়ে আমি এবং কুমুরডাঙ্গার মানুষজনের ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটানোর কালে তবারক এমন ভূমিকায় অবতীর্ণ।
মুহাম্মদ মুস্তফার কাহিনী সমতলে প্রতিষ্ঠিত কুমুরডাঙ্গার জনপদের কাহিনী যার কেন্দুবিন্দুতে কাবাল নদীর কান্না স্থিত। নদীর সে কান্না ব্যক্তি থেকে ক্রমশ ব্যক্তি-নির্বিশেষের দিকে এগোয়। মাইনর স্কুলের শিক্ষিকা সকিনা খাতুনের শ্রবণ দিয়েই এ পর্যায়ের উদ্বোধন। তারপর তা জনান্তরে একে একে মিহির মণ্ডল, বৃদ্ধ ঈমান মিঞা, রুকুনুদ্দিনের স্ত্রী, মুদিখানার মালিক ফনু মিঞা, জনতুন বিবি, মধ্যবয়সী উকিত সুরত মিঞা, স্কুলের হেডমাস্টার, জয়নাব খাতুন হয়ে করিম বক্স পার হয়ে প্রকৃতপক্ষে পুরো জনশ্রবণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসের আলেখ্যকে ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় রূপ দিয়েছেন, যা যে কোন মহৎ সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশারি; কেননা সাহিত্য তো সর্বোপরি ব্যক্তিক কোন বিষয় নয়, তা সামগ্রিক, সর্বজনের। ‘এমন এক যৌথ শ্রবণের দিকে না এগোলে তা সকিনা খাতুনের আখ্যান’ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে উপন্যাসকে কৌশলে ওয়ালীউল্লাহ্ রক্ষা করেন। আর তারই পরিণতিতে উপন্যাসটি সমগ্র মানবজাতির প্রতি লেখকের আহ্বানের রূপক হয়ে পড়ে। যেমনটি সৈয়দ শামসুল হক নির্দেশ করেছেন: ‘যেন একটি মিনতি তিনি করেন, মানুষ তুমি মানুষের জন্যে কাঁদো’। 9
এবার অন্য একটি বিষয়ের প্রতি পাঠককে ইঙ্গিত করতে চাই। উপন্যাসে শেষ পর্যায়ে আমরা জানতে পারি খোদেজার আত্মহত্যা বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা কথক ‘আমি’ তার চাচাতো ভাইকো প্রশ্ন করেছিল সে-এ বিষয়টি নিয়ে কী ভাবে অর্থাৎ সেও কী ভাবে খোদেজা আত্মহত্যা করেছিল? অর্থাৎ এই ‘আমি’র উত্তরটি মুস্তফার কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বের। এ কারণেই কি ঔপন্যাসিক মুস্তফার আখ্যান বলার দায়িত্বটি ঐ আমি’তেই ন্যস্ত করেন? এবং সুকৌশলে ঔপস্যাসিক ‘আমি’র এই অবস্থান উপন্যাসের দীর্ঘ বর্ণনাকালে অনুল্লেখিত রাখেন। যেমনভাবে সে প্রশ্নে ‘আমি’র উত্তর ‘কি করে বলি? আমি তখন বাড়ি ছিলাম না’ (পৃ. ৩৫৫) ক্রান্তিলগ্নে উপন্যাসটিতে নতুন ইঙ্গিতের সূচনা করে যার চূড়ান্ত পরিণতি হল মুস্তফার আত্মহত্যা। শুধু তাতেই আবার ওয়ালীউল্লাহ্র মত কথাকার পরিতৃপ্ত নন। আর সে কারণেই মুস্তফার আত্মহত্যার নেপথ্যের কারণ নায়ক হিসেবে ‘আমি’ দগ্ধ।
তার প্রতি কখনো এমন ক্রোধ করিনি। ক্রোধ বোধ করেছিলাম এই দেখে যে খোদেজা আত্মহত্যা করেছে তেমন একটা বিশ্বাস হলেও মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটু অনুতাপ নয়, মৃত মেয়েটির প্রতি ঈষৎ স্নেহমমতা নয়, সামান্য বিয়োগ শোক নয়, নিদারুণ ভীতিই দেখা দিয়েছে’। হয়তো তাও সহ্য হতো যদি সরলা নিষ্পাপ খোদেজা তার চোখে একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ দুষ্ট আত্মায় পরিণত না হতো। তা কিছুতেই সহ্য হয়নি। বোধ হয় সে জন্যেই সত্য কথা বলা সম্ভব হয়নি।
তবু বলতাম যদি জানতাম সত্য না বললে কী পরিণতি হবে, যদি বুঝতাম ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা একটি অতল গহ্বরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। (পৃ. ৩৫৫)
এমন চূড়ান্ত ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে ‘কাঁদো নদী কাঁদো’-র পরিসমাপ্তি এবং নিজের ব্যক্তিক পাঠকে উদাহরণ ধরে সহজেই বলা চলে তা আসলে উপন্যাসটিতে প্রবেশের দ্বার উন্মোচক মাত্র। নদীর কান্না যেমন করে কুমুরডাঙ্গার মানুষের কানে নিরত শ্রব্য, তেমনি উপন্যাস জুড়ে খেলে যাওয়া রহস্যরাশি পাঠকের করোটিতে প্রতিধ্বনিময়, প্রতিদ্যুতিময়। আর সে ধ্বনি আর দ্যুতির উৎস অনুসন্ধানে পাঠকের নতুন অভিযাত্রা অবশ্যম্ভাবী।
মনোযোগী পাঠে লক্ষ করা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকেই বিষয়বস্তুকে যেমন সমাজ ও মানুষের ঘনিষ্ঠে রাখতে চেয়েছেন তেমনি সেসবের সন্নিবেশন ঘটিয়েছেন চিন্তাউদ্রেককারী, আলস্যনিরোধক এক আখ্যান-কাঠামোয় যার সহযোগী তার বহুমাত্রিক ও ব্যঞ্জনাময় ভাষা। নিজের শৈল্পিকবোধের পরিণতির সাথে সাথে তাঁর প্রকাশ হয়ে উঠেছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। প্রথম দুটি উপন্যাসের রচনাকালের বিশাল দূরত্ব সে দুটির বোধ ও শৈল্পীর বিপুল পার্থক্যের কারণ দ্বারা সূচিত। শেষ দুটিতে সে পার্থক্যের মাত্রা তত অধিক নয় যেহেতু ঔপন্যাসিক তাঁর বিনির্মাণগত পরিণতিতে আকাশ-পাতাল ফারাক করতে পারেন নি। তবে শেষ দুটি উপন্যাসে তিনি যে মাত্রাবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন তার তুলনা বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যে মেলা ভার। ওয়ালীউল্লাহ্্র উপন্যাস প্রসঙ্গে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) নাম যত সারম্বরেই উচ্চারিত হোক না কেন, এমন সিদ্ধান্ত অঅজ সর্বজনস্বীকৃত হওয়ার পথে যে কথাসাহিত্যের অভিরূপ অর্থচ্ছটা সম্ভবত আর কোন বাঙালি ঔপন্যাসিক সৃষ্টি করতে পারেন নি। বাংলাদেশের উপন্যাসে তো নয়ই, সমগ্র বাংলা ভাষার উপন্যাস পরিমণ্ডলেও নয়।
টীকা:
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও নিঃসঙ্গ নায়ক’, সমকালীন বাংলা সাহিত্য, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। ১৯৮৯, পৃ. ১৫৮ ↩
- রশীদ করীম, ‘সমসাময়িকের চোখে: ‘লালাসালু’, আর এক দৃষ্টিকোণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৬ ↩
- লালসালু উপন্যাসে তিন ধরনের ভাষারীতির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেছেন মনসুর মুসা তাঁর ‘লালসালু: ভাষারীতি’ প্রবন্ধে (লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ্, সম্পা. মমতাজউদ্দীন আহমদ, ঢাকা, ১৯৮৯) ↩
- আলী আনোয়ার, ‘বাংলাদেশের উপন্যাস: থীম ও ফর্ম’, সমকালীন বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮ ↩
- শিবনারায়ণ রায়, ‘ঔপন্যাসিকের বিবেক: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, শারদীয় ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫ ↩
- আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬৪ ↩
- সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ১১৭ ↩
- সৌদা আখতার, ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র চাঁদের অমাবস্যা’, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তেত্রিশ বর্ষ প্রথম, সংখ্যা কার্তিক ১৯৩৬, পৃ. ৯৪ ↩
- সৈয়দ শামসুল হক, ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: একটি শ্রদ্ধা নিবেদন’, সমকালীন বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-১৬৯ ↩