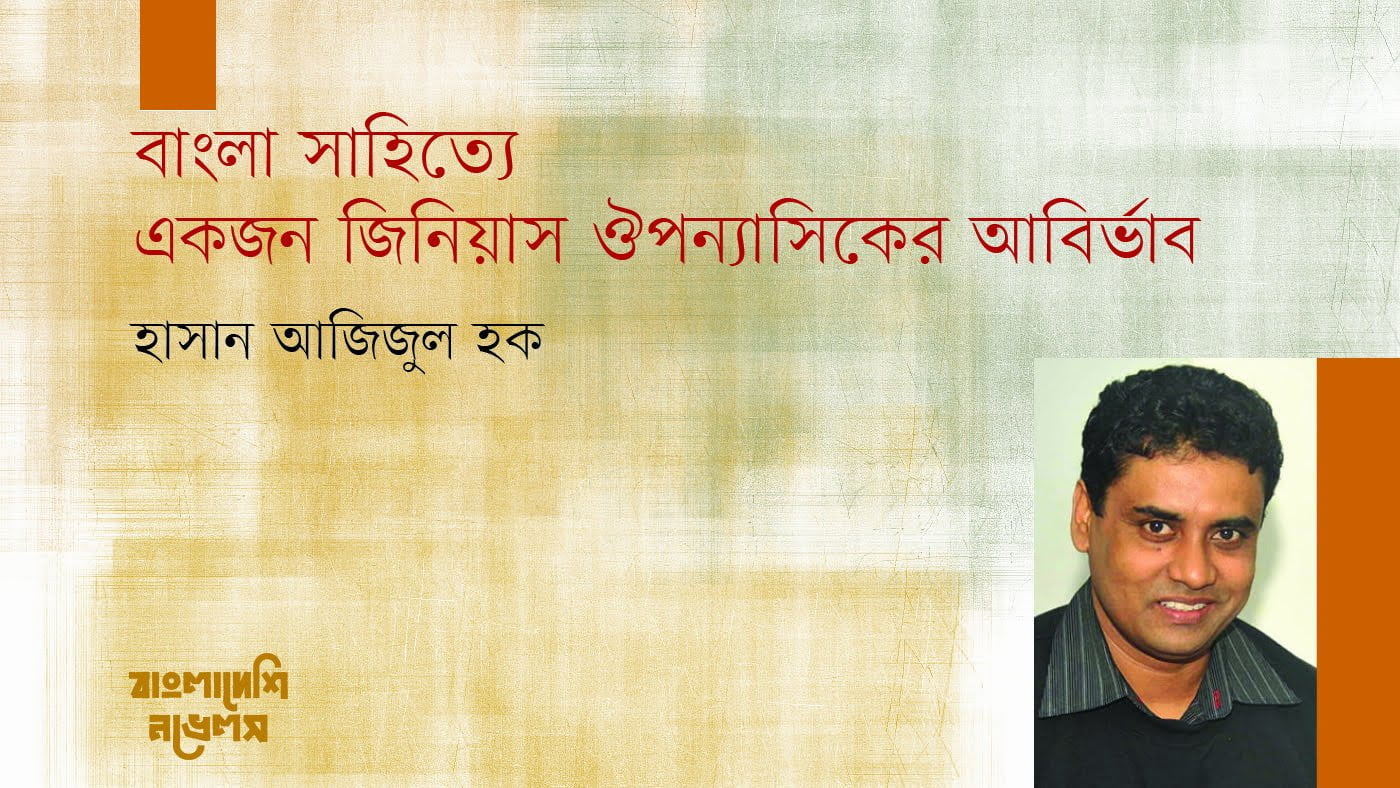হরিশংকর জলদাস (জন্ম. ১৯৫৫) বাংলাদেশের উপন্যাসে নবাগত এক নাম যদিও ঔজ্জ্বল্য আর দার্ঢ্যতায় পুষ্ট তাঁর আগমন। এই মাত্র সেদিন, ২০০৮ সালের বইমেলায় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জলপুত্র’-র আবির্ভাব এবং প্রথম সে-প্রয়াসেই বাংলাদেশের পাঠকের চিত্তজয়ী তিনি। লেখকের পারিবারিক পেশা এবং উপন্যাসের মানুষদের জীবনাচারের সাজুয্যের কারণে অদ্বৈত মল্লবর্মনের (১৯১৪-১৯৫১) নামের সাথে উচ্চারিত হতে থাকে তাঁর নাম। জলজীবী সমাজের প্রতিনিধি অগ্রগ সে-লেখকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৭)-এর জনমানুষ যেন আশ্রয় নেয় একবিংশ শতাব্দীর শূন্য দশকের সে উপন্যাসে। এ ধারাবাহিকতাতেই ২০১০ সালে দহনকাল। সেটিও মৎস্যজীবীদের জীবন-আশ্রিত। কিন্তু ঔপন্যাসিক ভুল করেন নি তাঁর নির্বাচনে। একই লেখকের কলমে একই জীবনের চিত্র যে ক্লিশে হতে বাধ্য সে উপলব্ধি থেকেই তিনি ২০১১ সালে লিখলেন ‘কসবি’ – বেশ্যাজীবন কথা। আর ২০১২ সালের বইমেলায় এসেছে ‘রামগোলাম’ – মেথরজীবনের আখ্যান।
ব্রাত্যজীবন নিয়ে লেখা হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) ‘বিদ্রোহী কৈবর্ত’ (১৯৬৯), মহাশ্বেতা দেবীর (জন্ম ১৯২৬) ‘চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর’ (১৯৮০), অভিজিৎ সেনের (জন্ম ১৯৪৫) ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ (১৯৮৫) বা গুণময় মান্নার (১৯২৫-২০১০) ‘মুটে’ (১৯৯২)-এর কথা। পেশাগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে থাকা এমন সব মানুষদের নিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮-২০০১) ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ (১৯৮১) বা ‘বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী’ও (১৯৯৭) অসামান্য সৃজন। ‘মহিষকুড়ার উপকথা’তে বাথানের শ্রমজীবীদের কথা আর ‘বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী’তে রয়েছে শূকরপালকদের জীবনচিত্র। সে-পৃথিবীর প্রধান মানুষটি তো পায়খানার গাড়ির ড্রাইভার হারান। হারানের সহযোগী চরিত্রটি? হ্যাঁ, তাঁর মেয়ে চৌদ্দ বছর বয়সী তরু, যে-কন্যার পেটে পিতা হারানের সন্তান। এই যে নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য তাঁর ইতিহাস বাংলা উপন্যাসে হ্রস্ব নয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ (১৯৫৯) উজ্জ্বল এক উদাহরণ। আবার যদি জেলেজীবনের প্রসঙ্গেই আসি, যে ঔপন্যাসিকেরা সামনে ভাসেন তাঁদের মধ্যে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬)-র জন্যে খ্যাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বা ‘কুরপালা’র (১৯৪৬) রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪-১৯৬২) বা ‘গঙ্গা’র (১৯৫৭) সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) কথা মনে পড়ে।
ডোম, হাড়ি, নিষাদ, বাগদী, কৈবর্ত, কোল, ধীবর প্রভৃতি ব্রাত্য পেশার মানুষেরা বাংলা উপন্যাসে জোরেশোরে উপস্থিত হতে শুরু করে ‘কল্লোল’-এর কাল থেকেই। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বৈষম্য বিষয়ে সচেতনতা সে-লেখকদের দৃষ্টিভ্রম কাটিয়ে তাঁদেরকে উপস্থিত করলো নিম্নবর্গের সে-মানুষদের দোরগোড়ায়। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বা শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) উপন্যাসে যে নিম্নবর্গকে দূর থেকে দার্শনিক দৃষ্টিতে অবলোকন করা হয়, কল্লোলে এসে সে-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষতা যুক্ত হলো যার পরিণতিতে কয়লাখনির শ্রমিক, রাজমিস্ত্রী, মুটে, মুচি, পতিতা প্রভৃতি শ্রমদাসেরাও এসে সামিল হয়। জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) উপন্যাসগুলো যাদের পড়া আছে তারা নিশ্চয়ই সাহিত্যে নিম্নবর্গীয়ের স্থান নিয়ে বিতর্ক তুলবেন না। অর্স্পৃশ্য সে মানুষগুলো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজে ক্রমে ক্রমে মূল জনস্রোতের সাথে একীভূত। ১৯৪৭ এর ভারত-ভাগ, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষকে তাঁর সহস্র বছরের শ্রম-বিভাজিত সমাজ থেকে অনেকটাই মুক্তি দিয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) ‘কালিন্দী’ (১৯৪০), বা ‘কবি’ (১৯৮২) বা ‘সন্দীপন পাঠশালা’ (১৯৪৬) প্রভৃতিও ছিল ভেদ-অভেদের চিত্রণ। অর্স্পশ্যতার ছ্যুৎমার্গে আটকে রাখা দলিত মানুষদের যে দীর্ঘশ্বাস তার সুগভীর ধ্বনি বাংলা উপন্যাসে শতাব্দী পেরিয়েও বর্তমান। হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস তেমন দীর্ঘশ্বাসেরই এক শীলিত, মথিত চিত্র।
‘নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন’ বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে যিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন, অথবা ছোটগল্পে নিম্নবর্ণ অন্যান্য প্রসঙ্গ বা কবিতা ও ধীবরজীবন কথা শিরোনামের গবেষণা গ্রন্থ যিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম কথাসাহিত্য প্রকাশ হিসেবে ২০০৮ সালের বইমেলায় এসেছিল ‘জলপুত্র’ – জেলেজীবনের কথা। পূর্বপুরুষের ধীবর পেশার কারণেই কি হরিশংকর জলদাস এমন নিখুঁত হতে পারেন তাঁর সৃজনে? আপাতভাবে তেমনটি মনে হলেও পরবর্তী উপন্যাস ‘কসবি’ বা ‘রামগোলাম’ প্রমাণ করেছে ঔপন্যাসিকের মেধা যদি তাঁর সহজাত সৃজনক্রিয়ায় নিয়ামক হয় এবং সাথে যদি যুক্ত হয় অধ্যবসায়ের মতো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণটি, তাহলে ‘সোনা ফলতে’ বাধ্য।
‘জলপুত্র’ শুরু হয়েছে ভুবনেশ্বরীকে নিয়ে যে কিনা অপেক্ষায় আছে পূর্বরাতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া তার স্বামী চন্দ্রমণির। উনিশ বছরের ভুবনেশ্বরীর সে অপেক্ষা যেন শেষ হওয়ার নয়। আর তাই বোধ হয় আমরা দেখি উপন্যাসের শেষেও ভুবন অপেক্ষমাণ। নিহত একমাত্র পুত্র গঙ্গাপদর লাশের সামনে বসে সে অপেক্ষা করছে গঙ্গার স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য। সে সন্তানের নাম তো গঙ্গা আগেই ঠিক করে রেখেছিল ‘বনমালী’, কেননা গঙ্গার প্রিয় মানুষ সমাজপ্রিয়-জন জয়ন্ত তো গানের কলিতেই উচ্চারণ করে ‘বনমালী তুমি পর জনমে হইও রাধা’। যে-বনমালীকে নিয়ে গঙ্গার বা ভুবন এবং গঙ্গার যৌথ স্বপ্ন ‘আঁর বড় আশা আছিল আঁর বংশর কেউ বিদ্ধান অইবো। জাইল্যাপাড়ার মাইনষে কইবো চন্দ্রমণির বাড়ির উঙ্গা পোয়া শিক্ষিত অইয়ে, ব্যালেস্টর অইয়ে’ (পৃ. ১০৪)।
জেলেপল্লীর মানুষ যে শিক্ষিত হবার নয়, ব্যারিস্টার হবার নয় সে সত্য গঙ্গা উপলব্ধি করেছে তার শৈশব থেকেই। বাবা চন্দ্রমণি প্রকৃতির আঘাত সহ্য করতে পারেনি, কিন্তু গঙ্গা পেরেছে। বারবার পেরেছে। প্রকৃতির পর তার প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সমাজের মানুষ। নিজ সম্প্রদায়ের সকলকে সুসংগঠিত করে নায্য হিস্যা আদায়ের ব্যাপারে ঐক্যমত্য তৈরি করার সফলতার কারণেই সামাজিক সে শত্রুর বিষানল গঙ্গাকে বারবার আক্রমণ করেছে। ধনবাঁশি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, শুক্কুর আলী গভীর রাতে লোক দিয়ে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে ছেড়েছে তাকে। সম্পদ আগ্রাসন এবং মুনাফা নিশ্চিত করার এই দুই প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল গঙ্গা। সরল-স্বপ্নচারীকে মাকে সাহস জগিয়েছে এই বলে, ‘মা, তুঁই নো ডরাইও। জাইল্যা অল বঅর অসহায়। হিতাবারে পথ দেখাইন্যা কেউ নাই। আঁর হিতারা ভালবাসে। আঁই হেই ভালবাসার প্রতিদান দিতাম নো না মা’ (পৃ ১১৬)।
উত্তর পতেঙ্গার ভদ্রপল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন যে জেলে পাড়ার মানুষ এই গঙ্গা তার পাড়াটি আসলে কেমন? পাড়ার মানুষরা কেমন?
‘প্রায় মাইল দুয়েক দূরে বঙ্গোপসাগরের কোলে পাড়াটি নীরক্ত হয়ে শুয়ে আছে। হিন্দু ও মুসলিম পাড়াগুলো এই জেলেপাড়াটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করছে। সেখানে তাদের জীবন চলছে সংস্কৃত পরিমণ্ডলে। কিন্তু জেলেপাড়ার জীবন গাবের রসে চুবানো। এখানে প্রাণ আছে, প্রাণবান পরিবেশ নেই। জীবন আছে, জীবনায়নের সুস্থির বাতাবরণ নেই। এদের জীবনরস ফুরিয়ে যায় পারস্পারিক গুঁতোগুতিতে। হিংসা, কুৎসা, গালিগালাজ, ছোটোখাটো মারামারি এই পাড়াটিকে জাগিয়ে রাখে সারাক্ষণ। আর আছে জেলেপাড়ার সারা গায়ে শত শতাব্দীর দারিদ্রের গভীর চিহ্ন।’ (পৃ. ১৩)
সেই জেলেসমাজের ভেতর থেকে জেগে ওঠা মানুষ গঙ্গা। যে জেলেরা বুঝেছিল শুক্কুর বা শশিভূষণের কাছ থেকে দাদন নিলেও সুদ থেকে নিজেদের মাছ রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধতা এবং শিক্ষার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই আসতে পারে মুক্তি। শিক্ষিত রামগোলাম ঐক্যবদ্ধ করার সে প্রচেষ্টাতেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিল।
কিন্তু সমাজ তো নীতি দিয়ে চলে না। আর চলে না বলেই জেলেপাড়ার সকল মানুষ সব সময়ই একইভাবে ঐক্যবদ্ধও থাকে না। বারবার ভাঙচুরের ভেতর দিয়ে সে ঐক্যকে ধরে রাখার প্রয়াস। গঙ্গার নিজের পরিবারের মানুষদের কাছ থেকেও আসে আঘাত। দুঃসম্পর্কের ভাই এর দাবিদার গোলকবিহারীর কাছ থেকে সে আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে গঙ্গা আর ওর মা ভুবনেশ্বরীর সহায় সম্পদ। পাড়ার মানুষদের সামাজিক প্রচেষ্টায় রক্ষা পায় তারা। শশিভুষণ-শুক্কুরের যে ষড়যন্ত্রে গঙ্গাপদকে হত্যা করার কথা চিন্তা করা হয় সেখানে কিন্তু হাজির জেলে-প্রতিনিধি গোপালও। গোপাল যে মিরজাফর তা সকলেই জানে, সে নিজেও কম জানে না। গোপালই বিভীষণের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেয়।
আর শিক্ষা প্রসঙ্গটি জলপুত্রতে গুরুত্বের সাথে আলোচিত। সে আলোর প্রতিভূ দীনদয়াল – সন্দীপে ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ার পর এসে উঠেছে পতেঙ্গার জেলেপাড়ায়। ‘আঁই লেয়াপড়া জানি। আন্নাগো পোলাপাইনেরে আঁই পড়াশোনা শিখায়্যুম’ (পৃ ৫৩) বলতেই জেলেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাকে পরিবারসহ গ্রামে আশ্রয় দেওয়ার। সে-আশ্রয়ের কারণে গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলোও আসছিল দরকার মতো। কিন্তু ‘জেলেসন্তানদের শিক্ষিত হওয়ার সকল স্বপ্ন-সাধ ধূলিসাৎ হয়ে গেল’ দীনদয়ালের চারিত্রিক স্খলনে। মঙ্গলীর সাথে তার শরীরক্রিয়ার উপস্থাপন করে শিক্ষাকে, শিক্ষিতকে, জেলেপাড়ার শিক্ষার আলোক সম্ভাবনাকে ঔপন্যাসিক কেন এমন অসম্মান করলেন তা অস্পষ্ট লাগে। উপন্যাস তো জীবনের হুবহু চিত্র হবে না, বরং হবে লেখকের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনের গল্পকাঠামো বিন্যাস। দীনদয়ালের এ চ্যূতি তো ‘জলপুত্র’-র গল্পকে এগুতেও খুব সাহায্য করে না। বরং যেন মনে হয় সে শিক্ষার জন্য ভুবনের আকাক্সক্ষা, যে-শিক্ষাকে আশ্রয় করে গঙ্গার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি যে শিক্ষাকে লেখক অনবধানবশত চপেটাঘাত করে ফেললেন।
গঙ্গার জেগে ওঠার মতোই দহনকাল-এর হরিদাসের জাগরণ যেন। গঙ্গা এবং হরিদাসকে আলাদা করে চিনতে পাঠকের অসুবিধে হবারই কথা। গঙ্গা যে সমাজ, যে পরিবার, যে আকাক্সক্ষার ভেতর বেড়ে ওঠে হরিদাসের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অতিরিক্ত যেটুকু ঘটেছে সেটি হলো মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গটি ঘটনাসমূহ। গঙ্গা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল জেলেসম্প্রদায়ের উপর নিপীড়নকারী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তার পেশার মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে এগুলেও শেষ পর্যন্ত গঙ্গা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। মৃত্যুকে মেনে নিতে হয়েছে তার।
রাধানাথ-বসুমতীর জ্যেষ্ঠ সন্তান হরিদাসকে নিয়ে পিতার বড়ো স্বপ্ন। শৈশবে সামান্য লেখাপড়া রাধানাথের হয়েছিল। কিন্তু সে সবের ভেতর দিয়ে সে যা অর্জন করেছিল তা হচ্ছে কঠিন এক দার্ঢ্য। যে দার্ঢ্যে বহিঃপ্রকাশ ‘আঁর পোয়াঅল কোনোদিন দইজ্যাত যাইতে নো মাছ ধাইত্যো মা-গঙ্গার ভোগত যাইতো নো’ (পৃ ৩৯)। নিজের বাবা সমুদ্্ের মারা যাওয়ার নিজ পুত্রকে সমুদ্র থেকে রক্ষা করার জন্য রাধানাথের এই দৃঢ়তা। সেই দৃঢ়তা ভেতর দিয়েই হরিদাস শৈশব-কৈশোর অতিক্রমণ। সাফল্যের সাথে যে অতিক্রমণে বাধা স্বাভাবিক এবং মোকাবিলাও প্রত্যাশিত। এবং সেভাবেই যদি বলা যায় ‘দহনকাল’-এর কাহিনি প্রথম মোটামুটি শ’খানেক পৃষ্ঠা ‘জলপুত্র’-এর কাহিনিরই ছাপ তাহলে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। গঙ্গাপদ পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, যুক্ত হয়েছিল পৈত্রিক পেশায়। হরিদাস পড়াশোনা চালিয়ে চলেছে ভর্তি হওয়ার অপেক্ষার কালে মুক্তিযুদ্ধ আসন্ন। পূর্ববর্র্তী কাহিনিতে ভিন্নতা আছে, সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু ভিন্নতা নেই প্লটে। ‘দহনকাল’ দু’বছর পরের হওয়ার কারণে প্রথম সে অংশটিতে লেখক নির্মাণ করেন আরও সুসংহতির সাথে। ‘দহনকাল’-এ যুক্ত হয় নতুনতর সামাজিক উপাদান। জেলেদের পেশাটিতে কুটিল পদক্ষেপে প্রবেশ ঘটে মুসলমানদের। জালাল নামের মানুষ যে কিনা মেম্বার সে আস্তে আস্তে গ্রাস করতে থাকে জেলেদের নৌকা, নৌকোর মাছ ধরা পেশায় নিযুক্ত করে নিজ ধর্মাবলম্বীদের।
আর এভাবেই ‘জলপুত্র’-এ একজন জলজীবী মানুষের হয়ে ওঠার যে কাহিনি সেটিই যেন অধিক পুষ্টতায়, সামগ্রিক সমাজচিত্রকে আশ্রয় করে ‘দহনকাল’-এ উপস্থিত হয়। ‘জলপুত্র’-এ কাহিনির বিভিন্ন স্থানে যে শৈথিল্য সেটি ‘দহনকাল’-এর মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব অংশটিতে অধিক দক্ষতায় হরিশংকর জলদাস পাঠককে উপহার দেন।
কিন্তু ‘দহনকাল’-এ বিপত্তি ঘটে বাকি অংশটিতে। প্রায় ষাট পৃষ্ঠা ব্যাপি সে-অংশটির কারণে উপন্যাসের প্লটের যে আঁটুনী সেটি গুঁড়িয়ে যায়। পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধ আশ্রিত ঘটনা হওয়ায় দহনকাল না হতে পারে হরিদাসের হয়ে ওঠার আখ্যান, না হয় মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণ কাহিনি। পাকিস্তানি সৈন্যরা জেলেপাড়ায় মানুষদের উপর অত্যাচার করে, তাদের নারীদের ধর্ষণ করে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। আর সেসব কাজে প্রধান সহায়ক হয় পূর্বের জালাল মেম্বার। এলাকায় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয় সে। জেলেপাড়ার উপর যে-নির্যাতন তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের স্পৃহায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে হরিদাস। তৈরি করে সকলকে। মানসিকভাবে, এবং অস্ত্রশস্ত্রগতভাবেও। এরপর পাকিস্তানিরা রাজাকারসহ একদিন প্রবেশ করলে প্রতি-আক্রমণ করে হরিদাসেরা। কেউ কেউ মারা যায়, আহত হয়। কিন্তু ‘সর্বোপরি কি হয়?’ প্রশ্নটি নিয়েই হঠাৎ করে উপন্যাসটি শেষ হয়ে যায়।
প্রধান যে চরিত্রগুলোকে আশ্রয় করে ‘দহনকাল’ শুরু থেকে এগিয়ে এসেছিল, বিস্তার লাভ করেছিল ইচাখালির জেলেপাড়া ছাড়িয়ে কাঁঠালিয়ার কৈবর্ত্য পাড়া পর্যন্ত সে বিস্তারকে অনুপুক্সক্ষতার ব্যবহার করা যায় নি উপন্যাসে। ইচাখালির জেলেরা যে জালিক, ছোটোজাতের এবং কাঁঠালিয়ার জেলেরা হালিক, স্বচ্ছল, শিক্ষিত। জেলেরা তো শুধু মুসলমানদের দ্বারা ঘৃণিত হয় নি, বর্ণহিন্দুদের দ্বারা হয়নি, হয়েছে ধনবান জেলেদের দ্বারাও। সমাজ-দ্বন্দ্বের এই জায়গাগুলোতে দহনকাল বড় স্পর্শী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক সৃজন। অথবা শুরু থেকে ‘আদাবস্যার’ নামে খ্যাত চিত্তরঞ্জন দে-র কথা ধরা যাক। খুবই প্রীতিকর এক সৃজন তিনি। পাঠককে নাড়া দিতে দিতে আদাবস্যার-হরিদাস পর্ব এগুতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আদাবস্যার ভারতে চলে যান। উপয়ান্তর না পেয়ে। ‘হরিদাসের আঁই পাড়ইয়ম। মাছ মারইন্যা জাইল্যা হইতাম দিতাম নো। পড়ালেখা শিখইন্যা জাইল্যা বানাইয়ম’ – রাধানাথের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে যিনি ঔদার্যের চূড়ান্ত তিনিই তো আদাবস্যার। জেলেপুত্র বলে হরিদাসকে তিনি ফেরত পাঠান নি, বরং হরিদাসের অক্ষরজ্ঞান ভালো থাকায় তাকে সমাদর করেছেন। বিশেষ যতœ নিয়েছেন তার পড়াশোনায়। হরিদাস ক্রমে ক্রমে স্কুলে পাস দিচ্ছে, নতুন নতুন স্বপ্ন দেখছে আর উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে যাচ্ছে। যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন চরিত্র, নতুন নতুন উপকাহিনি। সুধীর নামের দুষ্ট বালকটির প্রসঙ্গ, অথবা ভালো মনের ভূপালের কথা। এই ভূপালই তো কলেজে পড়ার সময়, যখন কিনা হরিদাস এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে কর্মহীন, তখন গ্রামে এসেছে, হরিদাসকে দেশ সম্পর্কে, দেশের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। আর গ্রামের পাগল খু-উ বুইজ্যা। সে বারবার এসেছে পাগলামির ভেতরেও মঙ্গলের পক্ষ অবলম্বন করেছে এবং যুদ্ধ চলাকালে হরিদাসদের সাথে থেকে লড়াই করেছে। অন্যদিকে হরিদাসের মা বসুমতীর বাবা হরবাঁশিও অংশটিও বড়ো আন্তরিক।
কিন্তু এমন আন্তরিক চিত্রণের মধ্যেও ‘জলপুত্র’ ও ‘দহনকাল’ যেন উৎরাতে পারে না। জলদাসের জীবনবিত্তের যে রূপ প্রথম উপন্যাসটিতে পাঠক পান তার পৌনঃপুনিকতা দ্বিতীয়তে পাঠককে মর্মাহত করে। আবার চরিত্রের অপূর্ণতা বা ঘটনার অপ্রয়োজনীয়তাও উপন্যাস দুটির পাঠককে ক্লিষ্ট করে। ‘জলপুত্র’-এর মাগন্যার কথাই ধরা যাক। কুৎসিত সে চরিত্রটি আসলে গঙ্গাপদর পিসতুতো ভাই। মাগন্যা অন্যায় করে, বারবার করে। এবং সবশেষে যে অন্যায়টি সেটি মারাত্মক। সে না জানিয়ে ভুবনের বোনের সম্প্রতি বিবাহিতা কন্যাকে নিয়ে এসে ধর্ষণের পরিকল্পনা করে। কিন্তু সে উপ-কাহিনিটি মূল কাহিনিটিকে কোনভাবেই সহযোগিতা করে নি। এমনকি সেটি শেষও হয়েছে অযৌক্তিকভাবে।
কাহিনি ও প্লটের সাফল্য-অসাফল্যের এই চড়াই উৎরাইয়ের মাঝে একটি শক্তিশালী বুনোনের উপন্যাস কসবি। প্রতিটি চরিত্রের যৌক্তিকতা নিয়ে, প্রতিটি উপ-কাহিনির প্রয়োজন নিশ্চিত করে মূল কাহিনি দাড়িয়ে আছে উপন্যাসাটিতে। আর সে-সবের ভেতর আছে বঞ্চনার চিত্র ও ইতিহাস। আছে দ্রোহের স্ফূরণ। আর সে সব কারণেই জলজীবনের চিত্র না হয়েও ‘কসবি’ হয়ে উঠেছে ‘জলদাস’ লেখক হরিশংকরের প্রথম অসাধারণ কীর্তি যার অধিকতর সফল প্রয়াস ‘রামগোলাম’।
‘কসবি’-র কাহিনি চট্টগ্রামের পতিতালয় সাহেবপাড়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সাহেবপাড়ার নামীদামী পতিতা দেবযানীকে দিয়ে উপন্যাস শুরু। রূপবর্তী দেবযানীর আগে ছলা-কলায় পারদর্শী অন্য উল্লেখযোগ্য রূপজীবী হলো পদ্মাবর্তী। এ যে দেবযানীর সময়, উপন্যাস কিন্তু শেষ হয়েছে সে সময়ের অনেক পরে গিয়ে, আর মাঝে মাঝে প্রবিষ্ট হয়েছে সেকালেরও বহু আগের কথা। আর এভাবেই কাহিনিটি পুষ্ট হয়েছে, যুক্তি-বুদ্ধি আশ্রিত হয়েছে অগ্রসর হয়েছে এবং একটি সুসংহত পরিণতি পেয়েছে।
উপন্যাসটি আপাতভাবে সতেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যদিও সেগুলোর কোনোকোনোটির ভেতর একাধিক অধ্যায়ের উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মোটামুটি একশোচল্লিশ পৃষ্ঠার উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায়টি মাত্র সাড়ে চার পৃষ্ঠায় – যার ভেতরে সাহেবপাড়ার দেবযানী এবং তার দালাল সেলিম ও সেলিমের বাল্যবন্ধু সেকান্দার হোসেন, যে কিনা কলেজের অধ্যক্ষ – এই তিনজন উপস্থিত। তিন জনের সে ক্ষুদ্র অধ্যায়টি একটি পতিতাপল্লির দৈনন্দিন চিত্রকে মূর্ত করে।
দ্বিতীয় অধ্যায়ে জানা যায় পল্লির ভূতপূর্ব সুন্দরী পতিতা পদ্মাবতীর কথা। পদ্মাবতীর বাঁধা খদ্দের ছিল আবদুল জব্বার সদাগর। পরোপকারী সওদাগর নামাজ-রোজা-যাকাত কিছুই বাদ যায় না। বউ-সন্তানদের প্রতিও দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ। ‘কিন্তু একজনের ব্যাপারে সে কারো সঙ্গে, কিছুর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নয়। সে পদ্মাবতী। পদ্মাবতী বেশ্যা’ (পৃ ১৬)। এ সওদাগরই কিন্তু পদ্মাবতীর কাল হয় – সে কাহিনি যদিও এখানেই উচ্চারিত হয় না। প্রেক্ষাপটটি নির্মাণ করেই ঔপন্যাসিক সরে যান অন্য প্রাসঙ্গিকতা সৃজনে। আর কালদুষ্ট পদ্মাবতীর কথা আমরা শুনতে পারি আরও অনেক পরে, যখন দেবযানী কালু সর্দারের আওতার বাইরে মোহিনী সর্দারনির আশ্রয়ে, আর পদ্মাবতীকে মোহিনী নিয়ে আসে দেবযানীর দেখভাল করার জন্য। তেমন একটা সময়েই পদ্মাবতী বলেছিল সওদাগর তাকে না পেয়ে পেয়ে, অপমানিত বোধ করতে করতে একদিন কেমন করে একটি গরম পানি ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল তার সুন্দর মুখমণ্ডল। সে প্রসঙ্গ আমরা জেনেছি উপন্যাসের চৌদ্দতম অধ্যায়ে।
সাহেবপাড়ার দেবযানীকে ছুঁয়ে, পদ্মাবতীকে ছুঁয়ে হরিশংকর গিয়ে পৌঁছেন নরসিংদীর বীরপুরের জেলোপাড়ায়। যে পাড়ার মানুষ শৈলেশ দাস যে কিনা স্ত্রী যশোদার সাথে ঝগড়া করতে করতে একসময় পরিবার ত্যাগ করে ট্রেনে উঠে চলে যায় চট্টগামে। সাহেবপাড়ার কাছে সদরঘাটে বিষণ্ণ মনে বসে থাকার সময় তার সাক্ষাৎ ঘটে সাহেবপাড়ার দালাল শামছুর সাথের। পরিচয় হলে জানা যায় শামছুর বাড়িও নরসিংদীতে। শিবপুরের শামছু বীরপুরের শৈলেসকে ফেরত পাঠায় ছিল বাড়িতে।
অদ্ভুত নৈপূণ্যতায় লেখক সব উপকাহিনিগুলোকে গ্রন্থন করেছেন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। সেগুলোকে বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করে ইতিহাস ঘনিষ্ট করেছেন এবং কাহিনির অভিনবত্ব আনেন, যুক্ত করেন নতুন মাত্রা। চতুর্থ অধ্যায়ে সাহেবপাড়ার অতীত যুক্ত করে সে মাত্রাকে তুঙ্গ করেছেন হরিশংকর। তিনি কল্পিত মানুষদেরকেই আশ্রয় করে কাহিনি বানিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসকে ছুঁয়ে দিয়ে যেন পাঠককে দিয়েছেন নতুন এক স্বাদ, যেমনটি ‘রামগোলাম’-এও দেখা যায়। মেথরদের ইতিহাস রচনা না করেও সে ইতিহাসের স্পর্শ দিয়েছেন তিনি, কেমন এক নতুনত্ব এসে পাঠকে শক্তিশালী করেছে।
সাহেবপাড়ার বয়স তিনশ বছর। তার আগে তো সেটি ছিল জেলেপাড়া। ১৭৬০ সালের ১৫ অক্টোবর মীর কাসিমের কাছ থেকে চট্টগ্রাম কেড়ে নেয় ইংরেজরা। পরের বছরের ১৫ জানুয়ারি চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা। আর শতাব্দী শেষে দিকে চট্টগ্রাম পোর্টে এসে ভিড়েছিল মার্টিনেজ নামের এক জাহাজ। জাহাজের নাকি ম্যাগ্রিজ নারী সঙ্গ পেতে ক্ষুধার্তের মতো এসে ঢুকলো পূর্বপাড়া নামে জেলেপাড়াতে। বলাৎকার করলো রাইচরণের বউ জটিলাকে। বউ ধর্ষিতা হবার অপরাধে সমাজ রাইচরণকে একঘরে করলো। অন্নাভাবে উপায়হীন জটিলা বেশ্যাবৃত্তিকেই আশ্রয় করলো ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় হিসেবে। লেখকের ভাষায়,
‘জটিলাকে দিয়ে যে-কাজ শুরু হয়েছিল, সেটা থেকে গেল না। প্রথমে চুপিসারে পরে প্রকাশ্যে এই বৃত্তি চলতে থাকল। ধীরে ধীরে এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে সংক্রমিত হল এই পেশা। সাদা চামড়ার নাবিকরা কখনো জোর করে কখনো বা অর্থের বিনিময়ে দেহের ক্ষুধা মিটাতে লাগল। এইভাবে একদিন ক্ষুদ্র এই জেলেপাড়াটি বেশ্যাপল্লীতে রূপান্তরিত হল; পূর্বপাড়ার নাম সাহেবপাড়া হয়ে গেল।’ (পৃ. ৩৬)
এরপর লেখক সাধারণীকরণ করেছেন বেশ্যাপল্লির সামগ্রিক অবস্থানকে। খদ্দেরদের কষ্ট, তাদের আচরণের কথা। আর তেমন প্রসঙ্গেই এসেছে মোহিনীর যে কিনা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী মাসি, যার অধীনে দেবযানীর অবস্থান। এলো কালু সর্দারের কথা। আর এভাবেই নির্মিত হতে থাকলো মোহিনী-কালু সর্দার দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিত।
পঞ্চম অধ্যায়ে এসে যেখানে শৈলেস-শামছুর অনাবিল বন্ধুত্ব সেখানেই কিন্তু এসেছে শৈলেসের মেয়ে কৃষ্ণার দেবযানী হওয়ার কথা। একসময় তরুণী কৃষ্ণা পড়লো স্টেশনে ফল বিক্রেতা তপন দত্তের লোভী চোখে। দ্রুতই পৌঁছে গেল তপন কৃষ্ণার শরীর অবধি। অসৎ বন্ধু মফজলের প্ররোচনায় ‘একরাতে কৃষ্ণা তপনের সঙ্গে পালাল’ (পৃ ৪৬)। চট্টগ্রামে সোনালি বোর্ডিং-এ কয়েক দিন ভোগের পর পালাল তপন আর ‘শামছু কৃষ্ণাকে নিয়ে গিয়ে কালু সর্দারের কাছে কড়া দামে বেচে দিল’ (পৃ ৪৭)। কালু সর্দারের মা শৈলবালার দায়িত্ব নতুন মেয়েদের পোষ মানানো। আর এ ঘটনার ভেতর দিয়ে ক্রমেই চিত্রিত হতে থাকলো পতিতাপল্লিতে মেয়েদের আগমন, জীবনযাপনসহ সামগ্রিক জগতটি। সে-জগতেও যে স্বপ্নের বীজ বোনা হয় তাও অলিখিত থাকে না। তেমন একটি স্বপ্নের বুনন চলে পতিতা মমতাজের মস্তিষ্কে। তার স্বপ্ন তার মেয়েকে নিয়ে, ‘মাইয়াটার বাপের ঠিকানা নাই। হেরে আমি লেখাপড়া শিখাইয়া একটা ঠিকানা দিমু, লেখাপড়ার ঠিকানা। হে একদিন বড় অইবো। এই পাড়া থেইক্যা বাইর অইয়া ভদ্দর লোকদের মাইয়ার মতো জীবন কাডাইবো’ (পৃ ৬৮)- এই স্বপ্নই পূরণের ত্রাতা হিসেবেই পতিতাপল্লিতে কৈলাসের জন্ম। ‘কৈলাশ জন্মানোর পর মোহিনীর বেলেল্লাপনা অনেকটা কমে এল। তার মধ্যে যে বেপরোয়া ভাব ছিল, যে উদ্দামতা ছিল – ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল’ (পৃ ৯৪)। কৈলাস কর্ণফুলির ওপারের পাচহাডি এলাকা জলধির মরিয়ম একাডেমি থেকে এসএসসি পাস করে ফিরে এলো সাহেবপাড়ায়। ক’বছর পর নির্মলার সাথে বিয়েও দিল তাকে। নাতনিও হলো। আর যা হলো তা হচ্ছে, ‘সাহেবপাড়ার নষ্টামি কৈলাসকে স্পর্শ করে না, মেয়েদের কামুক কটাক্ষ তাকে কাহিল করে না। পতিতাদের খোলা শরীর আর চটুল কথায় কৈলাস বিচলিত হয় না। দুপুরের দিকে এই পাড়ায় যত জারজ-সন্তান আছে, তাদের প্রায় সবাইকে নিয়ে মন্দিরচত্বরে বসে কৈলাস। তাদের সঙ্গে গল্প করে, রবীন্দ্র-নজরুলের কথা বলে; মার্টিন লুথার কিং-আরে কাহিনি শোনায় তাদের। রামায়ণ-মহাভারতের বীরযোদ্ধাদের গল্প শোনায়, শোনায় কারবালার বিষাদময় মৃত্যুর করুণ কাহিনি। এই অবোধ সন্তানরা কৈলাসের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কৈলাসের কাঁধে থাকে কাপুড়ে ব্যাগ। সেই ব্যাগে থাকে রামসুন্দর বসাকের আদি বাল্যশিক্ষা। কোনো কোনো দিন সেই ঝোলা থেকে বই বের করে বালক-বালিকাদের হাতে দিয়ে বলে, ‘পড় – অ, আ, ই, ঈ…’ (পৃ. ৯৫)।
সেই কৈলাস যেন জাগাতে চাইলো পতিতাপাড়ার মানুষদের। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে চাইলো, তাদের শিশুদের শিক্ষার আলো দিতে চাইলো। আর এ সব চাইলো বলেই সংঘাত হয়ে উঠলো অনিবার্য। বেশি আঘাত লাগলো পাড়ার সর্দার কালুর গায়ে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল যেন দু’জন। নির্বিরোধ চুপচাপ কৈলাস হুংকার দিয়ে উঠলো যেন। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারলো না শেষ অবধি। আর তাই কালু সর্দারের হাতেই খুন হতে হলো তাকে। অসাধারণ দক্ষতায় সামগ্রিক এ চিত্রটিকে রূপ দিয়েছেন হরিশংকর। সে-কাহিনি নির্মাণে দেবযানীর অংশটি মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে যথেষ্ট।
দেবযানীর যখন সিফিলিস হয়ে মরো মরো অবস্থা, তখন কালু সর্দার তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে পল্লি থেকে। রাস্তা থেকে ঐ দেবযানীকে তুলে আনার ব্যবস্থা করে মোহিনী। শহরের ডাক্তারের সাথে সুস্থ করে তোলে তাকে। নতুন করে সেরা সুন্দরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় দেবযানী। এরপর আস্তে আস্তে শুরু হয় দেবযানীর প্রতিহিংসা গ্রহণের পালা। খুঁজে বের করে শামছুকে যে কিনা হোটেল থেকে কৃষ্ণাকে ‘মা ডেকে’, ‘বাসায় নিয়ে আশ্রয় দেওয়ার ছুঁতো করে’ নিয়ে গিয়ে কালু সর্দারের কাছে বিক্রি করেছিল। খুঁজে বের করে তপনকে যে ছিল প্রেমিকবেশী শরীর-ভোক্তা। আর সবশেষে হত্যা করে কালু সর্দারকে।
কৈলাসকে হত্যা করার পর থেকে তো কালু সর্দার উধাও। পুলিশ তাকে ধরতে পারে নি। কিন্তু সবশেষে শিউলি নামে এক পতিতা জেনে ফেলে কালুর আস্তানা। এরপর পুলিশ যখন কালুকে ধরে নিয়ে ফিরছিল, পতিতারা স্লোগান দিচ্ছিল ‘শৈলমাগির বিচার চাই, কালু সর্দারের ফাসি চাই’, আর তা শুনে মোহিনী ভাবছিল ‘কার বিচার? কিসের বিচার’? ‘হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এলে কালু একদিন বেরিয়ে আসবে। পৃথিবী টাকার গোলাম’ ইত্যাদি তখন জনতার ভিড়ে নেমে যায় দেবযানীও। কালু সর্দারকে জড়িয়ে ধরার আড়ালে তার পেটে ঢুকিয়ে দেয় ছোরা। মৃত্যু হয় কালুর।
শিল্প-নৈপূণ্যের প্রশ্নে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ‘কসবি’ লেখকের প্রথম দুটি উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত, পরিশীলিত। ‘জলদাস’ অধ্যায় বিন্যাসে অসঙ্গতি, সকল চরিত্রের উপস্থিতির যৌক্তিকতার অভাবে দুষ্ট, যেমনভাবে ‘দহনকাল’-এ মুক্তিযুদ্ধ পর্বের ব্যাপকতা ইত্যাদির কারণে উপন্যাস দুটি এলিয়ে পরেছে। ‘কসবি’-তে হরিশংকর সেই এলানো ভাব থেকে তাঁর রচনাকে রক্ষা করেছেন সুকৌশলে, দক্ষভাবে। আর কৌশল ও দক্ষতার ভেতর দিয়ে মানবমন এবং মানব জীবনের মর্মস্পর্শী চিত্র নির্মিত হয়েছে ‘রামগোলাম’।
‘রামগোলাম’ শুরু হয় নাম চরিত্রের মানুষটিকে দিয়েই। চট্টগ্রামের চারটি মেথরপট্টির মানুষদের সর্দার মান্যবর গুরুচরণের নাতি রামগোলাম তার এমন নামের পেছনের রহস্য জানতে ব্যাকুল। আর সে ব্যাকুলতা নিরসনে সর্দারের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আজন্ম ক্রোধ আর হতাশা। ‘হিন্দুসমাজে আমরা অচ্ছুত। বড় অপবিত্র জাতি আমরা। আমাদের ছোঁয়া তো দূরের কথা, আমাদের ছায়া মাড়ালেও হিন্দুরা, বামুনরা অপবিত্র হয়ে যায়। … তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও আমাদের ঘেন্না করে, মানুষ ভাবে না। জন্তুর মতো আচরণ করে আমাদের সাথে’ (পৃ ১১)। হিন্দু হরিজনদের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মের নামে নীচতর পেশার মানুষ হিসাবে অগ্রাহ্য করার এই ভাবনাই গুরুচরণকে ক্লান্ত করে, একই সাথে অপরাধ বোধ জন্মায় রামগোলামের ভেতরের যা সঞ্চারিত পাঠকহৃদয়েও।
গুরুচরণের দীর্ঘলালিত এমন ক্ষোভ থেকেই সিদ্ধান্ত আসে নাতির নাম হবে ‘রামগোলাম’, যে নামের ভেতরে লুকিয়ে আছে হিন্দুদের দশ অবতারের প্রধান রামচন্দ্রের নাম এবং একই সাথে ‘মুসলমানি’ শব্দ ‘গোলাম’। দাদুর ধারণা এই নাম তার নাতিকে বাঁচিয়ে দেবে লাথি-কিল থেকে, ‘শালা-বানচোৎ’ গালি থেকে। কিন্তু দুইশ পৃষ্ঠা দীর্ঘ উপন্যাসটির শেষে পাঠক আবিষ্কার করেন রামগোলামের মুক্তি হয় নি। বরং নিজ সমাজের নিজ পেশার মানুষদের মুক্তির স্বপক্ষে কাজ করতে যেয়ে মিথ্যে মামলায় চৌদ্দ বছর জেল হয় তার। জেল শেষে ফিরিঙ্গি বাজারের হরিজন পল্লিতে ফিরে আসে সে, অপেক্ষায় থাকে হরিজন মুক্তির আন্দোলনে নতুন নেতার আগমনের।
একুশটি অধ্যায়ে বিশ্লিষ্ট ‘রামগোলাম’ উপন্যাসটি একুশতমটি কিন্তু খুব ছোট – জেল ফেরত রামগোলামের প্রত্যাশার কথা। বাকি বিশটি জুড়ে রয়েছে তিন প্রজন্মের কথা। গুরুচরণ-শিউচরণ-রামগোলাম। তিন প্রজন্মের মানুষরাই কিন্তু এক সাথে দুই রুমের একই ঘরে বাস করে মেথর পল্লিতে। কাজ করে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। আঠারো পেরোলেই তারা চাকরিতে যায়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। কাজও সবার প্রায় একই রকমের – ময়লা সাফ। কারও জন্যে পায়খানা পরিষ্কারের, কারো ভাগে রাস্তা-ঘাটের ময়লা। কেউ সেখানে ময়লা গাড়ির ড্রাইভার। বড় হৃদয়বান সে ড্রাইভার, যার নাম গুরুচরণ। পুরো ধাঙড় সম্প্রদায়কে আগলে রাখে সে। সম্প্রদায়ের প্রতিটি নাগরিক তাকে মান্য করে।
‘রামগোলাম’-এর কাহিনি সেই গুরুচরণকে আশ্রয় করে। অথবা বলা যায় উপন্যাসটি আসলে রামগোলামকে আশ্রয় করে যে কিনা প্রকৃতপক্ষে গুরুচরণেরই প্রতিভূ। অথবা আরও সহজ করে বলা যায় এটি আসলে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নয় বরং গুরুচরণ বা রামগোলামের পরিবারিক পেশা মেথরবৃত্তির সাথে যুক্ত সকল মানুষকে আশ্রয় করে। আর সে কারণেই পুরো উপন্যাস জুড়ে ঐ মানুষদের নিয়ে হাহাকার যেন কিছুতেই থামে না।
সে হাহাকার আর অসহায়ত্বের মাঝে কেউ কেউ জেগে ওঠে ব্যক্তিগত পরিচয়ে, লোকচক্ষুকে আড়াল করতে। কেউ কেউ সামষ্টিক জাগরণকে মুখ্য মনে করে। সকলকে সাথে নিয়ে সামাজিক যে লড়াই সে লড়াইয়ের প্রধান পুরুষ গুরুচরণ, যে কিনা ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় নি কখনো। আর তেমন বোধকেই আশ্রয় করে দলের নেতা হয়েছিল মেথরপল্লির প্রথম এসএসসি পাস করা ছেলে রামগোলাম। কর্পোরেশনে ছোট জমাদারের চাকরি নিয়েও সে বিক্রিত হয়ে যায় নি, অর্থ এবং লোভ তাকে তার সামাজিক দায়িত্ব থেকেও বিকৃত করতে পারেনি। চেতনার শাসন এমন তীক্ষ্ম ছিল যে চৌদ্দ বছরের জেল জীবনও তাকে খর্ব করে নি।
জেলটা হয়েছে কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের পেশাকে নিরাপদ রাখতে। কর্পোরেশন চেয়েছে মেথরদের বাইরের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধকে এমন কাজে সম্পৃক্ত করতে কিন্তু বাধা দিয়েছে ধাঙড়রাই। তাদের বক্তব্য একজন ধাঙড়ের যেহেতু অন্য পেশায় যোগদানের কোনো সুযোগ নেই, তাই কেন ধাঙড়দের পেশায় অন্যরা ভাগ বসাবে। ঘুষ নিয়ে অন্যলোকদের চাকরিতে অনুপ্রবেশের পথে অন্তরায় ছিল রামগোলাম আর তার পেছনে হাজার পাঁচেক হরিজন। চাকুরিপ্রার্থী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধদের মুখোমুখি হয়ে পড়লো হরিজনরা। চেঁচামেচি, হট্টগোল, গালাগালি, যেয়ে ঠেকলো মারামারিতে। খুন হলো যোগেশ। কাজটা করলো কর্পোরেশনের বড় সাহেব। কিন্তু কাজটার জন্য ঐ বড় সাহেবই থানা থেকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিলো রামগোলামকে। হত্যা মামলার আসামী হলো রামগোলাম, আর হত্যার পরিকল্পনাকারী বড় সাহেব আব্দুস সালাম হলো খুনের প্রত্যক্ষদর্শী।
এই যে খুনের মতো চূড়ান্ত ঘটনায় পৌঁছানো এর ক্ষেত্রটাই তৈরি হয়েছে সারা উপন্যাস জুড়ে। সামাজিক অর্স্পৃশ্যতার অভিশাপের সাথে বারবার যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন অনুষঙ্গ। ধাঙড়পল্লির স্কুলে ধাঙড়দের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাদের মন্দিরের পাশে কসাইখানা করা হয়েছে, যেখান থেকে জবাই করা গরু-খাসির রক্তে ভেসে গেছে ধাঙড়দের চিরায়ত বিশ্বাস। এভাবেই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের কোপানলে পড়েছে অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত সাধারণ চিন্তা-ভাবনার এই মানুষেরা। শত সহস্র বছরের সামাজিক ক্লেদ স্বাধীন বাংলাদেশে এসে নতুন আঙ্গিকে ধাঙড়দের উপর চড়াও হয়েছে।
বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে সামাজিক এই অনাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মেথর রাধা আর শক্তিচন্দ্র ভিন্ন কলোনিতে বাসা ভাড়া নিয়েছিল। পোশাক পরিচ্ছদে প্রমাণ করতে আপ্রাণ হলো দু’জনে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি ওদের। আসন্ন সন্তান প্রসবা রাধাকে বাড়িওয়ালা জহিরউদ্দিন ঘেন্নায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তার আসন্ন মুত্যুও কোনো প্রতিবেশি বাঙালি হিন্দু মুসলমানকে ‘মানুষ’ বানাতে পারে নি।
এই যে সামাজিক অনাচার তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দরকার সামাজিক লড়াই। রামগোলাম হয়তো এমন ইঙ্গিতই দেয়। আর তাই মধ্যবিত্তের নাকি-কান্নার উপন্যাস না হয়ে, এটি হয়ে পড়ে দার্ঢ্যতার এই চূড়ান্ত চিত্রণ। যে দার্ঢ্যরে আপাত জয় নেই, কিন্তু জয়ের প্রত্যাশা আছে। সামষ্টিক সে লড়াই তীব্র বলেই গুরুচরণের মৃত্যু হলে তাকে ‘মেথর’ বলে হিন্দুদের শ্মশানে পোড়াতে দিতে বাধে। আর সে বাধার জয় হয় ঐক্যবদ্ধতার ভেতর দিয়েই। চতুর্থ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক যে ধারাবাহিক দণ্ড মেথরদের ওপর তুলে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে যুথবদ্ধ শক্তিতে বেরিয়ে আসছে যেন রামচরণের মত গোলামেরা।
অসাধারণ সুখপাঠ্য এ উপন্যাসের কয়েকটি দুর্বলতার দিকে এবার চোখ ফেরাতে চাই। যথার্থ বিবেচনা করলে সেগুলোর কিছু কিছু পরবর্তী সংস্করণে এড়ানোও সম্ভব বলে মনে হয়। প্রথম যে বৈশিষ্ট্যচ্যুতি পাঠকের চোখে পড়বে সেটি হলো মেথরদের ভাষা। যে ভাষায় বঙ্গদেশে আশ্রিত হরিজনরা আলাপন করে থাকে তেমনটি হুবহু গ্রহণ করা না হলেও সেটির কাছাকাছি একটি ভাষাকে ধারণ করা ঔপন্যাসিকের কর্তব্য ছিল বলে মনে হয়। যদিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ‘জলপুত্র’তে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা যথার্থভাবে ব্যবহার করায় উপন্যাসটির অনেক সংলাপ চট্টগ্রামের বাইরের পাঠকদের কাছে অনেকখানিই দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছিল ধারণা করা যেতে পারে। আর তেমন সব কারণেই লেখক ‘দহনকাল’ উপন্যাসে সে-ভাষার ব্যবহার কমিয়ে আনেন। আর হয়তো গড়পড়তা বাংলাভাষী পাঠকের কাছে দুষ্পাঠ্য হবে আশঙ্কায় হরিশংকর ‘রামগোলাম’ উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু স্কুলশিক্ষক কুতুবউদ্দীনের মুখে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা বসাতে কিন্তু ঔপন্যাসিক পশ্চাৎপদ হননি। ভাষা ব্যবহারের লেখকের এমন সিদ্ধান্তের কারণে মেথর সমাজের সকলের মুখের ভাষাই হয়ে যায় প্রমিত চলিত ভাষা। যার কারণে শিক্ষিত রামগোলামের সাথে অশিক্ষিত সহজনদের ভাষাগত ভিন্নতা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আর তাই যখন এসএসসি পাস রামগোলামের কথাবার্তার প্রশংসা করে বলা হয় ‘তুমি তো ভালো গুছিয়ে কথা বল’ তখন তা পাঠকের কাছে মিথ্যে ভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। অ-স্বাভাবিক এমন কথ্যভাষার পরিমিতিতে যখন কুতুবউদ্দীনের মতো মননশীল শিক্ষিত মানুষ বলেন, ’নদী তো তোমরা চিন… কী সোন্দর হানি তার …’ (পৃ ১১৫) তখন কুতুবউদ্দীনের শিক্ষা এবং মননশীলতাকেই চপেটাঘাত করা হয় যেন।
এবার আসছি কাহিনির সময়কাল প্রসঙ্গে। উপন্যাসের শুরুতে গুরুচরণ যখন সর্দারের পদে আসীন, তখন যেন মনে হচ্ছিল সময়টা ভারত বিভাগের পরপরই। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে সেটি মুক্তিযুদ্ধের কাল অতিক্রম করেছে। করে অনেক বেশি দূর পর্যন্ত এসে গেছে যেন। কেননা শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনও বলা হচ্ছে (পৃ ১০২)। এবং এরও পরে অনেক দিন পার হয়ে তবেই না চূড়ান্ত বিদ্রোহের ঘটনা যার পরিণতিতে রামগোলামের চৌদ্দ বছর জেল। এ ব্যাপারে ঔপন্যাসিকের খানিকটা অনবধান কাজ করছে কি? এ ছাড়া, আমরা তো প্রথম থেকে এমন ধারণাতেই ছিলাম যে মেথরদের অন্য পেশায় যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে রাধিকা ‘ভালো চাকরি’ (পৃ ১৪৯) পেলো কিভাবে? তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি রামগোলামের বাবা শিউচরণ এবং মা চাঁপারানীর স্বপ্ন সম্ভাবনা এবং স্বপ্নভঙ্গের ইঙ্গিত। চাঁপারানীর স্বপ্ন ছিল ‘আমি কিন্তু আমার রামগোপালকে পড়াব। স্কুলে ভর্তি করাব তাকে …’ (পৃ ২৬)। সে স্বপ্ন ভাঙতে থাকে যখন শিউচরণ বলে, ‘ওরা পড়তে দেবে না রামগোলামকে। ওরা মেথরদের পড়তে দেয় না…’ (পৃ ২৮)। অসাধারণ এক চিত্র। নবাগত শিশুকে নিয়ে পিতামাতার ঐতিহাসিক স্বপ্নযাত্রা যেন। কিন্তু একটা ফাঁক রয়ে গেছে এখানে। চাঁপারানীও তো ঐ পল্লিরই মানুষ, সেও তো ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছে পড়াশোনার অধিকার নেই মেথরদের। তাহলে সে অনধিকারের কথা শোনার পর বিস্মিত কেন সে?
বাংলাদেশের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের ছড়াছড়ি। সে জীবনের বহুধা বৈশিষ্ট্য আমাদের উপন্যাস জগৎকে শাসন করে। মধ্যবিত্তের সামাজিক জঞ্জাল, ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব, মানসিক খিন্নতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসে প্রবল প্রতাপশালী। সে প্রতাপে ‘কাঁদো নদী কাঁদো’, ‘পুষ্প, বৃক্ষ এবং বৃহঙ্গ পুরাণ’, ‘ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল’, ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’, বা ‘উড়ুক্কু’ প্রভৃতির লেখকরা সংযোজন করেছেন অভিনবত্বের নিশান। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধকে আশ্রয় করে ‘বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ’, ‘জীবন আমার বোন’, প্রভৃতির লেখকেরা সংযোজন ঘটান নতুন কাহিনির। ‘কাঞ্চনগ্রাম’, ‘সংশপ্তক’, ‘আগুনপাখি’, ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’, ‘খোয়াবনামা’, ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’, ‘মধ্যাহ্ন’, ‘নূরজাহান’ বা ‘জীবনের রৌদ্রে উড়েছিলো কয়েকটি ধূলিকণা’র কথাকাররা বাংলাদেশের উপন্যাসকে নিয়ে যান এক আকাঙ্ক্ষিত উচ্চতায়। ‘কবে পোহাবে বিভারবী’, ‘পদ্মা মেঘনা যমুনা’, ‘অজগর’ বা ‘নুহূলের মনচিত্র’ উচ্চামার্গীয় হয়েও অনাদৃত। এমন সময়েই মনন আর বোধের উচ্চমার্গেই হরিশংকর জলদাসের আবির্ভাব। আর তার ফলেই সম্ভব হয় বাংলাদেশে রচিত বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিককালের অন্যতম এক কারিগরকে নতুন অবলোকনে।
যদিও বর্তমান আলোচকের ভাবনা এই যে জলপুত্র-কে খানিকটা পরিশীলন করলে সেটিও সহজেই হতে পারে রামগোলাম মার্গের একটি মহৎ সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বাংলা ভাষার প্রধান দুই কথাকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। তাদের সকল উপন্যাসই নতুন নতুন মুদ্রণে নতুনতর রূপ পেয়ে বর্তমান সংস্করণে এসেছে। নতুন সংস্করণের জন্য ত্রুটিমুক্তির এই চর্চা বর্তমানের বাংলাদেশে খুব বেশি লক্ষিত নয়। কিন্তু এটি সন্দেহাতীত যে এমন পরিশীলনের মাধ্যমেই সাহিত্য অধিক মর্যাদাবান হয়ে ওঠে। ‘রামগোলাম’ বা ‘কসবি’ বা ‘দহনকাল’-এর লেখক ইতোমধ্যেই সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের জগতে উচ্চারিত একটি নাম। তাঁর প্রথম উপন্যাসও আদরযোগ্যতায় উচ্চারিত হোক এমনটিই ভবিতব্যের প্রত্যাশা।
খুব যত্ন করে খেয়াল করলে স্পষ্ট হয় ‘জলপুত্র’-র সাথে ‘রামগোলাম’-এর সাজুয্য। রামগোলামের জন্ম থেকে বিদ্রোহ হয়ে জেল পর্যন্ত সাম্প্রতিক যে উপন্যাসটি উপস্থাপিত। অন্যদিকে ‘জলপুত্র’-র গঙ্গাপদর ক্ষেত্রেও অনুরূপ। তবে রাম জেল থেকে বেড়িয়ে নতুন স্বপ্ন দেখে বিপ্লবের, আর গঙ্গার মৃত্যুর পর সে স্বপ্ন গঙ্গার অনাগত পুত্র বনমালীর প্রতিক্ষায়। রাম যেমন মেথর পল্লির মধ্যে শিক্ষিত হয়ে জেগে উঠেছিল তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের অধিকার ও সম্মান রক্ষায়, গঙ্গাও কিন্তু তেমনই। গঙ্গার মা’র স্বপ্ন ছিল ‘গঙ্গাপদ পড়বে, সমুদ্রে মাছ মারতে যাবে না কখনো’ (পৃ ১২)। একটু মাথা উঁচু হলেই বাপের সাথে জেলেপাড়ায় সকল কিশোরেরা মাছ ধরা পেশায় যুক্ত হওয়ার যে শত সহস্র বছরের প্রচল, গঙ্গার মা বিধবা ভুবনেশ্বরী কিন্তু সেখান থেকে তার পুত্রকে বের করে আনতে চেয়েছে। ‘হিন্দু-মুসলমানের সন্তানদের মতো সেও শিক্ষিত হয়ে বাপের অপমৃত্যুর দাগ ভুবনেশ্বরীর হৃদয় থেকে মুছে দেবে’ ভাবলেও বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। গঙ্গার পড়াশোনা বেশি এগোয় নি সামাজিক বহুধা প্রতিবন্ধকের কারণে। গঙ্গা শেষ পর্যন্ত তার পারিবারিক পেশাতেই যুক্ত ছিল। ভিন্নতা এই যে সে পেশায় যে বঞ্চনা তা থেকে জেলেদেরকে বের করে আনতে চেয়েছে গঙ্গা, তার সামান্য শিক্ষা গঙ্গাকে যে এই চেতনায় স্থাপন করেছে সেটা রীতিমত প্রীতিকর। দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষদের জন্য আত্ম নিবেদনের এমন চেতনা নির্মাণের প্রশ্নে ‘জলপুত্র’ থেকে ‘রামগোলাম’ অনেক বেশি সংহত।
সংহতির যে অভাব ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, তেমনটিই হয়তো স্বাভাবিক। প্রথম উপন্যাসে বোধ ও ব্যাপ্তির প্রাচুর্য্য থাকতেও সেগুলোকে সংহতভাবে উপস্থাপনে ঘাটতি ছিল। অধ্যায় বিভাজনে যৌক্তিকতা কাঙ্ক্ষিত হয় নি সর্বত্র। প্লট নির্মাণে শৈথিল্যের কারণে কাহিনি মার খেয়েছে, প্রত্যাশিতভাবে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেননি ঔপন্যাসিক।
উলগুলানের যে তেজে একসময় সাঁওতাল সমাজ জাগরিত হয়েছিল তেমন তেজেই বলীয়ান রামগোলাম বা কৈলাস বা হরিদাস বা গঙ্গাপদ। গঙ্গাপদ বা কৈলাস নিহত হলেও হরিশংকরের হরিদাস আর রামগোলাম কিন্তু জীবিত। পাকিস্তানি সৈন্যদের উপর আক্রমণ করেও হরিদাস বেঁচে আছে। চৌদ্দ বছর জেল খাটলেও জীবিত রামগোলাম। হরিজনপল্লীকে জাগিয়ে তোলার তার আকৈশোর স্বপ্নও জীবিত। ধীবর জন-প্রতিনিধি গঙ্গাপদ বা কসবিপুত্র কৈলাস মৃত্যুকে এড়াতে না পারলেও রামগোলাম পারে। তবে লক্ষণীয় উভয় ক্ষেত্রেই যে বিষয়টি চলমান তা হলো তাদের সকলের চেতনা-সমাজকে, সমাজের মানুষ শৃঙ্খল থেকে মুক্তির স্বপ্নকে তাদের সকলের মধ্যে প্রবহমান রেখেছিল হরিশংকর জলদাস।